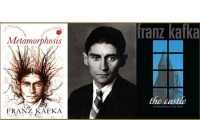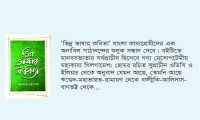সাময়িকী
১৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি
প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
এম. আবদুল আলীম
মাইকেল মধুসূদন দত্ত / জন্ম : ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪, মৃত্যু : ২৯ জুন ১৮৭৩
‘মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্গাতা। এই আধুনিকতা তাঁর রচনা, কাব্যভাবনা ও কাব্য আঙ্গিক- উভয় দিকেই সমভাবে সঞ্চারিত।’ -মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের এ উক্তি যথার্থ। কারণ, ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শতাব্দী সঞ্চিত জড়ত্বে প্রবল আঘাত হেনে’ মধুসূদন আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মূলত, তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শেই বাংলা সাহিত্যের ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে ওঠে। বিস্ময়কর প্রতিভা বলতে যা বোঝায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাই। পুরনো ও গতানুগতিক চিন্তা-চেতনায় তাঁর আস্থা ছিল না। দেশি-বিদেশি সাহিত্য গভীরভাবে আত্মস্থ করে নিজের প্রতিভাকে শানিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে সাহিত্যের বিচিত্র আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন করতে পেরেছেন, তেমনি নিত্য-নতুন সৃষ্টিপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন বাংলা সাহিত্যকে। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনা; পত্রকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, আধুনিক নাটক প্রবর্তন এবং সর্বোপরি কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকে আমূল পরিবর্তন সাধন- এ সবই মধুসূদন-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভা সম্পর্কে বলতে গেলে কতকগুলো বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রথমেই আসে মধুসূদন-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, সেকালের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার চালচিত্র- এরপর আসে সমকালীন যুগমানস, তাঁর চিন্তাচেতনা ও সাহিত্যবোধের নানা দিক- আসে পূর্বতন সাহিত্যের বিষয়-আঙ্গিক থেকে মধুসূদনের সাহিত্য-চেতনার মাত্রাগত পার্থক্য পর্যালোচনা।
বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ ও জীবন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তখনকার জনজীবন ছিল ‘আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শান্ত্রবচনের’ গ-ির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেকালে ‘চ-ীম-পে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমতো পাড়া-পড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগে-দ্বেষে, গল্প-গুজবে, তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা তিন-চার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে’ (কালান্তর)। মধ্যযুগেও এ অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ ‘বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি।... সেই জন্য পল্লীর চণ্ডীম-পেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর’ (কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জনজীবনের মতো সাহিত্যের বিষয়ও ছিল স্থবির এবং ধর্মীয় বাতাবরণে দেব-দেবীর মহিমাকীর্তনের মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণর পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, মিশ্র-ভাষারীতির কাব্য- সবই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কিছুটা আধুনিকতার স্ফুরণ ঘটলেও মধুসূদন পূর্ববর্তী কাব্যভাবনা ছিল- ‘আশ্চর্য জঙ্গমতায় আচ্ছন্ন, গতিবেগ নিশ্চল ও অসুস্থ।’
মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের কাল ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তরের কাল। তখন ‘য়্যুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি’ ভারতবাসীর ‘স্থবির মনের উপর প্রবল আঘাত হেনে’ তাদের জাগিয়ে তুলেছিল। যুগমানসের এই পরিবর্তন মধুসূদনের কবিচিত্তে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদী চেতনায় পরিশুদ্ধ হয়ে তিনি দেব-দেবীনির্ভর চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে মানব-মাহিমার জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন। মধ্যযুগের অনুকরণপ্রিয়তায় গা না ভাসিয়ে মৌলিক চিন্তার অভিনিবেশ ঘটালেন। তাঁর এ-প্রবণতার শ্রেষ্ঠ ফসল মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)। এ-কাব্য বাংলা সাহিত্যে অর্গলমুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। ‘এই কাব্যই আধুনিকতার প্রবাহ পথ মুক্ত করে দেয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজীবনের যৌবনাবেগে পূর্ণশক্তি ও অনুপম শ্রীধারণ করে প্রথম প্রকাশ পায়’। ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-মেঘনাদকেই শ্রেষ্ঠরূপে প্রকাশ করেছেন। ‘এখানকার রাবণ বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রাবণ নয়, রামও হিন্দুর ভগবান নয়, কবিমানস প্রসূত সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র।’ কবিচিন্তার প্রাখর্যে ধর্মীয় চরিত্রগুলো মানবীয় সত্তায় উদ্ভাসিত হলো। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলো মর্ত্যরে রক্ত-মাংসের মানুষরূপে গড়ে উঠেছে। এভাবে মধুসূদন তাঁর কাব্যচিন্তায় নতুনত্ব আনয়ন করেছেন।
দেশপ্রেম মধুসূদনের চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে আমরা লক্ষ করি রাজস্তুতি। কবি ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা পরিদৃষ্ট হলেও মধুসূদনের কাব্যেই সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধ তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণকে দিয়ে তিনি উচ্চারণ করিয়েছেন স্বদেশপ্রেমের বজ্রনির্ঘোষ বাণী : ‘জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে/ যে ডরে ভীরু সে মৃঢ়; শত ধিক তারে?’ তাঁর হৃদয়ের গহীন তলদেশ থেকে উৎসারিত দেশপ্রেমের নিদর্শন চতুর্দশপদী কবিতাবলী। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাংলার প্রকৃতি এবং আবহমান কালের বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি অবলম্বন করে এসব কবিতায় মধুসূদন ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রবাসে অবস্থানকালে মাতৃভূমির মায়ায় তাঁর মন ডুকরে কেঁদে উঠেছে : ‘যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে;/ চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ সদনে;/ সে দেশে জন্ম মম, জননী ভারতী।’ বাল্যকাল থেকে যে নদীর স্নেহের পরশে তিনি বেড়ে উঠেছেন প্রবাস জীবনে সেই কপোতাক্ষ নদের বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁর সংবেদনশীল মন আবেগ-ভারাক্রান্ত হয়েছে : ‘বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,/ কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?/ দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি, জন্মভূূমি স্তনে।’
নারী-প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের কবিভাবনায় গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যেই প্রথম নারী চরিত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ঘটেছে। তাঁর লেখনীর প্রাখর্যে অন্তঃপুরবাসী নারী বীরাঙ্গনা মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। মেঘনাদ-পতœী প্রমীলার উক্তিতে এর মূর্ত প্রকাশ : ‘দানব-নন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ,/ রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী;/ আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে?’ মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা, মন্দোদরী; ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধা, বীরাঙ্গনা কাব্যের তারা, শকুন্তলা, কৈকেয়ী ও জনা ব্যক্তিত্বের প্রভায় উজ্জ্বল। যুক্তিবাদ মধুসূদনের কবিভাবনার উল্লেখযোগ্য দিক। মধ্যযুগের কবিদের চিন্তায় যুক্তিবাদের প্রকাশ ঘটে নি, ইউরোপীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মধুসূদন বাংলা কাব্য-ভাবনায় যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদা বিনা যুক্তিতে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ মেনে নিতে পারে নি। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্য বিভীষণকে যুক্তিবাণে ক্ষত-বিক্ষত করে বলেছে : ‘তুমি কোন ধর্মমতে কহ দাসে শুনি/ জ্ঞাতিত্ব, ভাতৃত্ব, জাতি এ সকলে দিলা/ জলাঞ্জলি?’ বস্তুত, মধুসূদনের কবিসত্তায় অভিনবত্বের যে প্রকাশ, তাতে রয়েছে ধর্মীয় চেতনার পরিবর্তে মানব-মহিমার জয়গান- রয়েছে স্বাজাত্যবোধ, ব্যক্তিসচেতনতা এবং যুক্তিবাদ।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো কাব্যভাষার উৎকর্ষ সাধন। তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের ভাষায় ছিল ওজস্বী গুণের অভাব। গভীর ভাব এবং শৌর্যবীর্যের স্ফূর্তি তাতে ঘটে নি। মধুসূদন মেধার প্রাখর্যে, সুনিপুণ শব্দ প্রয়োগকৌশলে তাঁর কাব্যভাষায় গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রাচীন যুগের কাব্যে আমরা পাই : ‘আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা।’ মধ্যযুগে পাই : ‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান।/ কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥’ মধুসূদন লিখেছেন : ‘ধবল নামেতে গিরি, হিমাদ্রির শিরে/ অভ্রভেদী দেব আত্মা, ভীষণ দর্শন,/ সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল।’ মধুসূদন কাব্যভাষায় কেবল গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি, শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন : ‘মধুসূদন শব্দশিল্পী; শব্দাড়ম্বর দ্বারা তিনি কাব্যের মধ্যে একটি গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন।’ তাঁর কাব্যে এ উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণিত হয় : ‘ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত/ তাহে শোভে রতœরাজি মানস সরসে/ সরস কমলকুল বিকশিত যথা।’
ঝিমিয়ে পড়া বাংলা কবিতার ভাষায় মধুসূদন গাম্ভীর্য এনেছেন। ব্যঞ্জনাবাহী নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি এবং অভিনব স্টাইলে বাক্যগঠন করে তিনি কাব্যের ভাষায় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিত করে বাংলা কাব্যভাষাকে তিনি মনোহর রূপমাধুর্য দান করেছেন। এর আগে বাংলা কাব্যে অলঙ্কার ব্যবহারে চমৎকারিত্ব ছিল না। কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে অনুপ্রাস ব্যবহারের দৃষ্টান্ত : ‘সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন/ সহস্র মুকুটখানি কিরীটভূষণ।’ কিন্তু মধুসূদন যখন লেখেন : ‘লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে’। কিংবা: যথা তরু তীক্ষèশর সরস শরীরে/ বাজিলে কাঁদে নীরবে।’ -তখন ধ্বনির মুহুর্মুহু ব্যঞ্জনায় অনুপ্রাস নতুনরূপে প্রতিভাত হয়। এছাড়া উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারে মধুসূদন বাংলা কবিতার ভাষাকে ঋদ্ধ করেছেন।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান অমিত্রাক্ষর ছন্দ। বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল পয়ার-ত্রিপদীর একটানা বৈচিত্র্যহীন সুর। এতে চৌদ্দ মাত্রার দুটো পঙ্ক্তির মধ্যে ভাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ঘটতো। মধুসূদন পয়ারের দুই চরণের নিগড় ভেঙে যতিপাতের স্বাধীনতা এনে ভাবের প্রবহমানতাকে বাড়িয়ে দিলেন। ইংরেজি ব্ল্যাঙ্কভার্স-এর আদলে তিনি বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগের কবিতায় পাওয়া যায় : ‘যে সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ।/ সেই সীতা বনে যান দেখে সর্বজন ॥’ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে আমরা পাই : ‘সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি/ বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে/ অকালে, কহ, হে দেবী অমৃত-ভাষিণী,/ কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,/ পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি/ রাঘবারি?’
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে মধুসূদন বাংলা কাব্যের ভাবজীবনের জড়তা মোচন করেছেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন’ সাধিত হয়। এ-ছন্দের মাধ্যমেই তিনি বাংলা ছন্দের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এর বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে পরবর্তীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ গৈরিশ ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবহমান পয়ার ও মুক্তক ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতিপাতের স্বাধীনতা, মিল বর্জন ও ভাবের প্রবহমানতা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় : “মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত ছাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিল ‘পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইল’র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কি আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ যতির উর্মিলতা।”
বাংলা কাব্যে প্রথম আধুনিক গীতিকবিতা রচনার কৃতিত্বও মধুসূদনের। ইতালিয়ান কবি পেত্রার্কার সনেটের আদলে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তাঁর গীতিরসসিক্ত মনের যথার্থ স্বরূপ ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরগুপ্ত বাংলা কাব্যে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার প্রথম পুরোহিত হলেও সার্থক গীতিকবিতা তিনি রচনা করতে পারেন নি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পক্ষেই প্রথম সার্থক গীতিকবিতা রচনা সম্ভব হয়েছে। ‘ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা রচনার অগ্রদূত হইলেও গীতিকবিতার প্রকৃষ্ট গুণ তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। পরবর্তী কবি মধুসূদনের মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।’ সনেটের মতো ‘আত্মবিলাপ’ কবিতাতেও তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আত্মবেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তিনি লিখেছেন : ‘আশার ছলনে ভুলি/ কি ফল লভিনু হায়/ তাই ভাবি মনে?/ জীবনপ্রবাহ বহি/ কালসিন্ধু পানে ধায়।/ ফিরাব কেমনে?’
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কব্যের বিষয় ও আঙ্গিকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে তাতে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটান। তাঁর প্রতিভার স্পর্শেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও নতুনত্বের জোয়ার এসেছে। মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন : ‘তিনিই (মধুসূদন) সর্বপ্রথম বাঙালির ভাবজীবনের জাড্য মোচন করিয়াছিলেন। কবিমানসের মুক্তি সাধনে তিনিই প্রথম বিজয়ী বীর।’ বাস্তবিকই মধুসূদন ছিলেন বাঙালির ভাবজীবনের জাড্য মোচনকারী প্রথম সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন জন্মবিদ্রোহী। সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ছিল তাঁর জীবনের মূল প্রত্যয়। দুরন্ত আবেগে তিনি প্রথম জীবনেই ভেঙেছিলেন পরিবার, সমাজ ও ধর্মের অর্গল। বিদ্রোহীর অগ্নিমূর্তি ধারণ করেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও আবির্ভূত হন এবং নিত্য-নতুন সৃষ্টিপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ করেন বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের পুরনো রীতি ও কাঠামো ভেঙে চুরমার করে তার উপর নির্মাণ করেন আধুনিকতার নতুন সৌধ। সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকে অভিনবত্ব সৃষ্টির জন্যই তিনি লাভ করেছেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নান্দীকরের মুকুট।
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-

আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ