উপ-সম্পাদকীয়
আমলাতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধিত্বের মেরুকরণ
ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ
আধুনিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আমলাতন্ত্র। মূলত তাদের মেধা, কর্মতৎপরতা, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। উন্নয়নশীল দেশের সমাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধনে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন। আমলারা আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন, মন্ত্রীদের সহায়তা করেন এবং প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করেন। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আমলাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ আমলাদের ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। রিচার্ড ক্রসম্যান যথার্থই বলেছেন, ‘অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।’ নিয়ন্ত্রিত আমলা ক্ষেত্রসমূহ- ১. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ : রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হলো বাহ্যিকভাবে আমলাদের নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আইনসভা, মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে আয়োজিত নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। ২. আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ : আইনসভা কয়েকটি উপায়ে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- ক্স আইনসভা কর্তৃক প্রশ্ন, অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ক্স আইনসভায় বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ক্স অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং সংস্থার মাধ্যমে, প্রস্তাবিত নতুন আইনের শুনানির মাধ্যমে, প্রচলিত আইনের সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ। এভাবে আইনসভা আমলা ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ চর্চা করতে পারে।
কেবল উন্নয়নই জনপ্রিয়তার মাপকাঠি নয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ও বাকস্বাধীনতা খর্ব করে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের জন্য। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বিজাতীয় ভাষাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার ওপরে স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার আন্দোলনের মাধ্যমে যে জনসমর্থন গড়ে ওঠা শুরু হয়েছিল, তার মূলে ছিল স্বায়ত্তশাসন এবং ওপরে আলোচিত দুটি বিষয়ই ছিল মুখ্য। তারই ভিত্তিতে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং পরে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ।
কাজেই প্রকৃত গণতন্ত্র এবং ভোটের অধিকার বাংলাদেশিদের জাতীয় চেতনার মূল। বাংলাদেশিরা বিশ্বের অন্যতম গণতন্ত্রকামী এবং রাজনীতি-সচেতন জাতি। সে কারণেই আমরা গণতন্ত্র যেমন চাই, তেমনি চাই সর্বক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন ও সুশাসন। আমরা আমাদের রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এ দুটোই চাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্ট মেম্বাররা সরকার গঠন করে থাকেন। এ ধরনের সরকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অভিহিত। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার আপনা আপনি তৈরি হতে পারে না। রাজনীতিকদেরই তা তৈরি করে নিতে হয়। তাদের দায়িত্ব থাকে সরকার পরিচালনার। আর তা সঠিকভাবে করতে গেলে আমলাতন্ত্র দক্ষ হাতে নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করেন, অনেকে ক্ষমতার দাপটও দেখান। তারা সব সময় চান আলাদা গুরুত্ব, আলাদা মর্যাদা, বাড়তি সুযোগ-সুবিধা। এই বাড়তি মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে তাদের অনেকেই সাধারণ মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলেন। অথচ তাদের সেটা করার কথা না। জনসেবা, জনকল্যাণ, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করাই যাদের একমাত্র কাজ হওয়ার কথা। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বা রাষ্ট্রের এসব স্থায়ী কর্মচারীদের ইংরেজিতে বলা হয়Ñ পাবলিক সার্ভেন্ট বা জনগণের সেবক। তাদের একমাত্র কাজ জনগণের সেবা করা। কারণ তাদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের করের টাকায়।
রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদক্ষতা ও দুর্বলতার সুযোগে আমলাতন্ত্র সকল সরকারি কর্মকান্ডে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। এই করোনা সংকটকালে সরকারি আমলাদের মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে জনপ্রতিনিধিরা অভিযোগও করেছেন। মাঠপর্যায়ে আমলাতন্ত্রের একপক্ষীয় কাজ গণতন্ত্রের জন্য পরিপূরক নয়। আমলাতন্ত্রের কারণে মন্ত্রী, এমপি, সিটি মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়ররা অনেক সময় নিজের কর্মীদের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এটি নিঃসন্দেহে জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতা।
সাম্প্রতিক সময়ে পৌরসভার মেয়র যাদের মধ্যে ৯০ ভাগই আওয়ামী লীগের তারা এখন বলছেন যে আমলারা তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাচ্ছে। পৌরসভায় যে প্রধান নির্বাহী পদ তৈরি করা হচ্ছে তার বিরোধিতা করছেন পৌরসভার মেয়ররা। উপজেলার চেয়ারম্যানরাও ইতিমধ্যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, জেলায় জেলায় এমপিদের সঙ্গে জেলা প্রশাসক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবদের বিরোধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে আমলাবিরোধী একটি রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটতে যাচ্ছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।
জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিভিল সার্ভিসের বাইরের পেশাজীবীদের ওপর সরকারের এক ধরনের অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ এটি। এমনকি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপরও আস্থা রাখছে না সরকার। তাদের পর্যবেক্ষণ বলছে, এ চর্চা যে আমলাতন্ত্রের বাইরে যোগ্য লোক না পাওয়ার কারণে ঘটছে, তা নয়। এটি ঘটছে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব ও অযোগ্যদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতের কারণে। আমাদের রাষ্ট্র এখন আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানের শাসনামলে আমরা আমলাতন্ত্রের অধীনে ছিলাম। আমরা আন্দোলন করেছিলাম যেন জনগণের প্রতিনিধি সবকিছু পরিচালনা করেন। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসনামলের আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ করতেন না। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ সেই আমলাতন্ত্রের জট বহাল থাকলে জাতির জন্য হতাশাজনক বটে। সুশাসন ও নির্বাচনে সৎ, যোগ্য প্রার্থীর জন্য হাহাকার করছি আমরা দেড় যুগ ধরে। সে জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি নিয়ে আর্তনাদেরও শেষ নেই।
শুধু ত্রুটিমুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সরকারই সুশাসনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যত ভালো নির্বাচনই হোক, অযোগ্য, অদক্ষ ও অসৎ আমলাদের দিয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। সেই রাষ্ট্র থেকে জনগণ সুশাসন পেতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকার কখনই আমলানির্ভর নয়। সামরিক বা আধাসামরিক সরকার যারা বাহুবলে বলীয়ান কিন্তু জনসমর্থনের দিক থেকে দুর্বল, তেমন সরকার চায় নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কর্মকর্তাদের নিজেদের পক্ষে রাখতে। কর্মকর্তাদের বশে রাখার অন্যতম উপায় ঘন ঘন পদোন্নতি দেওয়া। আজ বাংলাদেশে উঁচু পদমর্যাদার কর্মকর্তার সংখ্যা বিপুল। পদ নেই, তবু প্রমোশন। গণতন্ত্রের জন্যও জিনিসটি ক্ষতিকর। নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যত অর্থনৈতিক উন্নয়নই করুক, জনগণের কল্যাণ করতে পারবে না। বাংলাদেশে যে হারে কর্মকর্তাদের দলীয়করণ হচ্ছে এবং অপ্রয়োজনে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে তাতে প্রশাসন ভেঙে পড়তে পারে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বড়মাপের একজন নেতা হয়েও যেভাবে জনগণের কাছে গিয়ে, কৃষকের চিন্তায় ঢুকে গিয়ে রাজনীতি করে গেছেন সেভাবে এখন কজন মানুষ রাজনীতিতে আসছেন বা জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পেরেছেন। বেশিরভাগ যারা রাজনীতিতে আসছে বা আসতে চাচ্ছে তাদের মধ্যে আগে থেকেই ক্ষমতার একটি লোভ কাজ করছে এবং অন্যদিকে যারা এমপি ও মন্ত্রিত্ব লাভ করছেন তাদের অধিকাংশ উচ্চবিত্ত ও বণিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এখানে ক্ষমতার শ্রেণি-বিভাগও কল্পনা করা যেতে পারে। কেউ কেউ চাচ্ছে পেশিশক্তি আবার কেউ কেউ চাচ্ছে অর্থনৈতিক শক্তি! আর যার ফলে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনীতিক সরকার ও আমলাদের মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণে জনগণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। কি আমলা, কি রাজনীতিবিদ, কি জনপ্রতিনিধি সবার লক্ষ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একমাত্র দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে মনোযোগী হওয়া। এক্ষেত্রে কে বড়, কে ছোট-তা বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তি স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে সব আমলা ও জনপ্রতিনিধিদের মনে প্রাণে লালন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই জটিলতামুক্ত একটি উদার, গণতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী, জনপ্রশাসনবান্ধব ইতিবাচক রাষ্ট্র গঠনে নিবেদিত হয়ে সবাইকে কাজ করে যেতে হবে।
তাই আসুন মেরুকরণ নয়, আমরা সবাই মিলেমিশে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে একটি সুন্দর, সাবলীল ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে সচেষ্ট হই। এর অন্যথা হলে গণতন্ত্র বিকাশের পথে আসবে প্রতিবন্ধকতা। গণতন্ত্র হবে ভূলুণ্ঠিত। মুখথুবড়ে পড়বে অংশগ্রহণ প্রতিনিধিত্বের সংস্কৃতি। সুতরাং দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, মেরুকরণ নয় বা পক্ষ প্রতিপক্ষের বাকবিতন্ডা নয় বরং সমস্ত বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয় ও নির্ভরতার সংস্কৃতিতে ভর দিয়ে সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে উন্নয়ন প্রত্যয়টিকে আরাধ্য বিষয় ভাবতে হবে। এর বিকল্প অন্য কোন চিন্তা মাথায় নিতে যাওয়ার অপর নাম হবে জাতিকে আত্মহননের দিকে ধাবিত করা। কাজেই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা দিয়ে কোন অনর্থের দিকে পা বাড়ানো নেহায়েত বোকামি ছাড়া কিছু নয়।
পরিশেষে আমলা, রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধি সবপক্ষকে দেশমাতৃকার সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। সেই উপলব্ধির জাগরণ ঘটুক- এটাই আজ সাধারণের প্রত্যাশা।
[লেখক : সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি]
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
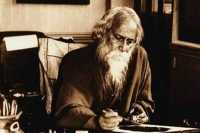
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম







