উপ-সম্পাদকীয়
কেমন ছিল কৃষ্ণের চরিত্র?
নান্টু রায়

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ মানুষের, বিশেষত বাংলাদেশের সব সনাতন ধর্মাবলম্বীর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং- এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশে কৃষ্ণের উপাসনা সবচেয়ে বেশি। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, ঘরে ঘরে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, মুখে মুখে কৃষ্ণগীতি, সবার মুখে কৃষ্ণনাম। কারও গায়ে কৃষ্ণনামাবলি, কারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেউ কৃষ্ণনাম না করে কোথাও যাত্রা করেন না; কেউ কৃষ্ণনাম না লিখে কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী ‘জয় রাধে কৃষ্ণ’ না বলে ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনলে ‘রাধে কৃষ্ণ!’ বলে আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখি পুষলে তাকে ‘রাধে কৃষ্ণ’ নাম শেখাই। কৃষ্ণ এদেশে এমনই সর্বব্যাপক।
কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং- এই যদি বাঙালির বিশ্বাস, তবে সব সময়ে কৃষ্ণ আরাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সব সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার চেয়ে মানুষের মঙ্গল আর কী আছে? কিন্তু এরা ভগবানকে কী রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর- ননী-মাখন চুরি করে খেতেন; কৈশোরে পারদারিক- অসংখ্য পতিব্রতার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করেছেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ- বঞ্চনা করে দ্রোণ প্রভৃতির প্রাণহরণ করেছিলেন! ভগবৎচরিত কি এমন? যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, যার থেকে সব ধরনের শুদ্ধি, যার নামে অশুদ্ধি ও পাপ দূর হয়, মানবদেহ ধারণ করে এসমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবৎচরিত্রে শোভা পায়?
ভগবৎ চরিত্রের এমন কল্পনায় ভারতবর্ষে পাপস্রোতই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরাণ-ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে-সব পাপ-উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত- সবই অমূলক কুনাট্য ছাড়া কিছু নয়। এসব বাদ দিলে বাকি যা থাকে, তা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ। তার মত সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নেই। কোন দেশীয় ইতিহাসে না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু তার মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করব। তবে এখন সমাতন ধর্মের আলোচনা প্রবল হচ্ছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছে। ধর্ম-আন্দোলনের এই প্রবলতার সময়ে কৃষ্ণ চরিত্রের সবিস্তার আলোচনা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণ জীবন যথাযথভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। আমরা জানি, মানুষের কতকগুলো শক্তি আছে। এই শক্তিগুলোর নাম বৃত্তি। সেগুলোর অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। এগুলোই মনুষ্যত্বের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা, বৃত্তিগুলোর পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেই সুখ। এই সমস্ত বৃত্তির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এমন আদর্শ মানুষ নেই বললেই চলে। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথম অবস্থায় তার আদর্শ হতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মানুষেরা অর্থাৎ যাদের গুণাধিক্য দেখে ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায় অথবা যাদের দেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হতে পারেন। এজন্য যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টানদের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। হিন্দুশাস্ত্রে এমন আদর্শের অনেক উদাহরণ আছে। জনক প্রভৃতি রাজর্ষি, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি- সবাই অনুশীলনের চরম আদর্শ। তার ওপর রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রা আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ।
খ্রিস্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু এরা তা নন। এরা সর্বগুণবিশিষ্ট- এদের মধ্যে সব ধরনের বৃত্তি সম্পূর্ণত স্ফূর্তিলাভ করেছে। এরা সিংহাসনে বসেও উদাসীন; ধনুকহাতেও ধর্মবেত্তা; রাজা হয়েও পন্ডিত; শক্তিমান হয়েও সর্বজীবে প্রেমময়। কিন্তু এসব আদর্শের ওপর হিন্দুর আরেক আদর্শ আছে, যার কাছে আর সব আদর্শ খাটো হয়ে যায়- যুধিষ্ঠির যার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যার অংশমাত্র, যার তুল্য মহিমাময় চরিত্র কখনও কোন ভাষায় কীর্তিত হয়নি- তিনি সর্বগুণান্বিত কৃষ্ণ।
কাজেই, কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যানের আগে আমাদের জানা উচিত, আদৌ কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন কিনা! কৃষ্ণের বৃত্তান্ত যেসব প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার মধ্যে মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণ প্রধান। পুরাণ ১৮টি। এর মধ্যে ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত, স্কন্দ, বামন ও কূর্মপুরাণে কৃষ্ণবৃত্তান্ত আছে। এসবের মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তে বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে আবার একই কথা আছে। অতএব আমাদের আলোচনায় বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ছাড়া অন্য কোন পুরাণের প্রয়োজন হবে না। মহাভারত আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে পার্থক্য হচ্ছে, যা মহাভারতে আছে, তা হরিবংশ ও পুরাণগুলোতে নেই। এর একটি কারণ এই যে, মহাভারত পা-বদের ইতিহাস; কৃষ্ণ পা-বদের সখা ও সহায়; তিনি পা-বদের সহায় হয়ে বা তাদের সঙ্গে থেকে যেসব কাজ করেছেন, তা-ই মহাভারতে আছে বা থাকবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দু’একটা কথা আছে মাত্র। তার জীবনের বাকি কথা মহাভারতে নেই বলেই হরিবংশ রচিত হয়েছিল, তা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও তেমন কথা আছে।
বেদব্যাস চার বেদ সংকলনের পর মহাভারত রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন বলে কথিত আছে। মহাভারত, হরিবংশ এবং অষ্টাদশ পুরাণ- সবই মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত, এমন কথা প্রচলিত। কিন্তু একজন কবির পক্ষে সপ্তলোকের জন্য সাত লক্ষ শ্লোক রচনা সম্ভব কিনা, তার ওপর হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাণও একই ব্যক্তির, এমন নাও হতে পারে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করা গেলে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন হয়। যাতে পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পূর্বে যা ঘটেছে, তার আবৃত্তি আছে- তাই ইতিহাস। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে কেবল মহাভারত অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস বলে পরিগণিত। সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন অনেক কথা আছে যা স্পষ্টত অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেসব কথা অলীক ও অনৈতিহাসিক বলে পরিত্যাগ করতে পারি। কিন্তু যে-সব কথায় সারবত্তা আছে, সেগুলো অনৈতিহাসিক বলে পরিত্যাগ করব কেন? প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থাদি প্রণীত হয়ে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখে প্রচারিত হতো। তাতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। এভাবেই ব্যাসদেবের ২৪ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট মহাভারত চারগুণ বেড়ে ৯৬ হাজারে উন্নীত হয়েছে। মহাভারতের অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে আছে যে, ব্যাসদেব প্রথমে তার পুত্র শুকদেবকে ২৪ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট মহাভারত অধ্যয়ন করান। শুকদেবের কাছে বৈশম্পায়ন মহাভারত শিক্ষা করেছিলেন। অতএব এই ২৪ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট মহাভারতই স¤্রাট জনমেজয়কে পাঠ করে শোনানো হয়।
মহাভারত বারবার পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে, এর তিনটি স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাতে পান্ডবদের জীবনবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছু নেই। এটিই বোধহয়, ২৪ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট ভারতসংহিতা। দ্বিতীয় স্তরের মহাভারত অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। তৃতীয় স্তর নানা পরমার্থিক দার্শনিকতত্ত্বে ভরপুর। প্রথম স্তর বাদ দিলে মহাভারত থাকে না। দ্বিতীয় স্তর বাদ দিলে মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় অলংকার বাদ পড়ে। প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলে পরিচিত নন; তিনি নিজেও নিজের দেবত্ব কোথাও স্বীকার করেননি। দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টত বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলে পরিচিত ও অর্চিত। তৃতীয় স্তরে লোকশিক্ষামূলক বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্ব, সামাজিক অনুশাসন, দাম্পত্য উপদেশ সন্নিবেশিত হয়েছে। শান্তিপর্ব ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব-অধ্যায়, বনপর্বের মার্ক-য়সমস্যা পর্ব-অধ্যায়, উদ্যোগপর্বের প্রজাগর পর্ব-অধ্যায়- এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয়কালে রচিত বলে বোধহয়।
কাজেই মহাভারতের আদিম কঙ্কালে যেটুকু কৃষ্ণচরিত্র পাই, তাই-ই আমাদের অনুশীলনের বিষয় হওয়া উচিত। সেখানে আমরা কৃষ্ণকে একজন সর্বগুণসমন্বিত আদর্শ মানুষ হিসেবে পাই। এখন বাজারে কৃষ্ণচরিত নামে মৎপ্রণীত একখানি বই পাওয়া যাচ্ছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সেটি সংগ্রহ করে পড়তে অনুরোধ করি।
(বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র-এর আলোকে)
[লেখক : ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট,
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়]
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
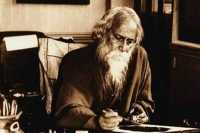
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম







