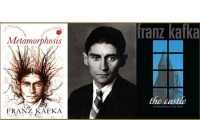সাময়িকী
বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি একটি পর্যবেক্ষণ
কামরুল ইসলাম
শিল্পী : সঞ্জয় দে রিপন
(পূর্ব প্রকাশের পর)
৫.
অধ্যাপক পবিত্র সরকার লিখেছেন- ‘যে দেশের ভাষা বাংলা তা-ই বাংলাদেশ হয়ে উঠল ক্রমশ। এখন আর রাজনৈতিক অর্থে কোনো অখ- বঙ্গভূমির অস্তিত্ব নেই। বঙ্গভাষীদের মূল অঞ্চল তিনটি প্রধান রাজনৈতিক অস্তিত্বে বিভক্ত- স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ আর ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। এছাড়া বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশা এবং অন্যান্য অঞ্চলেও বঙ্গভাষী মানুষের বসতি আছে, যেমন আছে বহুসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি- বিশে^র নানা স্থানে আবাস ও কর্মে লিপ্ত।’ (ভূমিকা, বঙ্গদর্শন। ১ (২০০১)।
এই যে ভাষা থেকে দেশ- এতো এমনি এমনি হয়নি, এর মূল্য আমাদের বুঝতে হবে। দেশের ভাষাকে ভালোবাসলেই কেবল দেশকে ভালোবাসা যায়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা দেখানোর মতো মানুষও রয়েছে এদেশে, যারা টেলিভিশনের চ্যানেলে অথবা কোনো অনুষ্ঠানে বিকৃত উচ্চারণে বাংলা বলে। কখনো আবার বাংলা ও ইংরেজি একসাথে বলে (বাংরাজি- তাও অশুদ্ধভাবে), যা আমাদের ভাবিয়ে তোলে বৈকি। ইংরেজি কিংবা অন্য কোনো ভাষা শেখার ব্যাপারে আমাদের কোনো সংস্কার থাকা ঠিক নয়, কিন্তু শুদ্ধভাবে না-শেখা, না-বলাটা কোনো ভাষার প্রতি অবিচার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষাটাও আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে শিখছে না। এ দায় রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ আছে, তা নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে।
কোনো ভাষার দিগন্ত প্রসারিত হয় সেই ভাষায় রচিত কবিতায়। কবিতা ও ভাষার ইতিহাস প্রায় একই সময়ের। কারণ, কবিতার মধ্যেই ভাষা বিকাশিত হয়, বেড়ে ওঠে, হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে যায় বলিষ্ঠভবে। কানাডিয়ান কবি ও ঔপন্যাসিক মার্গারেট অ্যাটউড এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- ‘For me poetry is where the language is renewed. If poetry vanished, language would become dead. ... It’s true that poetry doesn’t make money. But it’s the heart of the language’ একজন সৃষ্টিশীল লেখকের জন্য তার নিজস্ব ভাষা তৈরি প্রয়োজন। আর নিজস্ব, নতুন ভাষা কেবল কবিতার মাধ্যমেই তৈরি হয়। যে কারণে আমরা দেখেছি জয়েস-ফকনারসহ পৃথিবীর অনেক বড় বড় গদ্যশিল্পীই প্রাথমিক জীবনে কবিতাচর্চা করেছেন। অবশ্য একথা সবারই জানা যে, উত্তীর্ণ গদ্যশিল্পও কবিতা। সঙ্গতকারণেই আজকে কবিতা ও ফিকশনের ব্যবধানটা কমে আসছে। যা হোক, বাংলা ভাষা মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ হয়ে এক বিশেষ পর্যায়ে এসেছে আজ, যা নিয়ে বাঙালি গর্ব করতে পারে। মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের দরবারে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ভাষা মুক্ত আকাশে উড়াল দেওয়ার সানন্দ সাহস পেয়েছে। তাঁর শিল্পমানস, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপৃত থেকেছে চিরকাল। অবহেলিত এই ব্রাত্যজনের ভাষায়ই সাহিত্য করে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এ ভাষার অন্তঃস্থ স্রোতে এক অমেয় শক্তির যোগান দিয়েছেন; আরবি-ফারসি শব্দের সফল প্রয়োগে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক বিশিষ্ট মাত্রা যোগ করেছেন, যা কেবল কালজয়ী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করায় সে-সময়ে তিনি অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হন। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, ‘বাংলা ভাষা হইতে আরবি-ফারসি শব্দ বাদ দিতে হইলে বীরবলকে প্রথমে কলম ছাড়িতে হয়’। কারণ, ‘কলম’ আরবি শব্দ। যাহোক, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি এই ভাষাকে যে কতটা সমৃদ্ধ করেছে, তা আজ স্পষ্ট হয়েছে। আরবি-ফারসি শব্দের এই ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল। নজরুল ইসলামের লেখা তিন হাজারেরও বেশি নিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই হয়ে ওঠার দীর্ঘ পথে ছড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত ইতিহাস।রবীন্দ্রনাথ কালচারের বাংলা ‘কৃষ্টি’ শব্দটি বর্জন করে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃতি একটি মারাঠি শব্দ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই শব্দটিরবীন্দ্রনাথকে জানালে রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটিকেই কালচারের সমার্থক শব্দ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কোনো মানবগোষ্ঠী বা সমাজের সামগ্রিক আচরণ যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে, তাই সে সমাজ বা জাতির সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কোনো সমাজ বা জাতির দর্পণ। হাজার বছরেরও বেশি সময়ের বাঙালি সংস্কৃতির যে ইতিহাস তা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে আছে প্রথমত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, যেখানে বাংলা একমাত্র জাতীয় ও রাষ্ট্রভাষা। অন্যদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম, যেখানে বাংলা প্রধান এবং দাপ্তরিক ভাষা। স্বকীয় ঐতিহ্য এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালিরা এই অঞ্চলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মহাগৌরবে। বাংলা ছিল নদী-নালায় ভরপুর একটি সম্পদে ভরপুর অঞ্চল এবং উপমহাদেশের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই সম্পদের মোহে এ অঞ্চলে বার বার বিদেশি তস্করদের আগমন ঘটেছে এবং তারা দখল করেছে নানা অঞ্চল, করেছে অবাধ লুটপাট। এখনো বাংলা দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির মূলধারাকে চালিত করে। বাঙালি উৎসবগুলোর যে প্রাণবন্ত ও অসম্প্রদায়িক পরিচয় ছিল তা ক্রমশ ম্লান হয়ে আসার পিছনে রয়েছে নানা কারণ। আমাদের যাত্রাশিল্প ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যাত্রাশিল্পের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য রাষ্ট্রের অপরিসীম অবহেলা ও উদাসীনতাই মূলত দায়ী। একসময় গ্রামে-গঞ্জে উৎসবমুখর পরিবেশে যাত্রাপালার আয়োজন হতো। এই শিল্পকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্রের কখনোই কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। যাত্রাশিল্পীদের দারিদ্র্য-অভাব-অনটন তাদের বাধ্য করে অন্য কোনো পেশায় আত্মনিয়োগ করার। এছাড়াও ছিল একশ্রেণীর ধর্মান্ধগোষ্ঠীর নানারকম বাধা, যা এখনো রয়েছে। আগে গ্রামে যখন যাত্রাদল আসতো. কী উৎসব উৎসব ভাব হতো গ্রামগুলোতে। এ বিষয়ে আমরা জানতে পারি আমার এক বন্ধু গল্পকার নিশিত সৌরবের ‘হলুদ পাতার মায়া’ গল্প থেকে। উল্লেখ্য, গল্পকার খুব পরিচিত কেউ নন, এক নিভৃতের সাধক।
একদিনের ঘটনা এখানে না-বললেই নয়। বহু অপেক্ষার পর, একদিন সন্ধ্যায় যাত্রাদল এসে গোলাবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে উঠামাত্রই খবির প্রামাণিক ধুলোর রাস্তায় প্রায় এককিলো. দৌড়ে গিয়েছিল আর চিৎকার করে বলেছিল- ‘ওরে ছলিম, ওরে নয়ির, গোলাবাড়িতে অপর পাটি আইসিচে, সব বাইর হ! খবির একটু মাথাখারাপ মানুষ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার বলল- আল্লাহ, তুমি শেষে আমাদের কতা শুইনলে। অপর পাটি আইসিছে গো, কে কোতি আচো বারাও! হ্যাচাকের আলোয় দুনিয়া জ্বইলি উইঠপি রাইতে, আর ডানা কাটা পরীর নাচ! ’ আগেই বলেছি যাত্রাদল আসা মানেই এই গ্রামে উৎসব। সবাই তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়াতে শুরু করে। কেউ ধুলোর রাস্তায় দৌড়াচ্ছে লুঙ্গি মালকোচা করে বেঁধে, কেউ বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে, কেউ আমগাছ তল দিয়ে, কেউ আবার জামার বোতাম না লাগিয়েই গোলাবাড়ির মাঠের দিকে দৌড়াতে শুরু করে। হাশেমের বউ আকলিমাও চুলোয় ভাত রেখে দৌড়ে যাওয়ার সময় বাঁশের কঞ্চিতে বিঁধে তার শাড়ি খসে গেলে সে কোনোরকম শাড়ি বাঁচিয়ে দৌড়াতে শুরু করে। সেই সন্ধ্যায় সারা গ্রামেই এমন এক ভুতুড়ে অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, না জেনেও কেউ কেউ দৌড়াতে থাকে। সেদিন ওই গ্রামে হঠাৎ এক দমকা বাতাস সন্ধ্যার অন্ধকার বেয়ে ছুটে গেলে গ্রামের সমস্ত গাছপালা, লতাপাতাও মনে হয়েছিল মানুষের এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়েছে। এমনকি গরু-ছাগলগুলোও যেন হাম্বা হাম্বা ব্যাঁ ব্যাঁ করে এই উৎসবের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অভাব-দারিদ্রের মধ্যেও মানুষ এই যে উৎসবিত পরানে কয়েকদিন একটানা কাটাবে, তারপর যাত্রাদল চলে গেলে যে শূন্যতা এসে ঘিরে ধরবে, যে হাহাকার এসে গ্রাস করবে পুরো গ্রামটিকে, সে চিন্তা কারো মাথায় থাকে না। পুরো গ্রামটাই যেন অপার আনন্দে নড়েচড়ে ওঠে।’ (আলপথে জ্যোৎ¯œার ঝাঁক-২০২০)।
যাত্রামঞ্চে অমলেন্দু বিশ^াসের মাইকেলের চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয়ের কথা নিশ্চয়ই আমাদের অনেকের স্মরণে আছে। জানোয়ার, লেনিন, হিটলার, অচল পয়সা, সন্ন্যাসী, সিরাজউদ্দৌলা ইত্যাদি যাত্রাপালায়ও তাঁর অভিনয় ছিল অনবদ্য। এইসব যাত্রাপালায় তিনি নায়কের অভিনয় করে সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেন এবং পলিচালক হিসেবেও তিনি তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ রেখে গেছেন। যাত্রাশিল্পের আঙ্গিক ও কাঠামোগত দিকের আমূল পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। এই যাত্রা স¤্রাট সত্যিই এক কিংবদন্তীতুল্য অভিনেতা ও নির্দেশক ছিলেন। একুশে পদক (মরণোত্তর)সহ অনেকগুলো জাতীয় পুরস্কার পান। তাঁর স্ত্রী জ্যোৎ¯œা বিশ^াস প্রায় ৩০০ যাত্রাপালায় অভিনয় করেন। পরিচালনাও করেছেন। তাঁকে যাত্রা স¤্রাজ্ঞী বলা হতো। তিনিও একুশে পদকে ভূষিত হন। গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছে এগুলো কেবল বিনোদনেরই মাধ্যম ছিল না, এর মাধ্যমে সমাজের অসংগতি, অত্যাচার, কুসংস্কার এবং মানুষের অসহায়ত্বের দিকগুলোও ফুটিয়ে তোলা হতো।
গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছে লাঠিখেলা আজও বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম। বিশেষ করে পহেলা বৈশাখ, রথের দিনে, মহরম উপলক্ষে কিংবা কোনো মেলা উপলক্ষে গ্রামগুলোতে লাঠিখেলার প্রচলন রয়েছে। ঢোল কাঁশি বাজিয়ে এবং খেলোয়াড় লাঠি নিয়ে এই খেলায় নেমে পড়ে। উল্লেখ্য, জমিদাররা জোরপূর্বক খাজনা আদায়ের জন্য লাঠিয়াল পুষতো। ইংরেজরাও এই লাঠিয়ালদের ব্যবহার করেছে প্রজাপীড়নে। নীলদর্পণ নাটক থেকে আমরা সেসব অত্যাচার নিপীড়নের কথা জানতে পারি। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর এবং ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটলে লাঠিয়ালরা অনেকটা বেকার হয়ে পড়ে। এইসব লাঠিয়ালদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। অনেকে অবশ্য আত্মরক্ষার জন্যেও এই প্রশিক্ষণ নিত। পরে এর সাথে আরো কিছু আঙ্গিক-কৌশল যোগ হয়ে লাঠিখেলা বিনোদনমূলক খেলায় রূপান্তরিত হয়। লাঠি খেলা একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি মার্শাল আর্ট। ভারত ও বাংলাদেশে কেবল এই খেলার প্রচলন রয়েছে। ভারতে পুজোর সময়ে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় প্রতিবছর লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা হতো, কিন্তু দর্শক কমে যাওয়ায় এবং পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় এখন বছরে একবার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েরাও এখন এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। তবে এই খেলাটিও এখন অনেকটা বিলুপ্তির পথে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় গ্রাম-বাংলার এই জনপ্রিয় খেলাসহ আরো অনেক খেলা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-বাংলার এইসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।
পাকিস্তান আমলে এমনকি স্বাধীনতার পরেও আমরা গ্রামের ক্লাবগুলোতেও উৎসবমুখর পরিবেশে নাটক মঞ্চায়ন হতে দেখেছি। তা প্রায় উঠেই গেছে বলা যায়। জেলা শহরের শিল্পকলা একাডেমিগুলোতেও নাটক মঞ্চায়ন আর আগের মতো হয় না। রাজধানীকেন্দ্রিক নাট্যশালাগুলোতে মাঝে মাঝে নাটক মঞ্চায়ন হতে দেখা গেলেও সেই ব্যাপকতা আর নেই।মানুষের বিনোদনের জন্য এখন অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ফোন মুখ্য হয়ে উঠেছে। ফেসবুক, টুইটার, রিলস নিয়ে বাচ্চা থেকে বুড়োরা পর্যন্ত রাত-দিন পড়ে থাকছে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে ব্যস্ত করে তুলেছে আর এই অনিবার্যতাকে অস্বীকার করবারও উপায় নেই। প্রযুক্তি যেমন আমাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে, তেমনি আমাদের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের একধরনের আসক্তির ভেতরে নিমজ্জিত করেছে। ছেলেরা এখন আর ডাংগুলি খেলে না, বদন কিংবা গোল্লাছুটও না। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রায় সর্বত্রই দেখা য়ায় ছেলেমেয়েরা মোবাইল নিয়ে পড়ে আছে। তবে একথাও ঠিক যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবন থেকে অনেককিছুই হারিয়ে যায়। একসময়ের কাবাডি খেলা (হা ডু ডু) এখন তেমন আর দেখা যায় না। জারি সারি ভাটিয়ালির দিনও শেষ। আমাদের মাঝি-মাল্লাদের কণ্ঠে কোনো গান নেই। নদীগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে। পুকুর-খাল-বিল ভরাট করে বানানো হচ্ছে বড়ো বড়ো বিল্ডিং কিংবা মার্কেট। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন সেই দলের লোকজন এই রকম দখলদারিত্বের খেলায় মেতে ওঠে। পাহাড় কেটে, অবৈধভাবে গাছপালা কেটে ইকোসিস্টেমকে মারাত্মকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, দেখার কেউ নেই। ইকো-সংস্কৃতি বলে একটা কথা আছে, যা আমাদের কোনোভাবে স্পর্শ করে না। (আগামী সংখ্যায় পড়ুন)
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কাফকাকে পড়া, কাফকাকে পড়ানো
-
এ মুখর বরষায়
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা