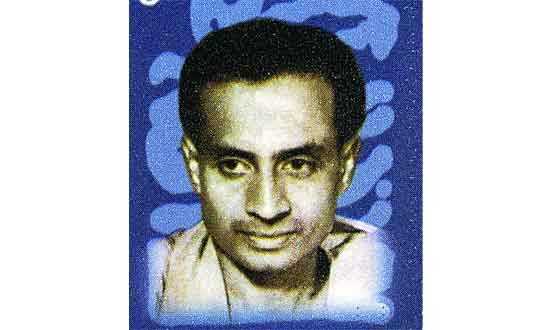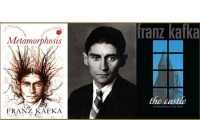সাময়িকী
বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ বিষয়ভাবনা
খুর্শিদা বারী
বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)
বুদ্ধদেব বসু বাংলা ভাষা সাহিত্যের আধুনিক কালের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক। যিনি তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায় দিতে চেয়েছেন প্রাচীন ও নতুনের মিশ্রণে নতুনতর কিছু এবং বোধের উত্তরণে চিরকালীন বার্তা। তেমনি এক রচনা ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’, প্রথম নাটক যা কবিতায় বা কথাসাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির একটি। পূর্ণাঙ্গ অভিনয়যোগ্য ও শিল্পমূল্যে উজ্জ্বল এই নাটকের পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীর মাঝে তিনি সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব, প্রেম, বেদনা ও রোমান্টিক আবেগ, যা সাধারণ মানুষেরা ‘কাম’ নাম দিয়ে অপলাপ করে থাকে, তারই পথ ধরে দুজন মানুষের পুণ্যের পথে উত্তরণের অসাধারণ প্রকাশনা। এই নাটকের দুই উল্লেখ্যযোগ্য চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী ছাড়াও রয়েছে লোলাপাঙ্গী, চন্দ্রকেতু, বিভাজক, রাজমন্ত্রী অংশুমান ও রাজকুমারী শান্তা- যারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পাপ-পুণ্য, লাভ-লোকসানের হিসাবে ষোলআনা পাকা; ঠিক তাদের উল্টো চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী, যারা আপন সত্তার উদ্বোধনের সাধনায় আপনাকে জানতে ও খুঁজতে ব্যাকুল। বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে তাদের মাঝে কেবল মানবিক দিকের প্রকাশ, স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও সত্তা হিসেবে মানবমূল্য খোঁজা ও বোঝার চেষ্টায় যারা রত।
তরঙ্গিণী অসাধারণ সুন্দরী এক বারবণিতা যে তার পেশাগত দক্ষতা, ছলাকলায় শীর্ষে। যার অঙ্গুলি হেলনে যে-কোনো পুরুষোত্তমের হৃদয় হেলতে সময় নেয় না অনুক্ষণ; কিন্তু তার এই গর্ব, এই ক্ষমতা মুহূর্তেই নীল হয়ে যায় ঋষ্যশৃঙ্গের উচ্চারিত প্রশ্নের মাধ্যমে।
তরঙ্গিণীকে পুরুষবধের সব কলা শেখানো হয়েছে, কিন্তু দেওয়া হয়নি পুরুষ সম্পর্কে কোনো ধারণা, যে পুরুষ কেবলই নিরপেক্ষ ভালোবাসার বাহন। পুরুষ মানেই যে কেবল সম্পদ আহরণের মাত্রা নয়, পুরুষ যে নারীর আলাদা এক চরিত্র প্রকাশের সহায়ক, তরঙ্গিণী কেবল ঋষ্যশৃঙ্গের কথার মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছে।
নারী স্বতন্ত্র, নারী এক আলাদা সত্তা- যেখানে বহিরাবরণের সঙ্গে তার অন্তঃআবরণের সংযোগ কেবল নির্লোভ একান্ত চাওয়ায়; যা বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ায় ভাস্বর নয়, যেখানে নারীর বাহ্যিক রূপ প্রধান। ঋষ্যশৃঙ্গকে তার অন্তঃআবরণের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করান; যেখানে তরঙ্গিণী কেবলই একান্ত নারী, ভোগের উপাচার নয়।
ঋষ্যশৃঙ্গও জানত না পুরুষ সত্তার মানে। পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজনীয়তা উপস্থিতির কার্যকারণ। তার পিতা বিভা-ক একান্তভাবে চেয়েছেন ছেলে তপস্বী হোক, এতে তাঁর পিতার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় সিদ্ধিই সম্ভব; কিন্তু তরঙ্গিণীর উপস্থিতি তার সমস্ত বোধ-সত্তা কে করে তোলে নির্বোধ। প্রশ্নবাণে মুখরিত হয় আপন সত্তা। নিজেকে নতুন রূপে ও নতুন সত্তায় আবিষ্কার করে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত তপস্বী হয়ে ওঠেন আরক্ত, নারীকে কাছে পাবার চরম লালসা তাকে অকস্মাৎ ভূ-পতিত করে এবং নতুন এই বোধের সিদ্ধি লাভের লিপ্সা তাকে করে তোলে ব্যাকুল। তথাপিও হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তি তাকে করে তোলে বিষণœ। অন্ধকারেও তাই খুঁজে ফেরে স্বার্থবিহীন সেই নারী, সুখ ও দেহকে যে কেবলই তার পুরুষসত্তাকে জাগ্রত ও অতিক্রম করতে সফল ও সক্ষম। বৈষয়িক লাভ-লোকসানের হিসাবে সে ভালোবাসা নয়, কেবল নারী-পুরুষের একান্ত ভালোবাসাই যেখানে উপজীব্য ও কাম্য। তাইতো দ্বিতীয়বার তরঙ্গিণীর উপস্থিতি তাকে আবার তার সেই সত্তা সম্পর্কে করে তোলে সচেতন, সে পুনরায় ফিরে যায় তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতায়।
তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গ পুনরায় পথে নামে সেই ভালোবাসার খোঁজে, যেখানে ভালোবাসা কেবলই ভালোবাসার জন্য, কোনো পক্ষের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও এককসত্তার দাবিকে অবদমন করা নয়। হতে পারে তা মানুষের সাথে, হতে পারে তা ঈশ্বরের সাথেও। সেই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কেবলই খুঁজে যেতে হবে- নির্লোভ, ক্ষমতাহীন, ক্ষমতার স্বার্থে; যে ক্ষমতা কেবল ভালোবাসার, যে ক্ষমতা আদি, পূর্ণ ও নিরপেক্ষতার মূর্তিতে উজ্জ্বল ও ভাস্বর।
নৈঃসঙ্গ্যচেতনাই ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকের মূল সুর হয়ে ফুটে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারতের চরিত্রের প্রেম ও কামের বিবরণ দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁদেরকে রক্তমাংসের আধুনিক যুগের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।
বুদ্ধদেব বসু কেবল প্রেমের চিত্র আঁকেননি, এঁকেছেন বিরহের চিত্র। এই বিরহ অনন্ত। এই বিরহে ঘরে ফেরার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যখনই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ আর পতিতা তরঙ্গিণী অনন্ত শূন্যতার পথে যাত্রা শুরু করে, তখনই মঞ্চের শেষ দৃশ্যে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর মিলনের দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিরহ ও মিলনের বাস যে পাশাপাশি, নাট্যকর হয়তো সেই সত্যই প্রকাশ করেছেন। প্রেমের প্রকাশ এতোই তীব্র যে, ঋষ্যশৃঙ্গ আর তরঙ্গিণী পরস্পরকে পেয়েও, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করেও একসূত্রে গ্রথিত হতে পারলেন না। যৌন প্রশান্তির অভাবের কারণেই ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের বেদনা। এই বিচ্ছেদকে তাঁরা সজ্ঞানে মেনে নিয়েছেন। যে যার অজানা গন্তব্যে চলে গিয়েছেন।
তবে ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকে পতিতাকে প্রেমিকা হওয়ার যোগ্য করে তুলেছেন নাট্যকার পুরুষরঞ্জনের পেশাকে পায়ে দলে তরঙ্গিণী হয়ে উঠেছে যথার্থ প্রেমিকা। ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী হয়েও হয়ে উঠেছেন আধুনিক যুবক। তিনি পিতার আহ্বান ফিরিয়ে দিতে পারেন। ‘বিবাহ’ নামের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানকে তিনি অবলীলায় অস্বীকার করতে পারেন। তপস্যা ছেড়ে তিনি নারীর প্রেমে মত্ত হয়েছেন। কামে জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু তরঙ্গিণীকে পেয়েও কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেননি। আবার ছেড়ে আসা আশ্রমেও তিনি ফিরে যাননি। তিনি যাত্রা করেছেন নৈঃসঙ্গ্যের পথে, অনন্তের পথে; যে পথের প্রান্তে আছে কেবলি শূন্যতা আর রিক্ততা। এভাবে পুরাকালের তপস্বী আমাদের কাছে হয়ে ওঠেন আধুনিক পুরুষপ্রবর। বুদ্ধদেব এভাবেই পুরাণের নবজন্ম দেন। পুরাণের কাহিনি ধারণ করেও ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ হয়ে ওঠে বুদ্ধদেব বসুর রূপায়ণে এক আধুনিক নাটক।
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কাফকাকে পড়া, কাফকাকে পড়ানো
-
এ মুখর বরষায়
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা