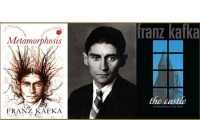সাময়িকী
শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি
স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
হামিদুজ্জামান খান
হামিদুজ্জামান খান / জন্ম : ১৬ মার্চ ১৯৪৬; মৃত্যু : ২০ জুলাই ২০২৫
গত ২০ জুলাই স্মৃতি হয়ে গেলেন দেশের খ্যাতিমান ভাস্কর ও অনন্য চিত্রশিল্পী হামিদুজ্জামান খান। ফর্ম, বিষয়ভিত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী ভাস্কর্যের জন্য তিনি সুপরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত “একাত্তর স্মরণে” শীর্ষক কাজের জন্য তিনি ভাস্কর হিসেবে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সিউলে অলিম্পিক ভাস্কর্য পার্কে ভাস্কর্য স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি অর্জন করেন। তাঁর নকশাকৃত অন্যতম ভাস্কর্য ‘সংশপ্তক’ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত। সেনানিবাস, বঙ্গবভনসহ আরো অসংখ্য জায়গায় তাঁর ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে। তিনি ঢাকা আর্ট কলেজের (বর্তমানে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক। ভাস্কর্যে অবদানের জন্য তিনি ২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদক লাভ করেন। বছর কয়েক আগে তাঁর এ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ওবায়েদ আকাশ ও খন্দকার মুনতাসীর মামুন
বিশেষ সাক্ষাৎকার
ওবায়েদ আকাশ : আমরা আপনার সাম্প্রতিক সময়ের কাজগুলোর ব্যাপারে জানতে চাই। শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নেয়ার পর উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়েছে কিনা।
হামিদুজ্জামান খান : আমি ২০১২-তে ছুটিতে যাই। এক বছর তো প্রিপ্রারেটরি লিভ-এর মতো থাকে। আমার জীবনের একটা বড় সময় চলে গেছে চারুকলায়। বেশ বড় সময়ই। কারণ বাইরে আসলেও আমি তো কাজ করতে থাকতাম কিন্তু একটা তাড়াও থাকত যে, চারুকলায় যেতে হবে, ক্লাস আছে। যখনই অবসরের ফ্রিডম পেলাম অর্থাৎ এই প্রায় সাত বছরে প্রচুর কাজ করলাম।
ও. আ. : এক্সিবিশন হয়েছে এর মধ্যে?
হা. খা. : এর মধ্যে বেশ কয়েকটি এক্সিবিশন করেছি, সলো। গত বছর জাতীয় জাদুঘরে একটা বড় এক্সিবিশন হয়েছে, নভেম্বরে। এর আগে কায়াতে করেছিলাম। অবসরের পর পাঁচ বছরে পাঁচটি এক্সিবিশন করেছি কায়াতে। অবসরের পর বেশ কিছু কাজ আমি বড় স্কেলে করেছি। এ বছরে আমি প্রচুর ছবি এঁকেছি। প্রচুর ক্যানভাসে কাজ করেছি। এ মাসের ১৭ তারিখে আমার একটা এক্সিবিশন আছে। এটা হবে অবিন্তা গ্যালারিতে।
ও. আ. : ঐ এক্সিবিশনে কী ধরনের কাজ প্রদর্শিত হবে? ভাস্কর্য নাকি শুধুই পেইন্টিং?
হা. খা. : আমি এবারের এক্সিবিশনটা পেইন্টিং-প্রধান করবো। তবে কিছু ভাস্কর্য থাকবে। আমাদের গ্যালারিগুলোতে স্থান সংকুলান করা খুব কঠিন। মিউজিয়ামের বড় গ্যালারিটা স্কাল্পচারের জন্য ভাল। প্রচুর স্পেস। তবে অন্যান্য গ্যালারিগুলো শুধু পেইন্টিং-এর জন্যই তৈরি করা হয়।
এবারের এক্সিবিশনে বড় পেইন্টিং থাকবে। একটা পেইন্টিং লম্বা হবে প্রায় ৪২ ফুট। হাইট ৭ ফুট। তাহলে বুঝতে পারছেন এই স্পেসটা ঐ গ্যালারিতে আছে। ওদের ওয়াল প্রায় ৪৮ ফুট লম্বা।
ও. আ. : গ্যালারির কথা যেহেতু উঠল, তাই প্রসঙ্গক্রমে জানতে চাই, এক্সিবিশনের ক্ষেত্রে গ্যালারির ভূমিকা কতটুকু?
হা. খা. : একটা গ্যালারির উচিৎ অন্তত দশটা আর্টিস্টকে সাপোর্ট দেয়া। সেটা এখনও আমাদের দেশে হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু গ্যালারির সঙ্গে কিছু কিছু আর্টিস্ট যুক্ত আছেন। আবার কোনো কোনো গ্যালারিতে সেই স্কোপও নাই। যেমন আমি কায়া গ্যালারিতে সলো করেছি প্রায় আটটা। এখন আমার ফ্রী টাইম। আমি ভাবছি একটু বড় পেইন্টিং করবো। ঐ পেইন্টিং তো কায়া গ্যালারিতে ঝোলানো সম্ভব না। একটা পেইন্টিং ছিল ১৪ ফুট লম্বা। ঐটা কায়া তার ওয়ালেই লাগাতে পারেনি। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু পাল্টাচ্ছে। এখন শুধু গ্যালারির জন্যই গ্যালারি করা হচ্ছে। নতুন গ্যালারি হচ্ছে। কাজ করছে ব্যবসায়িক চিন্তা, পেশাদারিত্ব।
আর্কিটেক্ট পলাশ একটা গ্যালারি করলেন বনানীতে। তিনি নিজেও ছবি আঁকেন। গ্যালারি উদ্বোধনের দিন আমরা গিয়েছিলাম। অনেক কথা হলো। উনি বললেন, আমি তো একটা গ্যালারি দিলাম। কিন্তু এই স্পেসটার তো একটা মেনটেনেন্স খরচ আছে। কথাটা কিন্তু সত্যি। একটা গ্যালারি চালাতে বাৎসরিক খরচ অনেক। আমাদের গ্যালারিগুলো যে এখনও টিকে আছে এর কারণ হয়ত তাদের নিজস্ব জায়গা, নিজস্ব বাড়ির কারণে। পলাশের গ্যালারিটাও নিজের জায়গায়। উনি বলেছেন, স্পেস তো আমি দিলাম। কিন্তু এর মেনটেনেন্সটা করতে হবে।
খন্দকার মুনতাসীর মামুন : আমরা জানি, আপনি বাংলাদেশে ভাস্কর্য শিল্পের একজন পথিকৃৎ। বাংলাদেশে ভাস্কর্য শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষাপট আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?
হা. খা. : আমরা যখন এসেছি তখন ভাস্কর্য শিল্পের আন্ডারস্ট্যান্ডিংও ছিল না, গ্রহণযোগ্যতাও ছিল না। এটাকে মূর্তি বলা হতো তখন। এটা যে ক্রিয়েটিভ একটা জিনিস, এবং মডার্ন স্কাল্পচারের সঙ্গে ধর্মের যে কোনো ক্ল্যাশ নেই- তখন সেটা জানত না অনেকেই। আমি ফর্ম নিয়ে কাজ করি। আমার সঙ্গে ধর্মের কোনো ক্ল্যাশ থাকার কথা না। তবে চিরদিনই ভাস্কর্যে অবয়বের একটা আবেদন আছে। এখনও আছে। এটা থাকবে। আমার মনে হয়, চেতনার দিক দিয়ে অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে।
আমার প্রথম কাজ ছিল বঙ্গভবনে। লাইফের প্রথম কাজ, ১৯৮২ সালে। স্কাল্পচারটার নাম ছিল পাখি পরিবার। সেসময় কিন্তু আমার ওপর দিয়ে রীতিমতো ঝড় বইছিল। এমন একটা স্টেজ এসেছিল যে, ওরা ভাবছিল, কাজটা ওরা রাখবে না। কারণ এটা কেউ পছন্দ করছিল না। ওরা মিটিংয়ে বলেছিল, ‘আমরা ওনাকে বললাম একটা সুন্দর কিছু বানাতে। উনি বানালেন লাইন-টাইন দিয়ে একটা পাখির কংকাল। এটা কিছু হলো?’ মিনিস্টাররা এসে বললেন, ‘কী বানাইসেন, এটা সরান’। এই ছিল অবস্থা! পরে যখন বিদেশীরা এসে বলতে শুরু করলো, বাহ তোমাদের এখানে তো খুব সুন্দর স্কাল্পচার আছে। তখন আস্তে আস্তে ভাস্কর্যটি গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। এখন কিন্তু ঐ স্কাল্পচারটিই বাংলাদেশের একটি ইম্পরটেন্ট স্কাল্পচার হিসেবে সুধীসমাজে বিবেচিত হয়।
ও. আ. : সংশপ্তক তৈরির পেছনের গল্পটা একটু শুনতে চাই।
হা. খা. : এটা আমি বসাই ’৮৯-এ। যেহেতু সে সময় আমি আরেকটা বড় কাজ করেছি, আমার বেশ সাহসও ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গ্রুপ আসে আমার কাছে। ওনারা বলেন, আমাদের ক্যাম্পাসে একটা স্কাল্পচার দরকার। আমরা ঠিক করেছি, কাজটা আপনিই করবেন। আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে জায়গা-টায়গা দেখলাম। একটা প্রপোজাল তৈরি করলাম। একটা মডেল বানালাম। ওরা ওদের সিন্ডিকেটের জন্য ঐ মডেলটা চাইল। আমি দিলাম। কাজটা আমি বিমূর্ত আঙ্গিকে করতে চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছি, মুক্তিযুদ্ধ মানে একটা স্পিরিট, একটা গতি। মুক্তিযুদ্ধ তো সাধারণ জিনিস না। এটা উচ্চারণ করলেই মনে একটা ধাক্কা লাগে। মনে হয়, এ জাতি মুক্তির জন্য লড়াই করেছে। এই অনুপ্রেরণা যাতে আমার স্কাল্পচারটার মধ্যে বহমান থাকে ঐ ভাবনাটাই আমার ছিল। আমি কারও অবয়ব করিনি। অথচ তখন কিন্তু অবয়ব নিয়েই বেশিরভাগ কাজ হচ্ছিল। তখন অনেকেই কাজ করছিলেন। আবদুল্লাহ খালেদ করছিলেন, রাজ্জাক স্যার করছিলেন, আরও কাজ হচ্ছিল। কিন্তু বেশিরভাগই অবয়ব নিয়ে হচ্ছিল। সরাসরি ফিগারের আদল। আমি কিন্তু ফিগারটাকে ভেঙে দিয়েছি। হাত একটা নাই, পা একটা নাই। লেংড়া! সিম্বলিক করেছি মডেলটা। মডেলের তেমন একটা ডিটেইলও করি নাই। আমি শুধু আমার স্পিরিটটা দেখাতে চেয়েছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আমার মডেলটাকে বাতিল করে দিল। যারা আমার কাছে এসেছিল সেই গ্রুপ তখন সিন্ডিকেটকে বলল, যে শিল্পী এটা তৈরি করেছেন, ওনাকে তো আমরা সিলেক্ট করেছি, ওনাকে একটু ডাকি। উনিই না হয় আমাদের বোঝাক যে, আসলে উনি কী বানাতে চাচ্ছেন। পরের মিটিং-এ আমাকে ডাকা হলো। আমি গিয়ে কথা বললাম। আমি বললাম, আমি তো হুবহু মুক্তিযুদ্ধ বানাতে চাই নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ একজন করেনি। লক্ষ লোকের সিম্বল আমি করতে চেয়েছি। আমি ঐভাবে চিন্তা করেছি। স্পিরিটটাকে আমি ধরার চেষ্টা করেছি। এমনকি বেইসটাকেও আমি একটু এঙ্গেল করে দিয়েছি। আমার কথা শুনে ওরা রাজি হলো। ওদের চিন্তাটা ছিল, আমি একটা মুক্তিযোদ্ধা বানাবো, দশ-বারো ফুটের। ওটা বসাবে। আমি না করলাম। আমি বলেছি, এমন কোনো জায়গায় ভাস্কর্যটি বসানো যাবে না যেখানে ছেলেরা পোস্টার মেরে ভাস্কর্যটিকে ঢেকে ফেলবে। এমন একটা জায়গায় সংশপ্তক বসাতে হবে যেন সেটা সবার নজরে আসে, ভাস্কর্যটি ভাল থাকে। পরে লাইব্রেরির সামনে সংশপ্তক বসানোর সিদ্ধান্ত হলো। আমি বললাম, কাজটি এত ফুট হবে। এবং এত টাকা লাগবে। ওদের ঐ টাকার বাজেট ছিল না। তখনকার সময় এক লাখ টাকা অনেক। ঐ টাকা বাজেট করেই ভেবেছে অনেক দেয়া হয়েছে। আমি বলেছি, কাজটা আমি ব্রোঞ্জে করতে চাই। ব্রোঞ্জে একবার করলে আর হাত দিতে হবে না। সিমেন্টে করবো, কালো হয়ে যাবে কয়দিন পরে। আস্তে আস্তে লংজিভিটিও কমে যাবে। পরে আমি বললাম, আমার তিন লাখ টাকা লাগবে। ওরা তো আমার কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সিন্ডিকেট আবার বসায়ে টাকা বরাদ্দ করল। এভাবেই কাজটা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত ঐ কাজটার মেরামতে আমাকে ডাকে নি। অর্থাৎ নষ্ট হয়নি এতটুকু, আগের মতোই আছে।
খ. মু. মা. : সার্কের মিশুকও তো আপনার কাজ। ওটা কবে করেছিলেন?
হা. খা. : মিশুক করেছিলাম ১৯৮৬ সালে। মিশুকসহ অনেকগুলো কাজে মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছেন। উনি স্কাল্পচার পছন্দ করতেন। উনি একবার মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা কাজের কথা বললেন। বললেন, আপনি কাজটা করেন, আমি ওটা সিলেট ক্যান্টনমেন্টে বসাবো। আমি বানালাম, বেয়োনেট নিয়ে একটা মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়ানো, ১৩ ফিট। ব্রোঞ্জে করি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আর্মিদের যে প্রতিবাদ সেটা নিয়েই কাজটা করতে বলেছিল। আমার তখন বয়স কম। আমি ফিগার করি। উনি আমাকে মডেল পাঠান। আর্মিরা এসে আমার কাছে বসে থাকে। ওদের দেখে দেখে আমি ড্রয়িং করি, ফিগার তৈরি করি। আমার মনে হয় তখনই এটাতে ২৩ মন মেটাল লেগেছিল। স্কাল্পচারটার নাম ছিল ‘হামলা’।
আমি ভারতে যখন পড়াশোনা করি, আমার সাবজেক্ট ছিল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি সেসময় ছোটখাটো করে অনেক স্কাল্পচার বানিয়েছিলাম। আমাকে আমার টিচার বললেন, তুমি ছোটখাটো কাজ করছ। তুমি যখন দেশে যাবে তখন এগুলো নিয়ে যেতে পারবে। আমি সেসময় একটা রিক্সা বানিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের পার্টিসিপেশন বোঝাতে কাজটা করি। একটা রিক্সাওয়ালা মারা গেছেন। তার কোন নামডাক নেই, কিন্তু তিনি তো দেশের জন্যই মারা গেছেন। এই সাধারণ উপলব্ধিগুলো আমি ধরার চেষ্টা করতাম।
আমার মাস্টার্স যখন শেষ হলো আমি আমার অনেক কাজ নিয়ে আসি। তখন আমার থাকার জায়গাও ছিল না। কাজগুলো কোথায় রাখবো তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। ঐ অবস্থায় আমি বুদ্ধি করে আমার সাত থেকে আটটা স্কাল্পচার মিউজিয়ামকে দিয়ে দিয়েছি। ’৭৬ সালের কথা বলছি। সেই রিক্সাটা এবার এক্সিবিট করলাম।
’৭৬ সালে আমি যখন বরোদা থেকে আসলাম তখন ঢাকায় প্রথমবারের মতো স্কাল্পচারের ওপর একটা গ্রুপ এক্সিবিশন হয়, শিল্পকলায়। তখন কিন্তু এখানে খালেদ, রাজ্জাক স্যার, আনোয়ার জাহান এবং নিতুন কু-ু ছাড়া আর কেউ স্কাল্পচার করতেন না। আর এমনিতেই তো একটা বিরোধ ভাব ছিল স্কাল্পচারের প্রতি।
ঐ এক্সিবিশনে আমি একটা কাজ দিই। ঐ কাজে আমি ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড পেয়ে যাই। আমি তখন থেকেই স্কাল্পচারের ব্যাপারে প্রফেশনালে পরিণত হই।
ও. আ. : আপনি ছোটবেলায় ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন দেখে আপনার বাবা আপনাকে জয়নুলের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। জয়নুল আবেদিন সম্পর্কে যদি একটু স্মৃতিচারণ করেন।
হা. খা. : ম্যাট্রিক পাস করার পর আমি ভর্তি হয়েছিলাম ভৈরব কলেজে। আমার বাবা চেয়েছিলেন, আমি যেন সায়েন্স নিয়ে পড়ি। আমাকে ভর্তিও করেছিলেন কলেজে। দুই তিন মাস পড়ার পর আমার বিরক্ত লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম, এসব সাবজেক্ট আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি বাড়ি চলে গেলাম। গিয়ে বললাম, আমি পড়বোই না। আমি কিন্তু গ্রামে বড় হয়েছি। আমি বড় শহর দেখি নি, আউটলুকটা সেভাবে তৈরি হয়নি। ঢাকায় কোনোদিন আসিনি। বয়স সতেরো-আঠারো। ভৈরব কলেজে ভর্তি হই। বাড়ি থেকে দূরে যাওয়ার বিষয় বলতে তখন এটুকুই। অর্থাৎ আমার গ-ি ছিল এটুকুই।
আমি কলেজ থেকে যখন চলে আসি তখন বাবা বুঝলেন আমি বেঁকে বসেছি। আমাকে জোর করলেন না। আমি আগে থেকেই ছবি আঁকি, আঁকার প্রতি ঝোঁক, খোঁজখবর রাখি চারুকলার। বাবা বললেন, ঠিক আছে, চল, তুমি যা পড়তে চাইছো তাই পড়বে। বাবা আমাকে সরাসরি আবেদিন স্যারের বাসায় নিয়ে এলেন। আবেদিন স্যার থাকতেন নয়া পল্টনের একটা পুরনো বাড়িতে। গিয়ে দেখি স্যার বসে আছেন। আমি বললাম, আমি কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। উনি তখন খুশি হয়ে আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। ওনার জন্মও কিন্তু কিশোরগঞ্জে, কেন্দুয়ায়। ওনার বাবা ছিলেন দারোগা। যাই হোক, আমাকে খুব ভালভাবে একসেপ্ট করলেন উনি। আমি বললাম, স্যার আমি চারুকলায় ভর্তি হতে চাই। উনি বললেন, তুমি কি ছবি আঁক। আমি আমার আঁকা কিছু ছবি ওনাকে দেখালাম। উনি দেখেটেখে বললেন, যাও। আর কিছু লাগবে না। কালকে চারুকলায় গিয়ে বলবে, জয়নুল আবেদিন স্যার পাঠিয়েছেন, কোনো ইন্টারভিউ লাগবে না। আমার নাম বললেই ওরা তোমাকে ভর্তি করে নেবে। তখন কিন্তু চারুকলায় অলরেডি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমি তো ভৈরব কলেজে মাস তিনেক পড়েছি, এতে দেরি হয়ে গেছে। আমি ক্লাসে গিয়ে দেখি, ছেলেরা খুব স্মার্ট। কী সুন্দর ড্রয়িং-ট্রয়িং করছে, মানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি আস্তে আস্তে কাজ শুরু করলাম। তখন চারুকলায় যারা পড়ত তাদের থাকার জন্য নিউমার্কেটের পিছনে একটা হোস্টেল (শাহনেওয়াজ হল) হচ্ছিল। অর্থাৎ নির্মাণের কাজ চলছিল, শেষ হয়নি। আমি আবেদিন স্যারকে বললাম, স্যার আমার তো থাকার কোনো জায়গা নেই। উনি বললেন, ঐ হোস্টেলের একটা রুম আমরা ঠিক করে দিচ্ছি। তোমরা যে কয়জন থাকতে পারো, উঠে পড়। একদম নতুন হল, বিছানা নাই, টেবিল নাই। আমরাই নিজেরা চকি বানিয়ে থাকা শুরু করলাম।
এই হোস্টেলে থাকতাম। ক্লাসে যেতাম কখনও রিক্সায়, কখনও হেঁটে। সব ছিল খোলা। চারুকলায়ও তখন কোনো বাউন্ডারি ছিল না। পিছনটা একদম খোলা ছিল। কোনো বিল্ডিং ছিল না। তখন আর্টস ফ্যাকাল্টিও হয়নি। নীলক্ষেত ও নিউ মার্কেটের দিকে বড় বড় টিনের শেড ছিল, আমাদের বলে দেয়া হলো স্কেচ কর। আমরা বসে বসে ছবি আঁকতাম, ঐ শেডের, মাঠের, সবকিছুর।
আমি বলছি ১৯৬২ সালের কথা। চারুকলায় ভর্তি হলাম। প্রথম একটা বছর শুধু বুঝতে বুঝতেই গেল। প্রচুর কাজ করতাম। সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের টিচার হিসেবে এলেন মুস্তাফা মনোয়ার। খুব ডায়নামিক মানুষ। উনি আমাকে খুব খেয়াল করতেন। মাঝে মাঝেই বলতেন, এই ছেলে তো অনেক পরিশ্রম করে। একদিন আমি ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছি, উনি দেখে বললেন, ওকে ডেকো না। ওর ব্যাগে কী আছে দ্যাখো। ব্যাগে আমার খাতা ছিল। পুরো খাতা ড্রয়িং-এ ঠাসা। উনি বললেন, ও তো সারারাত স্টেশনে বসে ছবি এঁকেছে। কেউ ওকে ডেকো না। ঘুমটা ওর প্রয়োজন।
এভাবেই স্যাররা আমাকে খুব ইন্সপায়ার করতেন। আমাকে বড় বড় ছুটি দিতেন। বাড়ি গিয়ে আমি বসে বসে শুধু ছবি আঁকতাম। বলে দেয়া হতো, ছুটির পর অন্তত দশটা স্কেচ আনতে হবে। অন্যরা দশটাই আনত, কিন্তু আমি আনতাম ষাট কিংবা সত্তরটা। প্রচুর স্কেচ করতাম। এভাবে আমি কাজের ভেতরে প্রবেশ করলাম। থার্ড ইয়ারে গিয়ে রেজাল্টও ভাল করে ফেললাম। ছবি আঁকতাম ওয়াটার কালারে। আবেদিন স্যার ওয়াটার কালার খুব পছন্দ করতেন।
প্রতি বছর চারুকলায় একটি বড় এক্সিবিশন হয়। আমি আমার অনেকগুলো ছবি সেখানে দিলাম। দেখলাম, আমার ছবি দেখে সবাই ফিসফিস করে কী যেন বলছে। টিচাররা সবার দুইটা করে ছবি নিয়েছে। কিন্তু আমার কোন ফেরত দেয়া হলো না। এক্সিবিশন যখন হলো, দেখলাম আমার সব ছবি টাঙ্গানো হয়েছে। আবেদিন স্যার বললেন, তোমার ছবি অনেক অনেক ভাল। আমাকে বলেছিলেন ফ্রেম করতে। তখন ফ্রেম কীভাবে করবো সেটাই আমি জানি না। দেখলাম, সব ছবি ফ্রেম করে টাঙ্গানো। অর্থাৎ চারুকলাই সব করেছে। জয়নুল আবেদিন স্যার গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ফ্রেম এনে আমার ওয়াটার কালারের সব ছবি ফ্রেমিং করে দিলেন।
শফিকুল আমিন স্যার ছিলেন আমাদের প্রিন্সিপাল। আমাকে ডাকলেন একদিন। আমি ভয়ে ভয়ে হাজির হলাম। উনি বললেন, তোমার ছবি খুব সুন্দর। তোমার সব ছবি আমি কিনে নিলাম। আমি তো খুশিতে আত্মহারা। উনি বললেন, তোমার ছবিগুলো ঠিক করে রেখ। মুনিরের ছবিও নিয়েছি। ছবিগুলো আমি ভিজিটরদের উপহার দেব। আবেদিন স্যারের কাছে তখন অনেক বড় বড় ভিজিটর আসতেন। আমি বুঝতে পারলাম, এজন্যই এত ছবি কেনা হলো।
মনির ভাই মানে শিল্পী মনিরুল ইসলাম আর আমার ছবি কিনে নিল চারুকলা। কলেজে তখন ব্যাপক আলোচনা আমাদের নিয়ে।
শফিকুল আমিন স্যার বললেন, কাল কাপড়-টাপড় ভাল করে ধুয়ে নাও। আগামীকাল পরিষ্কার কাপড় পরে আসবে। গেস্ট আসবে। আমরা তখন পায়জামা পরতাম, আর লম্বা শার্ট পরতাম। পরদিন সত্যি সত্যি বড় গেস্ট এলেন। নেপালের রাজা বীরেন্দ্র। আবেদিন স্যার আমাকে ডেকে বললেন, তুমি ওনাদের হাতে ছবিগুলো তুলে দাও। উনি বললেন, এই ছেলেটা ভাল ছবি আঁকে। এই ইন্সপিরেশনগুলোই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।
আবেদিন স্যার বলেছিলেন, ওয়াটার কালারটা তোমার ভাল হয়। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করেছি। আমি আমার ইম্প্রেশন নিয়ে কাজ করতাম। সকালে কোন স্পটে চলে যেতাম। শীতের সকাল। কিছুই দেখা যায় না কুয়াশায়। আমি সেসব আঁকতাম আমার ক্যানভাসে। কিন্তু ডিটেইল করতাম না। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন, আনোয়ারুল হক। উনি আবার ডিটেইল পছন্দ করতেন। আমি উনাকে একদিন আমার ছবি দেখালাম। উনি বললেন, কিচ্ছু হয় নাই। আসলে ওনার ফিলোসফি ছিল ভিন্ন। ছবিতে আমার ফিলিংস আছে, কিন্তু ড্রয়িং নাই। অন্য স্যাররা এসব দেখে ভাল বলেন। কিন্তু ওনার কাছে ডিটেইল করাটাই আসল। উনি বললেন, আমার বাসায় একদিন আসো। ওনার বাসা পুরান ঢাকায়। গেলাম যথারীতি। আমাকে নিয়ে নদীর পাড়ে গেলেন। প্রথম দিন শুধু ড্রয়িং করা হলো। দ্বিতীয় দিন ঐ ছবিতেই একটা ওয়াশ দিল। তৃতীয় দিন আরেকটা ওয়াশ দিল। এভাবে চারদিন গেল একটা ছবি নিয়েই। আমার যেটা লাগে একঘণ্টা। কথাটা বলছি আমি এজন্য যে, ওনার ফিলোসফিটাই ছিল এরকম। একটা পিওরিটির চেষ্টা ছিল তার ফিলোসফিতে। কিন্তু আর্টের জগতটাই তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না!
মুস্তাফা মনোয়ার স্যারের শেখানোর ধরনটা খুব আধুনিক ছিল। উনি বলতেন, রঙ ছেড়ে দাও। তোমার কাজ হলো, রঙ ছেড়ে দেওয়া। বাড়িঘরের মতো আঁকতে হবে না। মুস্তাফা মনোয়ার স্যারের ওয়াটার কালারের কাজও খুব ভাল ছিল। উনি কিন্তু ওয়াটার কালারে অল ইন্ডিয়া গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। ওনার গাইডেন্সেই আমি বুঝতে পেরেছি, ওয়াটার কালারটা কীভাবে করা উচিৎ।
ফাইনালে ইয়ারে পড়ার সময় ১৯৬৭ সালে আমার একটা বড় দুর্ঘটনায় পড়ি। সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় আমার মাথা ফেটে যায়। হাসপাতালে ছিলাম চার মাস। ভাল হই। কিন্তু মাথার একটা অংশে বড় ক্ষত থেকে যায়। খুব খারাপ অবস্থা। ড. আসিরুদ্দিন আমার অপারেশন করেন। আমি ছিলাম উনার চিকিৎসা জীবনের সবচেয়ে কঠিন রোগী। আমি যে বেঁচে আছি এটাই ছিল একটা মিরাকল। আবার ট্রিটমেন্ট দরকার ছিল আমার। ট্রিটমেন্টের জন্য লন্ডন যেতে হবে। আবেদিন স্যারের কাছে গিয়ে বললাম, স্যার আমাকে তো চিকিৎসার জন্য লন্ডন যেতে হবে। স্যার বললেন, চিটাগাংয়ে একটা ক্লাব হচ্ছে। সেখানে একটা গ্যালারি হয়েছে, ঐ গ্যালারিতে তুমি গিয়ে তোমার ছবিগুলো টাঙাও। আমি আসছি।
আবেদিন স্যার গেলেন। আমি ওনার কথামত আমার ভাল ভাল ছবি টাঙ্গাতে শুরু করেছি। উনি হঠাৎ এসে বললেন, আর টাঙ্গাতে হবে না, থামো। তুমি একটা চেক নিয়ে চলে যাও। স্যার ওদের বলে দিলেন তোমরা ওর সব ছবি কিনে নাও। আমি সেখান থেকে একটা বড় চেক নিয়ে চলে আসি। তখন তো ছবির দাম অত বেশি ছিল না। এক একটি ছবি বিক্রি হয়েছিল তিনশ’-চারশ’ টাকায়। যাই হোক, আমি চেকটা নিয়ে চলে আসি। লন্ডন যাওয়ার জন্য আমার পরিচিত একজন একটা জাহাজের টিকিট করে দেয়। সোয়াত নাম ছিল জাহাজটির। কার্গো শিপ। দেড় মাস লেগে যায় লন্ডন যেতে। আমি রঙ, ক্যানভাস নিয়ে জাহাজে উঠি, খুলনা থেকে। প্রথম গিয়ে শ্রীলংকা নামল। আমি নেমেছি, ঘুরেছি, সিনেমা দেখেছি। তখন শ্রীলংকা অত উন্নত ছিল না। সিনেমা হলে বাঁশ দিয়ে সব ডেকোরেশন।
তারপর গেলাম আফ্রিকা, ডাকারে। সেখানে গিয়ে দুদিন শিপটা ছিল। আমি নেমে শহরে গেছি, গিয়ে দেখি, লোকগুলো সব কালো কালো। হোটেলে বসে খাচ্ছি। দেখলাম অনেকের ব্যাগে ছোট ছোট স্কাল্পচার। একটা দুটো কিনে নিলাম। এই থেকে স্কাল্পচারের ওপর আমার একটা ঝোঁক চলে আসে।
কেপটাউনে গিয়েছিলাম। আমরা যখন সমুদ্র থেকে ঐ শহরে ঢুকছিলাম, মনে হলো যেন একটা স্বপ্ন। উঁচু পাহাড়, মেঘ এসে আটকে যায়, সমুদ্র কী নেই সেখানে। অপূর্ব জায়গা কেপটাউন।
আমি দেখলাম প্রকৃতির বৈচিত্র্য। আর সমুদ্র তো আমি নানাভাবে দেখেছি। কোনো কোনো জায়গায় সমুদ্র একবারে শান্ত। আবার কোনো কোনো জায়গায় সমুদ্র উত্তাল। যখন আমরা আফ্রিকা পার হয়ে স্পেনের দিকে যাচ্ছি তখন সমুদ্রে ঝড় হয়েছে। ঐ জায়গায় নাকি সমুদ্র সবসময় উত্তাল থাকে। আমি দেখলাম, আমাদের জাহাজটা যেন রোলার কোস্টার হয়ে গেছে। এত বড় জাহাজটাকে বিশাল সমুদ্রে বাদামের খোসার মতো দেখাচ্ছে।
অবশেষে আমরা পৌঁছলাম। চলে গেল ডান্ডিতে। ওখানে গিয়ে নামলাম। তখন ছিল প্রচ- শীত। আমি তাড়াহুড়ো করে নেমে শীতের কাপড় কিনলাম। গেলাম এডেনবার্গ। আমার বয়স তখন তেমন বেশি না, চারুকলা থেকে মাত্র বেরিয়েছি। ইংরেজি বলতে পারি। একটু ভাঙা ভাঙা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি আমার হসপিটালে গেলাম। হসপিটালে আমার সব এরেঞ্জমেন্ট করা ছিল। আমার চিকিৎসা হলো সেখানে, ধারাবাহিকভাবে। আমি যখন বিল দিতে গেলাম, ওরা বলল, তুমি যেহেতু স্টুডেন্ট হিসেবে এক্সিডেন্টে পড়েছ, আর তোমার দেশের সরকার আমাদের রিকোয়েস্ট করেছে, এজন্য তোমার সব খরচ আমরা মওকুফ করে দিয়েছি। তোমাকে টাকা দিতে হবে না। আমার কাছ থেকে ওরা কিছুই নিল না। ওরা শুধু বলল, তুমি চার মাস লন্ডন গিয়ে থাকো। এক মাস থাকবে শুধু এডিনবার্গে। সরাসরি তোমাকে আমরা খেয়াল রাখবো। আমি তাদের কথামত একটা হোটেলে ছিলাম চার মাস। ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। লন্ডন দেখতাম। আমি একটা জায়গায় ঘুরতে গিয়ে দেখি পার্কের মধ্যে স্কাল্পচার। আমার চোখটা ছানাবড়া হয়ে গেল। কী সুন্দর, পাথরের স্কাল্পচার। পরে খোঁজ নিলাম। জানলাম, এগুলো হেনরি মুরের কাজ। সাধারণ একটা পার্কের মধ্যে হেনরি মুরের কাজ! তো এগুলো দেখে দেখেও স্কাল্পচারের প্রতি আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে। আমি মাঝে মাঝে ওদের গ্যালারিতে যেতাম, মিউজিয়ামে যেতাম। বিদেশি শিল্পীদের সঙ্গে গল্প করতাম।
আমি তিন সপ্তাহ ছিলাম প্যারিসে, আসার সময়। টাকা ছিল সঙ্গে, যেহেতু চিকিৎসায় কোনো খরচ হয় নি। সেখানে ল্যুভ মিউজিয়াম দেখি, ল্যুভে ঢোকার আগে একটা গ্যালারি আমি দেখি ইম্প্রেশনিস্টদের। এসব আমাকে স্কাল্পচারের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে।
আমার মনে আছে আমি একটা এক্সিবিশনে গিয়েছিলাম। হলে ঢুকে ওপরে উঠছি। সিঁড়িটা অনেক বড়। দুই দিকে প্রচুর কাজ। আমি ওপর পর্যন্ত গেলাম। আমি ভাবলাম দেখা শেষ। ওরা আমাকে বলল, তুমি তো কিছুই দেখো নাই। দেখামাত্র শুরু হবে এবার। রুমের ভেতরে যাও।
এই যে বিশালত্ব, অর্থাৎ একজন শিল্পীর এত এত কাজ এগুলো দেখার ফলে আমার জীবনটাও বদলে গেছে। ঢাকায় এলাম। চারুকলায় রাজ্জাক স্যার স্কাল্পচার বিভাগ শুরু করেছেন। আমি গিয়ে বললাম, স্যার আমি স্কাল্পচার শিখতে চাই। রাজ্জাক স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাহলে কাজে নেমে পড়। আমি কিন্তু তখন বিএফএ পাস করেছি। কাজ করতে থাকলাম। প্রায় ছয়-সাত মাস। একদিন আবেদিন স্যার ডাকলেন। তখন উনি প্রিন্সিপাল। স্যার খুব খুশি হলেন দেখে যে, আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমাকে ডেকে বললেন, শোন, তুমি একটা দরখাস্ত কর, তোমাকে একটা চাকরি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি চারুকলার টিচার হয়ে যাবে। আমি বললাম, স্যার আমি কোন বিষয়টা পড়াব। উনি বললেন, স্কাল্পচার। আমি তো ভয়ই পেয়ে গেলাম। বললাম, স্যার, স্কাল্পচার তো পারি না। স্যার বললেন, তুমি পারবা, তোমার ড্রয়িং ভাল, কাজ তো করা শুরু করেছ। স্কাল্পচারে এখন পোস্ট খালি আছে। আনোয়ার জাহান ছিলেন তখন টিচার। উনি চলে যান। উনার জায়গায় ১৯৭০ সালে আমি ঢুকি।
ও. আ. : পেইন্টিং আর স্কাল্পচারের ভেতরে এখন কোন কাজটা বেশি স্বচ্ছন্দে করছেন?
হা. খা. : ইদানীং তো পেইন্টিং খুব ভাল লাগে।
ও. আ. : এখনকার স্কাল্পচারে যে তথ্যপ্রযুক্তির অনেক বিষয় এসে পড়েছে। আর আপনারা কাজ করেছেন মাটি, সিমেন্ট, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। এই পার্থক্যটা আপনার শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে কেমন লাগছে?
হা. খা. : আমি তো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। নর্থ সাউথে ক্লাস নিই, ব্র্যাকে ক্লাস নিই, সাউথ ইস্টে ক্লাস নিই, আর্কিটেক্টদের সঙ্গে অনেক চলাফেরা করি। অনেক কিছু জানি। ওরা বলে, বিশ বছর আগে যে মেটেরিয়ালে ওরা কাজ করত তা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওকে বুঝতে হয় মেটেরিয়ালটা। যে আর্কিটেক্ট গ্লাস ব্যবহার করেন, তাকে গ্লাসটা ভাল করে বুঝতে হয়। তা না হলে ভাল কাজ করা যাবে না। শুধু ডিজাইন করলেই হবে না, প্রযুক্তিটা না বুঝলে গ্লাসটা ব্যবহার করা যাবে না। এখন অনেক বিল্ডিং-এ দুটো গ্লাসকে একসঙ্গে রেখে বাইরের হিটটাকে ভেতরে আসতে দেয় না। এই সিস্টেমগুলো ওরা খুব সহজে জেনে যাচ্ছে। এই যে চেঞ্জটা এটা তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। স্কাল্পচারেও কিন্তু এটার ইনফ্লুয়েন্স আছে। আবার আর্কিটেকচারের সাথে স্কাল্পচারেরও যোগাযোগ আছে, সম্পর্ক আছে। মেটেরিয়ালটাকে না বুঝলে কিছুই করা যাবে না। যেমন আগে স্কাল্পচারের জন্য পপুলার ছিল মার্বেল পাথর। এখন কিন্তু মার্বেলটা পপুলার না, পপুলার হল গ্রানাইট। কারণ স্কাল্পচার এখন ওপেন এয়ারে রাখে, মিউজিয়ামে রাখে না। একটা পার্ক বানানো হয়েছে, সেখানেই থাকে স্কাল্পচার। খোলা। নেচারের সঙ্গে এটাকে টিকে থাকতে হবে। এজন্য মেটেরিয়ালও কিন্তু আগের জায়গাতে নাই।
ও. আ. : স্কাল্পচারের পপুলারিটি এখন কি বেড়েছে?
হা. খা. : আমি একটা এক্সাম্পল বলি। যেমন সাউথ কোরিয়া। এরা তো পঞ্চাশ কিংবা ষাট বছর আগে আমাদের মতোই ছিল। এদের ডেভেলপমেন্টটা নতুন। ইকোনমিক্যালি সাউথ কোরিয়া আমাদের সমান সমানই ছিল। কিন্তু এখন সাউথ কোরিয়া জাপানকেও টেক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট, কালচারাল ডেভেলপমেন্ট- এসব নিয়েই কিন্তু দেশটা এগিয়েছে। শুধু অর্থনীতি দিয়েই কিন্তু এগোয়নি।
আমি বহুবার গিয়েছি সাউথ কোরিয়াতে। আমার পাঁচ ছয়টা কাজও আছে সেখানকার অলিম্পিক পার্কে। এগুলো তো আমাদের এশিয়াতেই হচ্ছে। ওখানে সবচেয়ে বড় কাজটা যার সে মারা গেছেন। অর্থাৎ ঐ কাজটা এখন মিউজিয়াম পিস। কারণ সেই শিল্পী আর বেঁচে নেই। ধরুন, আবেদিন স্যারের একটা কাজ তো পাওয়াই মুশকিল।
এই পার্কগুলোই এখন মিউজিয়াম হয়ে যাচ্ছে। যে রাস্তাটা পার্কে ঢুকেছে তার আইল্যান্ডেও স্কাল্পচার রাখা শুরু হয়েছে। ওখানে আইল্যান্ডগুলোও তো অনেক বড়।
ফুটপাতে স্কাল্পচার রাখছে, বাগানে স্কাল্পচার রাখছে। ঐতিহাসিক টেম্পল কিংবা সিমেট্রিগুলোতে স্কাল্পচার রাখছে। এভাবে স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে।
খ. মু. মা. : বাংলাদেশের ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশে আরও কী কী বিষয় দরকার বলে আপনার মনে হয়?
হা. খা. : আমি এর আগে এক এক্সিবিশনের উদ্বোধনী বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরকে বলেছিলাম, কোনো একটা মাঠের মধ্যে আমাদের স্কাল্পচারগুলো রেখে একটা পার্ক বানিয়ে দেন। উনি বলেছিলেন, আমি একটা পার্ক করবো, কথা দিচ্ছি। এটা রমনা পার্কের কোনো একটা কর্নারে হতে পারে। গত বছর শিল্পকলার এক অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে ওনার আবার দেখা হলো। আমি বললাম, আপনি তো কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তো কোনো পার্ক পেলাম না। উনি তখন বললেন, দ্যাখেন রমনা পার্কের একটা এলাকাই কয়েকটা মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে। আমার মনে তো ইচ্ছা আছে কিন্তু পারছি না, ঐ সব মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাচ্ছি না। আমি বলেছি, আপনি শিল্পকলায় একটা ছোটখাটো জায়গা এরেঞ্জ করে আমাদের জন্য একটা পার্ক বানিয়ে দেন। কিছুদিন আগে উনি বললেন শিল্পকলার সামনের জায়গাটা আমি আপনাকে দিলাম। আপনি স্কাল্পচার বসান। আমরা কিন্তু স্কাল্পচার বসিয়েছি সেখানে। অর্থাৎ এগুলো তো হচ্ছে। জায়গা কিন্তু আরও অনেক আছে। যেমন যমুনা ব্রিজ পার হলেই কত জায়গা পাশে পড়ে আছে, তাই না। আমরা যদি একটা সুন্দর জায়গাকে বেছে নিয়ে প্ল্যান করে কাজ করি, মানুষ গাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে স্কাল্পচার দেখবে। এসবও কিন্তু হতে পারে।
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-
এ মুখর বরষায়
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

ব্রেশায় উড়োজাহাজ