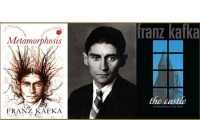সাময়িকী
ফিলিস হুইটলি
কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
ভূমিকা ও ভাবানুবাদ : চন্দন চৌধুরী
ফিলিস হুইটলি
ফিলিস হুইটলি পিটার্স, যিনি আঠারো শতকে আমেরিকায় দাস হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম সুপরিচিত কবি। বস্টনের প্রখ্যাত বণিক জন হুইটলির বাড়িতে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং দাসত্বে আবদ্ধ হন। তাসত্ত্বেও, নিউ ইংল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড উভয় স্থানেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, এবং উভয় জায়গার প্রকাশনা সংস্থাগুলো তার কবিতা প্রকাশ করত। দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের জন্য তিনি একটি জীবন্ত প্রমাণ ছিলেন যে কৃষ্ণাঙ্গরাও শিল্প ও বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী হতে পারে।
প্রায় সাত বছর বয়সে হুইটলিকে পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল/গাম্বিয়া থেকে ধরে আনা হয় এবং ১৭৬১ সালের আগস্ট মাসে বোস্টনে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। জন হুইটলির স্ত্রী সুজানা হুইটলি তাকে কিনে নেন। হুইটলি পরিবার তার বুদ্ধিমত্তা আবিষ্কার করার পর তাকে পড়া ও লেখা শেখান। বাইবেল, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, ব্রিটিশ সাহিত্য এবং গ্রিক ও ল্যাটিন ক্লাসিক্সে তিনি গভীরভাবে নিমগ্ন হন। তার প্রথম দিকের কবিতা ‘টু দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ ইন নিউ ইংল্যান্ড’ ইঙ্গিত দেয় যে, একজন দাসের জন্য এমন ব্যতিক্রমী সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, তার আত্মা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইচ্ছাপোষণ করত।
প্রথমদিকে মনে করা হতো ‘অ্যান এলিগিয়াক পোয়েম...’ (১৭৭০) তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা। তবে, কার্ল ব্রিডেনবগ ১৯৬৯ সালে প্রকাশ করেন যে ১৩ বছর বয়সে লেখা তার ‘অন মেসার্স. হসি অ্যান্ড কফিন’ ১৭৬৭ সালের ২১ ডিসেম্বর নিউপোর্ট, রোড আইল্যান্ডের ‘মার্কারি’তে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু হোয়াইটফিল্ডের শোকগাথাই তাকে জাতীয় খ্যাতি এনে দেয় এবং ১৭১১ সালে লন্ডনে এর প্রকাশনা তাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়।
১৮ বছর বয়সে, হুইটলি ২৮টি কবিতার একটি সংকলন তৈরি করেন। বোস্টনের উপনিবেশবাদীরা একজন আফ্রিকান দাসের সাহিত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তিনি এবং হুইটলি পরিবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে লন্ডনে প্রকাশকের সন্ধান করেন। হোয়াইটফিল্ডের ধর্মযাজকের সহায়তায় ১৭৭৩ সালের ৮ মে হুইটলি তার অসুস্থতার কারণে নাথানিয়েলের সাথে লন্ডনে রওনা হন। সেখানে তিনি আর্ল অফ ডার্টমাউথ, ব্যারন জর্জ লিটেলটন, স্যার ব্রুক ওয়াটসন, জন থর্টন এবং বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সাদরে গৃহিত হন। তিনি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ফিরে আসার সময় তার প্রথম কবিতার সংকলন, ‘পোয়েমস অন ভেরিয়াস সাবজেক্টস, রিলিজিয়াস অ্যান্ড মোরাল’ (১৭৭৩), আধুনিক যুগে প্রকাশিত একজন আফ্রিকান আমেরিকান দ্বারা লিখিত প্রথম কবিতার সংকলন, প্রকাশিত হয়।
‘পোয়েমস অন ভেরিয়াস সাবজেক্টস’ থেকে জানা যায় যে হুইটলির প্রিয় কাব্যিক রূপ ছিল যুগলবন্দী। তার রচনার এক-তৃতীয়াংশের বেশি শোকগাথা। তিনি ধ্রুপদী থিম এবং কৌশল ব্যবহার করে কবিতা লিখতেন। ধ্রুপদী এবং নব্যধ্রুপদী কৌশল ছাড়াও, হুইটলি বাইবেলীয় প্রতীক ব্যবহার করে দাসপ্রথা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তার সবচেয়ে পরিচিত কবিতা ‘অন বিয়িং ব্রট ফ্রম আফ্রিকা টু আমেরিকা’-এ তিনি খ্রিস্টান শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেন যে আফ্রিকানদের খ্রিস্টান সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তার অবশিষ্ট কবিতাগুলিতে আমেরিকার উদযাপন দেখা যায়। তিনিই প্রথম এই জাতিকে ‘কলম্বিয়া’ নামে অভিহিত করেন এবং জর্জ ওয়াশিংটনের সাথে তার চিঠিপত্র ছিল। ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর টমাস হ্যাচিনসন, জন হ্যানকক এবং জেমস বোডিনের মতো উপনিবেশিক নেতারা তার কাজকে প্রমাণ ও সমর্থন করেছিলেন।
১৭৭৪ সালের ৩রা মার্চ মিসেস হুইটলির মৃত্যুর প্রায় তিন মাস আগে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে, এই মুক্তি তার জন্য অর্থনৈতিকভাবে কঠিন ছিল। তার উপকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর, হুইটলি এক অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশ করেন। যুদ্ধের বছরগুলিতে এবং মন্দার সময়ে তার জাতিগত বাস্তবতার কঠোরতা তার অসুস্থ শরীর ও নান্দনিক আত্মাকে বিধ্বস্ত করে তোলে।
১লা এপ্রিল, ১৭৭৮ সালে, হুইটলি জন পিটার্সকে বিবাহ করেন। পিটার্স একজন মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। তিনি ড. পিটার্স নামে পরিচিত ছিলেন, আইন অনুশীলন করতেন, একটি মুদি দোকান চালাতেন এবং নাপিত হিসেবে কাজ করতেন। সেকালে যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের কেবল শারীরিক শক্তির মূল্য ছিল, পিটার্সের ব্যবসায়িক দক্ষতা তেমন ছিল না। বিপ্লবী যুদ্ধের সময় বোস্টন থেকে পিটার্স দম্পতি উইলমিংটন, ম্যাসাচুসেটসে চলে যান।
যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল কঠিন, বিশেষ করে মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য। এই সামাজিক কারণগুলিই হুইটলি পিটার্সের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী ছিল। এই দম্পতির সম্ভবত তিনটি সন্তান ছিল। পিটার্স আরও দারিদ্র্যের দিকে চলে যান, যার ফলে হুইটলিকে প্রায়শই বিভিন্ন কাজ করতে হতো।
বোস্টনে ফিরে আসার পর, হুইটলি পিটার্স তার এক ভাগ্নির সাথে একটি বিধ্বস্ত প্রাসাদে কিছুদিন ছিলেন। এরপর পিটার্স তাদের বোস্টনের একটি জরাজীর্ণ একটি অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যান, যেখানে হুইটলি অসুস্থ ও নিঃস্ব অবস্থায় ছিলেন।
এই কঠিন বছরগুলিতেও হুইটলি কবিতা লেখা ও প্রকাশ করা চালিয়ে যান এবং সীমিত আকারে দেশ-বিদেশে চিঠিপত্র আদান প্রদান চালিয়ে যান। সংসারের দৈন্যদশা সত্ত্বেও তিনি কবিতার বই প্রকাশের জন্য আমেরিকান পাঠকদের সমর্থন আশা করেছিলেন। ১৭৭৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি তার পরিবারের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বই প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন দেন, কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি। তার মৃত্যুর বছরে (১৭৮৪), তিনি ‘ফিলিস পিটার্স’ নামে ‘লিবার্টি অ্যান্ড পিস’ শিরোনামে একটি প্যামফলেট (ছোট আকারের প্রকাশনা) প্রকাশ করতে সক্ষম হন, যা আমেরিকাকে ‘কলম্বিয়া’ হিসাবে ‘ব্রিটানিয়া ল’-এর বিরুদ্ধে বিজয়ী হিসাবে বর্ণনা করে।
১৭৮৪ সালের ৫ ডিসেম্বর ফিলিস হুইটলি পিটার্স মারা যান। তার মৃত্যুর সময় জন পিটার্স কারাগারে ছিলেন।
সাম্প্রতিক গবেষণায় হুইটলি পিটার্সের প্রায় ১৪৫টি কবিতা (যার অধিকাংশই অপ্রকাশিত), চিঠি এবং তার জীবন সম্পর্কে আরও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গবেষণা তার দাসপ্রথার প্রতি ঘৃণা প্রমাণ করে। ২০ শতকের গোড়ার দিকের সমালোচকরা দাসপ্রথা সম্পর্কে তার উদ্বেগের অভাবের জন্য তাকে কঠোরভাবে বিচার করলেও, তিনি চার্চের মতো প্রভাবশালী অংশের কাছে বাইবেলীয় ইঙ্গিত এবং প্রতীক ব্যবহার করে দাসপ্রথা সম্পর্কে তার বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। একটি শোকগাথায় তিনি এমন দেশপ্রেমিকদের তিরস্কার করেন যারা খ্রিস্টধর্মের কথা স্বীকার করেও তার লোকদের উপর অত্যাচার করে। একটি চিঠিতে তিনি আমেরিকান দাসত্বকে প্রাচীন মিশরের পৌত্তলিক দাসত্বের সাথে তুলনা করেন।
কাব্যবোদ্ধাদের মতে হুইটলি তার লেখায় নান্দনিকতার উল্লেখযোগ্য ব্যবহার এবং বাইবেলীয় ইঙ্গিতগুলির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন। অতি শীঘ্রই হয়তো তার শিল্পের সম্পূর্ণ নান্দনিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্য এবং তার জীবন ও কাজ সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। তিনি আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবেই চিরকাল সম্মানিত হবেন।
ফিলিস হুইটলি’র কবিতা
আমাকে আফ্রিকা থেকে আমেরিকা আনার কথা
দয়া করে আমাকে আনা হয়েছিল পৌত্তলিক ভূমি থেকে
আমার অজ্ঞ আত্মাকে বুঝতে শিখিয়েছিল
একজন ঈশ্বর আছেন, আাছেন একজন ত্রাণকর্তাও:
একদা আমি মুক্তি চাইনি বা জানতামও না।
কেউ কেউ আমাদের কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে ঘৃণাভরে দেখে,
‘তাদের রঙ এক শয়তানি রঙ।’
খ্রিস্টানরা, মনে রেখো, নিগ্রোরা কেনের মতো কালো হলেও,
বিশুদ্ধ হতে পারে এবং যোগ দিতে পারে স্বর্গীয় দলে।
সদ্গুণের প্রতি
হে উজ্জ্বল রতœ, ছিলাম সন্ধানে তোমার,
তোমাকেই ধরতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি।
তুমিই তো বলো-
জ্ঞান অতি উচ্চ, যেখানে মূর্খের পৌঁছানো দুঃসাধ্য।
আমি আর বিস্ময়ে ভাসি না,
তোমার গভীরতা মাপার চেষ্টাও করি না আর।
কিন্তু হে আমার আত্মা, হতাশ হয়ে যেও না,
সদ্গুণ তোমার খুব কাছেই আছে,
সে কোমল হাতে তোমাকে আলিঙ্গন করতে চায়,
তোমার মাথার উপরেই যেন ভাসছে-
স্বর্গজ আত্মা তার সঙ্গে কথা বলতে চায়,
তবে খোঁজো, তবে তাকে প্রণয় নিবেদন করো তার
প্রতিশ্রুত পরম সুখের জন্য।
হে শুভ্র রানী, মেলে দাও তোমার স্বর্গীয় ডানা,
আর স্বর্গীয় শুচিতাকে সাথে নিয়ে চলো;
দেখো! এখন তার পবিত্র অনুচরবর্গ নেমে আসছে,
উপরের গোলক থেকে গৌরবময় রূপে সজ্জিত হয়ে।
আমাকে সঙ্গ দাও, সদ্গুণ, আমার তারুণ্যের বছরগুলো জুড়ে!
ওহ্ আমাকে সময়ের মিথ্যা আনন্দের কাছে ছেড়ে দিও না!
বরং আমার পদক্ষেপগুলোকে
অনন্ত জীবন ও পরম সুখের দিকে পরিচালিত করো।
মহত্ত্ব, নাকি সদ্গুণ, বলো তোমাকে কী নামে ডাকবো,
যদি আরও উচ্চতর কোনো নাম দিতে হয়,
আমাকে শেখাও আরও ভালো সুর, আরও মহৎ গান,
ওহ্ তুমি, দিনের রাজ্যে সিংহাসনে আসীন!
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-
এ মুখর বরষায়
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

ব্রেশায় উড়োজাহাজ