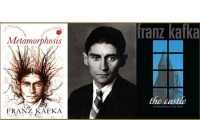সাময়িকী
নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
আতিক আজিজ
কাজী নজরুল ইসলাম
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কৈশোর জীবনেই গল্প লেখা আরম্ভ করেছিলেন, কাব্য রচনা আরম্ভের পরে পরেই। বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে একটা কৌতুকপ্রদ তথ্য জানা যায়। বর্ধমানের শিয়ারশোল রাজস্কুলে পড়বার সময় কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ ছিলেন নজরুলের সহপাঠী। অবশ্য সহপাঠী এই অর্থে যে তাঁরা একই শ্রেণিতে পড়তেন তবে কাছাকাছি দু’টি স্কুলে। দুই উচ্চাকাক্সক্ষী কিশোর পরস্পরকে নিজের লেখা দেখাল: নজরুল দেখালেন তাঁর গল্প, এবং শৈলজানন্দ তাঁর কবিতা। দু’জনেই দু’জনের লেখা পড়ে এমন মুগ্ধ হলেন যে তখন থেকে শৈলজানন্দ লিখতে লাগলেন গল্প এবং নজরুল লিখতে লাগলেন কবিতা। অনতিকাল পরে কবি হলেন কথাসাহিত্যিক, কথাসাহিত্যিক হলেন কবি।
নজরুল ইসলামের গল্পের বই তিনখানি, এবং তিনখানি উপন্যাস। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন ‘ব্যথার দান’ প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে, সর্বশেষ গল্প-সংকলন ‘শিউলিমালা’ ও সর্বশেষ উপন্যাস ‘মৃত্যুক্ষুধা’ ১৯৩১ সালে। এই সময়টি ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে সৃষ্টিমুখর, কথাসাহিত্যে সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দেওয়া তাঁর পক্ষে এই সময়েই ছিল স্বাভাবিক। কথাসাহিত্যের উপযোগী প্রচুর অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন সমৃদ্ধ, এবং বহু নাটকীয় ঘটনায় বিশিষ্ট; তিনটি গল্পগ্রন্থ ও তিনটি উপন্যাস প্রকাশের সুযোগও তিনি পেয়েছেন, অতএব কথাসাহিত্যে সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগও তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন ও প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নয়। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ করে না।
এই বিবরণের মধ্যে ভ্রান্তি এইখানে যে শৈলজানন্দের সংগে সাহিত্যালোচনার সময় থেকে নয় তার আগে থেকেই, একেবারে বাল্যকাল থেকে নজরুল কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা থেকে এই একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে কথাসাহিত্যিক হবার আকাক্সক্ষা ও সাধনা নজরুলের কিশোর-জীবন থেকেই ছিল। সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় করাচি থেকে যে সব লেখা তিনি কলকাতার সাহিত্য-পত্রিকাগুলোতে পাঠাতেন, এবং তাঁর যে সব প্রথম লেখা এই পত্রিকাগুলোতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে গল্প নামে কথিত গদ্য রচনাও ছিল, যেমন ‘বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী’ বা ‘হেনা’।
এতদিনের গল্পচর্চার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে অনন্যসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও নজরুল গল্প লেখার সাফল্য দেখান নি। তাঁর গল্পগুলি পড়ে বারে-বারেই মনে হয়, গল্প লেখকের সংযম, পরিমিতিবোধ ও শিল্পচেতনা তাঁর ছিল না। ছোটগল্পের শেষে ব্যক্তি, জীবন বা সমাজ সন্বন্ধে যে লিরিকধর্মী চেতনা বা উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার লক্ষণ তাঁর কোনো গল্পেই নেই। ছোটগল্পের সঠিক রূপ কী সে সন্বন্ধে নজরুলের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি তাঁর গল্পগুলিতে নায়ক-নায়িকাদের জীবন-কাহিনী বা স্বগতোক্তি উচ্ছ্বাসময় ভাষায় অনর্গল লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এইমাত্র। বিশেষভাবে ‘ব্যথার দান’ এবং ‘রিক্তের বেদন’ সন্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে। ‘শিউলিমালায়’ দেখা যায় নজরুল গল্প বলার আর্ট সন্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছেন, নিছক স্বগতোক্তি বা উচ্ছ্বাসময় ভাবপ্রবণ কথার খৈ না ফুটিয়ে গল্প যে ভাবে লেখা হয়, অনেক ঘটনা ও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে গল্প যেভাবে গড়ে তোলা হয় সেইভাবে তিনি লিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু এ বইয়েও তিনি গল্পের কৌশল আয়ত্ত করতে পারেননি।
দু’একটি গল্প- যেমন ‘পদ্মগোখরে’ এবং ‘সালেক’ ছাড়া নজরুলের বাকি সমস্ত গল্পেরই বিষয়বস্তু প্রেম, এবং ব্যর্থ প্রেম। অতএব একঘেঁয়েমি। কিন্তু এর চেয়েও বড় ত্রুটি হচ্ছে, তাঁর গল্পগুলির কাহিনী অংশে কার্যকারণসূত্র এবং অনিবার্যতার পরিমাণ একান্তই নগণ্য। ‘রিক্তের বেদন’-এর ‘বাউ-েলের আত্মকাহিনীতে’ বা ‘ব্যথার দান’-এর ‘অতৃপ্ত কামনা’ গল্পে, বা ‘শিউলিমালা’র নাম গল্পে কী কারণে নায়ক-নায়িকাদের প্রেম ব্যর্থ হলো তার কোনো হদিসই পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না, বস্তুত, নজরুলের প্রায় কোনো গল্পেই। মনে হয়, যে কোনো প্রকারে হোক করুণরসের সৃষ্টি করতে হবে এই ছিল তার শিল্পলক্ষ্য।
‘বাঁধনহারা’ নজরুলের প্রথম উপন্যাস, পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত ১৯২৮ সালে, ধারাবাহিকভাবে ‘মোসলেম ভারতে’ বেরিয়েছিল তার কয়েক বছর আগে। এর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য- এটি পত্রোপন্যাস। যতদূর জানা যায়, বাংলা ভাষায় নজরুলই সর্বপ্রথম পত্রোপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসের এই নতুন আঙ্গিকের সদ্ব্যবহার করতে নজরুল পারেন নি। চিঠিগুলির লেখক-লেখিকাদের নামেই যা-কিছু পার্থক্য, ব্যক্তিত্ব বলতে তাদের কিছুই নেই। তাদের রচনারীতি ও চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সহজে চোখে পড়ে না। লেখক-লেখিকাদের প্রত্যেকেই ভাবপ্রবণ ও হয়ত কিছুটা চিন্তাশীল, এবং প্রত্যেক চিঠির লাইনগুলির মধ্য দিয়ে মাত্র একজন লোকই উঁকি দিচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন নজরুল। পত্রোপন্যাস, নাটকে অথবা আধুনিক উপন্যাসে লেখকের যতখানি আত্মলোপ করা প্রয়োজন নজরুল তা করতে পারেন নি। চিঠিগুলির লেখক-লেখিকাদের নারী-পুরুষের পার্থক্য যদিবা বোঝা যায়, বয়স বোঝা যায় না। অভিজ্ঞ গৃহিণী রাবেয়ার চিঠি আর পনেরো-ষোল বছরের মাহবুবার চিঠি চিন্তা ও রচনারীতির দিক দিয়ে প্রায় একই রকম পরিণত। অনেকগুলি চিঠি হয়ে ওঠেনি, হয়ে পড়েছে কতকটা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অথবা ভাবপ্রবণ নির্জনচিন্তার দীর্ঘ অনুলিপি। বক্তব্য পেশের রীতি অতিপল্লবিত। নায়ক নূরুল হুদার চিঠি কোথাও কোথাও অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। গল্পাংশের গতি শামুকের মত মন্থর; বইয়ের মোট ১৮৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েও দেখা যায়, কাহিনী কিছুই এগোয় নি।
তবে এ উপন্যাসে কিছুই যে ঘটেনি তা নয়, ঘটেছে, কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, চিঠিপত্রের মারফত রটেছে মাত্র। নায়ক নূরুল হুদাকে মাহবুবা আর শোফিয়া নামে দুই সই এক সংগে ভালবাসত, কিন্তু কেন যে তাদের কারো সঙ্গেই হুদার বিয়ে হলো না তার কোনো সন্তোষজনক কার্যকারণই দেখানো হয়নি। নজরুল এ বইয়ে প্রচুর করুণ-রসের হয়ত তাঁর ধারণামতে ট্র্যাজেডির-সৃষ্টি করতে চেয়েছেন স্বল্পপড়–য়া পাঠক-পাঠিকাদের জন্য, ঠিক তাঁর গল্পগুলির মতো, এই সন্দেহ পাঠককে পেয়ে বসে।
নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘কুহেলিকা’ এবং তৃতীয় উপন্যাস ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ বেরিয়েছিল ১৯৩১ সালে, এই একই বছরে পুস্তকাকারে বেরিয়ে ছিল ‘শিউলিমালা’। অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের তুলনায় নজরুল এই তিনটি বইয়ে একটি ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে এগিয়েছেন- ভাবপ্রবণতা এখানেও আছে কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাস অনেক কমে গেছে, এবং গল্পাংশের সংগঠন ও সংলাপের দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছেন। লক্ষ্য এখনও তাঁর স্থির নয়, কিন্তু কথাশিল্পের আর্ট তিনি অনুশীলন করেছেন, আয়ত্ত করারও চেষ্টা করেছেন।
‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে নজরুলের কৃতিত্ব এইখানে যে, বাংলা ভাষায় সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস বিচারে এরূপ কৃতিত্বের মূল্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু শিল্পমূল্যের প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড়। ‘কুহেলিকা’র শিল্পমূল্য বেশি নয়।
উপন্যাসের নায়কের নাম জাহাঙ্গীর। সে একটা আর্কষণীয় চরিত্র হতে পারত, আকর্ষণীয় চরিত্র হবার মতো গুণ তার মধ্যে ছিল, ছিল উদ্দামতা, বিশালতা, ঔদার্য, সাহসিকতা, বন্ধনহীনতা, কিন্তু সে আকর্ষণীয় হতে পারে নি, তার অতিমাত্রিক ভাবালুতা- যা নজরুল ইসলামের সর্বব্যাপী দোষ, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গন। জাহাঙ্গীরকে জারজ সন্তান করা হলো কেন তার কোনো সঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের জন্মের ইতিহাস জানবার আগেই সে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিল, এবং তার চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা অসম্ভব হতো না সে জারজ সন্তান না হলেও।
এমনি শিল্পগত ক্রটি ‘কুহেলিকা’য় আরও আছে। উপন্যাস পড়তে বসেই রুচিবান পাঠক ধাক্কা খাবেন: এর প্রথম পরিচ্ছেদে নারী সম্পর্কিত আলোচনাটা অশোভন না হলেও স্থূল। তবে উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ত্রুটি বোধ হয় জাহাঙ্গীর আর ভূণীর আকস্মিক বাগদান। এই ঘটনাকে সম্ভাব্য করে তোলার জন্য ভূণীর মাকে পাগলিনী বলে চিত্রিত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বাগদান প্রসঙ্গটি ঠিক বাস্তব হয়ে ওঠেনি। এ নিছকই একটা ঘটনা, এবং অদ্ভূত ঘটনা। অথচ যথেষ্ট শিল্পচর্যা থাকলে এই ঘটনাই সুন্দর হয়ে উঠতে পারত। ব্যাপারটা নজরুল অতি তাড়াতাড়ি ঘটাতে চেয়েছেন। কোনো নাটকীয় মেলোড্রামটিক নয়) পরিস্থিতি, কোনো সাসপেন্স, কোনো কাব্যময় পরিবেশের সৃষ্টি তিনি করেননি। তার পর ভূণীর কয়েকটি উক্তি। এই লজ্জাশীলা অশিক্ষিতা ষোড়শী পল্লীবালা কথা বলেছে পূর্ণবয়স্কা সুশিক্ষিতা নারীর মতো, যা সে বলেছে সোজাসুজিই বলেছে, নারীসুলভ কমনীয়তা, ব্রীডা, ব্যঞ্জনা তার মধ্যে নেই। কিন্তু থাকা উচিত ছিল, কারণ জাহাঙ্গীরের সংগে বিয়ে তো তার হয়ই নি, দু’তিন ঘণ্টার পরিচয়ের মধ্যে উন্মাদিনী মাতা অজ্ঞান অবস্থায় অকস্মাৎ বাগদান করেছে মাত্র। অথচ সে বলছে:
“আপনি যেটা মিথ্যা বলছিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, সেটার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই। আপনি বলবেন, মা আমার উন্মাদিনী। তবু তিনি আমার মা। আমরা নারী, আমরা হয়ত সকল কিছু অন্ধের মতো বিশ্বাস করি। খোদার ইঙ্গিত না থাকলে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমার উন্মাদিনী মায়ের হাত দিয়ে ঘটত না।” তাহার পর সে একটু থামিয়া বলিল, “আমি খুলেই বলি আপনাকে, মা যার হাতে আমার সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নাই! এমনি ‘কুহেলিকা’র অনেক ঘটনাই ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে নয়, নজরুল ইচ্ছা করেছেন বলেই। এবং এই ইচ্ছা শিল্পগত নয়, যে কোনোভাবে হোক চমকপ্রদ একটা কিছু ঘটাতে হবে এই নজরুলের ইচ্ছা, এই উপন্যাসে এবং অন্যান্য সর্বত্র। শিল্পচর্যা থাকলে যা হয়ে উঠত স্বাভাবিক, শিল্পচর্যার অভাবে তাই হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক, যেমন উল্লিখিত ঘটনা।
কিন্তু এ উপন্যাসে কিছু কিছু ভালো অংশ আছে, যেমন তৃতীয় পরিচ্ছেদ, যেখানে বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে তাদের আন্দোলনে মুসলমানদের নেওয়া যায় কিনা।
জাহাঙ্গীরের প্রিয় বন্ধু অনিমেষ বলিয়া উঠিল- “প্রমত-দা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ার অন্ততঃ আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান তা ভেবে দেখিনি! তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর না বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামীকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি- ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরি প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক বিপ্লবসঙ্ঘের অধিনায়ক। আপনি বোধ হয় বুঝেছেন। প্রমত-দা, আমি কা’কে কা’কে মনে ক’রে এ-কথা বলছি।” প্রমথ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। অনেকেই সে-হাসির অর্থ বুঝিল না।
অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল- “তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? বলেন- “আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে। সন্ধি করব ল-ন এবং মক্কা অধিকার করে।” তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না।”
এক শ্রেণির হিন্দুর মুসলিম-বিদ্বেষী মানসিকতাকে নজরুল এখানে নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন। এ মানসিকতার ভিত্তি ছিল। উনিশ শতকে বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাস রচনার পেছনে ছিল এমনি মানসিকতা, নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর অহ অঁঃড়নরড়মৎধঢ়যু ড়ভ অহ টহশহড়হি ওহফরধহ বইয়ে এবং মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনী ওহফরধ ডরহং ঋৎববফড়ড়স-এ এই মানসিকতা সন্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ‘কুহেলিকা’র এই অংশে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের সংগে নজরুলের কিছু যোগাযোগ ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে তিনি উচ্চকণ্ঠ হতে পেরেছিলেন অনেক কবিতায়, গানে ও এই উপন্যাসে! রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদীদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সকলের সামনে। তাঁর উদার ও সুস্থ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায় ‘কুহেলিকা’র এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে এবং এর আলোচনার ধারাটাও মর্যাদাময়, ফরমহরভষবফ-ছেলেমি নয় বা মেঠো বক্তৃতার মতো নয়। এই পরিচ্ছেদটি, আমার মতে, যে-কোন ভালো উপন্যাসের উপযুক্ত।
নজরুলের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ সর্বশেষ এবং এই বিভাগে এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’র সূচনা থেকে ১৫শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশ যে কোনো ভালো উপন্যাসের মতো। তারপর এর কাহিনী অংশ পথভ্রান্ত হয়েছে- কিন্তু সে কথা পরে। নিচুতলার মানুষ এ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা, তাদের জীবনযাত্রা ও পাড়ার বর্ণনা দিয়ে এর শুরু। এ বর্ণনা যথাযথ; ভাষা, উপমা ও চিত্রকল্প বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী।
এরা যেন মৃত্যুর মান-গুদাম। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই। আমদানী হতে যতক্ষণ, রপ্তানী হতেও ততক্ষণ।
বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পান্তাভাত খেয়ে মজুরীতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বিশ ক’রে দু’ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সন্বন্ধের বাছ-বিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজেঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।
এই সমাজের মেয়েলি ঝগড়ার একটা নিপুণ ও উপভোগ্য বর্ণনা প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে। তার কিছু নমুনা: গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িন্বা তার পেতলের কলসীটা ঢং ক’রে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে থ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত ক’রে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, “তা বলবি বই কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ীর হারামরাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!”
গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসীর সব জলটা মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, “ওলো আগ্-ধুম্সী। (রাগ্-ধুম্সী) ওলো ভাগলপুুরে গাই। ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল- জজ সায়েবের লো, ইংরেজের!”
পুটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষè ক’রে উঠল, “আ-সইরণ সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি, অ গজালের মা! ঐ জজ সায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা ‘আজার’ (রাজার) জাত, জানিস?” (বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় পড়–ন)
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-
এ মুখর বরষায়
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

ব্রেশায় উড়োজাহাজ