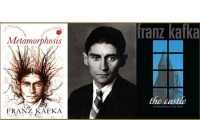সাময়িকী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
খুর্শিদা বারী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহরের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিলো নোয়াখালী। তিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিও ছিলেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন তাঁর পিতা। শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ ঘটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর। আট বছর বয়সে তিনি তাঁর মা নাসিম আরা খাতুনকে হারান। ওয়ালীউল্লাহরা ছিলেন তিন ভাই ও তিন বোন। সকল ভাই ও বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর মা ও খালা ছিলেন সুলেখিকা। মাতার শিল্পবোধ ওয়ালীউল্লাহকে শৈশব অবস্থায় নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এ পাশ করেন ১৯৪১ সালে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি. এ পাশ করেন ১৯৪৩ সালে। কলকাতা বিশ^বিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগ এম. এ ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করলেও তা শেষ না করেই সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন। তিনি সেই আমলের বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এর সাংবাদিক হন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার ‘দৈনিক স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। একই সময় তিনি ‘কমরেড পাবলিশার্স’ নামে একটি পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত লালসালু (১৯৪৮) প্রকাশিত হয়। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই সময় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে ‘পরিচয়’ পত্রিকার যে নিয়মিত আড্ডা বসতো, সেই আড্ডায় যোগদান করতেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তিনি নিজেও আগে থেকেই লিখতেন, এবার বিস্তৃত পরিসরে এসে তিনি নতুন ভঙ্গির লেখায় মনোযোগী হন। দেশভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। করাচি বেতারকেন্দ্রের বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন ১৯৫০-১৯৫১ সাল অবধি। ১৯৭১ সালে প্যারিসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি সক্রিয় কর্মপরিচালনা করেন।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে: উপন্যাস- লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮), কদর্য এশীয় (২০০৬), শিম কীভাবে রান্না করতে হয় (২০১২)। ছোটগল্পগ্রন্থ- নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫), গল্পসমগ্র (১৯৭২)। নাটক- বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন প্রথম উপন্যাস লালসালুকে কেন্দ্র করেই। আমাদের দেশে মোল্লা, মৌলভী ও পীরেরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের ওপর কী রকম প্রভাব বিস্তার করে আছে তা সেই বিখ্যাত বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন। গ্রন্থটি ১৯৪০ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে। বহিপীর নাটকটি ১৯৬৫ সালে পিএন-এর আঞ্চলিক পুরস্কার পায়। এছাড়া তাকে দুই তীর ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার প্রদান করা হয় ১৯৬৫ সালে। ১৯৮৩ সালে তিনি একুশে পদন লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেথক। তাঁর লেখার সংখ্যা কম কিন্তু গুণে সেগুলো বিশিষ্ট। তিনি এক স্বতন্ত্র লেখক। তাঁর লেখার ভঙ্গি আলাদা। তিনি তাঁর লেখায় মানবজীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের চমকপ্রদ বিশ্লেষণ আছে। অনন্য শৈল্পিক বিশ্লেষণ তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখার ভাববস্তুকে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলার উপেক্ষিত গ্রামজীবন থেকে গল্পের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন ঠিকই, পটভূমিকায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ছবিও। কিন্তু তাঁর উপস্থাপনায় বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক শিল্পকৌশল সবসময় প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করার নিরঙ্কুশ বাস্তবতা বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে গল্পের ভাবকল্প, বিষয়বস্তু ও চিত্রচরিত্রের যোগাযোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। লেখকের ইচ্ছায় হোক অথবা তাঁর শিল্পচেতনার স্বভাবধর্মেই হোক, এই দূরত্ব তাঁকে পাঠকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তিনি যে শিল্পকৌশল সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, সেটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব এবং এই নিজস্বতা কোনোক্রমেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গড়ে তোলা নয়, বরং বলা চলে আধুনিক অনেক বিশিষ্ট গল্প লেখককে তাঁর সেই অসাধারণ শিল্পকৌশল নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।
বহিপীর নাটকটি ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের আগে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় ‘পিইএন ক্লাবে’র উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতায় বহিপীর নাটক পুরস্কার লাভ করে।
বহিপীর নাটকের ঘটনা ছোট ও মামুলি। রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলী বজরায় তাঁর স্ত্রী খোদেজা ও হাশেমকে নিয়ে শহরে যাচ্ছিলেন। ডেমরা ঘাটে পৌঁছে তারা দেখেন তীরে ভিড়। একটি ছোট ছেলে কাঁদছে, পাশে অল্প-বয়স্কা একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চাকরের কাছে তারা জানতে পারেন যে একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে। দয়াপরাবশ হয়ে তারা মেয়েটিকে বজরায় তুলে নেন। মেয়েটার নাম তাহেরা। তাহেরার বাবা ও সৎ-মা তাদের এক বুড়ো পীরকে, যার নাম বহিপীর, খুশি করার জন্য তাকে সেই পীরের সাথে বিয়ে দেন। বিয়েতে তাহেরা রাজি না থাকায় বিয়ের রাতেই ছোট এক চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। নতুন বউকে খোঁজার জন্য বিপতœীক ও বুড়ো বহিপীরও নৌকাযোগে বেড়িয়ে পড়ে। ঝড়ের মধ্যে বহিপীরের বজরার সঙ্গে অন্য বজরার ধাক্কা লাগে। জমিদার হাতেম আলি বহিপীরকে তার বজরায় তুলে নেন। একসময় বহিপীর জানতে পারে এই বজরায়ই তার নববিবাহিতা স্ত্রী আছে। তখন তিনি তাকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কূটকৌশল আটতে থাকেন। অন্যদিকে জমিদারের পুত্র হাশেম আলি তাহেরার করুণ কাহিনি জানতে পেরে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। এতে হাসেম ও বহিপীরের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। বহিপীর তার জঘন্য কূটকৌশল গ্রহণ করেতই থাকে। এমনকি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগও গ্রহণ করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হতে পারেন না। এখানেই নাটক শেষ হয়নি, এগিয়ে গেছে আরও একটু। হাশেম-তাহেরাকে নিয়ে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ায়। বাস্তব পরিস্থিতিতে বহিপীরও তা মেনে নেয়।
বহিপীর নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নামচরিত্র বহিপীর নিজেই। সে অত্যন্ত ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। সে কথাবার্তায় বইয়ের ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। তার ভাষায়:
আপনি হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকবেন যে আমি কথাবার্তা বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। ... সে সমস্যার সমাধান করবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান।
বহিপীর মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ^াসকে পুঁজি করে তার ধর্মব্যবসা পরিচালনা করে। সে সারাবছর মুরিদদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ান। তাদের কাছ থেকেই অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেন। এবার তিনি বৃদ্ধ বয়সে এক মুরিদের মেয়েকে বিয়ে করেন কিন্তু পাত্রী পালিয়ে যায়। আবার ঘটনাক্রমে তার সন্ধানও পেয়ে যায়। তখন তিনি অত্যন্ত চালাকি ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয়গ্রহণ করে। নাটকের এক পর্যায়ে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন সে বাস্তবতা মেনে নেয়। তাই তাকে আমরা বলতে শুনি, ‘তাহারা গিয়াছে, যাক। তা ছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।’
তাহেরা এই নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা। বৃদ্ধপীরের সাথে অন্যায় বিয়ে সে মেনে নেয়নি, পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরগামী বজরায় চড়ে বসেছে। কিন্তু একসময় পীরের কাছে ধরা পড়েও তার সাথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এই হিসেবে তাহেরা একটি অত্যন্ত অনমনীয় চরিত্র।
হাশেম আলী চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র। সে অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপীরের কূটচালকে মোকাবিলা করেছ এবং পরিশেষ জয়লাভ করেছে। বহিপীর নেতিবাচক টরিত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসেবে জীবন ও জগৎকে গণনা করে। অন্যদিকে হাশেম আলী ইতিবাচক চরিত্র। মানবীয় মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের গুরুত্ব তার কাছে সর্বাধিক।
হাতেম আলী একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। জমিদারি নিলামের কথা কারও কাছে না বললেও পরে বহিপীরের কাছে কথাটি সে আর গোপন রাখেনি। বহিপীর সুযোগ গ্রহণ করে টাকা দিতে চাইলেও শেষে সে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ শেষে তার মানবিক মূলবোধ জাগ্রত হয়। এতে হাতেম আলীর উচ্চনৈতিকতাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি স্থিতধী, আত্মনিমগ্ন মানবিক চেতনাসম্পন্ন একটি উজ্জ্বল চরিত্র।
হকিকুল্লাহ ও খোদেজা এই নাটকে দুইটি অপ্রধান চরিত্র। খোদেজা অত্যন্ত সাদামাটা চরিত্র। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অত্যন্ত ধর্মভীরু। হকিকুল্লাহ পীরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে পীরের সহকারী।
নাটক বিভক্ত পাঁচটি অঙ্কে। আরম্ভ, প্রবাহ, চরম, গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার- এই প্রচলিত রীতিকে আধুনিক অনেক নাট্যকারের মতো অস্বীকার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। বহিপীর নাটকের যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করার মতো তা হলো-
ক. এর মঞ্চ-পরিকল্পনা ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব
খ. সংলাপ, যা নাটকের একটি বিশিষ্ট উপাদান, ব্যবহারের নতুনত্ব
গ. অধিকাংশ বাংলা নাটকের মতো ভাঁড়-বিদূষকের সস্তা হাস্যরসের অনুপস্থিতি
ঘ. পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও কম, চারটি পুরুষ দুটি নারী।
কয়েকটি সূক্ষ্ম কাজ ও ইঙ্গিতময়তা বহিপীর নাটকে লক্ষ্য করার মতো। যেমন- পীরের বইয়ের ভাষায় কথা বলাটা পরজীবী ও ভন্ড এই শ্রেণিটির স্বভাবের কৃত্রিমতার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত; বজরা, যা জমিদারের চলমান প্রাসাদ, পুরোনো মূল্যবোধের আশ্রয়ের প্রতীক যদি হয় তাহলে সেই বজরা থেকেই বেরিয়ে নবীন নায়ক-নায়িকা চলে যেতে থাকে, তা হয়ে ওঠে পুরোনোকে প্রত্যাখ্যান অথবা পুরোনো থেকে পলায়ন; প্রাচীনের সংকীর্ণতা থেকে নতুনের যাত্রা।
সামাজিক সমস্যা ও পুরোনো মূল্যবোধ সংক্রান্ত এই নাটকটির প্রতিটি চরিত্রই বিকশিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বাভাবিকভাবে। ওয়ালীউল্লাহর স্বভাবসুলভ বাক-সংযম বহিপীর নাটকের বৈশিষ্ট্য। কোনো চরিত্রই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। আধুনিক বাংলা গদ্য থেকেই বস্তুত সাধু ভাষা বিদায় নিয়েছে, গল্প-উপন্যাসে এমনকি প্রবন্ধেও সাধুভাষার ব্যবহার যখন নেই বললেই চলে, তখন মধ্য ১৯৫০-এ নাটকের মূলচরিত্রের সংলাপে সাধুভাষার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সাহসী ও অভিনব পদক্ষেপ। লালসালুর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিলো, বহিপীর-এ আঞ্চলিক ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীতে সাধুভাষাকে নিয়ে এলেন নৈপুণ্যের সঙ্গে। নাটকে বহিপীর ছাড়া আর সকলেই চলিত ভাষায় কথা বলে, তা সত্ত্বেও বহিপীরের দীর্ঘ সংলাপের ক্রিয়াপদগুলো পর্যন্ত কানে বাজে না, কৃত্রিম মনে হয় না ভাষারীতি, বরং কৃত্রিমতা ও কপটতার প্রতিভূ হয়ে ওঠেন পীর স্বয়ং। পীরের সন্দেহপরায়ণতা ও সংকীর্ণচিত্ততা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এঁকেছেন নাট্যকার। তাহেরার প্রতি হাশেমের দুর্বলতার কথা তিনি অনুমান করতে পারেন অতি সহজেই। একসময় তিনি হাশেমকে বলেই বসেন, ‘এমন যোয়ান-মর্দ ছেলে মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস কেন?’
লালসালুতে আমরা দেখেছিলাম পুরোনো মূল্যবোধের প্রতি অবিচল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক অনড় সমাজ, কিন্তু বহিপীর নাটকে পুরোনো থেকে নতুনে পদার্পনের আভাস বিদ্যমান।
লালসালু এবং বহিপীর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাস ও নাটক দুটিতে অন্তঃসারশূন্য ধর্মাচারের লেবাস খুলে ফেলা হয়েছে। পুরাতন, অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে লালসালুর জমিলার যে বিদ্রোহ তা পরোক্ষ, কিন্তু বহিপীর নাটকে তাহেরার যে বিদ্রোহ তা প্রত্যক্ষ ও সরাসরি। লালসালুতে জমিলার অচৈতন্য পা অনিচ্ছাকৃতভাবে মাজারের গায়ে লাগে কিন্তু বহিপীর নাটকের তাহেরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাদঘাত করেছে পীর-মোল্লা কবলিত সনাতন সমাজকে; তাহেরার ধাক্কা এসে সশব্দে লাগে বহিপীরের শরীরে। এ বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ড। পুরোনো ঘুণেধরা মূল্যবোধের জায়গায় নতুন মূল্যবোধের বিজয় সূচিত হয়।
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-
এ মুখর বরষায়
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

ব্রেশায় উড়োজাহাজ