সাময়িকী
প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
মোহিত কামাল
শিল্পী : সমর মজুমদার
সাহিত্যতত্ত্ব
সাহিত্যসৃজনে সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা কি অপরিহার্য? নতুন ধারা বা তত্ত্বের নামে উপন্যাসের সঙ্গে ‘মনোবৈজ্ঞানিক’ শব্দের ব্যবহার কতটুকু যৌক্তিক?
কোনো কোনো খ্যাতিমান কথাশিল্পীকে বলতে শুনেছি, সাহিত্যতত্ত্বের যাবতীয় বিষয়-আশয় জানা অপরিহার্য নয়, তবে জানা থাকা ভালো। সাহিত্যকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে এর ঐতিহাসিক নানা দিক জেনে-বুঝে অগ্রসর হলে লিখতে বসে মেধাবীদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, প্রাসঙ্গিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আরাধ্য শিল্পমানসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। সাহিত্য আরও বেশি জীবনকে প্রতিবিম্বিত করবে, সমৃদ্ধ করবে। তাই জানা-বোঝার অপরিহার্যতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না- এমন মতও আছে।
সাহিত্যতত্ত্বের গ্রহণযোগ্য বিশ্বজনীন কোনো স্থায়ী সংজ্ঞা নেই। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সৃজনশীল সাহিত্যের যাত্রালগ্ন থেকে ক্রমাগতভাবে তা বদলেছে, সমকালীন সাহিত্যিক বা তত্ত্ববিশারদদের কাছে কখনো তা গৃহীত হয়েছে অথবা সমালোচিত হয়েছে কিন্তু কোনো ধারাই ক্রমবিকাশের উত্তরণ থেকে একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যায়নি।
অভিধান মতে, কোনো পঠিত বিষয়ের মূল ধারণার ভিত্তিই হচ্ছে ‘তত্ত্ব’।
বলা যায়, সাহিত্যতত্ত্ব হলো সাহিত্য হিসেবে আমরা যা অধ্যয়ন করি তার ধারণা, সারাংশ। এসব সারকথা বা সারমর্ম সাহিত্যের ওপর প্রয়োগ করলে সৃষ্টি হয় সাহিত্যসমালোচনা অর্থাৎ ‘সাহিত্যতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক হলো সাহিত্যসমালোচনা’ (সাহিত্যতত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা; মুহম্মদ মুহসিন, ঐতিহ্য, পৃ: ১১)। এভাবে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে আমরা সাহিত্যের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাই।
চিরায়ত বা ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব খুঁজতে গেলে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চারশ’ বছরের চলমান ধারার দিকে চোখ ফেরাতে হবে। সক্রেটিস-প্লেটোর তত্ত্বকে উড়িয়ে না দিয়ে গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল সাহিত্যসমালোচনার প্রাথমিক যুগের সূচনা করেন। তিনি বিশ্বসাহিত্যের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনিভাবে গ্রিক সাহিত্যের নানা প্রকরণ ও বিষয়-আশয় তুলে ধরেছেন। দার্শনিক গুরু প্লেটোর তত্ত্বের পাশাপাশি আর কী কী বিষয়কে মূল্যায়ন করতে হবে তার যৌক্তিকতাও বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তিবাদী তত্ত্ব ব্যবহার করে। অ্যারিস্টটল রচিত পোয়েটিকস গ্রন্থটি সাহিত্যসমালোচনার বাতিঘর হিসেবে উজ্জ্বল অবস্থান দখল করে। তার আলো গ্রিসের সীমানা অতিক্রম করে ইতালির সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেখানে কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস (হোরেস) ও লঙ্গিনাসের বিচার-বিশ্লেষণে আরেক দিগন্তের সূচনা হয়। তবে গ্রিক দার্শনিক ও পণ্ডিত সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এবং ইতালিয়ান হোরেস ও লঙ্গিনাসের ঐতিহাসিক চিন্তাধারার মধ্যে মতভেদ থাকলেও অবিচ্ছিন্ন একটা যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তবু গ্রিকদের ‘মাইমেসিস’ থিওরি এবং লঙ্গিনাসের ‘সাবলাইম’ তত্ত্ব ব্যবচ্ছেদ করেও শেষ পর্যন্ত সাহিত্যতত্ত্বের সংজ্ঞার বিষয়ে স্থায়ী ঐকমত্য পাওয়া যায়নি। ক্রমাগতভাবে সমালোচনা এবং পাল্টা সমালোচনা চলে এসেছে, এখনো চলছে, ভবিষ্যতেও হয়তো চলতে থাকবে।
গ্রিকদের মাইমেসিস তত্ত্ব, ইতালিয়ান লঙ্গিনাসের সাবলাইম তত্ত্ব কী? পার্থক্য কোথায়?
Mimesis?representation or imitation of the real world in art and literature, সাহিত্যপদবাচ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘অনুকৃতি’ শব্দটিই অগ্রগণ্য বা অধিক প্রাসঙ্গিক। ‘নকল’ বা ‘অনুকরণ’ বেশ আলাদা সমাজতাত্ত্বিক ধারণাকেই ধারণ করে বেশি।
প্লেটো বলেছেন, মাইমেসিস প্রকৃতিকে তথা প্রকৃত সত্যকে এক ধাপ বিকৃত করে।
অ্যারিস্টটলের মতে, অনুকরণ করা মানবের জন্মগত প্রবৃত্তি। আরও বলেছেন, অনুকৃতি যেমন চিত্রাঙ্কন একটি সর্বজনীন নান্দনিক আনন্দের উৎস; অন্যদিকে সাবলাইম (Sublime) ইংরেজি শব্দটির আভিধানিক অর্থ মহিমান্বিত, মহামহিমান্বিত, ভীষণ সুন্দর বা ভয়াল সুন্দর, বিস্ময় উদ্রেককর ইত্যাদি। লঙ্গিনাস বলেছেন, ‘রচনার উৎকর্ষ নিহিত রয়েছে শ্রেয়তর দক্ষতা ও বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির মধ্যে।’
লঙ্গিনাস সাবলিমিটির পাঁচটি উৎসের কথা বলেছেন : মহৎ ধারণা সৃষ্টির সামর্থ্য; শক্তিশালী অনুপ্রেরণাদায়ক আবেগের উদ্দীপনা আর চিন্তা ও বক্তব্য; মহৎ মননের সৃষ্টি- যথাযথ শব্দচয়ন ও কল্পনাপ্রসূত শব্দালঙ্কারের ব্যবহার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে এবং সবশেষে ভাবোন্নয়নের সামগ্রিক দক্ষতা। স্বর্গীয় ভাবানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে- এমন অনুভূতিই সাবলাইম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিষয়টির গভীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লঙ্গিনাস মন্তব্য করেছেন, ‘রচনার উৎকর্ষ হচ্ছে এক মহৎ মনের প্রতিধ্বনি।’
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কিংবা অনুষদগুলোর প্রকাশ ঘটে থাকে অথবা এসব মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ব্যবহার করে যাপিত জীবনকে গভীর থেকে উন্মোচন করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়। তা কেবলই জীবনের অনুকরণ তৈরি না করে মহৎ সৃষ্টিশীলতাও উপহার দেয়।
লঙ্গিনাসের মতে, মহৎ ভাব ও উচ্চ ভাব তিন ভাবে অর্জিত হতে পারে। প্রথমত ঈশ্বরের দান হিসেবে, দ্বিতীয়ত মহৎ লেখকের লেখা অনুকরণ করার মাধ্যমে, তৃতীয়ত কল্পনার জোরেও অর্জিত হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে তৎকালীন গ্রিক কিংবা ইতালিয়ান সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে লঙ্গিনাসই প্রথম কল্পনার বিষয়টি সাহিত্যে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন।
আলোচনায় দেখা যায়, গ্রিক প-িতের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি মাইমেসিস তত্ত্ব আর রোমান থেকে পেয়েছি সাবলাইম তত্ত্ব। এ দেখাই শেষ নয়।
পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে নিওক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, নিউ ক্রিটিসিজম, ফরমালিজম বা আঙ্গিকবাদ, বাখতিনিজম, রিডারস রেসপন্স থিওরি, স্ট্রাকচারালিজম বা কাঠামোবাদ, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ও বিনির্মাণবাদ, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, মনোসমীক্ষণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনা সর্বোপরি আধুনিকতাবাদ ও উত্তর আধুনিকতাবাদ। অর্থাৎ দেখা যায় ভাবনাতত্ত্ব, যুক্তিবাদ, রিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম, ম্যাজিক রিয়ালিজম, সেন্টিমেন্টালিজম কিংবা রোমান্টিক যুগের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কোথাও সাহিত্যের সংজ্ঞা স্থায়ীভাবে আসন গ্রহণ করে থাকেনি। তবে একেকটা মতবাদ একেক দিকে আলো ছড়িয়েছে। সাহিত্যতত্ত্ববিদেরা এসব মতবাদ জানেন, আগ্রহী লেখকেরাও এসবের ভেতর থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করতে পারেন, করেনও। সাধারণ পাঠকের কি এগুলো জানা উচিত, বা জানার প্রয়োজন আছে?
প্রয়োজন থাকুক কিংবা না থাকুক, উল্লিখিত মতবাদ থেকে অন্তত দুটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কারণে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমে তুলে ধরছি নিওক্ল্যাসিসিজম বিষয়ে- শব্দটির অর্থ হলো, ‘ক্ল্যাসিকসের ভিত্তিতে দাঁড় করানো সাহিত্যভাবনা।’
মূলত গ্রিক ও রোমান কথাকারদের সাহিত্যভাবনা বা সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে নিওক্ল্যাসিসিজম বা নব্যধ্রুপদীবাদ। ওই কালটাকে সাহিত্যবিষয়ক ফতোয়ার কালও বলা যেতে পারে। এ সময় কোনটা সাহিত্য বলে বিবেচিত হবে তা মূলত নির্ভর করতো গ্রিক ও রোমান ক্ল্যাসিক পণ্ডিতদের গ্রহণ ও বর্জনের ওপর। ওই সময়টি সাহিত্য-শাসনের যুগ হলেও ক্ল্যাসিকসের অন্ধ অনুকরণ সাহিত্যে কল্পনার জায়গা ব্যাপকভাবে সংকুচিত করে ফেলে নিওক্ল্যাসিকাল যুগ। ফলে বিপুল শক্তিধর তাত্ত্বিকদের এই চর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জন্ম হলো ‘রোমান্টিসিজম’ নামের নতুন সাহিত্যভাবনা বা সাহিত্যতত্ত্ব। শব্দটির উদ্ভব হয়েছে রোম (Rome) থেকে। রোমের লাতিন থেকে উদ্ভব হয়েছে ইউরোপের অনেক ভাষা?যেমন পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান ইত্যাদি। সব কটি ভাষাকে এক নামে রোমান্স (Romance) ভাষা বলা হয়। ‘রোমান্স’ শব্দটি ইতালির রাজধানী রোম বলয় থেকে বেরিয়ে একটি সাহিত্যধারার মুকুট পরে নেয়। এই ধারায় অবিশ্বাস্য বীরের গল্প থাকত, সতী নারীর প্রেমের বিষয় থাকত, জিন-পরি জগতের চরিত্ররাও হাজির হতো। আজগুবি, কল্পিত, যুক্তিহীন বানানো কাহিনি থাকত। সাহিত্যে এ সময়কালটা মধ্যযুগীয়, রেনেসাঁস-এর আগের। এসব আখ্যান পাঠককে আনন্দ দিত, আজগুবি আর কল্পনাজাত বলে কেউ এগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়নি, মিথ্যা বা যুক্তিহীনতার দায়ে অভিযুক্তও করেনি। কিন্তু নিওক্ল্যাসিকাল যুগে যা কিছু কল্পনায় সৃজন করা হয়েছে, লালন করা হয়েছে তাকেই মূর্খতা উপাধি দিয়ে বর্জন শুরু হয়েছিল। অপরদিকে ক্ল্যাসিকাল যুগের যুক্তিবুদ্ধিচর্চাকে সাহিত্য ও সমাজ দুইয়ের জন্য আবশ্যিক করে তুলেছিল। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মাইমেসিস থিওরিকে খানিকটা চ্যালেঞ্জ করল। মাইমেসিস থিওরিতে অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন, ‘সাহিত্য হলো জীবন ও জগতের অনুকৃতি (imitation)’?তাঁদের এই ক্ল্যাসিকাল এবং নিওক্ল্যাসিকাল মতাদর্শকে আমূল পাল্টে দিয়ে রোমান্টিকরাই কল্পনায় সৃজনক্ষমতা অবলম্বন করে সর্বপ্রথম দেখিয়ে দিল যে, সাহিত্যের কাজ অনুকরণ নয়; সৃজনও।
মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন এই যে, কল্পনাশক্তি এবং সৃষ্টিশীল ক্ষমতা মানুষের মেধার উপাদান, অঙ্গ (পরবর্তী পর্যায়ে তা খোলাসা করে তুলে ধরা হবে)। মেধার অন্যান্য অনুষদের মধ্যে আছে মেমোরি, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি এবং যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা, সমস্যার সমাধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। একজন সৃজনশীল লেখক এসব অনুষদ ব্যবহার করে সৃজন করতে পারেন যাপিত সমাজে জীবনঘনিষ্ঠ আখ্যান, অমর সাহিত্যভাণ্ডার।
রবীন্দ্রনাথ কিংবা লঙ্গিনাসের যুগের কথা স্মরণ করে বলতে চাই, সাহিত্যে মানবমনের প্রতিধ্বনি ঘটে, হোক সেটা কল্পিত, হোক বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে নির্মিত, হোক ঐতিহাসিক ঘটনা বা জীবনভিত্তিক কিংবা ভৌতিক-হরর।
কল্পনাশক্তি প্রসঙ্গে রোমান্টিসিজমের যুগের তাত্ত্বিক কোলরিজ তাঁর ‘বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া’ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন, কল্পনার উদ্ভব প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপে রয়েছে ‘স্মৃতি’। বর্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেমিশে একরকম নতুন নকশা তৈরি করে স্মৃতির ভা-ারে রক্ষিত তথ্যউপাত্ত। কোলরিজ এই স্তরের নাম দিয়েছেন ‘ফ্যান্সি’ বা কল্পনা। তিনি আরও বলেছেন, এই কল্পনা পৃথিবীর সব মানুষেরই আছে। তাহলে কবির কল্পনা কী? তাঁর মতে, ‘কবির কল্পনা হলো কল্পনার দ্বিতীয় স্তর, বিকশিত স্তর। এ স্তরে মনে জমে থাকা অন্য সকল বস্তু ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে জারিত করে, দ্রবীভূত করে লীন করে দেয় এবং এসবের মাধ্যমে সৃষ্টি করে নতুন এক রূপ যা স্মৃতির বস্তু নয়, কিংবা বর্তমান অভিজ্ঞতাও নয়।’
এটাই কি কল্পনাশক্তি? সাহিত্যজগতে প্রচলিত ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনের সঙ্গে মিলছে কি?
পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতা ছাড়াই ব্রেনে বা মনে আচমকা যে আইডিয়া বা ভাবনাতরঙ্গের উদয় ঘটে সেটাই কল্পনা, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি?এমনটাই প্রচলিত আছে বর্তমান সাহিত্যজগতে। ঐতিহাসিক সূত্রের সঙ্গে মিলুক কিংবা না মিলুক আমরা লক্ষ করেছি ইংরেজ রোমান্টিকেরা অনুকরণের পরিবর্তে সৃজনে নামলেন। ‘যাপিত জীবনের দুঃখ-জরা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রত্যেকে একটি আদর্শজগৎ নির্মাণের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন অপরিমেয় কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে।’ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, শেলি, কোলরিজ প্রমুখ দুনিয়ার শীর্ষ রোমান্টিক কবিগণ। তাঁরাও ‘আমিময়’ হয়ে গেছেন দোষে কটাক্ষের শিকার হলেন। তাঁদের মধ্যে বাস্তবতা থেকে পলায়নপর মনোবৃত্তির উদয় ঘটেছে?এমন সমালোচনার মধ্য দিয়ে জন্ম হলো নিউ ক্রিটিসিজম।
এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো, ইংরেজিতে ক্রিয়েটিভ শব্দটি বেশ প্রচলিত। ক্রিয়েট থেকে এসেছে ক্রিয়েটিভ। ক্রিয়েট ক্রিয়াপদটার মানে হচ্ছে সৃষ্টি করা, মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা, মৌলিক সত্যের উন্মোচন করা, মৌলিক পথ নির্মাণ করে সামনের জটিল পথ সহজ করা। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে আরও কয়েকটি শব্দের যোগসূত্র রয়েছে। শব্দগুলো হচ্ছে প্রতিভা, মেধা, বুদ্ধি। প্রতিভাবানেরাই সাধারণত হয়ে থাকেন মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত। প্রতিভার মূল উপাদান হচ্ছে স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও ধারণা বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা। প্রতিভার এসব উপাদানও সাহিত্য সৃজনে প্রভাব রাখে?প্রমাণিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো কোন সাহিত্য-মতবাদে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে? ধাপে ধাপে আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।
***
এসব বিতর্ক এবং উপরে উল্লিখিত মতবাদগুলোর সংজ্ঞা এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা এড়িয়ে ছোট পরিসরে এই গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা রবীন্দ্রনাথের কথার দিকে মনোযোগ দিতে পারি। তাঁর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কথার একটির সারমর্ম হলো, ‘জীবনের সহিত যা সম্পর্কিত তা-ই সাহিত্য!’ এখানে ‘সহিত’ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। কেবল জীবনচিত্র কিংবা জীবনকাহিনিই কি সাহিত্য? উপন্যাসে অবশ্যই জীবনচিত্র থাকবে আর জীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মন আর বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম। তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে জড়িত মন-বিজ্ঞান, দৃশ্যমান সমাজ এবং না-দেখার বাইরেও আছে আরও কিছু। সেই আরও কিছুটা কী? সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীল কল্পনা কিংবা ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন নয়? রোমান্টিক যুগের কবিদের মত হলো কবিতার প্রকৃত স্রষ্টা কবিকল্পনা- এটি ফ্যান্টাসি নয়, কল্পনাশক্তি। তাঁদের মতে কবিকল্পনা আসলে সৃজনশীল প্রক্রিয়া বা সৃজনশীল কল্পনা আর রবীন্দ্রনাথ কল্পনাকে আরও বিশাল শক্তিধর মনোক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। রোমান্টিক যুগের মতাদর্শের কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেছেন, ‘প্রতিটি মানুষের রয়েছে কল্পনাশক্তি।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের হয়ে ওঠে সেই শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি।’ অর্থাৎ স্মৃতি, অভিজ্ঞতা নির্ভরতা কিংবা কেবল অলৌকিক কবিকল্পনা ইত্যাদি বিতর্কের যে কোনো আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এই কল্পনা হচ্ছে মনেরই শক্তি, মনেরই অঙ্গ, উপাদান। মনেরই বিপুল শক্তির উদ্গিরণ।
এখানেও আলোচিত গ্রিক সাহিত্যতত্ত্ববিদদের মাইমেসিস থিওরি কিংবা জীবনজগতের অনুকরণবাদ এই তথ্যের আলোকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আমরা দেখছি উপন্যাসের পাতায় পাতায় উঠে আসে যাপিত জীবনের কাহিনি। সেই সঙ্গে আনন্দ-বেদনা-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রাগ-ক্রোধ, ঈর্ষা-হিংসা কিংবা প্রতিহিংসার মতো আবেগ।
মানবমনের অন্তর্জগৎ ও চারপাশের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগ, যোগসূত্র। এর ভেতরেই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান এবং সাহিত্যে প্রকাশিত মানবমনের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই মনোবৈজ্ঞানিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বলে রাখা ভালো, প্রাসঙ্গিকও- আলোচনায় তুলে ধরা এবং আলোচনার বাইরের সব সাহিত্যমতবাদের ভেতরই মনস্তাত্ত্বিক সূত্র কিংবা তত্ত্বের প্রতিধ্বনি রয়েছে- নিউরোসায়েন্স, বিহেভিয়ারাল, কগনিটিভ বা কনশাস স্ট্রিম অফ থটস, সাইকোডায়নামিক কিংবা হিউনিস্টিক মতবাদ- প্রতিটি মনস্তাত্ত্বিক থিওরিই সাহিত্যমতবাদের প্রাণের ভেতরের প্রাণ হিসেবে উৎসারিত হয় যা বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, লঙ্গিনাস এবং অ্যারিস্টটলও।
সাহিত্যতত্ত্বের নানামুখি আলোচনা-সমালোচনার রেশ টেনে ধরে একই সঙ্গে আমরা নজর দিতে পারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি উক্তির দিকে- ‘সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই।’
বর্তমান সময়েও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একজন প-িত হলেন জ্যাক দেরিদা। তিনি ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন ব্যক্তিত্ব হলেন জ্যাক লাকাঁ। তিনি ছিলেন মনোচিকিৎসক। আর স্ট্রাকচারালিজমের জনক ক্লদ লেভি স্ট্রস ছিলেন নৃবিজ্ঞানের প-িত। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁরা অবশ্যপাঠ্য নাম। তিনজনই সাহিত্যে দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও স্ট্রাকচারালিজমের কথা তুলে ধরেছেন।
তাহলে সাহিত্যতত্ত্বের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
সমাজ-জীবন-মন, এক কথায় মনোসামাজিক মূল্যবোধ, স্যোশাল কগনিশন, কাঠামোবদ্ধ সামাজিক দর্শন নয়? এমন হাইপোথিসিস দাঁড় করানো যায় না?
এ কারণেই লঙ্গিনাসের মূল কথাকে সামান্য বদলে বলা যায়, সাহিত্য রচনার উৎকর্ষ হচ্ছে মানবমনের প্রতিধ্বনি, শৈল্পিক স্বর। কথাটা মনস্তাত্ত্বিকভাবেও যৌক্তিক-উপন্যাসে ব্যবহৃত আবেগ, চিন্তা, প্রত্যক্ষণ, মোটিভেশন, সামাজিক অভিজ্ঞান বা সোশ্যাল লার্নিংয়ের কারণে বদলে যেতে পারে প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়া, বদলে যেতে পারে চারপাশ প্রত্যক্ষ করার ধরন, চিন্তনে ঢুকে যেতে পারে ত্রুটি, নানামুখী আবেগের প্রকাশ কিংবা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে চরিত্র থেকে চরিত্রের মনোজগতে। এভাবে উপন্যাসের মধ্যে ঘনীভূত হতে পারে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, জটিল জীবন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আলাদা ভাষিক ইঙ্গিতময় সংকেত, সাহিত্যশিল্প। আর তা ঘটে থাকে লেখকের মেধার গুণে, কেবল অনুকরণে নয়। এখানে উল্লেখ করা আবারও প্রাসঙ্গিক যে মেধা মনেরই অঙ্গ।
এইসাহিত্যশিল্প ‘কনশাস স্ট্রিম অব থটস’, মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ কগনিটিভ থিওরি ও ফ্রয়েডের সাইকোডাইনামিক থিওরিকেও প্রতিধ্বনিত করে, চেতন-অবচেতন কিংবা নির্জ্ঞান মন বিশ্লেষণ করে। সমাজ-সংস্কৃতিকেও। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটও সাহিত্যের মনোজাগতিক অনুষদ হিসেবে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব
মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি শব্দগুলো এসেছে ‘মন’ শব্দ থেকেই। আসলে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রোমান্টিক যুগের কবিকুল এবং পরবর্তীকালে আধুনিক মতবাদের লেখক ও কবিগণ কেউ-ই মনের বাইরে যেতে পারেননি, মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করেননি। মতভেদ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে বলা যায়, সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের বাইরে কিছু নাই। পরিবেশ-প্রকৃতি ঘিরে সাহিত্যে নির্মিত হয়ে থাকে প্লট, চরিত্র; এই নির্মাণশৈলীতে একাকার হয়ে যায় ভাবাবেগ, চিন্তন কিংবা সৃষ্টিশীলতার অন্তর্লীন শক্তি। সুতরাং প্লেটোর ভাবনা, অ্যারিস্টটলের যুক্তি-চিন্তন-প্রতিভা, কবির কল্পনাশক্তি সবই সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত; মনস্তত্ত্বের প্রাণরসায়ন। এ কারণেই ‘মনস্তাত্ত্বিক গল্প’ বা ‘মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস’ শব্দগুলো আলোচিত হয় সাহিত্যপ্রেমীদের মুখে মুখে। এসব বয়ানই প্রমাণ করে দেয়, লঙ্গিনাসের মূল কথা : ‘রচনার উৎকর্ষ হচ্ছে এক মহৎ মনের প্রতিধ্বনি।’ তবে কেবল মুখের কথায় নয়, মনোসমীক্ষণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সরাসরি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সাইকোডাইনামিক মতবাদের ওপর ভর করে সাহিত্যকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।
কেউ কেউ বলেন, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি মনস্তত্ত্বের কোনো বিষয় নয়, তাঁর কল্পনাশক্তি সৌরজগতের চেয়ে বিশাল, বড়। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বড়। অবশ্যই বিশাল। তবে যত বড়ই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই শক্তির মাধ্যমে মনের মিলন বা মনস্তাত্ত্বিক সংযোগের কথা বলেছেন। কবির এই অসীম কল্পনাশক্তি বায়বীয় কোনো বিষয় নয়। বরং এই কল্পনাশক্তি মনস্তত্ত্বেরই বিষয়-আশয়, অশেষ সৃজনক্ষমতার উৎস-উপাদান।
মানবমনের অন্তর্জগৎ ও চারপাশের বহির্জগতের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গোপন যোগসূত্র। মনের জানালা সেই যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়। এসব জানালা হচ্ছে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়?চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা। এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের আদি চর্যাপদের দিকেও ফিরে তাকাতে পারি আমরা : ‘কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥’ লুইপার এই পদের অর্থ হলো ‘দেহরূপ বৃক্ষে পাঁচটি ডাল, চঞ্চল মনে প্রবেশ করেছে কাল।’ এখানে পাঁচটি ডাল বলতে শরীরের পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে। যা মনের জানালা রূপে নানা ধরনের তথ্য সরবরাহ করে মস্তিষ্কে, মনের ওপর প্রভাব তৈরি করে?। আদি চর্যাপদেও লুকিয়ে ছিল এমনতর বৈজ্ঞানিক বিষয়।
বহির্জগতের পরিবর্তন হলে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তর্জগতে মানসিক প্রক্রিয়ায় বয়ে যায় বদলের হাওয়া। আবার অন্তর্জগতে ঝড় বইলে বহির্জগতের আবহও বদলে যায়, বদলে যায় অভিব্যক্তি। এই যোগসূত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সূত্র : মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে সাহিত্যের ভেতর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় মনোবৈজ্ঞানিক কলাকৌশল- প্রত্যক্ষণ, আবেগ, চিন্তা, বুদ্ধি, প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, কগনিশন (অবহিতি বা সচেতনবোধ), অন্তর্গত প্রেষণা বা ভেতরের আকাক্সক্ষা, চাহিদা-উৎসাহ-উদ্দীপনা, শিক্ষণ, বিশ্বাস, স্বপ্ন ইত্যাদি। এগুলোও মনের স্বাস্থ্যের অংশ, মনোক্রিয়া বা মনের অন্তর্লীন উপাদান। এছাড়া রয়েছে সচেতন উপলব্ধি (কনশাস ওয়ার্ল্ড), ব্যক্তিত্ব, চেতন-প্রাকচেতন-অবচেতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এসব উপাদান মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
এর মধ্যে নিউরোসায়েন্স মতবাদ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষের মন ও আচরণ বিশ্লেষণে। নিউরোসায়েন্স-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত আচরণের বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক কারণ খোলাসা করা হয়েছে। ব্রেনের দুই গোলার্ধ আলাদাভাবে কাজ করে- এই গবেষণার জন্য ১৯৮১ সালে নোবেল প্রাইজ জয় করেছেন রোজার স্পেরি। দৃশ্যমান আচরণকে গুরুত্ব দিয়েছে বিহেভিয়ারাল পারস্পেকটিভ (আইভান প্যাভলভ, ১৯২৭; এডওয়ার্ড থর্নডিক, জন বি ওয়াটসন)। হিউম্যানিস্টিক মতবাদে (আব্রাহাম মাসলো, ১৯৫৪; কার্ল রোজার্স, ১৯৬১) বলা হয়েছে, মানুষ তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, নিজের সুপ্ত প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে।
সমসাময়িককালে মনোচিকিৎসাবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হচ্ছে কগনিটিভ ওয়ার্ল্ড- নিজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এবং চারপাশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ নিয়ে মানুষ কী চিন্তা করছে, সচেতনভাবে কী উপলব্ধি করছে তা-ই মুখ্য কগনিটিভ মতবাদে। একজন মনোবিদ-মনোচিকিৎসক হিসেবে মনে করি, কগনিটিভ মনোজগতের যথাযথ ব্যবহার বিশ্বসাহিত্যকে ভবিষ্যতে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে। কারণ কগনিটিভ মনোক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করা হয় কনশাস বা মনের সচেতন অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি-অনুভব, উপলব্ধি, আকাক্সক্ষা, স্মৃতি ইত্যাদি নিয়ে। মানুষের ভেতরের অনুভব বা অন্তর্গত অন্ধকারকে বাস্তবতা ও সত্যের আলোয় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে এই মতবাদের প্রধান কাজ। এটির প্রধান গবেষক মনোবিদ অ্যারন টি বেক। বেকের গবেষণার সাফল্য হিসেবে ১৯৬৭ সালে মনোচিকিৎসাবিদ্যায় বিষয়টি উঠে আসে লাইমলাইটে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে বিষয়টির গুরুত্ব আবিষ্কৃত হয়নি মনস্তত্ত্বে। কগনিটিভ বা কগনিশন বা অবহিতি শব্দটি ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে, এ প্রজন্মের মনোবিদ হিসেবে বিস্ময়করভাবে লক্ষ করেছি, শব্দটির অর্থবহতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্র চিন্তা-ভাবনা-উপলব্ধি ও সচেতন মনের ঐন্দ্রজালিক অনুভব। ‘সমাপ্তি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব চরিত্রের মাধ্যমে পাড়াবেড়ানি মৃন্ময়ীকে বাস্তবতার আলোকে জাগিয়ে তোলেন নতুনরূপে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই বর্তমান সময়ের সফল মনোচিকিৎসা-কৌশল, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি তাঁর সময়েই ব্যবহার করে নিজেকে স্বভাবগত মনোবিজ্ঞানী হিসেবে তুলে ধরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানী বলার এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এ ধরনের আরও অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে।
আচরণ সৃষ্টিতে অবচেতনের অন্তর্গত শক্তির কথা বলা হয়েছে সাইকোডাইনামিক মতবাদে (সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ১৮৫৬-১৯৩৯)। অন্তর্গত এই গোপন শক্তিতে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তুলে ধরা হয়েছে এমন ধারণা। মতবাদটি নানাভাবে আলোচিত, সমালোচিত। মার্কিন মুল্লুকে মনোবিজ্ঞান সমিতির বিবেচনায় এর কোনো স্থান না থাকলেও সাহিত্যসেবীদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, নিউফ্রয়েডিয়ান মতবাদ। বিংশ শতাব্দী জুড়ে শিল্পসাহিত্যে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
-
সাময়িকী কবিতা
-
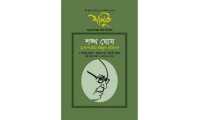
শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন
-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প
-

কল্পগল্প
-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’
-
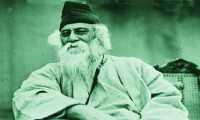
আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-

আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ





















