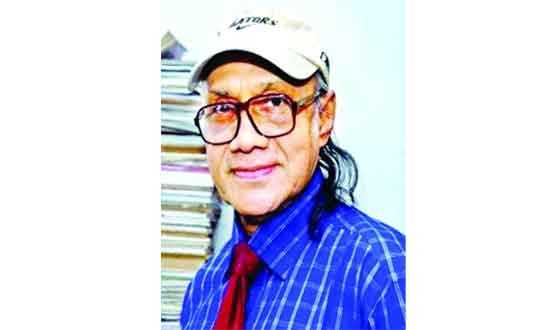সাময়িকী
আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’
হুমায়ুন কবির, সংগ্রহ ও ভূমিকা : মুহিত হাসান
আবদুল মান্নান সৈয়দ
[অকালে আততায়ীর বুলেটে নিহত কবি-সমালোচক হুমায়ুন কবির (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮-৬ জুন ১৯৭২) ১৯৭০ সালের ৩১ মে তদানীন্তন দৈনিক পাকিস্তান-এর ‘রোববারের সাহিত্য’ পাতায় আবদুল মান্নান সৈয়দের (৩ আগস্ট ১৯৪৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১০) দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা (ঢাকা : ধ্রুপদ, ১৯৬৯) নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ অথচ গভীর আলোচনা লিখেছিলেন। লেখাটি অদ্যাবধি অগ্রন্থিত, ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হুমায়ুন কবির রচনাবলী-তে এটি সংকলিত হয়নি। দুর্লভ এই গ্রন্থালোচনাটি মান্নান সৈয়দের জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে পুনরুদ্ধার করা হলো।]
পূর্ব বাংলার কবিতার আসরে আবদুল মান্নান সৈয়দ ইতিমধ্যেই একটি স্বতন্ত্র ও সবল কণ্ঠ শুনিয়েছেন বলে আমাদের ধারণা। ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ’-এর পর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা’। সম্ভবত নামকরণে বক্তব্য, তাঁর কবিসত্তার জন্মান্ধতা কেটেছে পৃথিবীর জ্যোৎস্না-রৌদ্রে। বইয়ের শেষের নাম-নাটিকায় কবি নাটিকার কবিচরিত্র, যিনি অবশ্যই আবদুল মান্নান সৈয়দের আত্মজ কারণ কবিতা ও কবিতানাট্য যে মূলত স্বগতোক্তি। অপরাপর সাম্প্রতিকদের মত মান্নান লেখা ও বক্তব্যে প্রমাণ করে বলেছেন- ‘ঘাসের একটি ব্লেডে যে সুন্দরতা আছে তা দেখে যেন এই বিশ্বভুবন পেরিয়ে আসা যায়।’ অথচ গ্রন্থের উৎসর্গ কবিতায় কবি এমন কোনো ইঙ্গিত রাখেননি যাতে বোঝা যায়, তিনি পরাবাস্তববাদী মনোকুয়াশা থেকে ছাড়া চাইছেন। সেখানে রয়েছে ‘এসো অপস্পার, এসো, ধেয়ান করেছি চোখ বুঁজে।’ অপস্পার অর্থাৎ মৃগী রোগ পৃথিবীর রক্তাভ রৌদ্রের ধারণার বিপরীত। তবুও এ গ্রন্থেই মান্নানের প্রতিবেশ চেতনা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট, হয়ত অংশত তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেই।
আরো একাধিক কারণে বইটি উল্লেখযোগ্য। এ যাবৎ, প্রথম কবিতার বই বের হওয়ার পরেও মান্নান মূলত গল্পকার হিসেবেই গৃহীত হতেন। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে তিনি মুখ্যত কবি বলে দাবি করলে আমরা প্রায়ই বিনীত প্রত্যাখান করতাম। আলোচ্য বইটি সাহস ও সততায় নিঃসন্দেহে তাঁর দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করল। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের গদ্যশরীরে ও মনোবাস্তবতার প্রহেলিকার একাধিক ঝলকিত স্থান যে সম্ভাবনার বার্তাবহ হয়েছিল, তা অপেক্ষাকৃত পক্কতার নজির দেখিয়েছে এ বইয়ে। আবদুল মান্নান সৈয়দ শব্দ ব্যবহারে যে যে হঠকারী সাহস (হঠকারী শব্দটি যদি প্রশংসার অর্থে ব্যবহার করা যায়) ও চিত্রাঙ্কনের বর্ণবৈভবে যে ইম্প্রেশনিস্ট ঔজ্জ্বল্য রপ্ত করেছেন তা স্থান-বিশেষের দুর্বোধ্যতার চোরাবালি পেরিয়েও আমাদেরকে ধরে রাখবে নিপুণ চুম্বকের মতো।
বইটিকে চারটি ভাগ করেছেন : শব্দের জ্যামিতি, সনেটগুচ্ছ, উড়ন্ত অনুভূতি ও কবিতা-নাট্য। উড়ন্ত অনুভূতির গদ্যশরীর ছাড়া অন্যসব অংশ মোটামুটি ছন্দস্পন্দিত। বিশেষত শব্দের জ্যামিতি ও সনেটগুচ্ছ অংশে তিনি প্রাথমিক ছন্দোবদ্ধ কবিতারূপ নির্মাণ করেছেন। সম্ভবত প্রধানত সেই কারণে কবিতার নিটোলতাপ্রাপ্তির যে অন্যতম মাধ্যম কনসিসটেন্সি সেই গুণ রয়েছে এতে। কেননা ছন্দ জাগ্রত চৈতন্যের সৃষ্টি। এই জাগর চেতনা কবিতাকে অলৌকিক উল্লম্ফনে যেতে বাধা দেয়, ধরে রাখে অর্থনিষ্ঠতায়। যদিও চতুর্থ প্রচ্ছদের বক্তব্যে বইটিকে স্যুররিয়ালিজমের স্পর্শসন্ততি আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবু বইটি সর্বদাই অবচেতনার বুদ্বুদ হয়ে ওঠেনি। শোনা যায়, জুরিখে স্যুররিয়ালিস্ট কিংবা দাদাইস্টদের এক শিল্পপ্রদর্শনীতে দর্শকরা এক-একখানা কুড়–ল পেয়েছিলেন প্রদর্শনীটি গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্যে (‘ডিকশনারী অব আর্ট এ্যান্ড আর্টিস্ট’ দ্রষ্টব্য)। এটাযদি শিল্পের চিরকালীন ধারণার বিরুদ্ধে রূপকীকৃত বিদ্রোহ হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে এ বামন প্রচেষ্টা একজন ব্রেতোঁ কিংবা জারার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। আরাগঁ এবং পিকাসো তাই স্ব স্ব শিল্পকর্ম এবং শিল্পভাবনার বিবর্তন ঘটালেন, ব্লক যেমন পরিত্যাগ করলেন প্রথাগত প্রতীকী আন্দোলনের ‘পা-ুর বেড়ানী’ জগৎকে পরিত্যাগ করে। যদিও মান্নান সৈয়দ বলেন, ‘ধ্যান করছি চোখ বুঁজে’, তবুও প্রতিবেশ চেতনা ঢুকে পড়ে তাঁর ছন্দচেতনা ও ছড়িয়ে রাখা চৈতন্যের জালের ফাঁক দিয়ে। যেহেতু ছন্দ জানি বিশ্ব-হার্মনির অংশ এবং তা পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে ভেদসূচক নয়। যে ছবিগুলোর গ্যালারি এ কাব্যগ্রন্থটি তারা সর্বদাই অবচেতনার পারা-ওঠা আপনায় পড়া বিচূর্ণ কাউন্টেনান্স নয়। যেমন—
দুঃস্বপ্নে আমার জন্ম;
উগরে দিয়েছে বঙ্গদেশে
পঞ্চাশের মন্বন্তর নামহীন
ফুটপাতে ভিড়ের ভিতরে
আমার জননী, সে তো ক্ষুৎকাতর
পঞ্চাশের মন্বন্তর ছাড়া
কেউ নয়।
যদিও কবিতাটির শিরোনামেই রয়েছে ‘রক্তের পলাশবনে কালো ফেরেশতা’ তার মধ্যেই বঙ্গদেশে অবজেকটিভ পদপাত—
স্থবির মেদিনী ব্যেপে
বিমর্ষ নুড়ির মত
বঙ্গ-সংস্কৃতি আছে পড়ে
ভাবলেশহীন চোখে মুখে।
মন্তব্য করা যায় বইটির ঘনবদ্ধতা ও ছন্দ পরস্পরনির্ভর। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বল ছন্দ ব্যবহারের কিছু কিছু নিদর্শনও স্বীকার করতে হয়। মনে হয়, ছন্দের কুশাগ্রতীক্ষèতা অংশত কবির অনায়ত্ত। না হলে—
পড়ে থাকে বিশদ বরফ
চলে গেছে। আকাশের
তারা এসে মাঠের উপরে
ধীরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে,
লাল গোলাপের ঝোপে বিঁধে
থাকে শে^ত তলোয়ার
এরকম সাবলীল পঙ্ক্তির পরই শ্রুতি থমকে যায় যেন—
পরস্পরকে দখল করে দিন রাত্রি
কাঁদে কেন ঘুঘু
(বিচ্ছেদ-২)
এর একটি কারণ কি কবি কাব্যজীবনের সূচনায়ই বপন করেছেন? তিনি গদ্যভঙ্গী নিয়ে প্রবেশ করলেন কবিতায়, অথচ কবিতার ইতিহাসেই জানি সর্ববিধ ছন্দসিদ্ধির পরই চালানো যায় গদ্যস্পন্দের আয়ুধ। আর একটি ছন্দদৌর্বল্যের উদাহরণ—
মাথার উপরে এরোপ্লেন
এত জোরে চলে যায়
মাথার ভিতর থেকে স্বজন
ফেটে ঝরে ঝরে পড়ে
বৃষ্টিলাগা গোলাপের এক ঝাঁক
পাপড়ীর মতো
এমন ক্ষুধার্ত তুমি সেই স্বপ্ন
খাচ্ছ তুলে তুলে।
এর পরই যে খটকা রয়েছে তা ব্যাকরণ দিয়ে না মাপলেও কবিতার কানেই ধরা পড়ে—
বলেছিলুম তোমার সঙ্গে কথা
শার্সি পড়ে যেতে
দেখি তুমি আধখানা ঘরে আর
বাকি অর্ধেক বাগানে...
পড়ে গেলে। কোলে নিয়ে
বসে থাকি তোমার অর্ধেক
খরগোশ পাক যায় বাকি অর্ধেক
শরীর নিয়ে (তুমি)
মোনালিসার ছবিতে গুম্ফ সংযোজনের মতো হাস্যকর নয় অথচ আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় ভিন্নতর অনুষঙ্গের শব্দ ও চৈত্রদ্বৈতের ব্যবহার এক আকর্ষণীয় কিম্ভূতের সূত্রপাত ঘটায়। শব্দের অনুষঙ্গ ভেঙে দিচ্ছেন তিনি চমকপদ ব্যবহারে। অসংখ্যের মধ্যে দুটি উদাহরণ—
(ক) কাঠুরিয়া, তোমরা কি এইসব
অয়েল গাছের সম্পাদক
(খ) তৈরী হবে কৃষ্ণচূড়ার মিস্তিরি
সবুজ রক্তের কেমিস্ট্রিতে বুকের রণনশীলতা
এরকম ব্যবহার সর্বত্র যে সুখদ হয়েছে এমন বলা যাবে না। কিন্তু কবির সাহস ও শুচিবায়ুহীনতাকে অঙ্গীকার দিতেই হবে।
চিত্র ব্যবহারে তাকে মনে হয় সাইকেডেলিক চিত্রকরদের মতো। ‘স্ট্রিটগুলো তাসের মতোন শাফল করছে’, ‘লোহা ও পারায় তৈরি কারো হাত’, ‘অমিতাভ রাত নীল গ্লাসে ঢোক গিলে তারা খায় ছাদের ওপরে’— কিছু কিছু চিত্রকল্পের গ্রন্থনায় তাঁর এমন একটা কমিকভঙ্গী আছে যে হেসে ফেলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আপাত পর্দার ঈষৎ অপসারণেই দেখা যায় কবির আসল সিরিয়াস মুখাবয়ব। ছবিগুলো যেন আধুনিক ডন কুইকজোটের ভূমিকা নিয়েছে। ঈষৎ সুড়সুড়ি দিয়েই রোপণ করছে চিন্তা। যেমন—
কবি : কে কল্পনা দেখেছা
পিস্তল এই হাতে
যাও চলে যাও বস্তু গ্রাসে
(কয়েকটি সংলাপ)
গোয়েন্দা গল্পের মতো মজাদার মনে হতেই ভাবতে বসি পিস্তলটি কি কবিত্বের উপমা? কবি, কাব্য ও জীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও চেতনার ছাপ রয়েছে বইয়ের বিভিন্ন বর্ণবিভায়, বিশেষত নাটিকাত্রয়ে। যে চূড়ান্ত ব্যক্তিকতা তাতে স্ফূরিত তাকে সীমিত করলে দাঁড়ায়—‘বরং একেলা কর এ প্রার্থনা’।
শিল্প ও সৌন্দর্যের মেধায় রচিত তাঁর একাধিক কবিতা আমাদের চিন্তাহীন যুগে কবির নন্দনভাবনার পরিচয় বহন করছে। ‘মধ্যরাতে নিদ্রাভঙ্গ উত্থিত’ কবিতায় মান্নান জীবন ও শিল্প-সৌন্দর্যের সমাহারের দুর্লভ প্রতীককে সম্ভবত ধরতে চেয়েছেন। ‘সম্পূর্ণ ময়ূর বাদ দিয়ে শুধু নাচ দেখে যেতে চাই’—এ বক্তব্যে নবীনতার সন্ধান না করেও বলা যাবে কবিতাটি অত্যন্ত সবল ও ধারালো। বর্তমান সমালোচকের এটিকেই বইয়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে হয়েছে।
আবদুল মান্নান সৈয়দের নিজস্বতা এ বইয়ে অত্যন্ত সোচ্চার হলেও দু একটি পঙ্ক্তিতে প্রভাবছায়া রয়েছে। ‘সন্ধ্যে থেকে পৃথিবীর শেষ জাফরান রৌদ্রালোকে’ এ রকম পঙ্ক্তিতে উপস্থিত রয়েছেন জীবনানন্দ।
ললিত বিভোল থাকে রচা
দ্বিধা
আমার পরান মিশেছে তোমার
চরণে—
লক্ষ বছরে একটি ক্ষণ সুবিধা
এখানে এবং আশেপাশে দুর্বল প্রতিধ্বনি তুলছে সুধীন দত্তের শাশ্বতী কবিতা—
একটি কথার দ্বিধা থর থর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।
অবাক লাগে যখন দেখি আবদুল মান্নান সৈয়দ ইচ্ছে করলেই ‘তুমি অবিরল শ্রাবণ সম্প্রপাত’, ‘কথা নয় সে তো মৃদু ঘাসফুল ফোটে’ কিংবা ‘কাঁদে কেন ঘুঘু, ঘুঘু, চুপ কর সোনামনির মতো’ সরল মৃদু প্যাস্টোরাল উচ্চারণ করতে পারেন, অথচ পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হন ইনসমনিয়া ও তার দরোজা জানালার ভেতর। আশা করছি, পৃথিবীর নিখিল পূর্ণিমা (তাঁর ভাষায়) তাকে স্যুররিয়ালিস্ট স্টিরিওটাইপিং-এর শিকার বানাবে না। কথাটির ব্যাখ্যা : শব্দের নতুন ডাইমেনশন আবিষ্কার ও স্বপ্ন প্রভুবনের ক্রমাগত একরৈখিক সন্ধান একটি বৃদ্ধিহীনতার জন্ম দেয়। ফলত তা কামিংস ও তাঁর কতিপয় অন্ধকারীর মত ব্যর্থ চাতুর্যের নজির হয়ে থাকে।
টলস্টয় কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যদি ফ্লাডলাইটের সর্বপ্লাবী আলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দস্তয়েভস্কি কিংবা জীবনানন্দ দাশের প্রতিভা তীব্র প্রখরতায় স্পষ্ট লাইটের মতো একটি বিন্দুকেই ধারণ করে। মান্নান ইতিমধ্যেই যে দ্বিতীয় গোত্রের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর পর্যবেক্ষণকে অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। ‘সূর্যাস্তের মতো রাঙ্গা বেশ্যা নীল জানালার পাটাতনে বসে আয়না ধরেছে। যেন সুখের সামনে থাবা ধরে আছে নিবিড় বাঘিনী’—পঙ্ক্তিটিতে যতীন্দ্রনাথের ‘রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গণা’ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ-এ থাবা চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে পড়া বাঘিনীর বর্ণনার অনুষঙ্গ মিশ্রিত হয়ে আবেদনের ঘনত্ব বাড়িয়েছে।
আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে অগ্রজ এক সমালোচক তাঁর কবিতার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবের এবং বুদ্ধি ব্যবহারে সে ঘাটতি পুরিয়ে নেবার কথা বলেছেন। আলোচ্য বইটিও স্থানে স্থানে অনুরূপ, এ কথায় সত্যের অপলাপ ঘটে না। কবিতা পাঠক মনোযোগী হলে দেখবেন অত্যন্ত আলোকিত স্থানের পাশে দু-একটি লাইন কেমন প্রসাধনসর্বস্বতায় দাঁড়িয়ে থাকে।
বলা যাবে, আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে যে সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা অগ্রজ কবিদেরও বিস্ময় ও কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে থাকবে।- দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ মে ১৯৭০
-
সাময়িকী কবিতা
-
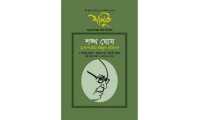
শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন
-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প
-

কল্পগল্প
-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
-
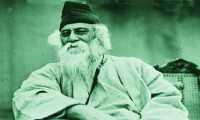
আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-

আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ