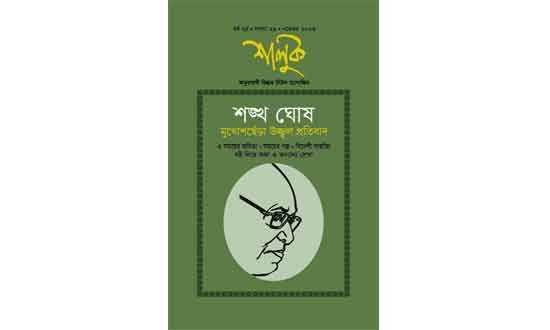সাময়িকী
শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন
রকিবুল হাসান
লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাস একেবারে নতুন নয়। বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সৎ সাহিত্যভাবনা এবং চিন্তা-চেতনায় দৃঢ় থেকে মাথা উঁচু করে সাহিত্যচর্চার জায়গাটি লিটল ম্যাগাজিন, বহু আগে থেকেই। এটা কারো চোখ রাঙানির ধার ধারে না, কারো স্তুতিতে মেরুদ-হীন হয়ে সাহিত্যচর্চ করে না। যে কারণে এটা কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুগত দাসে পরিণত হয় না, অনুকম্পাও আশা করে না। এতে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গিও থাকে না। বাণিজ্যিকীকরণের কোনো ব্যাপারও থাকে না। লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র ও মেজাজ একদমই ভিন্ন। যে কারণে এর জন্ম ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তির একক চেষ্টায়, আবার কয়েকজন সমমনার যৌথ চিন্তায়। সে কারণে বিশেষ চিন্তা-চেতনা-আদর্শভিত্তিক লেখার গুরুত্ব থাকে বেশি এবং তাতে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য থাকে। এসব বিবেচনায় যার কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে চলে আসে, সেটা হলো অধুনাবাদী চিন্তার লিটল ম্যাগাজিন ‘শালুক’। শালুক একটি লিটল ম্যাগাজিন। শালুক একটি আন্দোলন। শালুক একটি বিকল্প চিন্তার নাম। শালুক তারুণ্যের পত্রিকা। তারুণ্য যে কোনো বয়সীর মধ্যেই থাকতে পারে। শালুক এই তারুণ্যের শক্তিকে আশ্রয় করে তার স্বকীয়তায় বিস্তৃত হতে চায়। নতুন চিন্তা, ব্যতিক্রমী ভাবনা ও প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে চায় শালুক।
কবি ওবায়েদ আকাশ ছাব্বিশ বছর ধরে ‘শালুক’ সম্পাদনা করে আসছেন। লিটল ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতায় খুব কম লিটল ম্যাগাজিন আছে, যা এতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পেরেছে। এর পরেও কথা আছে, তিনি ‘যেনতেন’ভাবে এটা করেন না। দায়সারা গোছের করে করেন না। এতে তার কঠিন শ্রম সাধনা যেমন আছে, তেমনি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। সেটাকে ধারণ করেই ‘শালুক’ সম্পাদনা করছেন। রীতিমতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। শালুকের প্রত্যেকটি সংখ্যা প্রত্যেকটি সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে, এই অতিক্রম করানোর শক্তি একজন সম্পাদকের কতোটা দৃঢ়তার সঙ্গে থাকতে হয়, তা বোঝা যায় শালুকের সংখ্যাগুলো হাতে নিলেই। বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে নতুন লেখক তৈরির প্রয়াস, ভালো লেখা লিখিয়ে নেওয়া, সেসঙ্গে নিজের উপার্জিত অর্থের বলি দেওয়া-সবই লক্ষণীয় শালুকে। একেবারে সরাসরি বললে শালুক একটি বিপ্লবের নাম। বিপ্লবটি তিনি করছেন সিকি শতাব্দি ধরে। যে কোনো বিপ্লবের শুরু হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে; কিন্তু কোথায় কীভাবে শেষ হবে, কীভাবে সফল হবে, কতো বছর লাগবে সে সফলতা অর্জনে, এর উত্তর অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। এর ভেতর দিয়েও বহু বিপ্লব সফল হয়েছে, এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে বহু। মূল্য ছাড়া কখনো কোনো বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কবি ওবায়েদ আকাশ শালুক করতে কম মূল্য দেননি, কম মূল্য দিচ্ছেন না, রীতিমতো এক বিপ্লবের ভেতর আছেন, এর শেষ কোথায় তা বোধ হয় তিনি নিজেও জানেন না। তার এ বিপ্লবের নির্দিষ্ট কোনো মানচিত্রও নেই। পুরো পৃথিবীতেই তিনি ছড়িয়ে দিতে চান এই বিপ্লব। আর সেকারণেই তিনি অনেক সাধনা চেষ্টায় সম্পাদনা করতে পারেন স্বদেশি গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও বিষয়ের পাশাপাশি অন্য ভাষার সাহিত্যপাঠ কিংবা ইউলিসিস-ওয়েস্ট ল্যান্ড কিংবা লোরকা-মার্কেস-কাফকা-এর মতো আন্তর্জাতিকতার ঘ্রাণযুক্ত শালুকের বিশেষ সংখ্যা। প্রত্যেকটি সংখ্যা তিনি বিশেষভাবে উপস্থাপন করেন এবং সুদীর্ঘ কলেবরের এবং সুপরিকল্পিত, সেখানে অনুসন্ধান থাকে, আবিষ্কারের তীব্র বেদনাবোধ থাকে, যা তিনি লিখিয়ে নেন নির্দেশনা মোতাবেক, আর এর ভেতর দিয়েই তৈরি করেন নতুন লেখক, নতুন গবেষক। এই যে অন্যদের একদিকে নির্মোহ মূল্যায়ন এবং একই সঙ্গে লেখক তৈরি- এটা অসাধারণ একটা ব্যাপার। ফলে তাঁর লেখকগোষ্ঠী প্রসারিত হতে থাকে প্রতি সংখ্যাতেই, নতুন লেখক তৈরি করা, লেখক-প্রতিভা খুঁজে বের করা, এটা এই সময়কালে বিরল। কবি ওবায়েদ আকাশ এ জায়গাটিতে একজন সত্যিকারের সাধকের ভূমিকা পালন করছেন, অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছেন। কবি-সাহিত্যিকরা অধিকাংশই আত্মকেন্দ্রিক- এরকম একটা ব্যাপার যখন প্রতিষ্ঠিত, কবি ওবায়েদ আকাশ তা ভেঙে উদার এক আকাশ তৈরি করেন, যে আকাশটা সবার- তবে সেখানে চেতনা ও আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ। লিটল ম্যাগাজিনের যে চেতনা ও বিপ্লব ‘শালুক’ সচেতনভাবেই তা ধারণ করে। শালুকের মিথ সংখ্যা, ইজম সংখ্যা, সমালোচনা সাহিত্য, দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা, শহীদুল জহির, জীবনানন্দ দাশ, সিকদার আমিনুল হক, শহীদ কাদরী, আবুল হাসান, ফ্রান্ৎস কাফকাসহ সব সংখ্যা যে কোনো পাঠককে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। যে কথা কেউ বলেননি, বা যেভাবে কেউ ভাবেননি, অথবা যেভাবে তাকে কেউ আবিষ্কারের চিন্তা করেননি, শালুক সেই সব পথ উন্মুক্ত করে নতুন আলো দেখিয়েছে, সেই আলোতে বহু দূর বহু পথ হাঁটা সম্ভব, সেই পথ থেকে নতুন পথ নির্মাণও সম্ভব। শালুক এ কাজটি দূরদর্শিতার সঙ্গে করছে। বলা যায়, শালুক নতুন পথের নির্মাতা।
শালুকের নভেম্বর ২০২৩ সালে প্রকাশিত সংখ্যার মূল বিষয় ‘শঙ্খ ঘোষ: মুখোশছেঁড়া উজ্জ্বল প্রতিবাদ’। এছাড়াও রয়েছে সমকালীন কবিতা, সময়ের গল্প, বিদেশি সাহিত্য, বই নিয়ে কথা ও অন্যান্য লেখা। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার সংখ্যাটি এ সময়কালের লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে রীতিমতো একটি দৃষ্টান্ত। শঙ্খ ঘোষকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছেন শুধু বাংলাদেশেরই ৬৩ জন লেখক। ‘শঙ্খ ঘোষ: মুখোশছেঁড়া উজ্জ্বল প্রতিবাদ’ শিরোনামে শালুকের ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয় ভাষ্যের ভিতর দিয়ে সংখ্যাটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা যাবে। দীর্ঘ সম্পাদকীয়টিতে শঙ্খ ঘোষের একটি উজ্জ্বল ভাস্কর্য নির্মাণের প্রয়াস রয়েছে; যা শঙ্খ ঘোষের কবিতা, প্রবন্ধ, জার্নাল, রবীন্দ্র গবেষণা, বিশ্বসাহিত্যের দূর মুকুরে প্রতিফলিত দৃষ্টিধারায় উপস্থাপিত। কেন শালুক-এর এই শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা- এ সম্পর্কে কবি-সম্পাদক ওবায়েদ আকাশ তাঁর সম্পাদকীয় ভাষ্যে বলেন-
“আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস ফিরে দেখলে শঙ্খ ঘোষের গুরুত্ব ওজন করে দেখার মতো পাথর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে শঙ্খ ঘোষ এমন একজন কবি, এমন একজন ¯্রষ্টা, এমন একজন রবীন্দ্র গবেষক-গদ্যকার-অনুবাদক, যাকে পরিমাপ করা, সংজ্ঞায়িত করা কিংবা ব্যাখ্যা করা- কোনো গড়পড়তা ভাষা কিংবা চিন্তায় সম্ভব নয়। শঙ্খ ঘোষ বিশ শতকের কবিতায় একটি অবিস্মরণীয় আবির্ভাবের নাম।...
এই বহুমুখী প্রতিভার মৃত্যুর অব্যবহিত পরই সিদ্ধান্ত হয় যে, অধুনাবাদী চিন্তার লিটল ম্যাগাজিন, বিকল্প চিন্তার মুখপত্র ‘শালুক’ তাঁকে নিয়ে একটি ট্রিবিউট সংখ্যা প্রকাশ করবে। তাঁর মতো প্রতিবাদী, তাঁর মতো স্পষ্টভাষী কবি, আজকের দিনে বিরল। তাই তাঁকে সম্মান জানানো শালুক-এর সম্পাদকম-লীর কাছেও এক গুরুদায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সেই চিন্তার নির্যাস আজকের শালুক শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা।”
গুরুত্বপূর্ণ হলো, শুধু বাংলাদেশ ছাড়া দেশের বাইরের কোনো লেখকের কোনো মূল্যায়ন এ সংখ্যায় গ্রহণ করা হয়নি। এটি সম্পাদকম-লীর এক সাহসী সিদ্ধান্ত। শুধু ব্যতিক্রম আছে, কবি শঙ্খ ঘোষের কন্যা শ্রাবন্তী ভৌমিকের ‘বাবা নেই, এবার শরতের আলো আমার জন্য নয়’ সাক্ষাৎকারটির ক্ষেত্রে। সম্পাদকের মতে, যে কবি তাঁর জীবনের শুরুর ১৫টি বছর বাংলাদেশেই কাটিয়েছেন, তিনি তো বাংলাদেশেরই কবি। তাই শঙ্খ ঘোষের মতো একজন কবিকে মূল্যায়নের জন্য, তার প্রতি দায় শোধরানোর জন্য বাংলাদেশের লেখকদের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এবং বাংলাদেশের লেখকগণ লিখেছেনও প্রাণ খুলে। এর অর্থ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোনো স্থানের লেখকদের প্রতি কোনো বৈরিতা নয়; ভারতের অনেক কবির কবিতা মুদ্রিত হয়েছে এ সংখ্যাটিতে।
কবি শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে এরকম একটি প্রয়াস গ্রহণ একদিকে যেমন আশ্চর্যজনক বিষয়, অন্যদিকে সম্পাদকের জন্য অবশ্যই চ্যালেঞ্জ।
শঙ্খ ঘোষ এবং তাঁর সাহিত্যকর্মকে সম্পাদক কয়েক অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রবন্ধগুলো সাজানোও হয়েছে সেভাবেই, একবারে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি। অধ্যায়গুলো,- ১. সম্পাদকীয়: শঙ্খ ঘোষ: মুখোশছেঁড়া উজ্জ্বল প্রতিবাদ, ২. বিষাদের জলমুকুরে স্বদেশের মুখ, ৩. ‘চিত্রল ও ইন্দ্রিয়ঘন জীবনাভিজ্ঞতার কবি শঙ্খ ঘোষ’, ৪. ‘প্রতিবাদে, অভিমানে, অনুযোগে কবি শঙ্খ ঘোষ’, ৫. ‘কবিতায় কুয়াশাভাঙা ভোর’, ৬. ‘অতলান্তিক বোধ ও অমিয় শব্দতরঙ্গ: শিখরস্পর্শী উচ্চারণের কবি’, ৭. ‘তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না’। এছাড়াও শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে গল্প, শঙ্খ ঘোষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, শঙ্খ ঘোষকে নিবেদিত কবিতা, শঙ্খ ঘোষের সাক্ষাৎকার রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা পুরো শঙ্খ ঘোষকে আয়ত্ব করার দারুণ এক প্রয়াস। সেই প্রয়াস কতোটা সফলতার সিঁড়ি অতিক্রম করতে পেরেছে, সেটা বিবেচনার ভার পাঠকের, গবেষকদের।
শঙ্খ ঘোষের কবিতা বিষয়ে লিখেছেন- মিহির মুসাকী, ইমতিয়ার শামীম, বিপাশা মন্ডল, কুমারদীপ ও মাহফুজ আল-হোসেন। মামুন হুসাইন লিখেছেন শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে গল্প ‘ভূমি অধিগ্রহণের পাতালছায়া’। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সফেদ ফরাজী। শঙ্খ ঘোষ বহুমাত্রিকভাবে মূল্যায়িত হয়েছেন এ সংখ্যায়। লিখেছেন নাসির আহমেদ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলারা হাফিজ, আবুল কাসেম, মহীবুল আজিজ, সাদ কামালী, নাসরীন জাহান, হাফিজ রশিদ খান, পৃথ্বিলা নাজনীন, ওবায়েদ আকাশ, মোজাম্মেল হক নিয়োগী, রকিবুল হাসান, মিলটন রহমান, খসরু পারভেজ, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, তানিয়া হাসান, অদ্যনাথ ঘোষ, বহ্নি কুসুম, লুৎফুন নাহার লোপা, বকুল আশরাফ, ফারুক সুমন প্রমুখ।
শালুকের এ সংখ্যা কবি শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা হলেও নিয়মিত বিষয়গুলোও আছে। সমকালকে যুক্ত করে এ সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধিকরণ ও সম্পাদকের দায়িত্বশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ‘অগ্রজ কবিদের কবিতা অধ্যায়ের শিরোনাম : ‘এইখানে এসে তুমি দাঁড়িয়েছ আজ ভোরবেলা’। এ অধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি সমকালীন সময়ের অগ্রজ কবিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে মূলত ষাট-সত্তরের দশকের কবিতা স্থান পেয়েছে। একজন অনুজ কবি অগ্রজ কবিদের কতোটা মান্য করেন, তার নান্দনিক সংযোজন এ অধ্যায়। মোহাম্মদ রফিক, আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, কালীকৃষ্ণ গুহ, জাহিদ হায়দার হাইকেল হাশমী, হারিসুল হক প্রমুখ কবিদের কবিতা সংযোজনে সম্পাদকের গভীর শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় বিধৃত হয়। অগ্রজ ও অনুজের মধ্যে এমনটিই হওয়া স্বাভাবিক। বৈরি পরিবেশে তিনি সুশীতল এক আবহ তৈরি করেছেন। এ অধ্যায়ে তা লক্ষণীয়। আশির দশকের কবিদের কবিতা-অধ্যায়ের কী চমৎকার শিরোনাম ‘অধরা, কেন যৌবন আসে আশিতে!’ কবিতার শিরোমেই প্রতিভাস হয় দশকের পরিচয়। অভিনব ভাবনা। কবিতার মতোই শৈল্পিক-রহস্যে দশকের পরিচয়, বুঝে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, কবিতা উদ্ধৃত শিরোনামের ভেতরেই গ্রোথিত সেই দশকের কবিতা-চারিত্র্য। আবদুর রব, আব্দুল্লাহ জামিল, গৌতম গুহ রায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, প্রবালকুমার বসু, মহীবুল আজিজ, রাজা হাসান, রাহমান ওয়াহিদ, হাফিজ রশিদ খান প্রমুখ কবিদের কবিতা রয়েছে এ অধ্যায়ে।
নব্বইয়ের কবিদের কবিতার শিরোনাম, ‘তুমি আজ এমন করে কথা বলো মনে হয় শব্দ যেন শব্দের সন্ন্যাসিনী’। এই উদ্ধৃতিতে নব্বইয়ের কবিতার কবিচারিত্র্য ফুটে উঠেছে। তাদের কবিতার অনন্য দর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে। মুগ্ধতা যে তৈরি করেছে নব্বইয়ের কবিতা-নন্দনে সেটাও স্পষ্ট হয়েছে। অংশুমান কর, আকবর আহমেদ, ওবায়েদ আকাশ, কাজল ননন, কামরুল ইসলাম, কুমার দীপ, ভাগ্যধন বড়–য়া, মতিন রায়হান, মিহির মুসাকী, মুজিব ইরম, রকিবুল হাসান, শাহনাজ মুন্নী, শাহেদ কায়েস, শোয়াইব জিবরান, হাদিউল ইসলাম প্রমুখ কবিদের কবিতা রয়েছে নব্বইয়ের অধ্যায়ে।
একুশ শতকের শূন্য দশকের কবিতার অধ্যায়টিও শিল্প সুষমাপূর্ণ-“একুশের প্রথম প্রহর / ‘শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে- সেকথা জানো না’”। শূন্য দশকের কবিদের ভেতরে কবি যে অমিয় সম্ভাবনা দেখছেন, সেটাকেই ঢেউ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা গেঁথেছেন কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার উদ্ধৃতি গ্রহণ করে। এই ব্যাপারগুলোকে অভিনব ও শাণিত মেধার আলো বিচ্ছুরণ বলেই ধারণা করি। অতনু তিয়াস, অদ্বৈত মারুত, অপরাহ্ণ সুসমিতা, আফরোজা সোমা, আশরাফুল কবীর, জাকির জাফরান, জাফর সাদেক, জাহানারা পারভীন, নিলয় রফিক, পিয়াস মজিদ, ফারহানা রহমান, শারমিন সুলতানা রীনা, শেখর দেব, রাখি সরদার, হাশিম কিয়াম প্রমুখ কবিদের কবিতা স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি ষাট থেকে-শূন্য দশকের যেসব কবিদের কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে, প্রত্যেক কবিরই গুচ্ছ কবিতা স্থান পেয়েছে। এতে সম্পাদকের দুরদর্শিতার পরিচয় মেলে, কোনো কবি সম্পর্কে একটা কবিতা পাঠ করে কোনো ধারণা লাভ সম্ভব নয়।
মাতাল রোদের পদাবলিতে ঠাঁই পেয়েছে প্রজন্মের কবিতা। লিখেছেন অনন্য কামরুল, অনিন্দ্য ঋজু, অপার অরণ্য, অভি জাহিদ,অমৃতা ভট্টাচার্য, অরবিন্দ চক্রবর্তী, আদ্যনাথ ঘোষ, আশরাফ সিদ্দিকী বিটু,ইকবাল পারভেজ,,ইমন ভট্টাচার্য, ঋজু রেজওয়ান, এনাম রাজু, কস্তুরী সেন, চামেলী বসু, জারিফ আলম,,জীবন তাপস তন্ময়, ঝিনুক, তরুন ইউসুফ, তানিয়া হাসান, দেবশ্রী দে, নাজমা পাপড়ি, নিগার শামীমা, পঞ্চতপা দে সরকার, পাপড়ি গুহ নিয়োগী,,প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমিন সুমি, ফরিদা রানু, ফারজানা ফেরদৌস, বিভা বৃষ্টি, বেবী সাউ, মালেক মুস্তাকিম, মাহফুজা অনন্যা, মাহিরা রুবি, মিলি রায় মোনালিসা রেহমান, রঞ্জনা ভট্টাচার্য, রবীনা মিত্র, রিসতিয়াক আহম্মেদ, লিজা ফাহমিদা শামীমা শ্রাবণী, শাহ্ কামাল, সঙ্গীতা ইয়াসমিন, সাহেদ মুশতার, সুমন শামস, সোমা পালিত ঘোষ, সৌম্যজিৎ আচার্য, সৌম্য সালেক, সৌরভ দুর্জয়, স্নিগ্ধা বাউল, স্বরূপ ম-ল ও হাসান ইকবাল।
ওবায়েদ আকাশ পাঠকের এ দিকটি বিবেচনায় রেখেই হয়তো প্রত্যেক কবির একাধিক কবিতা স্থান দিয়েছেন। দুর্মূল্যের বাজারে এটাও এক কঠিন প্রয়াস। ‘তারপর উঠে আসি, শরীরের সজল প্রবণতা’ অধ্যায়ে সবকার আমিনের ‘হৃদয় একটা ওয়াফাই’ গুচ্ছকবিতা হৃদয়গ্রাহী। ইকবাল হোসেন বুলবুলের ‘গল্পের বারান্দা’য় কবিতারা সযতেœ দাঁড়ানো। ওবায়েদ আকাশের নতুন কবিতা শিরোনাম- অধ্যায়ে বারোটি কবিতা আছে। যা পাঠকের জন্য বিশেষ আগ্রহ তৈরি করবে।
সময়ের গল্পের অধ্যায় শিরোনাম ‘চোখের পাতায় এসে হাত রাখে শ্লথ বেলপাতা’। গল্পেও কবিতা গেঁথেছেনসম্পাদক। তিনি কবি বলেই এমন শৈল্পিক স্পর্ধা দেখাতে সাহস পান। সাদ কামালীর ‘শরীরী অশরীরী’, মোহিত কামালের ‘রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম’, হাসান অরিন্দমের ‘সন্ধ্যেবেলার একটি মানুষ’, ইকরাম কবীরের ‘ক্যাডেট কামরান ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে’, কাজী রাফির ‘নিঃসঙ্গতার ঘ্রাণ’, মহিবুল আলমের ‘অরণ্যের দিকে ফেরা’, স্বাতী চৌধুরীর ‘করোনা ভাইরাস’, মিলন হাসানের ‘কবি সৃজন হাসান নিখোঁজ’, ম্যারিনা নাসরীনের ‘রাজিয়া কাঁদুক’ সাগরিকা নাসরীনের ‘আপদ’, আহসান ইকবালের ‘সামাজিক ছেলেখেলা’, মনীষা সরকারের ‘রামধনু’ ও পিওনা আফরোজের ‘দহন শেষে’ স্থান পেয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে-সমাজভাবনা ও শিল্পগুণে গল্পগুলো সময়ের প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সিরিয়ার কবি আদুনিস (আলি আহমেদ সৈয়দ ইসবার)-এর চৌদ্দটি কবিতা ‘সাদৃশ্য ও শুরুর পুঁথি’ অনুবাদ করেছেন বিকাশ গণ চৌধুরী। অনুবাদকের কৃতিত্বে অনুবাদের চমৎকারিত্বে কবিতাগুলো নিজেদের মাটির-ঘ্রাণ-সজীবতায় আপন হয়ে ওঠে। কবিতাগুলো প্রেম ও বিপ্লবের তেজস্বি চিত্র, প্রতিবাদের উন্মাদনা তৈরি করে রক্তে ও দৃঢ়তায়। দুটি ভিন্ন প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধ দুটি গুরুত্বপূর্ণ। সুরাইয়া ফারজানা হাসানের ‘মার্কেসের অপেক্ষায় প্রহরগনা দারিদ্র্যপীড়িত নির্বাসিত জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং জয়নাল আবেদীন শিবুর ‘বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের কবিতা :বিষয়, প্রকরণ প্রকরণ ও বিশেষত্ব’। দুটি প্রবন্ধেই সযতœ পরিশ্রম ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হয়েছে। তবে জয়নাল আবেদীন শিবুর প্রবন্ধে আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় আশা করা যেতেই পারে। একেবারে শেষে মুদ্রিত হয়েছে ‘শালুক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মিলন-২০২৩’ নিয়ে পারভেজ আহসানের চমৎকার একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পাঠের সময় শালুক উৎসবের ছবিটা দারুণভাবে অনুভূত হয়, বর্ণনাগুণে।
লিটল ম্যাগাজিন দু চারটে সংখ্যা করাই যেখানে কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ঘটে। সে ক্ষেত্রে সময়ের হিসেব থাকে এলোমেলো। কখন কবে কোন সংখ্যা বেরুবে, তা কঠিন সমীকরণ। কারণ অর্থ। কিন্তু পঁচিশ বছর একটি লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত করা এবং বৃহৎ কলেবরে প্রত্যেকটি সংখ্যা প্রকাশ করার সুকঠিন দায়িত্ব ওবায়েদ আকাশ কীভাবে পালন করছেন, তা ভাবনার বিষয়। বুদ্ধদেব বসুর কথা দিয়েই শেষ করি, ‘লিটল ম্যাগাজিন ব্যবসা হিসেবে অচল, তাকে চালাতে হলে আর্থিক অপব্যয়ের শক্তি চাই। সে শুধু ধনের শক্তি নয়, মনেরও শক্তি।’ ওবায়েদ আকাশের শক্তিটা বোধ হয় মনেরই। সমৃদ্ধ এ সংখ্যাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪৪। মূল্য মাত্র ৭০০ টাকা।
-
সাময়িকী কবিতা
-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প
-

কল্পগল্প
-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’
-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
-
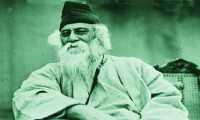
আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-

আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ