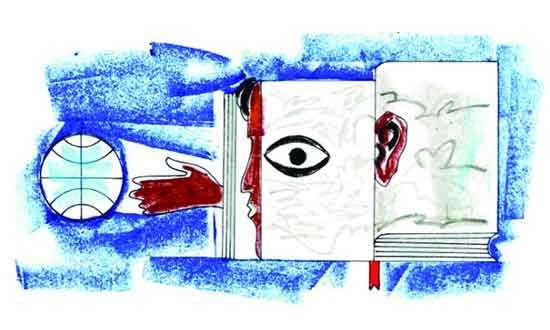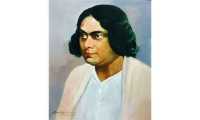সাময়িকী
প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
মোহিত কামাল
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী
(পূর্ব প্রকাশের পর)
ফ্রয়েডের মতে, মানবমনের- সহজাত প্রবৃত্তি (ইনস্টিংক্ট) হচ্ছে জীবনপ্রবৃত্তি (ইরোস) ও মরণপ্রবৃত্তি (থেনাটোস)। ইরোস-এর আড়ালে আছে দেহভোগ বা দেহ তৃপ্তির গোপন তাড়না। মানুষের সব ধরনের আচরণের শেকড় গেড়ে আছে ইরোসের মূলে; যৌনতৃপ্তিই সেই শেকড়ের অন্যতম চাহিদা। কিন্তু এটা নিয়ে বিতর্ক আছে। মানুষ এমন অনেক আচরণ করে যার সঙ্গে দেহতৃপ্তির কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই। ফ্রয়েড যুক্তি দেখিয়ে বলেন, দুই ধরনের বিধিনিষেধের কারণে দেহতৃপ্তির আগ্রহের বহিঃপ্রকাশে দেরি হয়, অথবা ভিন্ন বা পরিবর্তিত অন্য পথে লালিত গোপন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। বিধিনিষেধের একটি হচ্ছে বাস্তবতা ‘রিয়েলিটি’, অন্যটি হচ্ছে নৈতিকতা‘মোরালিটি।’ আত্মধ্বংসী প্রবৃত্তির সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, সংঘাত বাঁধে। এ কারণে ধ্বংসাত্মক তাড়নার প্রকাশ ঘটে অন্যের প্রতি সহিংস আচরণ বা অ্যাগ্রেশনের মধ্য দিয়ে।
এ বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে। হেনরি মুর এবং আব্রাহাম মাসলো মনে করেন, সব মোটিভ শারীরবৃত্তীয় চাহিদানির্ভর নয়। কিছু কিছু মোটিভ অর্জিত হয় সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায়। মানুষের চাহিদাকে সাতটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করেছেন মাসলো ধাপে ধাপে সাজিয়েছেন চাহিদাগুলো। সর্বনি¤œ চাহিদা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় চাহিদা এবং সবার উপরে আছে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির চাহিদা। বিশ্লেষকদের মতে, ‘ফ্রয়েডীয় মতামতের পাশাপাশি এই মতবাদ বিশ্বসাহিত্যকে প্রভাবিত করলেও সাহিত্যতত্ত্বের সুররিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ প্রাধান্য দিয়েছে এক সমগ্রতা বা অভিন্নতাকেযে অভিন্নতা গড়ে উঠেছে সজ্ঞান ও অবচেতন মনের স্তরকে কেন্দ্র করে। সুররিয়ালিজমে ফ্রয়েডের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে অবচেতন মনের রহস্য উদঘাটনের কৌশল, হেগেলের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সংস্কার এবং কার্ল মার্কসের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করেছে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার আবেগ। প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায়ও প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সুররিয়ালিজম।’ এ তত্ত্বে ব্যক্তিমনের চেতন-অবচেতন স্তর একাকার হয়ে যায়, স্বপ্নের সঙ্গে জাগতিক বিষয়-আশয় যুক্ত হয়ে স্বপ্নময়বাস্তবতা জেগে ওঠে। ফ্রয়েডের সজ্ঞান ও অবচেতন মনের স্তর, হেগেলের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের সংস্কার এবং দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার আবেগ; জীবনানন্দ দাশের কাব্যধ্বনির সর্বত্রই রয়েছে মনস্তত্ত্বের নিপুণ কারুকাজ, মনোশক্তির এই বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদুবাস্তবতার মধ্যেও বাস্তব সমাজচিত্রে জাদু উপকরণের আগমন ঘটে, ‘কুহক’ তৈরি হয়।
‘কুহক’ অর্থ কী?
এই বিশেষ্য পদটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মায়া, ভেল্কি, ইন্দ্রজাল, ছল, প্রতারণা, ঘুটঘুটে অন্ধকার। রূপকথার মধ্যেও এ ধরনের জাদু উপকরণ মিশিয়ে গল্প তৈরি করা হয়। তবে তার সবকিছুই জাদুময় আর জাদুবাস্তবতায় চারপাশে বাস্তব আবহ থাকে। যেভাবেই গল্প নির্মিত হোক না কেন, স্বপ্নবাস্তবতা কিংবা কুহক সৃষ্টিতেও লেখকের কল্পনাশক্তির বিপুল ঐশ্বর্য ব্যবহৃত হয় নিজের অজান্তে যা তাঁর মেধার অঙ্গ আর মেধাটা হচ্ছে মনের উপাদান।
রোমান্টিসিজম, সেন্টিমেন্টালিজম, হিউম্যানিজম ইত্যাদি সাহিত্যমতবাদেও উপস্থিত রয়েছে মনস্তত্ত্বের সূত্রসমূহের ব্যবহার বা তার অন্তর্লীন অনুরণন। রোমান্টিসিজমের প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে রোমাঞ্চ ও রোমান্সের মতো স্বতঃস্ফূর্ত মনস্তাত্ত্বিক বিষয় উত্তেজনা, ভয় বা বিস্ময়ে গায়ে কাঁটা দেওয়া; শিহরন, পুলক, কিংবা উগ্র বা অস্বাভাবিক প্রেমকাহিনি, যে কোনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপার, অলীক কল্পনায় রং মাখানো বর্ণনা; রোমান্টিক মানসিকতা ইত্যাদি। নিউরোসায়েন্স-এর দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে রোমাঞ্চ কিংবা রোমান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত মস্তিষ্কের জৈবরাসায়নিক পদার্থের রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এই বিমূর্ত প্রতিক্রিয়াগুলো মূর্ত হয়ে ধরা দেয় আচরণে। একজন নিপুণ কথাশিল্পী শৈল্পিক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে পারেন অন্তর্গত সেই সত্যের বাস্তব রূপ। আর আদর্শ ও নীতিবোধ নিয়ে অতিরিক্ত আবেগের প্রকাশ দেখা যায় সেন্টিমেন্টালিজমে। এই আবেগ হচ্ছে মনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা উপাদান। এই উপাদান প্রেষণা ও চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি ও সাহিত্যিকের মনে জাগিয়ে তোলে সাহিত্য সৃষ্টির গতিময় ধারা।
মনস্তত্ত্বের ‘ফাইভ ফ্যাক্টর সূত্র’ [পরিবেশ (অতীত ও বর্তমান)-(চিন্তন-আবেগ-আচরণ-শারীরিক প্রতিক্রিয়া), ১৯৮৬] অনুযায়ী, আবেগের সঙ্গে চিন্তনের রয়েছে পারস্পরিক যোগসূত্র। আবেগ বা চিন্তনের যে কোনো একটি মনোক্রিয়া নাড়া খেলে আলোড়িত হয় অন্যটিও, পৃথকভাবে মন জেগে ওঠার সুযোগ নেই মনস্তত্ত্বে, সাহিত্যসৃজনে। মন জাগাতে হলে সাহিত্যে নিমগ্ন হতে হবে; পেতে হবে মনের খোরাক। মনের নানা ধরনের খোরাকের মধ্যে আবেগ হচ্ছে অন্তর্লীন এক বিশেষ উপাদান বা মনোক্রিয়া। কেবল সেন্টিমেন্টালিজমে নয়, অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত আলোচিত সব ধরনের সাহিত্যমতবাদে সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্মাণে আবেগের রয়েছে দৌর্দ- প্রতাপ।
আবেগ বিছিন্ন রেখে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এ কথা বিশ্বাস করে গেছেন সময়ের শক্তিমান সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও। কোনো কোনো মতবাদে সুনির্দিষ্ট বিশেষ মননক্রিয়া প্রাধান্য পেলেও সাহিত্যসৃষ্টি কিংবা মূল্যায়নে কখনো আবেগের স্থানচ্যুতি ঘটেনি কোথাও।
ভাববাদ কিংবা যুক্তিবাদ, যাই বলি না কেন, সর্বত্রই চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের কারণে সাহিত্যের মূল প্লাটফর্মে রয়েছে আবেগের উজ্জ্বল উপস্থিতি।
সাহিত্যতত্ত্বের মতবাদ হিউম্যানিজমে মানুষ, তার কর্মময় জীবন, ধর্ম এসবের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। জীবনের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে মনোবিজ্ঞানের কলকব্জা। জীবনের সেই কলকব্জা খুলে খুলে, কিংবা মৌলিকভাবে লেখক নির্মাণ করেন অবিস্মরণীয় সব চরিত্র। কালজয়ী সাহিত্যে সেই চরিত্ররা যুগ থেকে যুগে প্রভাবিত করে আসছে চলমান সাহিত্যধারা, জীবনবোধ। তাই বলা যায় কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকেরা সৃজনশীল। তাঁরা জীবনের চিত্র খুঁড়ে খুঁড়ে, বিশ্লেষণ করে, শব্দের বুনোটে প্রতিবিম্বিত করতে পারেন নতুন জীবন। শব্দ-বুনোটে স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বভাবজাত গুণাবলির কারণে তাঁরা ব্যবহার করেন প্রতিভা কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, সৃজনশীলতা, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও ধারণা বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, যুক্তিপ্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা চিন্তনশক্তি, আবেগ, প্রত্যক্ষণ, সচেতনবোধ বা কগনিশন, অন্তর্গত প্রেষণা বা ভেতরের আকাক্সক্ষা চাহিদা-উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শিক্ষণ- মনের স্বাস্থ্যের এসব কলকব্জা। এভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায় সমৃদ্ধ, জীবনঘনিষ্ঠ মৌলিক সাহিত্যসম্ভার। ব্যঞ্জনাময় উপস্থাপনার মাধ্যমে সৃজনশীল মেধার স্ফুরণ ঘটে- সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পকর্মের বিস্তৃতি এভাবেই ঘটে চলেছে সমকালে। ঘটতে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে। তাই, আলোচ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিকগণ কেবল সৃজনশীলই নয়, তাঁরা এক ধরনের বিজ্ঞানীও।
এ ধারাও কি স্থায়ী থাকবে? নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবল প্রতাপে উড়ে যাবে? সময়ই তার জবাব দেবে। সময়ই উত্তম বিচারক।
চার মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস : স্বরূপ সন্ধানে
উপন্যাস মানে জীবনচিত্র। আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। উপন্যাসের পাতায় পাতায় উঠে আসে সৃষ্ট চরিত্রের জীবনযাপনের কাহিনি আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রাগ-ক্রোধ, ঈর্ষা কিংবা প্রতিহিংসা। মনের এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয় কথাসাহিত্যের চরিত্রদের বাইরের আচরণ। প্রত্যক্ষণ অথবা চিন্তনের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা পরিস্থিতি মূল্যায়নে ভুলভ্রান্তি নির্মাণ করে ব্যক্তির মনোজগতের অন্তর্নিহিত রূপ, গড়ে তোলে চারপাশের আবহ। চারটি উপন্যাসে আছে জীবনের নানাচিত্র আর মনোভূমি। এসব উপন্যাস নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলার তগিদ বোধ করছি। যদিও পাঠক এবং সাহিত্যতাত্ত্বিকেরাই উপন্যাসের গুণাগুণ বিচার করে থাকেন, গ্রহণ-বর্জন করে থাকেন। তবু লেখক হিসেবে পাঠকের কিংবা প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে তুলে ধরতে চাই।
‘মন’
মনোবিজ্ঞানের কলকব্জায় চড়েই উপন্যাসের জীবনধারা ও ডালপালা বিস্তৃত হয়েছে, শৈল্পিক শব্দমালার ভেতর থেকে মনস্তত্ত্বের অনুষদগুলো আপন আলো নিয়ে বেরিয়ে এসেছে।
কী সেই নির্মিত আখ্যান?
ভালোবাসায় পূর্ণ দাম্পত্য জীবনে ফাটল তৈরি হয়। বদলে যায় চরিত্রদের মনের গতি-প্রকৃতি। সুখী পরিবারের ভিত ভেঙে যেতে থাকে। ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ক্রোধের আগুনে পুড়তে থাকে তাদের মন। পুড়তে থাকে দেহ। সংকট কেবল তৈরি হয়ে থেমে থাকেনি, জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।
এ ধরনের সামাজিক সমস্যা চিত্রণে উঠে এসেছে জীবনযন্ত্রণার গোপন হাহাকার। ভালোবাসার গোপন শক্তি কাজ করেছে ওষুধ হিসেবে। সামাজিক ক্ষত দূর করা ও সমাজ সংস্কারের জন্য নৈতিকতা ব্যবহার করা হয়েছে চরিত্রদের মনোবিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। উপন্যাসের শব্দবিন্যাসের ধাপে ধাপে মনোথেরাপির বিষয়-আশয় ব্যবহার করে চরিত্রগুলোর ভেতরগত শুদ্ধির পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা নৈতিকতার চর্চার কারণে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হবে সামাজিক ঘা নিরাময়ের কৌশল।
সমকালীন জীবনধারায় মোবাইল ফোনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর ফলে সমাজের নারী-পুরুষের মধ্যে গেড়ে বসেছে মারাত্মক ধরনের ক্ষত। মোবাইলের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ হানা দেয় নারী-পুরুষের শয়নকক্ষে। আলোড়িত হয় মন। আলোড়িত হয় দেহ, যৌনতার গোপন কক্ষে ঢল নামে। গড়ে ওঠে পরকীয়া, সর্বনাশ হয়ে যায় পারিবারিক আবহ। অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় সন্তানের ভবিষ্যৎ। মা-বাবার নৈতিক স্খলনের কারণে সন্তানের ব্যক্তিত্বের কাঠামোয় গেড়ে বসে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। অনিয়ন্ত্রিত হয় আচরণ ও মেজাজ। বেড়ে যায় তাদের অনৈতিকতা ও মাদকাসক্তির ঝুঁকি।
‘না’
উপন্যাসের মূলস্রোতে রয়েছে ‘না’ বলার সুফল, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়ে নিজেকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জয়গান।
উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রুবা।
তেজস্বিনী এই তরুণী ইতিবাচক মূল্যায়নের মাধ্যমে তৈরি করে সুন্দর পথ চলা। নেতিবাচক চিন্তার ঝড় সামলে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যায় সামনে। রবিনকে ভালোবাসে রুবা। রবিনও ভালোবাসে রুবাকে। তারপরও সম্পর্কের টানাপোড়েনে সন্দেহের বিষ ঢুকে যায় দুজনের মনে।
কীভাবে জড়িয়ে গেল সন্দেহের ঘূর্ণিতে?
কীভাবে মোকাবিলা করল তুষের আগুন?
হোস্টেল-জীবনের রুমমেট সিমি, মণি, সানিয়াদের নিয়ে রুমে মায়ার জগৎ গড়ে তোলে রুবা। বন্ধুত্বের মর্মস্পর্শী আবেদনও। তাদের সংগ্রামী জীবনের মধ্য থেকে উপন্যাসে উঠে এসেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত অপরাধচিত্র। একজন ঘৃণ্য অপরাধী বন্ধু সেজে ছোবল বসাতে চায় রুবার বুকে। তার ব্যক্তিত্বের সাবলীল প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে ঢুকতে পারেনি বিষবাণ। এই বাণে আক্রান্ত হয় রুমমেট সিমি। সর্বনাশের শেষ সীমানায় পৌঁছে যায় সে। পাঠক-হৃদয় বেদনায় চিৎকার করে ওঠে। তরুণবয়সীরা বুঝতে পারবে মুখোশের আড়ালে ওত পেতে আছে কী বিপদ, চারপাশে বিছানো আছে কী ভয়াবহ জাল! এই জালে একবার পা দিলে নিঃশেষ হয়ে যায় জীবন।
মেয়েরা কীভাবে নিপীড়ন ভোগ করে, কীভাবে ভুল করে, ভুল আবেগের বশে বিপর্যস্ত করে নিজের জীবন ও পরিবার, তারই চিত্র দেখা যাবে শিমুল ও ইরা চরিত্রে।
‘না’ উপন্যাসে আরও রয়েছে স্কুলপড়–য়া দুটি টিনএজ চরিত্র- আনিকা ও তিমু। মোবাইলপ্রীতি ওদের পড়াশোনার বিঘœ ঘটায়। জেনারেশন গ্যাপের কারণে পারিবারিক বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। টিন-এজাররা বুঝতে পারবে নিজেদের ভুলত্রুটি। অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার পথ খুঁজে পাবে তরুণ-তরুণীরাও।
রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ভেতরের চেতনা থেকে উঠে আসে মানুষের ভালোবাসার গোপন ডাক। কুঠিবাড়ির বর্তমান ও ঐতিহাসিক ঘটনা যোগ হয়েছে উপন্যাসের অন্তর্গত স্বরের টানে। কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রস্পর্শে ভালোবাসায় ভরে উঠবে মন।
শব্দের মায়াজাল আর বিজ্ঞানের আলোয় খুলে যাবে পাঠকের চোখ।
‘মায়াবতী’
বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস, টিনেজ রূপবতী মেয়েদের নিয়ে লেখা। সাহিত্যের শব্দবিন্যাসে মনস্তত্ত্ব, সমাজের আড়ালের চিত্র দেখার সুযোগ পাবেন পাঠক। মা প্রত্যক্ষ করেছেন মেয়েরা নানাভাবে উৎপীড়ন ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়; সহজে মুগ্ধ হয়ে অবিশ্বাস্য পাতানো ফাঁদে পা দেয়। মায়ের একান্ত চাওয়া মেয়ে ক্যারিয়ার গড়ে তুলুক। বিধিনিষেধ আরোপ করেন মা। মেয়ে তখন মনে করে মা স্বাধীনতা দিতে চান না, বিশ্বাস করেন না ওকে।
মায়ের অবস্থানে মা ভাবছেন তিনি ঠিক।
মেয়ের অবস্থানে মেয়ে ভাবছে সে ঠিক।
মায়ের ‘ঠিক’ এবং মেয়ের ‘ঠিক’-এর মাঝে সংঘাত বাধে। সংঘাত থেকে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ভুল করে বসে মেয়ে, উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট রিয়া। পালিয়ে যায় ঘর থেকে।
এই ‘ভুল’ই হচ্ছে উপন্যাসের মূলধারা, মূলস্রোত।
আরও আছে দুটি সমান্তরাল ধারা : এক স্রোতে রয়েছে বুয়েট পড়ুয়া মাহিনের হৃদয়স্পর্শী এক্সপ্রেশন, নোবেল জয়ের অন্তর্গত অনুপ্রেরণার(উপন্যাসটি যখন লেখা চলছিল তখন বাংলাদেশ নোবেল প্রাইজ অর্জন করে শান্তিতে)।
এই অনুপ্রেরণার মূল হচ্ছে মাহিন। কুসুমকলি জয়ী হয়েছে মাহিনকে ভালোবেসে। অন্য সমান্তরাল ধারাটি হচ্ছে মায়াবতীদের জীবনের আড়ালে লুকোনো কঠিন সত্যের উদ্ঘাটন : দেহ নিয়ে টিনএজে শাশার মতো মেয়ের এ সময়ের ভাবনা, বুবলির মতো কিশোরীর লোভী পুরুষের চোখ চেনার কথা, আদিম সত্তায় পা রেখে কালো মেয়ের বেঁচে থাকার লড়াই, অর্কর মতো যুবকের ভালোবাসা কী চায়, আলোবতী বাঁধনের বিজয়গাথাও দেখা যাবে। দেখা যাবে মামা, খালু, হুজুর কিংবা কোনো কোনো টিচারের অনৈতিক ফাঁদে কীভাবে জড়িয়ে যায় তরুণীরা। এসব অনৈতিক ফাঁদের আড়ালে কাজ করে চরিত্রদের সহজাত প্রবৃত্তি, ফ্রয়েডের ইরোসতত্ত্ব।
উপন্যাসের আরেকটি উজ্জ্বল চরিত্র মেধাবী মেয়ে মুনা। বিদেশে থাকে, সুদর্শন পাত্র পেয়ে গলে যায় মুনার পরিবার। বিয়ে হয়, প্রেগন্যান্ট হয় মুনা। তারপর জানতে পারে ছেলের আসল চরিত্র। মিথ্যাচারের চিতায় পুড়ে যাওয়া মুনা ছাই হয়ে যায়নি। পাঠক দেখতে পাবেন এই প্রজন্মের কালজয়ী মাতৃত্ব।
‘মায়াবতী’ উপন্যাসটি পড়ে চিন্তনের বুননে ইতিবাচক গিঁট দেওয়ার কৌশল দেখার সুযোগ পাবেন পাঠক। যে কোনো ধরনের ভুল করার আগেই সামনের ভুলটা দেখতে পাবেন। পচা গর্তে পা দেওয়ার আগেই দেখতে পাবেন গর্তের বীভৎসতা। অগ্রিম দেখার সুযোগে সেই বীভৎসতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে এ সময় কিংবা আগামী দিনের টিনএজ প্রজন্ম।
‘সুখপাখি আগুনডানা’
সমাজে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা দেখে চলেছি জীবন-যন্ত্রণার গোপন হাহাকার, ভাঙ্গা-গড়ার রৌদ্রছায়া। ভালোবাসা ভাঙে, ভালোবাসা গড়ে। দেহ ভাঙে, যৌবন ভাঙে, জেনারেশন ভাঙে। ভেঙে ভেঙে বদলে যায় জীবন। কালযাপনের মধ্য দিয়ে তৈরি হতে থাকে মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ, জীবনদর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিত। চারপাশের আড়ালের চিত্র দেখার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে লেখার কনসেপ্ট, ধারণা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র নাদিয়া এবং উপন্যাসের মূল পটভূমি। নাদিয়ার প্রতি অঙ্কনের অসামান্য বন্ধুত্বের স্বরূপ দেখা যাবে উপন্যাসে। বান্ধবীর জন্য এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড়ই প্রয়োজন-অনন্যসাধারণ এই ভালোবাসার কারণে অঙ্কন হারিয়েছে সন্দেহপ্রবণ নোয়েলের ভালোবাসা। হেরে যায়নি সে। ত্যাগের বিনিময়ে মহিমান্বিত করেছে বন্ধুত্ব।
অন্যতম চরিত্র শিক্ষক জিয়াউল হক ছাত্রীর সঙ্গে আবেগনির্ভর সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের মেয়ের অসামান্য ক্ষতি মানতে বাধ্য হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মৌলিকভাবে বদলে গেছেন। জয় হয়েছে পিতৃত্বের-বিবেকবোধের আলোয় ফিরে এসেছেন বিদ্রোহী মেয়ে ও স্ত্রীর কাছে। নাদিয়ারা আছে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। কাছ থেকে দেখা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে বহু নাদিয়া মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়-ক্যারিয়ার গড়ার পথ থেকে দূরে সরে যায়। এ ধরনের অসংখ্য নাদিয়ার মধ্যে থেকে উপন্যাসের নাদিয়া চরিত্রটি উঠে এসেছে।
পাঠক দেখার সুযোগ পাবেন অধঃপতিত জীবনের ভেতরে ঢুকলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না মানুষ। দেখতে পাবেন, সর্বনাশের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়েও চরিত্রগুলোর ভাবনার ইতিবাচক পরিবর্তন, নৈতিক শক্তির উন্মেষ।
আরও দেখতে পাবেন মানুষের আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানব-মনের অন্তর্নিহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শিল্পিত বিজ্ঞান।
নাদিয়ার জীবন থেকেই বিজ্ঞান আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে অন্য চরিত্রগুলোরও মনোজগৎ। উদ্দেশ্য হচ্ছে অসংখ্য নাদিয়ার চোখ খুলে দেওয়া, অসংখ্য নোয়েল কিংবা লিমনের ‘ভুল’ আবিষ্কারের পথটা উন্মোচন করা, সেই সঙ্গে শিক্ষকদের সজাগ করা।
এই চারটি উপন্যাসের শেষে আলাদা পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে উপন্যাসের চরিত্রদের মনোবিশ্লেষণ, মনোবৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ।
শেষকথা
বিস্তৃত আলোচনার পরেও প্রশ্ন উঠতে পারে সব সাহিত্য-মতবাদেই তো মনস্তত্ত্ব রয়েছে। আলাদা করে ‘মনোবৈজ্ঞানিক’ শব্দটা ব্যবহারে যৌক্তিকতা কী?
একজন মনোবিদ হিসেবে মানুষের মনোগতের জটিলতা বোঝা এবং বর্তমান পৃথিবীর বহুমাত্রিক সংকট পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা, একজন লেখক হিসেবে জগৎ-জীবন দেখা আর কল্পনার মিশেলে কথাসাহিত্যে একটি নতুন ধারা সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এই সংকলনের উপন্যাস লেখার শুরু থেকে ছিল আমার মধ্যে। মানুষের সংকটের নানামাত্রিক উপাখ্যান, যাপিত জীবনের বিচিত্রতা-বৈচিত্র্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেণ আর মানবমনের সঙ্গে কথাসাহিত্যের মিলিত ধারারই নামকরণ করেছি ‘মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস’। কথাসাহিত্য বা সাহিত্যের অনান্য শাখার মধ্য থেকে বিভিন্ন মতবাদের যে উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং অনুশীলন, তারপর নানাভাবেই যে আবারও নতুনত্বের দিকে অব্যাহত যাত্রা তা নিয়ে এই ভূমিকাতেই আলোচনা করেছি। যদিও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই বিষয়টির আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে। তবু এখানে অল্পকথায় যা তুলে ধরা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যত ধরনের মতবাদ বা তত্ত্বের উদ্ভবই হোক অথবা যা কিছু যুগ ও কাল অস্বীকার করুক না কেন, মন কখনো কোনো মতবাদে অনুপস্থিত নয়। অর্থাৎ জীবন এবং জীবনবোধ, চারপাশ ও পরিবেশ, বাস্তবতা বা অতিবাস্তবতা, কাল কিংবা কালের পরিবর্তন, যুগ অথবা যুগ-যন্ত্রণা সব কিছুতেই মন বিদ্যমান, মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখাও তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।আর তাই চার উপন্যাস-সংকলনের এই ধারাকে বলতে চাই মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস।
সংকলনটি কি আশাজাগানিয়া সংকেত দিতে পারল সমকালীন প্রজন্মকে, আশা জাগাতে পারবে আগামী প্রজন্মের মনোজগতে? উপন্যাসের সঙ্গে কেন ‘মনোবৈজ্ঞানিক’ শব্দটি যোগ করা হলো, কেন এমন নামকরণ করা হলো, তার কি উত্তর পাওয়া গেল? ভিন্নমত পোষণকারীগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের মতামত জানালে খুশি হব। যারা ইতোমধ্যেই ধারাটি গ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য রইল অফুরান ভালোবাসা, শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে বলার ইচ্ছা শাসন না-করে বলতে চাই জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ ও সঙ্গীত বিষয়ক অধ্যাপক ও গবেষক মুস্তাফা জামান আব্বাসীসহ আরও অনেকে ধারাটির বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।
বিশাল কলেবরের নতুন ধারার এই সংকলনটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন, বিপুল লগ্নির বিষয়ে উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছেন বাতিঘর-এর অনন্য বাতি, বই বিপণনের তরুণ কিংবদন্তি দীপঙ্কর দাশ।
তাঁর প্রতি রইল ভালোবাসা।
কৃতজ্ঞতা : সহায়ক গ্রন্থসমূহ
১. মুহম্মদ মুহসিন, সাহিত্যতত্ত্ব : একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা; ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩
২. বদিউর রহমান, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব: সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হোরেস, লঙ্গিনাস; ঐতিহ্য, ডিসেম্বর ২০২৩
৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যতত্ত্ব: প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য; দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৬
৪. Paul Harrison, Philip Cowen, Tom Burns, Mina Fazel, Shorter Oxford Textbook of Psychiatry; Oxford university press 17 edition 2018
৫. Andrew B. Crieder et al, Psychology; Herper 1993 Collins college publishers
৬. Denis Green Berger & Padesky CA; Mind Over Mood; the Guilford, inc. New York 1995
-
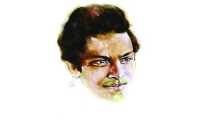
প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল
-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান
-
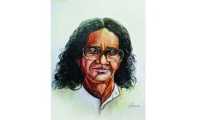
মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-
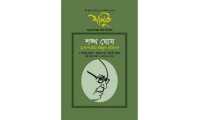
শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন
-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প
-

কল্পগল্প
-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’
-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
-
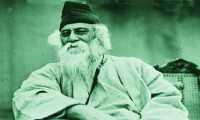
আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস