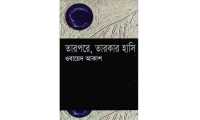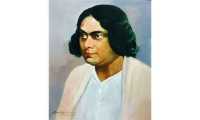সাময়িকী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
সোহেল মাজহার
১৯৫৬। করাচিতে স্ত্রী এ্যান মেরির সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
ভাষার মায়া, শব্দের পর শব্দ, বাক্যের বিস্তার যতি বিন্যাসের আড়ালে আশ্চর্য এক কুহক সৃষ্টি করেন, সমাজ-মানুষের বহিরাবরণ, অন্তর্ভুবনের ছবি আঁকায় পারদর্শী কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যকে আমূল বদলে দিলেন। অনেক ঘটনা, নাটকীয়তা, উত্তেজনা ও দৃশ্যের সরল বর্ণনার ভিতর বাংলা সাহিত্যের যে রীতি ছিলো সেখান থেকে বাংলা সাহিত্যকে ভিন্ন একটি অবয়ব দান করেন। তাঁর রচনায় মানুষের বাস্তুজগতের পরিপার্শ্ব, ছায়া দৃশ্যের পরিবর্তে মানুষের মনে প্রতিনিয়ত বাঁক বদলের খেলা চলে। অন্তর্জগতের দিকনির্দেশহীন প্রবাহের প্রকৃতি।তিনি অঙ্কন করেছেন নিপুণ হাতে। সমাজের সামান্য, বিশেষ, সাধারণ-অসাধারণ মানুষের যে গল্প তিনি বলেছেন তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কোনো অতি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেননি। প্রতি মুহূর্তে মানুষ যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতার বৃত্তে আবদ্ধ থেকে ক্ষণে-ক্ষণে ঘটনা, উদ্বেগ, উৎকন্ঠা ও বাক তৈরি করে যাচ্ছে উপন্যাসগুলোতে বারবার সে কথা মূর্ত হয়েছে।
ঘটনা, পটভূমি ও বলার ধরন ভিন্ন হলেও তাঁর উপন্যাসগুলোর মূল সুরগুলো কিন্তু এক। অর্থাৎ চরিত্রগুলোর জীব জিজ্ঞাসা, প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের বিশ্বাস ও বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো ও আপন সত্তার স্বরূপ উদঘাটন করে যাওয়া। ভ- মজিদ, খালেক বেপারি, রহিমা, যুবক শিক্ষক আরেফ আলী, কফিল উদ্দিন উকিল, মুহাম্মদ মুস্তাফা, স্কুল মিস্ট্রেস, খাদেম আলী, দরবেশ কাদের, তারা প্রত্যেকেই নিজেদের ভূমিকা-কৃতকর্মের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে চেয়েছেন। যদিও তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, রিরংসা, হিংসাপরায়ণতা, মহানুভবতা, পলায়নপর মনোবৃত্তি, মনোবিকলন, বিদ্রোহ, মমত্ববোধ, প্রেম ও সহানুভূতির মিশ্রণে দায়বোধ, প্রতিশোধ পরায়তা, দুর্বল মনোবৃত্তি, স্মৃতিকাতরতা, স্মৃতিবিভ্রম ও অসহায়ত্বের ছবি ফুটে ওঠে। তিনি মানুষ ও সমাজের উপরিতলের কেন্দ্র কিংবা প্রান্তে ছুটে যাননি, বরং মানুষের অন্তর্লীন রহস্য, গূঢ় অভিব্যক্তিকে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্লিপ্ত ভঙ্গি, নৈব্যর্ক্তিক অবস্থান, উপন্যাসের প্রতিপার্শ্ব ও চরিত্র তৈরি করা। এই অর্থে উপন্যাসের খল চরিত্র কিংবা নায়ক যেই হোক না কেন, তিনি তাদেরকে আরোপিতভাবে উপস্থাপন করেননি। অর্থাৎ উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহ এবং ব্যক্তি চরিত্রের ঘটনাপ্রবাহ তার আপন গতিতেই বিকশিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য যদিও তার প্রতিটি উপন্যাসে কমবেশি লক্ষ্যণীয়, তবে লালসালু উপন্যাসটিই অধিকতর সফল। প্রচলিত অর্থে লালসালু উপন্যাসে কোনো নায়ক নেই। উপন্যাসের খল চরিত্র মজিদই কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত রিচার্ড রাইটের বিখ্যাত উপন্যাস ‘দ্য নেটিভ সান’-এর কথা উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসটিতে একটি পর্যায়ে এসে; একজন কালো ছেলে শ্বেতাঙ্গ কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করে তাকে ফায়ার প্লেসে পুড়িয়ে মারে। নিঃসন্দেহে ঘটনাটি বীভৎস। অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য। কিন্তু অনুভূতিশীল ও বিচারবোধসম্পন্ন যে কোনো মানুষ সেই কালো ছেলেটির প্রতি সহমর্মিতা বোধ করে। তীব্র বৈষম্য-বঞ্চনা ও অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ তাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষ হতে দেয়নি। লেখকের বড় সাফল্য ছিল আখ্যানের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নির্বিকার ও নৈব্যর্ক্তিক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা। ‘লালসালু’র ক্ষেত্রেও লেখক তেমন নির্বিকার, নৈর্ব্যক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ একজন বক ধার্মিক ও ভ- মাজার ব্যবসায়ীর প্রতিভু। শস্যহীন, খরতপ্ত বসতি ছেড়ে যে কোনো উপায়ে মজিদ একদিন নিজেকে পীর হিসাবে আবিষ্কার করে। এটি একদিকে ছিলো নিজের কৌশলী উদ্ভাবন এবং নিজের কাছে নিজেই বিস্ময়। বেঁচে থাকার জন্য অন্য কোনো উপায় কি ছিল না তাঁর? হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না। কিন্তু লেখক উপন্যাসের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একটি আবহ তৈরি করেন, যেখানে ভ- মজিদের জন্য, প্রতারণার জন্য তার প্রতি মন বিরূপ হয়ে ওঠে, ঘৃণা জন্মে। কিন্তু আমাদের অবচেতন মনের কোণে ধীরে ধীরে সহানুভূতিও তৈরি হয়। উপন্যাসটি আমাদের গ্রাম জীবনের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মভীরুতা ও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির একটি আলেখ্য।
‘লালসালু’ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোষণের নিবিড় প্রক্রিয়াও দৃশ্যগোচর হয়। মজিদ ও খালেক বেপারী সমাজ কাঠামোর ভিতর এক অপরের পরিপূরক। উপন্যাসের খালেক বেপারী যতটা নতজানু চরিত্রের বাস্তবের বেপারীগণ ততটা নতজানু নয়। সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপট বলে পুরোহিত তন্ত্র হলো শোষণের সহায়ক শক্তি, শাসকগোষ্ঠীই ক্ষমতার মূল প্রতিভু। ক্ষমতার প্রয়োজনেই ধর্মের অপব্যবহার ও অমানবিক প্রয়োগ শুরু হয়। ধর্ম হয়ে ওঠে শোষণের পরিশুদ্ধ খোলস। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক হয়তো আখ্যান রচনায় নিজস্ব কৌশল ও শিল্পরীতির কারণে বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। লেখক রহিমা ও জমিলা দুজনকে দু’ধরনের প্রতিমূর্তি হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। হ্যাঁ এই কথা সত্য জমিলার কাছে মাজার শরীফ অসহ্য মনে হয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মাজারকে ভক্তি করতে বাধ্য করতে চাইলে, ঘৃণায় সে মজিদের মুখে থুথু ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে তার প্রতিবাদের ভাষা, বিদ্রোহের সুর পরিপূর্ণতা পায় না। কারণ মজিদের প্রতারণা, ধর্ম ব্যবসায় ও অর্থ উপার্জনের বিষয়ে সে সচেতন ছিল না। যৌবন ধর্মের চিরায়ত বিকাশ, বয়সের পার্থক্যের কারণে মজিদের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক একটা দূরত্ব থাকবে, এটিই বিশ্বাসযোগ্য। মাজার শরীফে যাওয়ার অস্বীকৃতি তাই যত না মাজার-বিদ্রোহ, তারচেয়ে বেশি একজন উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী বিদ্রোহ প্রকাশের প্রকাশের ভঙ্গি। যৌবন ধর্মের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে সে ছিল শারীরিক ও মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ ও অতৃপ্ত। জমিলার থেকে অনেক বেশি সচেতন বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী বলা যায় রহিমাকে। রহিমা ছিলেন বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে পরিপক্ব। মজিদের প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সে প্রতিবাদ করেছে যখন তাঁর বিশ্বাসের মূলে আঘাত এসেছে। চোখের পর্দা-আবরণ সরে যাওয়ার পর মজিদের অন্যায়ের স্বরূপ অনেকটাই তার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। কথকের নিজের বয়ানে- “এবং যে রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড় সেই যেনো হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।”
লেখক উপন্যাসের লাইনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যাতে কোথাও পাঠকের নিকট কবিতার লাইনের মতো বিভ্রম তৈরি হয়। অর্থাৎ তাঁর গদ্যভাষা কাব্য ভাষার মতো রহস্য, ইমেজ, চিত্রকল্প ও শব্দের কারুকাজে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তিনি কেবল ভাষা তৈরি করেছেন তাই নয়, শব্দ-ভাষা দিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য প্রলম্বিত ছবি এঁকেছেন। ভিটগেনস্টাইন যাকে শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা বলেছিলেন। তাঁর বাক্য বিন্যাস, শব্দের কুহক মায়া অপর দুই উপন্যাসেও আরো বেশি লক্ষ্যণীয়। ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র তুলনায় লালসালু কিছুটা সরল ভাষাভঙ্গিতে রচিত। লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো এই তিনটি উপন্যাসের একটি সরল সাদৃশ্য হলো মানুষের নীচুতা, শঠতা ও গোপন পাপাচার। উপন্যাসগুলোর সূচনায় হয়েছে গোপন পাপাচার ও নৈতিক স্খলন থেকে। আবার তিনটি উপন্যাসেই মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে। প্রলোভনতাড়িত হত্যাকা-, আত্মহত্যা, প্রতিশোধকেন্দ্রিক হত্যাকা- উপন্যাসগুলোতে ঘুরে ফিরে এসেছে, ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। কিন্তু আখ্যানটির সূচনা দরবেশ কাদেরের গোপন প্রণয় সৃষ্ট নৈতিক স্খলন ও ভয় থেকে। গোপন প্রণয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অসতর্কতাবশত সে হত্যাকা-ের মতো জঘন্য কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আখ্যানে দেখা যায় ঘটনা পরম্পরায় যুবক শিক্ষক আরেফ আলী যুগপৎ দ্বিধাগ্রস্ত, অসংলগ্ন ও ভয়কাতর হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য, আশ্রয়চ্যুতি, কৃতজ্ঞতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধের জায়গায় এক বিচিত্র তাকে ঘিরে ধরে। সে ভিতরে-ভিতরে কুকরে ওঠে। সে সর্বান্তকরণে সে নিজেকে বুঝাতে চেয়েছিলা ঘটে যাওয়া সমগ্র ঘটনাই একটি দুর্ঘটনা কিংবা প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়াল মাত্র। কিন্তু নিজের অগোচরে অবচেতনে দৃশ্য পরম্পরা একজন খামখেয়ালি, অমিতাচারী, মুখোশধারী, ঘৃণ্য কামুক ও খুনিকে তাঁর সামনে নিয়ে আসে। বিবেকের তাড়নায় ভাবনা, নিছক কৃতজ্ঞতার মূল্যবোধ ভেঙে সে ভিতর থেকে একজন দৃঢ়চেতা মানুষ হয়ে ওঠে। তার মানে আরেফ আলীর মধ্যে আপাত বুদ্ধিমনস্ক, কৌশলী ও স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা দেখি সে তাঁর পরিণতি সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত থাকলেও কোনো প্রলোভন শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারেনি। ঔপন্যাসিক দৃশ্য পরম্পরা এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যাকে কেউ জাদুবস্তবতা বলে ভুল করতে পারে। কারণ বাঁশঝাড়ে পাতার খসখস শব্দ, হঠাৎ দৃশ্য, মানুষ অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া, কিংবা নির্জন রাতে চাঁদের আলো-ছায়ায় বাতাসে কম্পমান কলাপাতাকে মানুষের আদল ভেবে ভুল করার ভিতর কোনো অলৌকিকতা নেই। এসব কিছু ব্যক্তি মানুষের মনের দুর্বল মুহূর্তের অনুভূতি মাত্র। আবার নদীর বালুচরে কোনোরকমে লাশ পুঁতে রাখলে যে কোনো মুহূর্তে জলের আঘাতে ভেসে যেতে পারে। তার ভিতর কোনো অতিলৌকিক ঘটনা নেই, যা আছে তা হলো ভাষার জাদুকরী বর্ণনা, দৃশ্যের কুহক, দেখা ও কল্পনার বিভ্রম। এখানে লেখক অত্যন্ত সফলভাবে পাঠকের মনোজগতে আশ্চর্য এক কথনভঙ্গির মায়া কুহক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসটি যত না জাদুবাস্তবতার রূপায়ণ, তার চেয়ে বেশি করে মানুষের অন্তর্জগতে প্রতিনিয়ত যে দ্বন্দ্ব চলে তার একটি সরল দৃশ্যভঙ্গির দৃশ্যায়ন। সামন্ততান্ত্রিক জীবন ও ধর্মবোধ, গ্রামীণ আনুগত্যপ্রবণ জীবন প্রবাহ, পরা উন্মুখ সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হয়ে নৈতিক স্খলনের পথে পা বাড়ানো ও নিষিদ্ধ সম্পর্কের সুতীব্র আকর্ষণের কামনা শৈলী। একইসঙ্গে আমরা দেখি ভাতৃস্নেহের কাছে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ন্যয়পরায়ানতা পরাভব স্বীকার করে। যথারীতি উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ও প্রশাসন চিরকাল পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করে চলে। উপন্যাসে আরেফ আলী নিরুত্তেজ প্রায় মেরুদ-হীন একজন মানুষ নামের প্রাণি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সে অটল পৌরুষের পরিচয়কেই বড় করে তোলে। বিস্তৃত গল্প না বলেও লেখক মানুষের আদিম প্রবণতা ও অন্তিম স্বার্থের গতি প্রকৃতিকেই বড় করে তোলে।
‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসটি তুলনামূলকভাবে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। উপন্যাসে যতনা ঘটনার বিস্তার ঘটে তার চেয়ে বেশি মনোজগতের ভিতর তার দ্বান্দ্বিক আলোড়ন। উপন্যাসে মূলত তিনটি স্তরের মাত্রায় আখ্যান কাহিনির বিন্যাস ঘটে। অর্থাৎ একজন কথক আরেকজন কথক তৃতীয় অন্য যে ব্যক্তির কাহিনী বলে যাচ্ছেন, প্রথম কথক তা বিবৃত করছেন। এভাবেই দৃশ্যের উপরিতলের নিচে আত্মমগ্ন কিছু মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা, অন্তর্গত যাতনা, পরাজয়, জীবন দর্শন-দ্বন্দ্ব, মোহ, স্বার্থপরতা-আত্মপরতার মায়া কুহক তৈরি হয়। আখ্যানভাগের শুরুতে দেখা যায় স্টিমারের একজন যাত্রী তবারক ভুঁইয়া একটি জনপদ, কিছু মানুষের অন্তিম পরিণতি, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক-সম্পর্কহীনতা,ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্বের যে সম্পর্ক মাত্রা তার গল্প বলেছেন। মূলত একটি মফস্বল এলাকার সংস্কৃতি, নগরায়ন, মানুষের বৃত্তি, স্বার্থভাবনা, সহজাত প্রবৃত্তি, অবকাশ যাপনের পদ্ধতি, পরচর্চা, রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নের আড়ালে নিজস্ব প্রতিষ্ঠার খেলা-কৌশল উপন্যাসের শিল্প ভাষ্যে ফুটে ওঠে। একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব কমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে অধিবাসীদের মধ্যে অন্তর্গত বিরহ তৈরি হয়। কথকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের সামনে যে ভাষা উপস্থাপন করেন তাতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। অর্থাৎ তিনটি কালখ- একটি কালপর্বে বর্ণনা হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’, ‘মুখের দিকে দেখি’ উপন্যাসে দৃশ্যমান। বিশ্বসাহিত্যে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেকের কথাসাহিত্যে এ ধরনের ভাষা বিন্যাসের দেখা মেলে। জেমস জয়েসের ইউলিসিসকেও এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। অবশ্য ইউলিসিসে শুধু শুধুমাত্র একইসঙ্গে একাধিক কথক নয়, তার মূল বৈশিষ্ট্য কালের সীমারেখা ভেঙে দিয়ে একটি স্থির সময়ের ফ্রেমে অতীতের ঘটনা বলে যাওয়া। একটি মুহূর্তের ভিতর পুরো একটি সভ্যতার গল্প-ঘটনা বিবৃত হয়।
উপরোক্ত প্রবণতা ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। সবকিছু অতিক্রম করে আখ্যানের কেন্দ্রে আছে কুমারডাঙ্গার মুহাম্মদ মুস্তাফা, যিনি তরুণ বিচারক ও তাঁর ফুফাতো বোন খাদিজা। প্রেক্ষাপটের অতীতে দেখা যায় মুহাম্মদ মুস্তাফা একজন পিতৃহীন মানুষ। তার পিতা খেদমুতুল্লা একজন শঠ ও গ্রাম্য টাউট শ্রেণির মানুষ। প্রতারণা, গ্রাম্য দলাদলি ও আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া তার নেশা ও পেশার অংশ হয়ে ওঠে। রেষারেষির কারণে কেউ একজন তাকে গোপনে খুন করে। এই ঘটনা বালক মুস্তাফার জীবনে গভীর অভিঘাত তৈরি করে। কৈশোর ও তারুণ্যের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস হারিয়ে সে হয়ে ওঠে অন্তর্মুখী ও বিষাদগ্রস্ত। অন্যদিকে পিতৃহারা খাদিজাকে নিয়ে তার মা মুস্তাফাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পারিবারিক ভাবে মুস্তাফার সঙ্গে খাদিজার বিয়ের কথা অনেকটাই চূড়ান্ত হয়। অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও মুস্তাফার মা ও খাদিজার মা এরকম সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে। এটি এক কান দুই কান করে একদিন খাদিজার কানেও ওঠে। আর তখন থেকেই খাদিজা মুহাম্মদ মস্তাফাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে। বিষয়টিকে মুহাম্মদ মুস্তাফা আক্ষরিক অর্থে কিংবা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খাদিজা একটি সম্ভাবনার। বীজ কিংবা স্বপ্ন ধীরে-ধীরে নিজের ভিতর লালন করতে থাকে। খাদিজা খুব সন্তর্পণে নিজের সেবা, ভালোবাসা দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মুহাম্মদ মুস্তাফার সমান্তরালে প্রতিস্থাপন করে। নিজের ভিতর ডুবে থাকা মুহাম্মদ মুস্তাফা কখনই খাদিজার মনের গহীন তলকে অনুভব করতে পারেনি। এমন নয় যে, সে খাদিজাকে সচেতন ভাবে অবহেলা করেছিল। অসচেতনতা ও খাদিজার প্রতি অমনোযোগ হেতু মুহাম্মদ মুস্তাফা অন্যত্র বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুহাম্মদ মুস্তাফার অন্যত্র বিয়ে করার সংবাদ শুনে খাদিজা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে।
এই সামান্য মৃত্যু দৃশ্যই উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। খাদিজা আত্মহত্যা করেছে নাকি পুকুরে ডুবে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে? এই বিষয়টি বুঝতে পাঠকের দীর্ঘ সময় লেগে যায়। পুকুরের কালো জলের উপর কচুরিপানার আবরণ সবুজ শ্যাওলার পিচ্ছিলতার মতো সৈয়দ শব্দ-দৃশ্য ও ভাষা বর্ণনার অর্থ যেনো নারকেল পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলতে সিদ্ধহস্ত। পাঠক ভাষা, শব্দ-ব্যাঞ্জনা, ছবি দৃশ্য ও বর্ণনার বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যায়। ভাষার সেই লুকোচুরি, শব্দ ও বাক্যের প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে দৃশ্যের বর্ণনা পাঠকের গভীর মনোনিবেশ দাবি করে। কিংবা খেদমুতুল্লা গোপন আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার দৃশ্য, কথক এমন এক নির্বিকার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন যেখানে মৃত্যু দৃশ্য ভাষার বর্ণনার কাছে ফিকে হয়ে যায়। আবার খাদিজার আত্মহত্যার প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদ মুস্তাফার স্বেচ্ছামৃত্যুকে মাছের বরফ চোখের প্রতিকী ব্যঞ্জনা দিয়ে পাঠকের শিরায়-শিরায় শীতল অনুভূতি প্রবাহিত করে দেন। পাঠকের ভিতর এক ধরনের নির্লিপ্ত কিন্তু মর্মভেদী আবহ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্টিমার ঘাট সরে যাওয়ার একটি জনপদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কমে যাওয়ার অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া লেখক চিহ্নিত করেছেন। সেই চিহ্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনায় উচ্চকিত ভাষা ব্যবহার না করে একধরনের নির্লিপ্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। পাঠক এমন এক ঘোরের মধ্যে আটকে যায় যে, আচ্ছন্ন শব্দ ও ভাষা তাকে গ্রাস করে।
উপন্যাসের দৃশ্য পরম্পরা, মনের গোপন ভাবনা, লোক বিশ্বাস, অতিলৌকিক বিশ্বাস, ঘাত-প্রতিঘাত সংঘাত, গ্রাম ও শহরের জীবন প্রবাহের ভিতর লেখক একটি আধিভৌতিক মিথ তৈরি করেন। সেখানে সবাই কোথাও হতে দূরস্থিত কান্নার ধ্বনি শুনতে পায়। প্রথম এই কান্না শুনতে পায় আটপৌরে স্কুল মিস্ট্রেস। ব্যক্তি জীবনের অপ্রাপ্তি, আকাক্সক্ষার অপূর্ণতা ও স্বপ্নভঙ্গের দীর্ঘশ্বাসই হয়তো স্কুল মিস্ট্রেসের নিজের অবচেতনে একটি গোপন কান্নার ¯্রােত তৈরি করে। সেই দীর্ঘশ্বাসই তার ভীতর যাতনা ও নদীর অন্তর্গত ঢেউ ¯্রােত তৈরি করে। ব্যক্তির বেদনাবহ অনুভূতি কান্না, অন্তঃসলিলা ¯্রােতে রূপান্তর হয়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে অন্যত্র। প্রথম পর্যায়ে অনাবিষ্কৃত কান্নার ধ্বনি স্কুল মিস্ট্রেসের একার হলেও পরে তা সমষ্টির ভিতর সংক্রামিত হয়। অর্থাৎ সেই জনপদের সবাই একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অতি লৌকিক আবহের দোলাচলে দোল খায়। স্কুল মিস্ট্রেসের শোনা সেই কান্নার ধ্বনি মুহাম্মদ মুস্তাফা, উকিল কফিল উদ্দিন, ডাক্তার বোরহানউদ্দিন, বৃদ্ধ কালু শেখ, স্টিমারঘাটের কেরানি খাদেম ও সাইকেল মেকানিকের স্ত্রী সবার জীবন একটা বিভ্রম ও ভীতির ঘুরপাকের ভিতর ঠেলে দেয়। এই যে সবাই রহস্যময় ক্ষীণ কান্না শুনতে পায়, তা ক্ষয়ে যাওয়া নদীর দুঃখ, একটি জনপদের দুঃখ ও ব্যক্তি মানুষের দুঃখ একটি বিন্দুতে এসে মিলে যায়। লেখক যেনো বলতে চেয়েছেন সব মানুষের ভিতর একটি গোপন নদী বয়ে চলে, কেউ তা টের পায়, কেউ পায় না। নদীই মানুষের গোপন কান্নার বিশ্বস্ত সঙ্গী। ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাস্তব- অতিলৌকিক বিশ্বাস ও জাদুবস্তবের আশ্চর্য বয়ান।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসগুলোর মধ্যে শিল্প বিচারে কাঁদো নদী কাঁদো নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি সবসময় একটি সমীহ দাবি করবে। তবে যে কথাটি বলতে হয় ‘লালসালু’ উপন্যাস যতটা বাস্তব ও জীবনঘনিষ্ঠ কাঁদো নদী কাঁদো ততটা নয়। কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসে স্কুল মিস্ট্রেস এর শোনা ক্রন্দন ধ্বনি মূলত নদীর বয়ে চলা জোয়ার ভাটা, জলের নিক্বণ ধ্বনি, নদী তীরবর্তী মানুষের অন্তর্গত জীবন প্রবাহের ধ্বনি। মানুষের আপাত সুখী, কিন্তু ভিতরে খুব গোপনে যে ব্যাথার সুর বাজে, লেখক তাঁর বিমূর্ত ভাষাচিত্র এঁকেছেন। কাঁদো নদী উপন্যাসের চরিত্রগুলো অন্তর্জগতের বাসিন্দা। চাঁদের অমাবস্যায় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও সামন্ত মানসিকতার গল্প প্রবাহ সৃষ্টি হয়। মূলত তিনটি উপন্যাসেই লাইনে-লাইনে ভাষা, ইমেজ-চিত্রকল্পের ব্যবহার কবিতার সাদৃশ্য তৈরি করে।
-
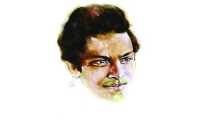
প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল
-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান
-
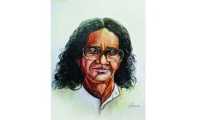
মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-
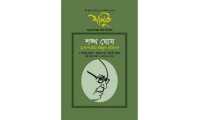
শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন
-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প
-

কল্পগল্প
-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’
-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
-
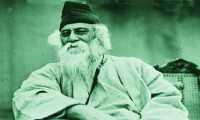
আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে