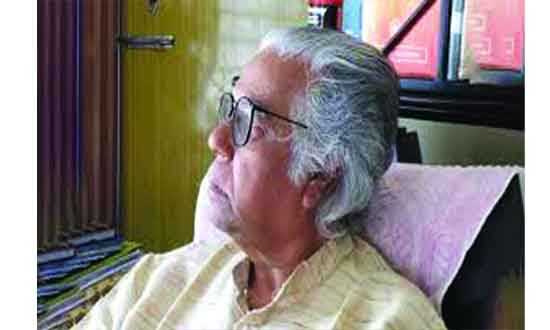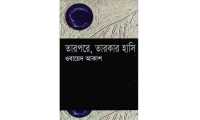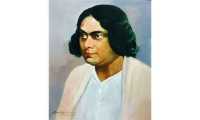সাময়িকী
আবুবকর সিদ্দিকের ছোট গল্পে রাজনীতি
মামুন মুস্তাফা
আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৪-২০২৩)
বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে কবি হিশেবে সমধিক পরিচিতি পেলেও তাঁর ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আঙিনাকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। আবুবকর সিদ্দিক নিজস্ব গদ্যভাষা তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিজের অপ্রতিরোধ্য আসনটি স্বতন্ত্র স্বাক্ষরে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারও আগে ষাটের দশকে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বাধীকার আন্দোলনে বামরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গণসংগীত রচনা করে গণমানুষের কাতারে নিজেকে শামিল করেছেন নির্দ্বিধায়। আবুবকর সিদ্দিক পিতার কর্মসূত্রে তাঁর শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ সময় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও বর্ধমান শহরে। এই সময় থেকেই তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি। আর আজীবন বামাদর্শে উজ্জীবিত এই লেখকের রাজনীতি সম্পৃক্ততাও তখন থেকেই।
ফলে বামঘরানার রাজনীতি সচেতন লেখক আবুবকর সিদ্দিকের ছোটগল্পে বামাদর্শে দীক্ষিত রাজনৈতিক জীবনদর্শনের ইতি ও নেতিবাচক নানাদিক প্রতিফলিত হতে দেখি। বিশেষ ভাবে গল্পগ্রন্থ ‘ভূমিহীন দেশ’ (১৯৮৫), ‘মরে বাঁচার স্বাধীনতা’ (১৯৮৭) এবং ‘মুক্তিলাল অভ্যুদয়ে’ (২০০৮) সেই ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও ‘ছায়াপ্রধান অঘ্রান’ (২০০০), ‘কান্নাদাসী’ (২০০৬) ও ‘বামাবর্ত’ (২০০৭)-এর বেশকিছু গল্পে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে কমরেড কবি আবুবকর সিদ্দিকের বামরাজনীতির আদর্শিক চলভাষ, ক্ষয়-পতন উঠে এসেছে। তবে ‘মরে বাঁচার স্বাধীনতা’ ও ‘মুক্তিলাল অভ্যুদয়’ গল্পগ্রন্থ দুটিতে সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গল্পগুলো স্থান পাওয়ায় এই গল্পগুলোতে বামাদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রত্যক্ষতাও লক্ষ করেন।
এমনকি ‘মরে বাঁচার স্বাধীনতা’র ‘লাশের নাম নেই’ গল্পটিতে আমরা লেখকের নিজের জীবনের ছায়া পরিলক্ষিত হতে দেখি। এই গল্পের প্রধান চরিত্র আসাদ লেখকের চরিত্রের আদলেই গড়া। আবুবকর সিদ্দিক নিজেই গণসংগীত লিখেছেন। খুলনার সন্দীপন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর গণসংগীত বাজানো হতো। সেই বিষয়গুলো গল্পে রূপলাভ করেছে। এবং এর জন্য যে, কবিকে রাজাকারদের দ্বারা নির্যাতিত হতে হয়েছিল, তাঁর ডান হাত পেছন দিকে নিয়ে মুচড়ে দিয়েছিল- সেই বিষয়গুলো এই গল্পের মূল রসদ। যদিও গল্পে প্রধান চরিত্রটির মৃত্যু ঘটেছে। একইসঙ্গে এই গল্পে যে শুকনো কালো লম্বা কুঁজো পার্টি কমরেডকে দেখানো হয়েছে, তিনি আসলে সন্দীপন গোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারী খুলনা গার্লস কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক খালেদ রশীদ ওরফে গুরু। তিনি হক-তোয়াহার এমএল-এ দল করতেন। একাত্তরে খুলনার ডুমুরিয়ার গেরিলাযুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার সময় খানসেনাদের হাতে শহীদ হন।
‘মরে বাঁচার স্বাধীনতা’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘খতম’ গল্পের দীনেশ এমএল পার্টির সক্রিয় কমরেড ছিল। তাছাড়া ‘এই সেই জয়বাংলা’ গল্পে মুক্তিযোদ্ধা-কমান্ডার কমরেড রফিকুল ইসলাম স্বয়ং আবুবকর সিদ্দিকের ছাত্র এবং তাঁর কাছেই বামরাজনীতির দীক্ষা নিয়েছিল। ‘মরে বাঁচার স্বাধীনতা’ গ্রন্থের শিরোনামের গল্পসহ ‘ফজরালি হেঁটে যায়’, ‘রক্তগর্জন’ কিংবা ‘খোঁড়া সমাজ’ গল্পগুলোতেও স্বাধীনতাযুদ্ধ নামক জনযুদ্ধের রাজনীতির সঙ্গে বামরাজনীতির আদর্শগত অবস্থান ও স্খলন- উভয়ই আলোকপাত করেছেন লেখক। আবার ‘মুক্তিলাল অভ্যুদয়’ গ্রন্থের ‘জাল যোদ্ধা’ গল্পে হাসান মওলা একজন বামরাজনীতিক। যে কিনা স্বাধীনতাউত্তর সময়ের মওকা লুটে নিতে বামরাজনীতির আদর্শ বিক্রি করে ভেক ও চোট্টা মুক্তিযোদ্ধা সেজে অবৈধ উপায়ে কেষ্টবিষ্টু বনে যায়। মূলত হাসান মওলা স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের বামরাজনীতির আদর্শিক পতনের প্রতীক মাত্র। এরকম ভাবে ব্রাত্যজনের অমলিন কথাকার আবুবকর সিদ্দিক তাঁর গল্পগুলোতে অনেক পোড়খাওয়া বামরাজনীতিকের জীবনছবি এঁকেছেন।
অন্যদিকে এক ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে আবুবকর সিদ্দিকের গল্পগ্রন্থ ‘ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ’। এই গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোর মানুষেরা অর্থনীতি ও রাজনীতির সার্বক্ষণিক পাকচক্রের সঙ্গে মোকাবেলারত এবং আপাত গৎবাঁধা একঘেয়ে তাদের জীবনচরিত; কিন্তু অবচেতন সত্তায় তারা ডাইন্যামিক। সেই দোধারী চেহারা গনগণে হয়ে ওঠে আবুবকর সিদ্দিকের শক্তিশালী কলমে। শক্তিমান কলমের স্পর্শে তার শিল্পরূপ নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। ‘ছায়াপ্রধান অঘ্রান’-এর গল্পগুলো সেই প্রত্যয়কে বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। আদি ও অন্ত্যে মূলত মানুষ; তার ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তা, তার অস্তিত্ব ও অবস্থান, উত্থান-পতন-পুনরুজ্জীবনের সাধনা ও দ্বন্দ্বদীর্ণতা;- এ রকম অজস্র গ্রন্থিউপগ্রন্থি জেগে থাকা গভীর সড়কে বিচরণ করে লেখকের রাজনীতি সচেতন আনুবীক্ষণিক কলম।
আবুবকর সিদ্দিক তাঁর গল্পের ক্যানভাসে মানুষের বিশ্বভূগোল পরিব্যাপ্ত করেন দেশ, মাটি, শেকড়ের ঐতিহ্যে। ফলে তাঁর গল্পের ক্যানভাস যে বিশালত্ব ধারণ করে, সেখানে জায়গা করে নেয়- মুক্তিযুদ্ধ বনাম নকশালপন্থী বাম রাজনীতির টানাপোড়েন ও ভ- মুক্তিযোদ্ধার স্যাবোটাজ; অশিক্ষিত সমাজে লম্পট রাজনীতিকদের খপ্পড়ে তথাকথিত গণতন্ত্রের বিকলাংগ দশা; ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজ মৌলবাদীর র্দোরা কেটে বসা বাংলার অসহায় নারীদেহ; সুন্দরবনের আদিম অরণ্য গহনে নোনা মেয়েমাংসের গন্ধসন্ধানে ঘুরপাক খাওয়া শহরের আধুনিক কর্মজীবী; থাকে এক সামন্তবিলাস গ্রামবাংলার নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। ‘ছায়াপ্রধান অঘ্রান’-এর গল্পগুলোতে এসব কিছুর সমকালীনতার ঝাঁঝ উত্তীর্ণ হওয়ার শিল্পমেধা পুরোমাত্রায় লক্ষ করা যায়। ‘বাইচ’, ‘গোনোসুন্দরী’, ‘ছায়াপ্রধান অঘ্রান’ ইত্যাদি গল্পগুলো তারই উদাহরণ।
এ দেশের বহুধা জটিল ও স্তরে স্তরে দ্বন্দ্বমান ঘটনাবহুল জীবনযাপনকে বিষয় করে গড়ে উঠেছে লেখকের ‘কান্নাদাসী’ গল্পগ্রন্থটি। বলা আবশ্যক, ‘কান্নাদাসী’র গল্পগুলো আবুবকর সিদ্দিকের লেখক হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বে লেখা। অথচ তাঁর এই উত্তরণপর্বের গল্পগুলোতেও ক্ষমতাহীন দলিত, প্রান্তিক, উপেক্ষিত, শোষিত, নিপীড়িত, ব্রাত্য, প্রাকৃত জনগোষ্ঠী স্থান করে নিয়েছিল। এ গ্রন্থের ‘বাপান্ত’ গল্পের নায়ক মন্তাজ সামন্ত শ্রেণির শোষণের শিকার। যে সময়কাল আমরা এই গল্পের ভেতরে দেখি, সে এক ভেঙে পড়া কলোনি-শাসনের উত্তরাধিকার। সেই সমাজব্যবস্থায় একজন চেয়ারম্যানের ভূমিকা ও দৌরাত্ম্যও অনেক। মন্তাজকে চেয়ারম্যানবাড়ির যে ঝি’র সঙ্গে বিয়ের প্রস্তুতি নেন স্বয়ং চেয়ারম্যান এবং তার বেগম, সে-ই ঝিও সামন্তপ্রভুর (চেয়ারম্যান) নেশার শিকার। আবুবকর সিদ্দিক স্যাটায়ার ও রাজনীতিকে বিষয় করে নিরীক্ষাধর্মী গদ্যরীতি প্রবর্তন করেছেন। বলা যায় ‘বাপান্ত’ গল্পটি তাঁর সেই নিরীক্ষার প্রথম সময়কালের ফসল। আর এই গল্পের চেয়ারম্যান সেই সামন্ত শ্রেণির জ্বলন্ত উদাহরণ।
‘কান্নাদাসী’ গ্রন্থের ‘দিগম্বরী ছায়া’ গল্পে আমরা আইয়ুব শাসনামলের কিছুটা আভাস দেখতে পাই। গর্ভনর মোনেম খাঁর চাটুকারিতাও বুঝা যায় গল্পের নায়ক রহমের বৃদ্ধ পিতার ছোটো একটি উক্তির ভেতরে। এই গল্পের নায়ক রহম সিনেমা হলের টিকেট বিক্রেতা। গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলোও লেখকের ভাষায় ‘আধামধ্যবিত্ত’। ফলে এরা ছোটো মফস্বল শহর বাগেরহাট আর অন্যদিকে দড়াটানার ওই পাড়ে যে গ্রামে তাদের বসবাস, সেই বৈটপুরের বৈপ্যরীতের মাঝে পরিবেশ, প্রতিবেশ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রগতি, এমনকি বিকৃতি- সবকিছুই অধ্যয়ন করে। আর তাই নকশাল দমনের সেই আইয়ুবি শাসনের আমলেও ভিলেজ পলিটিক্সের (মূলত চেয়ারম্যানি ক্ষমতার লড়াই) দ্বন্দ্বে মহব্বত আলী যখন নিজ মুখে রহমকে নজিমুদ্দিরে খুন করার খবর জানায়, তখন রহম অকস্মাৎ ভূত দেখার মতো ভয়ে আতঙ্কিত হয় এবং নিজেকে আবিষ্কার করে এক মনোবিকলনগ্রস্ত, নিমজ্জিত সমষ্টি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের আধারে। গল্পের শুরুতে লেখক ‘পথ বটে’ বলে যে সূচনা করেন, সেই গ্রামের, শহর বা শহরতলির চৌচির পথে উদ্ভাসিত চোরা লণ্ঠনের আলোয় রহম এখন নিজেকে অন্য ভাবে খুঁজে ফেরে। রহম নিজেই যেন জীবন বিচ্ছিন্ন বা জীবনের সঙ্গে যুক্ত নিঃসঙ্গ-বেদনার্ত, সরল-জটিল, সুখ-অসুখ, ঘৃণা-ভালোবাসার প্রক্ষেপণ। সুতরাং এই গল্পের পরিণতিতে লেখক ব্যক্তিমানুষের মনস্তত্ত্ব ও নিয়তির ধারণা থেকে জীবনের উদ্ভাসের দিকে এগোন।
‘কান্নাদাসী’ গল্পগ্রন্থের যে গল্পগুলো কথাসাহিত্যিক আবুবকর সিদ্দিককে একটু আলাদা করে চিনিয়ে দিতে সক্ষম, ‘নীল আসমান : লালসবুজ’ সেরকমই একটি রাজনৈতিক গল্প। যে নি¤œবর্গের কথা বলেন কথক, তারা সবসময়ই অতিক্রম করে তার দুঃসময়কে। এ গল্পের জিতেন মাস্টার নি¤œ-মধ্যবিত্তের অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠের একজন... সাব-অল্টার্ন সমাজেরই প্রতিভু। লেখক নিজে বামাদর্শে উজ্জীবিত বিধায় বাম রাজনৈতিক দৃষ্টির ভেতরে জীবনকে পাঠ করেন তিনি। সেখান থেকে যে গভীর অভিজ্ঞতা ও শাঁস তুলে আনেন লেখক, তা যেমন বাস্তবনিষ্ঠ, তেমনি অকৃত্রিম। ‘নীল আসমান: লালসবুজ’ গল্পের জিতেন মাস্টার মূলত সেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা। এ গল্পে লেখক সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির বাস্তব সমস্যার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেই শিল্পের দাবি মিটিয়ে দেন পূর্ণ মাত্রায়।
আর ‘বামাবর্ত’ গল্পগ্রন্থের ‘জীবনমৃত্যুর করাতের দাঁতের উপর দিয়ে’ এবং ‘একটি অমানবিক উৎসব’ গল্প দুটি একাত্তরের যুদ্ধদিনে লেখকের নিজের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনার চালচিত্র। ‘জীবনমৃত্যুর করাতের দাঁতের উপর দিয়ে’ গল্পে ১৯৭১-এর ২৩ আগস্টে রফিকবাহিনী ও খানসেনাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের ভেতরে লেখক খানসেনাদের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে দিয়ে সাড়ে চার মাইল খোয়ারাস্তা রিকশা ঠেলে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। ওই রিকশায় আহত খানসেনাকে বহন করা হচ্ছিল। রিকশাচালক তার গ্রামের পরিচিত রাজাকার মুরাদ ছিল। তার সহযোগিতায় তিনি প্রাণে বাঁচেন। অন্যদিকে ‘একটি অমানবিক উৎসব’ গল্পটিকে লেখক স্বয়ং একটি ‘নির্জলা সত্য ডকুমেন্টেশন’ বলে অভিহিত করেছেন। একাত্তর সালে আবুবকর সিদ্দিকের পিতৃবন্ধু জমিদার হরিশচন্দ্রগুহসহ অনেক সংখ্যালঘু নাগরিক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দড়াটানা নদী পেরিয়ে বাগেরহাট শহরের বাসাবাটির অধিবাসী এক মওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে পারহেড দশ টাকা ফি বাবদ কলেমা পড়ে পুরুষাঙ্গের মাথা কাটিয়ে খাৎনা দিয়ে নওমুসলিম হয়ে আসে। তাদেরই গরু জবাই করে খানাপিনার আয়োজন করে ওয়াজ মাহফিল বসিয়ে অমানবিক উৎসবের আয়োজন করেছিল গ্রামের কিছু প্রভাবশালী পরহেজগার মুসলমান। তবে এই ভোজসভার আগেই এক রাতে রাজাকাররা গ্রামে ঢুকে জমিদার হরিশচন্দ্র গুহসহ কয়েক ঘর হিন্দু গেরস্থকে রাস্তার উপর শুইয়ে জবাই করে রেখে যায়। এই সব ভীভৎস দুঃসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি উক্ত দুটি গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে।
শেষ করবো আবুবকর সিদ্দিকের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘ভূমিহীন দেশ’ (১৯৮৫)-এর প্রসঙ্গ টেনে। মূলত বুর্জোয়া শাসন ও শোষণে নিপীড়িত ও নির্যাতিত গণমানুষের শেষ সম্বল ‘ভোট’টুকুও কীভাবে ছিনতাই হয়ে যায়- সেই রাজনীতির দশাশই চেহারা উন্মোচিত করেছেন লেখক এর গল্পসমূহে। নিঃস্ব মানুষের নসিবের কোনো রদবদল হয় না। প্রতারণার মার খেয়ে খেয়ে আরও অন্ধকার গুহায় সেঁধিয়ে যায় তাদের জীবন। এই গ্রন্থের গল্পগুলো আদতে স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের হলুদ রাজনীতির কবলে পড়ে ভাগ্যতাড়িত জনজীবনের মোহভঙ্গের অবিকল বৃত্তান্ত। ‘ভূমিহীন দেশ’, ‘খালখসা লাল কংকাল’, ‘খাদ্যমন্ত্রণালয় কত দূরে’, ‘চন্দনের ঘুণ’ ইত্যাদি গল্পগুলো সেই সারবত্তা বহন করে।
বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ভাষা, চরিত্র এবং এর বিষয়-প্রকরণ নিয়ে যে অল্প কয়েকজন কথাসাহিত্যিক নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তাঁদেরই অন্যতম কথাকার আবুবকর সিদ্দিক। বিরলপ্রজ অথচ সময়ের চিহ্ন স্বাক্ষরিত ঋদ্ধ কথাসাহিত্যের অনন্য রূপকার আবুবকর সিদ্দিক তাঁর নিরীক্ষার শেকড় প্রোথিত করেছেন প্রধানত দলিত ব্রাত্যজনকে নিয়ে। সেই সাবল্টার্ন সমাজের এক নতুন প্রকাশ দেখতে পাই আবুবকর সিদ্দিকের ছোটগল্পে। তাঁর গল্পের মানুষগুলো সবসময়েই অর্থনীতি ও রাজনীতির পাকচক্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ফলে এদেরকে আপাতদৃষ্টিতে গৎবাঁধা একঘেয়ে মনে হলেও, অবচেতন সত্তায় এরা সকলেই ডাইন্যামিক। আবুবকর সিদ্দিকের গল্প-উপন্যাস তাৎক্ষণিক পঠনসুখ যুগিয়ে হারিয়ে ফুরিয়ে যাবার জন্যে আসেনি। সুতরাং এ কথা আজ স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আবুবকর সিদ্দিক অভাজন মানুষের ক্ষয়-পতন, প্রেম ও উত্তরণের কথাকার।
-
সাময়িকী কবিতা
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-
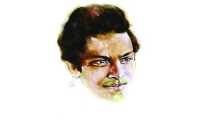
প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল
-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান
-
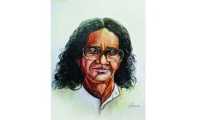
মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-
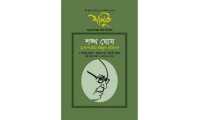
শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন
-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প
-

কল্পগল্প
-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’
-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস
-
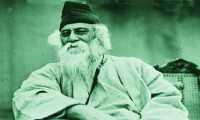
আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার
-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস
-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি
-
শ্রাবণ বর্ষণে
-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’
-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে