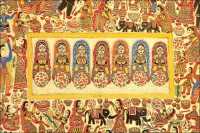উপ-সম্পাদকীয়
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে কীভাবে
এসএম জাহাঙ্গীর আলম
মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যে সাড়ে ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং বর্তমানে এ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।
বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো অর্থের জোগান বৃদ্ধি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে দেশে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৪৫ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৯,৩১৫ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সাল নাগাদ অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭,হাজার ১৩৬ কোটি টাকা। সুতরাং অর্থের যোগানের ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।
মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো উৎপাদন হ্রাস। বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া শিল্পের কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতির অভাব ও সুষ্ঠু শিল্পনীতির অভাবে দেশে উৎপাদন বিশেষ করে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। বস্তুত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে-দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতির মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
স্বাধীনতা লাভের পর দেশের যুদ্ধবিদ্ধস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান যথেষ্ট উদার করা হয়। ফলে দেশের ব্যাংক ঋরে পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ১,হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৬,৮৬৯ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সাল নাগাদ মোট ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৯৪ হাজার ২২২ কোটি টাকা। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ব্যাপক ঋণদানের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিভিন্ন খাতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ তীব্রতর হচ্ছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন বাংলদেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। দেশে চাহিদার তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হওয়ায় খাদ্যশস্যের মূল্য এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশে সার্বিক মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়।
অবমূল্যায়নের ফলে টাকার বাহ্যিক মূল্য হ্রাস পায়। এর ফলে আমাদনিকৃত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় এবং দেশের অভ্যন্তরে মূদ্রাস্ফীতি ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর বহুবার ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে টাকা ডলারের গড় বিনিময় হার ছিল ১ ডলারের বিপরীতে ৭.৩০ টাকা। ২০১১-১২ সালে টাকা ও ডলারের গড় বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলারের বিপরীতে ৭৮.১৮ টাকা। বর্তমান বাংলাদেশি টাকায় ডলারের বিনিময় হার হল ৮০.০০ টাকারও বেশি। টাকার অবমূল্যায়ন বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে সরকারকে বিভিন্ন সময়ে গ্যাস, তেল ও বিদ্যুতের মূল্য বাড়াতে হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক পণ্য ব্যাপক হারে রপ্তানি করা হয়। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং এসব দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায়।
সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধির ফলে আমদানি খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশে^র বাজারে পেট্রোলিয়াম, গম, ভোজ্যতৈল, সার, সিমেন্ট ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির দরুন বাংলাদেশে এসব আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, যেমন- শিল্পের কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, কাগজ ও নিউজ প্রিন্ট এবং পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের সরবরাহ মূল্যবৃদ্ধির দরূন উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো আমদানি নীতি। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতার জন্য বাংলাদেশে বিদেশ হতে পণ্য সামগ্রীর আমদানির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিলাসজাত দ্রব্য এবং কিছু কিছু ভোগ্যপণ্য আমদানির ওপর উচ্চহারে শুল্ক ও কর ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছুসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। মজুতদার, কালোবাজারি, মুনাফাখোর, চোরাচালানি প্রভৃতি অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশের অভ্যন্তরে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ফলে দ্রব্য মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেটের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে পরোক্ষ কর হতে। বাণিজ্য শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর প্রভৃতি পরোক্ষ কর ধার্যের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ তীব্রতর হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো সুষ্ঠু পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার দরুন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দ্রুত পণ্যসামগ্রী স্থানান্তরিত করা যায় না। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
স্বাধীনতার পর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির দরুন বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘ বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। স্বাধীনতার পর কয়েক দফা সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারি ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পায়। ২০১০ সালের গোড়ার দিকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে অনুপাতে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ে নি। এ কারণে বেতন বৃদ্ধির ফলে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অনুন্নয়ন ও অনুৎপাদনশীল খাতে অধিক ব্যয়। বিগত কয়েক বছরে দেশে স্টেডিয়াম, শিশুপার্ক নির্মাণ প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে যথেষ্ট ব্যয় করা হয়। কিন্তু এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির গতি তীব্রতর হয়েছে। এসব কারণে স্বাধীনতা লাভের পর দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- (ক) আর্থিক ব্যবস্থা, (খ) রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।
আর্থিক ব্যবস্থা :
মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণই হলো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে হলে অর্থের পরিমাণ কমাতে হবে। এ অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণও কমাতে হবে। কারণ, বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের সাহায্যে বহু লেনদেন হয়ে থাকে। এ ঋণের পরিমাণ কমাতে পারলে মোট প্রচলিত অর্থের পরিমাণ কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে তার মধ্যে নিম্নœলিখিতগুলো প্রধান: ব্যাংক হার বৃদ্ধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বানিজ্যিক ব্যাংককে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়ালে বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের সুদের হার সাধারণত বাড়িয়ে দেয়। ফলে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে এবং ঋনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ কমাতে চেষ্টা করে। এরূপভাবে ঋণপত্র বিক্রয় করলে ক্রেতাগণ তাদের নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর চেক কেটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা মিটিয়ে তাকে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকের রিজার্ভের হার পরিবর্তন, নৈতিক চাপ প্রয়োগ, প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি দূর করার চেষ্টা করে। তবে যাই হউক, মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে যা যা করনীয় তা করা প্রয়োজন।
[লেখক : সাবেক কর কমিশনার]
-
জামাই মেলা : উৎসব, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রঙিন চিত্রপট
-
হারিয়ে যাওয়া ক্লাস, কঠোর মূল্যায়ন আর প্রশ্নের জটিলতায় নুয়ে পড়া এক প্রজন্ম
-
বৈষম্য দূর করে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলুন
-
চিকিৎসা যেন বাণিজ্যের হাতিয়ারে পরিণত না হয়
-
পথশিশু ও বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির ব্যর্থতা
-
মেগা প্রকল্প : প্রশ্ন হওয়া উচিত স্বচ্ছতা নিয়ে
-
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি
-
স্মার্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : উপগ্রহ চিত্র ও ওয়েবসাইটের অপরিহার্যতা
-
ক্ষমতা ও জনপ্রশাসন : আমলাতন্ত্রের ছায়াতলে আমজনতা
-
জনসংখ্যা : সম্পদ না সংকট?
-
ব্রিকসে নতুন ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান
-
রম্যগদ্য : ‘ল্যাংড়া-লুলা, আতুড়-পাতুড়’
-
আষাঢ়ী পূর্ণিমা : আত্মশুদ্ধির সাধনায় বুদ্ধের অনন্ত আলো
-
বদলে যাওয়া মাটিতে সাহসী বীজ : জলবায়ুর বিপরীতে বাংলাদেশের কৃষির অভিযোজনগাথা
-

জুলাই অভ্যুত্থান-গাথা : ‘শিকলে নাহি দিব ধরা’
-
প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন
-
গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
-
টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি
-
রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা
-
রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...
-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক
-
জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা
-
টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং
-
ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়
-
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট
-
আসামি এখন নির্বাচন কমিশন
-
কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?
-
এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?