উপ-সম্পাদকীয়
শেষ আফ্রিকান টিক ওক গাছটি কি মারা গেছে?
পাভেল পার্থ
প্রাণজগতে শোক কিংবা সুখ সকলি স্মৃতি-বিস্মৃতির পাঠ। সেই তিন লাখ থেকে তিরিশ হাজার বছর ধরে প্রজাতি হিসেবে মানুষ স্মৃতি আঁকড়ে বা মুছে বড় হয়েছে। বিবর্তনের দীর্ঘধারায় সকল মানুষের সমাজই শোকবিহবল হয়েছে। ইরেকটাস, ডেনিসোভান, ফ্লোরিয়েনসিস, নিয়ানডার্থাল কিংবা আজকের এই স্যাপিয়েন্স আমরা সকলেই অগণিত শোকের স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছি। শুধু কী মানুষ; শামুক, মৌমাছি, বনরুই, তরুলতা কিংবা তিমিরও আছে শোক-দিনলিপি। মানুষ কত কী কারণে শোককাতর হয়, তবে সব শোকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কোনো না কোনো স্মৃতি। চলতি আলাপখানিও এক গাছের স্মৃতিকে ঘিরে শোকগাথা। গাছটির জন্ম বা নিবাস এই ভূগোলে নয়। প্রাকৃতিকভাবে এর বিস্তারও ঘটেনি বাংলাদেশে।
কিন্তু দীর্ঘসময় এই গাছ বনের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল একা। গড়ে তুলেছিল কত কল্পকথা কী স্মৃতিভান্ড। ‘আফ্রিকান টিক ওক’ নামের এই গাছ টিকে ছিল লাউয়াছড়া বনে। বনবিভাগের সূত্র উল্লেখ করে সম্প্রতি গণমাধ্যম জানাচ্ছে শেষ গাছটিও মরে গেছে। জানামতে, লাউয়াছড়া বনে গাছ ছিল দুটি। ২০০৬ সনের ঝড়ে অন্যটি মরে যায়। সদ্যপ্রয়াত এই গাছটির সঙ্গে আমার কিশোর ও তরুণ বয়সের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একটা লম্বা সময় অবধি গাছটি ‘ক্লোরোফরম গাছ’ হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। লম্বা এই গাছের তলে গেলে মা ঝিম ঝিম করে কিংবা এর পাতা নাকেমুখে লাগলে মানুষ অচেতন হয়ে যায় এমন কল্পকথা প্রচলিত হয়েছিল গাছটি ঘিরে। তখনো লাউয়াছড়ায় পর্যটকের ঢল নামেনি। শ্রীমঙ্গল বা তার আশেপাশের কিছু উৎসাহী পরিবার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসফরে আসা মানুষদের কাছে এই গাছ ছিল লাউয়াছড়ার অন্যতম নির্দশন। লাউয়াছড়া বনের বুক ফালি করে যাওয়া রেললাইন পেরিয়ে বামের মোড়ের গাছটি নিয়েই ছিল সকলের উৎসাহ। আর সদ্যপ্রয়াত লাউয়াছড়ার রাস্তার ছড়ার ধারের গাছটি যেন অনেকটাই ছিল আড়ালে। ডাকবাংলো, বনগবেষণার নার্র্সারি বা লাউয়াছড়া খাসিপুঞ্জি যতবার গেছি এই গাছ সাক্ষী হয়েছিল।
গাছটির সঙ্গে আমার পয়লা সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৯২ সনের দিকে। আমরা জানতাম এটি ক্লোরোফরম গাছ। এমনকি টিনের পাতে এমন নামও লেখা ছিল। বহুবার গাছের তলে গিয়ে পরীক্ষা করেছি। কুড়িয়ে নিয়েছি ঝরাপাতা। বহুবার মনে হয়েছে শরীর ঝিমঝিম করছে, হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাব। কিন্তু কখনো তা ঘটেনি, কারো কখনো ঘটেছে কীনা তাও শুনিনি। অনেক পরে গাছটির সঠিক উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম টানানো হয়েছিল। গাছটিকে ‘ক্লোরোফরম গাছ’ ভাবার একটা কারণ ছিল বৈকি। এমনিতেও এক অচেনা গাছ, তার ওপর এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ‘ক্লোরোফ্লোরা একসেলসা’। শুনেছি বনবিভাগের স্থানীয় প্রতিনিধিরা গাছটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের প্রথম অংশকে ভুল করে ‘ক্লোরোফরম’ করে ফেলেন আর গাছটিও ‘ক্লোরোফরম গাছ’ হিসেবে পরিচিতি পায়। মাত্র দুটি হলেও সকল বিবেচনায় ভিনদেশি এই গাছ দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি হয়ে ওঠে। আজ লাউয়াছড়া বন ১৬৭ থেকে একটি প্রজাতি হারাল।
একটি প্রাণপ্রজাতির মৃত্যু মানে বাস্তুতন্ত্রের এক বিশাল শূন্যতা। লাউয়াছড়া বনের ক্ষেত্রে এই গাছের পরিবেশগত অবদান কতখানি তা আমরা খতিয়ে দেখিনি, কিন্তু এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তৈরি হয়েছিল। জানা যায়, ১৯৩০ সনের দিকে এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা নাকি গাছটির চারা লাউয়াছড়াতে নিয়ে আসেন। সেসময় প্রাকৃতিক বনের অনেক গাছ কেটে চাপালিশ, সেগুন, গর্জন, লোহাকাঠ, রক্তন চারাও লাগানো হয়। তার মানে এই গাছ ছিল লাউয়াছড়ার শতবছরের স্বাক্ষী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে। শতবছরের মহামারী দেখেছে। জুলভার্নের ‘অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ’ কিংবা হুমায়ুন আহমেদের ‘আমার আছে জল’ সিনেমার শ্যুটিং দেখেছে। ১৯৯৭ সনে লাউয়াছড়া বনে অক্সিডেন্টালের অগ্নিকান্ড সয়েছে। দেখেছে গ্যাস জরিপের নামে ইউনোকল কী শেভরন কীভাবে লন্ডভন্ড করেছে লাউয়াছড়া বন। বাংলাদেশে এমন প্রজাতি আর কটিই বা আছে, যা কোনো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে স্মৃতিময় হয়ে দীর্ঘজীবন পাড় করছে।
দেশের শেষ ‘আফ্রিকান টিক ওক’ গাছটির মৃত্যুর খবর বহু প্রশ্নকে সামনে টেনে এনেছে। মানুষ বা বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হলে চিকিৎসক বা অভিজ্ঞজন পরীক্ষা করে মৃত্যুর খবর জানান। কিন্তু একটি গাছের মৃত্যু বিষয়ে আমরা কীভাবে নিশ্চিত হই? হাতি, বাঘ, ডলফিন, কুমির বন্যপ্রাণী মারা গেলে ময়নাতদন্ত হয়। কিন্তু গাছের কী ময়নাতদন্ত হয়? তাহলে আমরা নিশ্চিত হই কীভাবে একটি গাছ মারা গেছে। গণমাধ্যমে প্রচারিত লাউয়াছড়ার শেষ ‘আফ্রিকান টিক ওক’ গাছটির মৃত্যুর খবরও এসব চিন্তাকে সামনে আনছে। কে, কারা, কীভাবে কোন পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন গাছটি মারা গেছে তা জানা এবং এর কারিগরি জানা জরুরি।
একটি গাছে হয়তো পচন ধরেছে বা রোগাক্রান্ত হয়েছে, ডালপালা শুকিয়ে যাচ্ছে, আগা মরে যাচ্ছে, পুষ্প-পল্লব ঝরে পড়ছে এসব হয়তো সেই গাছটির মরণের দিকে যাওয়ার কিছু দৃশ্যমান নির্দেশনা। বইয়ের ভাষায় অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য। একটি গাছের জীবনচক্রে বীজ থেকে অংকুরোগদম হয়ে শিশু চারাগাছ থেকে যৌবনকাল, বার্ধক্য ও মৃত্যু পর্যায় থাকে। একবর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী কিংবা প্রজাতিভেদে এই জীবনকাল ও চক্র ভিন্ন হয়। কিন্তু ‘আফ্রিকান টিক ওকের’ মতো কোনো বৃহৎ বহুবর্ষজীবী বৃক্ষের ক্ষেত্রে এর মৃত্যু সম্পর্কে কীভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি? আবার এটি যখন দেশের কোনো পাবলিক বনের কোনো পাবলিক প্রাণসম্পদ হয়। আলোচ্য শেষ গাছটি কী মৃত্যুর দিকে যাত্রা করেছে নাকি তার মৃত্যু হয়েছে? তাহলে গণমাধ্যম কীভাবে এই গাছের ‘মৃত্যুসংবাদ’ প্রচার করছে?
একটি হাতি বা তিমির ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল নিয়ে বেশ সতর্কতার সঙ্গে মৃত্যুসংবাদ পরিবেশিত হয়। তাহলে একটি গাছের মৃত্যুসংবাদের ক্ষেত্রে কেন এমন সতর্কতা ও প্রামাণ্য দলিল থাকবে না? তো আমরা প্রাণজগতের এক এক প্রাণপ্রজাতির সঙ্গে কেন এক একরকমের আচরণ করি? সকল প্রাণসত্তার বিকাশ ও বিস্তারের সমান অধিকার থাকলেও মানুষ শুধু তার প্রয়োজনকে বিবেচনা করে কোনো প্রজাতিকে বেশি মনোযোগ দেয় এবং কোনো প্রজাতি মনোযোগের বাইরে থেকে যায়। পরিবেশ-দর্শনে এই ধরণের চিন্তাপদ্ধতিকে বলে ‘প্রাণকেন্দ্রিক বা বায়োসেন্ট্রিক মতবাদ’। দেশের শেষ আফ্রিকান টিক ওক গাছের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশনে আমাদের মনোজগতে প্রবল হয়ে থাকা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। আশা করি দেশের প্রবীণ, স্মৃতিময় এবং স্মারকবৃক্ষের মৃত্যু নিশ্চিত ও এর সংবাদ পরিবেশনে আমরা প্রতিবেশপরায়ণ হব।
আফ্রিকা থেকে আসা
মোরাসি পরিবারের একটি গোত্র হলো মিলিসিয়া। আর এই গোত্রে দুনিয়ায় দুটি মাত্র প্রজাতি আছে। একটি হলো মিলিসিয়া এক্সসেলসা এবং অন্যটি মিলিসিয়া রেজিয়া। আফ্রিকাতে এই গাছ ইরুকু, ইনটুলে, কামবালা, মোরেইরা, এমভুলে, ওডাম ও টুলে নামে পরিচিত। আর ‘মিলিসিয়া এক্সসেলসারই’ আগের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ছিল ‘ক্লোরোফ্লোরা এক্সসেলসা’। বৃহৎ এই পত্রঝরা গাছটি প্রায় ১৬০ ফুট দীর্ঘ হতে পারে। গাছের বাকল ধূসর রঙের এবং চিরলে দুধের মত কষ গড়িয়ে পড়ে। পুরুষ গাছে সাদা ক্যাটকিন ও স্ত্রী গাছে পুষ্পকান্ড থাকে। ফল লম্বা ও ভেতরে ছোট ছোট বীজ থাকে। গাছটি মধ্য আফ্রিকার নানা অঞ্চলে জন্মে। গবেষণায় দেখা গেছে, মাটির বৈশিষ্ট্য, বৃষ্টিপাত এবং আবহাওয়া গাছের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।
আফ্রিকার গিনিবিসাউ, মোজাম্বিক, অ্যাংগোলা, বেনিন, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, কঙ্গো, গিনি, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, ঘানা, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, মালাউয়ি, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, সাউতমে প্রিন্সপে, সিয়েরালিওন, সুদান, তাঞ্জানিয়া, টোগো, উগান্ডা ও জিম্বাবুয়িতে বেশি দেখা যায়। জানুয়ারি-ফ্রেবুয়ারিতে গাছে ফুল ফোটে। বাদুড়, কাঠবিড়ালি ও পাখি এই গাছের ফল খেয়ে বীজ বিসরণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে বাদুড়সহ বন্যপ্রাণীর মাধ্যমে খাওয়া ফলের বীজ থেকেই এই গাছের বেশি অংকুরোদগম হয় এবং এসব চারা বেশ রোগ প্রতিরোধী হয়। প্রাকৃতিকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ কার্বণ-আধার হিসেবে কাজ করে এই গাছ। আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ জোট আইইউসিএন ‘সংকটাপন্ন প্রায়’ হিসেবে লাল তালিকাভুক্ত করছে। মূলত বাসস্থান হারানোর কারণেই গাছটি দুনিয়া থেকে উধাও হচ্ছে।
আফ্রিকা অঞ্চলে Milicia excelsa এবং Milicia regia এই উভয় বৃক্ষপ্রজাতির কাঠ ‘আফ্রিকান টিক’ নামে পরিচিত। যেমন আমরা সেগুন কাঠকে বলি ‘বার্মিজ টিক’। এই কাঠ খুব শক্তিশালী ও গাঢ় বাদামি বর্ণের। উইপোকা প্রতিরোধী বলে স্থাপনা নির্মাণ, আসবাব, নৌযান, মেঝেতে ব্যবহৃত হয়। মাটির ক্ষয়রোধে এই গাছ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নাইট্রোজেন উৎপাদনকারী এ গাছের পাতা জৈব মালচিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল কফ নিবারণী, হৃদরোগের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। গাছের কষ টিউমার, পাকস্থলী ও গলার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে এটি এক পবিত্র বৃক্ষ।
সংরক্ষিত এই গাছের তলে উৎসর্গ ও সমর্পণমূলক কৃত্য পালিত হয়। বিশেষ করে গাছটি উর্বরতা ও নতুন জন্ম সম্পর্কিত কৃত্যের সঙ্গে জড়িত। দক্ষিণ নাইজেরিয়ার ইবো আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এই গাছ নবজাতকের আত্মাকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে। ঘানার হো অঞ্চলে এই গাছ বামনদের বাসস্থান হিসেবে গণ্য এবং এর তলে কৃত্য পালিত হয়। এই গাছের কাঠ পবিত্র বাদ্যযন্ত্র ও মৃতদেহের কফিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আইভরি কোস্টের গুয়েরে ও ঔবি আদিবাসীরা এই গাছের নিচে বলিদান করে। বাংলাদেশের লাউয়াছড়াতেও কিন্তু এই গাছ ‘ক্লোরোফরম গাছ’ নামের এক কল্পকথার জন্ম দিয়েছিল। লাউয়াছড়ার পর্যটনে ভূমিকা রেখেছিল।
আহারে নিঃসঙ্গ গাছ!
বাংলাদেশে এমন বহু নিঃসঙ্গ গাছ আছে। কোনো অচিন আবার কোনোটা জানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ভবনে যেমন টিকে আছে দেশের একমাত্র তালিপাম গাছ। বাইরে থেকে আসা কোনো প্রজাতি যদি কোনো বাস্তুতন্ত্রে প্রতিবেশগত বিশৃংখলা তৈরি করে এবং স্থানীয় খাদ্যচক্রে সংকট ঘটায় তখন সেই প্রজাতিটি ‘ইনভেসিভ/এলিয়েন’ হিসেবে পরিগণিত হয়। আমি একে ‘আগ্রাসি প্রজাতি’ নাম দেই। ‘বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২’ ‘আগ্রাসী’ প্রত্যয়টি গ্রহণ করেছে। ইউক্যালিপটাস, ম্যাঞ্জিয়াম, একাশিয়া, শিশু এমন আগ্রাসি প্রজাতির বিরুদ্ধে আমরা বহুবছর ধরে লড়ছি।
নেত্রকোনায় ‘মেনকীফান্দা আন্দোলনের’ নেতা অজিত রিছিল আগ্রাসী জাতের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জেলজুলুম খেটেছেন। প্রতিটি প্রজাতিরই একটি জন্মভূমি বা ‘সেন্টার অব অরিজিন’ থাকে। যেমন বেগুনের জন্মভূমি বাংলাদেশ, আলুর পেরু, কৃষ্ণচূড়ার মাদাগাস্কার। দীর্ঘসময় কোনো প্রজাতি বাইরে থেকে এসে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে খাপ খাইয়ে নেয় এবং খাদ্যশেকলের সহায়ক হয়ে ওঠে। আফ্রিকা থেকে এলেও আফ্রিকান টিক ওক গাছটি কোনোভাবেই একাশিয়া বা ইক্যালিপটাসের মতো এই দেশের বাস্তুতন্ত্রে আগ্রাসী নয়। তবে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং প্রতিবেশগত অবদান কতখানি তা গভীর অনুসন্ধান ও মূল্যায়ণের বিষয়। বন্যপ্রাণী আইনে এই ধরণের গাছকে ‘স্মারকবৃক্ষ’ বলা হয়েছে এবং এর সংরক্ষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
চিহ্ন সংরক্ষিত হোক
৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ গণমাধ্যমে গাছটির মৃত্যুর কিছু খবর প্রকাশিত হয়। ২০২২ সনের দিকে ছড়ার পাড়ে টিকে থাকা গাছটির পাতা ঝরে যায় ও গোড়ায় পচন ধরে। আর এতেই ধারণা করা হচ্ছে গাছটি মারা গেছে। বনবিভাগের জানায়, বহু চেষ্টা করেও এর বংশবিস্তার করা সম্ভব হয়নি। গাছটির কোনো বীজ ছিল না এবং ফুল ধরলেও ঝরে পড়ে যেত। কাটিং করেও সফল হওয়া যায়নি। শেষ গাছটি মরে গেছে নাকি মরণের প্রান্তে এটি জানা জরুরি।
আশা করি রাষ্ট্র দেশের শেষ আফ্রিকান টিক গাছটি বিষয়ে মনোযোগী হবে। ২০০৬ সনে ঝড়ে উপড়ে পড়ার পর প্রথম মৃত গাছটির গুঁড়ি বনবিভাগ বেশ যত্ন করে দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষা করেছে। লাউয়াছড়ার পাশাপাশি জাতীয় জাদুঘর ও পাবলিক সংগ্রহশালায় শেষ গাছটির অংশবিশেষ স্মৃতিস্মারক হিসেবে সংরক্ষণ করা জরুরি।
[লেখক : গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ]
-
জনসংখ্যা : সম্পদ না সংকট?
-
ব্রিকসে নতুন ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান
-
রম্যগদ্য : ‘ল্যাংড়া-লুলা, আতুড়-পাতুড়’
-
আষাঢ়ী পূর্ণিমা : আত্মশুদ্ধির সাধনায় বুদ্ধের অনন্ত আলো
-
বদলে যাওয়া মাটিতে সাহসী বীজ : জলবায়ুর বিপরীতে বাংলাদেশের কৃষির অভিযোজনগাথা
-

জুলাই অভ্যুত্থান-গাথা : ‘শিকলে নাহি দিব ধরা’
-
প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন
-
গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
-
টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি
-
রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা
-
রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...
-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক
-
জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা
-
টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং
-
ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়
-
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট
-
আসামি এখন নির্বাচন কমিশন
-
কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?
-
এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?
-
মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
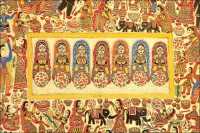
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা







