উপ-সম্পাদকীয়
মুনীরুজ্জামান : কালচার, লেবার ও পলেঝায়েভ
বিনায়ক সেন

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে মুনীর ভাই যখন মস্কো এলেন, তখন তার (তার সাথে আসা আরও কয়েকজনের) জন্য ‘ইন্টারপ্রেটার’-এর কাজ করতে হয়েছিল আমাকে কিছুদিন। মুনীর ভাইয়ের সাথে সেই আমার প্রথম দেখা। আমার তখন সদ্য পিএইচডি সমাপ্ত হয়েছে।
কাজ এমন কিছু নয়। অর্থনীতি, দর্শন, রাজনীতি বিষয়ে মুনীর ভাইরা পড়াশোনা করবেন হায়ার স্কুলে। আমার কাজ হলো ক্লাস চলাকালীন লেকচার-সেমিনারে শিক্ষক যা পড়াবেন, তার তাৎক্ষণিক অনুবাদ করে দেয়া। কিছুদিন যেতেই বুঝলাম- ভাবানুবাদে কিছু অর্থ হারিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করছে আমার নিজেরই চিন্তা-ভাবনা। মুনীর ভাইকে সে কথা একদিন জানাতে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, কোনো চিন্তা নেই, তোমার অনুবাদে আমরা আসল অর্থ ধরতে পারছি। তুমি খামোখাই চিন্তা করছ, তুমি আসলেই একটা ‘পলেঝায়েভ’ হয়ে গেলে দেখছি!
কেন আমাকে সেদিন তিনি ‘পলেঝায়েভ’ বলেছিলেন এবং তার দেখাদেখি দলের অন্য সদস্যরাও এই নামেই আমাকে ডাকতে শুরু করেছিলেন- সেটি সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই। পলেঝায়েভ (বা মতান্তরে পলেজায়েভ) ছিল ১৯৩৭ সালের একটি রুশ ছবি ‘বাল্টিক এলাকার প্রতিনিধি’ (‘বাল্টিক ডেপুটি’) ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র। চরিত্রটি এক বিজ্ঞানীর, নির্দিষ্ট করে বললে ৭৫ বছরের একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী বা বোটানিস্টের।
এই ছবিটা মুনীর ভাইকে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছিল। বিপ্লবের বাইরে থেকে আসা একটি লোক কীভাবে বিপ্লবের প্রতিনিধি (‘বাল্টিক ডেপুটি’) হয়ে দাঁড়ান তার একটি উদাহরণ ছিলেন পলেঝায়েভ চরিত্রটি। ছবিটি ইউটিউব হাতড়ালেই পাওয়া যাবে। এর শুরুতে উৎসর্গপত্রে পাই বিখ্যাত কৃষিবিদ অধ্যাপক তিমিরিয়াজেভের নাম। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, পলেঝায়েভ একটি ফিকশনাল চরিত্র : মূলত তিমিরিয়াজেভকে (বা তার মতো সৎ, পরিশ্রমী ও দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানীদের) মনে রেখেই একে গড়ে তোলা হয়েছে।
দ্বিতীয় যে-দিকটি মুনীর ভাইকে আকৃষ্ট করেছিল তা হলো তত্ত্ব ও অনুশীলনের যুগলবন্দি। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে মানুষ শ্রম-বিভাজনের দাসত্ব থেকে একপর্যায়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। সাধারণ শ্রমিক-জনতার কাতারে নেমে আসা পলেঝায়েভ বিপ্লবের শুরুর দিনগুলোতে শক্ত করে অবস্থান নিয়েছিলেন। তার কাছে দেশ-বিদেশ থেকে লোভনীয় সব প্রস্তাব আসছিল দেশত্যাগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে। তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চেয়ারের, আধুনিকতম ল্যাবরেটরির সমস্ত সুযোগ-সুবিধার। কিন্তু পলেঝায়েভ রাশিয়াতেই থেকে গিয়েছিলেন।
এটাও মুনীর ভাইকে আকর্ষণ করে থাকবে। কেননা, আমার ধারণা, পোস্তগোলায় শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন স্বচ্ছন্দ, তেমনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ‘একতা’-র কাজে, পরবর্তী সময়ে ‘সংবাদ’-এর সম্পাদনায়, অথবা মাস মিডিয়ার রাজনৈতিক ধারাভাষ্যকার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাম্প-পরিচালনার কাজেও তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। বহুমুখীন কর্মকান্ডের মধ্যে তার বহির্মুখী কাজের পরিচয়ই আমরা বেশি করে জানি।
তিনি তার অন্তর্গত কর্মকান্ডকে, তার সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনাকে- অনেকটা ইচ্ছে করেই আড়াল করে রেখেছিলেন যেন। ইউনিটি অব ফোর্সেস অব কালচার অ্যান্ড লেবার- এই ধারণার বাস্তব অভিব্যক্তি হয়েছিল তার জীবনে ও স্বভাবের মধ্যে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি যে একঝাঁক মেধাবী তরুণ-তরুণীর পদচারণায় প্রকম্পিত হয়েছিল ঢাকা ও বাংলাদেশ- যারা মেধায় ও রণে, কবিতায় ও বিপ্লববোধে, কোনো ক্ষেত্রেই আর দশজনের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না— তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন মুনীরুজ্জামান।
আশির দশকের শেষে রাষ্ট্র পরিপোষিত পুঁজিবাদের (স্টেট-স্পনসরড ক্যাপিটালিজম) একটি ‘নির্দিষ্ট অধ্যায়’ শেষ হলো। বিরাষ্ট্রীকরণ ও শিল্পঋণের বিতরণ— এই দুটোর মাধ্যমে এই পুঁজিবাদকে ‘ওপর থেকে’ পানি ঢেলে সযত্নে গড়ে তোলা হয় ১৯৭৬-১৯৯০ সময়পর্বে। এ দুটো পথে প্রচন্ড অপচয় (মতান্তরে, ইচ্ছাকৃত ‘হরিলুট’) ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে (যেমন খেলাপি ঋণকে ক্রমশ ‘মন্দঋণ’ বা ‘অবলোপনযোগ্য ঋণের’ অবস্থায় নিয়ে গিয়ে) একটি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তাদেরই তখন ‘লুটেরা ধনিক’ বলে চিহ্নিত করা হয়। এর বিপরীতে ছিল ‘উৎপাদনশীল ধনিক’ শ্রেণী, যারা মূলত রাষ্ট্র-সহায়তার বাইরে থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল নিজস্ব উদ্যোগে কখনো মাল্টি-ফাইবার্স অ্যারেঞ্জমেন্টের অধীনে গার্মেন্টস শিল্পে, কখনো স্ব-অর্থায়নে মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায়। তখনকার দিনে (এখনো) এটাকে দেখা হতো পুঁজিবাদের ভেতরের দুই প্রবণতা হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই, প্রগতিশীলরা লুটেরা ধনিক প্রবণতার সমালোচক ছিলেন এবং উৎপাদনশীল পুঁজিবাদের প্রতি (অপেক্ষাকৃত ‘কম খারাপ’ যুক্তিতে) সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন।
এই নিশ্চিত বিভাজন রেখার ন্যায্যতায় অতটা নিশ্চিত ছিলেন না মুনীর ভাই। এ বিষয়ে একাধিকবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘ডোন্ট বি সো শিওর। লুটেরা ধনিক যাকে বলছ, সেটা তার একটা দিক বটে, কিন্তু একমাত্র দিক নয়। তারও উৎপাদনশীল কল-কারখানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একই সঙ্গে সে লুটেরাও, আবার উৎপাদনশীল ধনিক চরিত্রেরও। আমাদের দেশে বড় ধনিকদের ক্ষেত্রে এই মিশ্র প্রবণতা কম নয়।’ আশির দশকের শেষে মুনীর ভাইয়ের সেই পর্যবেক্ষণ যথার্থ ছিল। আমাদের গণতন্ত্রের মতো আমাদের ধনিক শ্রেণীও হাইব্রিড চরিত্রের।
গত এক দশকে মুনীর ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগ একপ্রকার ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। টিভির পর্দায় তাকে প্রায়ই আলোচনা করতে শুনতাম। কখনো কখনো বাক্-স্বাধীনতা, ডিজিটাল সুরক্ষা আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে তাকে টিভি পর্দার বাইরেও সোচ্চার হতে দেখেছি। পত্রিকার জন্য সম্পাদকীয় ভূমিকা ছেড়ে তিনি প্রেস ক্লাবের সামনে ‘লিবার্টি প্রিন্সিপলের’ দাবিতে দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে তার সহকর্মীদের সঙ্গে। কিন্তু তখনো আমি জানতাম যে ‘সোশ্যালিস্ট প্রিন্সিপলকে’ তিনি ভুলে যাননি। কেননা, লিবার্টি ও সোশ্যাল জাস্টিস এ দুটোকে একসঙ্গে না পেলে আমাদের জীবন ‘পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়।’ ‘বাল্টিক ডেপুটি’ ছবির অধ্যাপক পলেঝায়েভের মতো তিনি কালচার এবং লেবার, লিবার্টি ও সোশ্যাল জাস্টিস উভয় ধারণাকেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। আমি নই, মুনীর ভাই-ই ছিলেন সত্যিকারের পলেঝায়েভ।
(সংক্ষেপিত। লেখাটি নেয়া হয়েছে মুনীরুজ্জামান স্মারকগ্রন্থ থেকে।)
[লেখক : অর্থনীতিবিদ। মহাপরিচালক, বিআইডিএস]
-
জনসংখ্যা : সম্পদ না সংকট?
-
ব্রিকসে নতুন ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান
-
রম্যগদ্য : ‘ল্যাংড়া-লুলা, আতুড়-পাতুড়’
-
আষাঢ়ী পূর্ণিমা : আত্মশুদ্ধির সাধনায় বুদ্ধের অনন্ত আলো
-
বদলে যাওয়া মাটিতে সাহসী বীজ : জলবায়ুর বিপরীতে বাংলাদেশের কৃষির অভিযোজনগাথা
-

জুলাই অভ্যুত্থান-গাথা : ‘শিকলে নাহি দিব ধরা’
-
প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন
-
গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
-
টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি
-
রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা
-
রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...
-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক
-
জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা
-
টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং
-
ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়
-
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট
-
আসামি এখন নির্বাচন কমিশন
-
কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?
-
এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?
-
মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
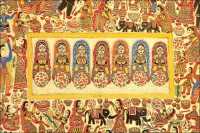
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা







