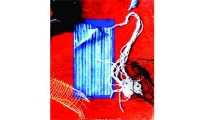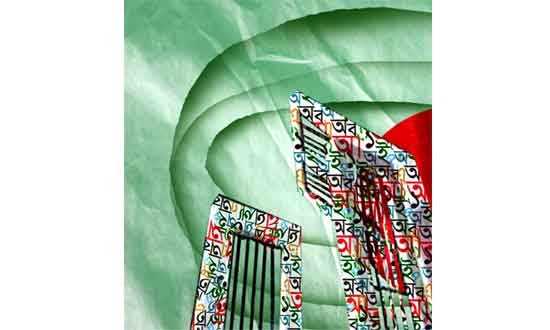
ভাষার আঞ্চলিকতা
দীপংকর গৌতম
মানুষের সঙ্গে ভাব আদান প্রদানের বিন্যস্ত মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষা আসলে একটি অদ্ভুত প্রতীকী ব্যবস্থা, যেখানে সচেতনতার উপাদানগুলো- যেমন বহির্জগতের অভিজ্ঞতা, আমাদের চিন্তা, অনুভব ইত্যাদি সম্পর্কিত হয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর কতকগুলো বিশেষ অঞ্চলের কাজের সঙ্গে। আমরা যখন কথা বলি তখন ক্রমাগতভাবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ চালিত হয়, সমন্বিত হয়। সে জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম থেকেই একটি বহুমাত্রিক প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বস্তুত মাতৃভাষায় শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও ভাব-প্রকাশের অধিকার বিশ্বের অধিকাংশ ভাষাভাষি মানুষই এখন কার্যকর করতে পারছে না। অধিকাংশ ভাষাই এখন হুমকির সম্মুখীন। অধিকাংশ ভাষাভাষি মানুষই বর্তমানে পরাজিত, বিপর্যস্ত অবস্থায় প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের সে চেষ্টায় একটি প্রতীকী অবলম্বন।
কিন্তু হালে আমাদের ভাষার অবস্থা কেমন হয়েছে সেটা ভাবা দরকার। উচ্চশিক্ষার দিকে তাকালে দেখি কোনও বই বাংলায় নেই। অর্থাৎ অনূদিত হয়নি। ফলে ইংরেজির প্রসার বাড়ছে। ইংলিশ মিডিয়ামে সন্তান পড়ানোর হিড়িক বেড়েছে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার জায়গায় আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বেশি গুরুত্ব পাওয়ায় সন্তানদের আগেই দক্ষ করা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায়। আর ঘরে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে শিশু কিশোররা শিখছে হিন্দি। তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা অনেক পিছিয়ে আছে।
বাংলা ফন্ট নিয়ে বিরাজিত সংকট রয়েই গেছে। শহরের সাইনবোর্ড থেকে হোটেল-ক্লিনিক সবখানে ইংরেজি ভাষার আধিক্য লক্ষ করার মতো। কোথাও খেতে গেলে যে মেন্যু চার্ট ধরিয়ে দেওয়া হয় তা ইংরেজিতে লেখা। দশকের পর দশক চলে গেলেও উচ্চশিক্ষা থেকে হোটেল-রেস্তোঁরা সবখানে ইংরেজির ব্যবহার বাড়ছে। একটা ভাষানীতি চালু হয়নি আজও। একদিকে অর্থনীতি অন্যদিকে বাণিজ্য, সবখানে ইংরেজির আধিক্য। অর্থাৎ বছরের পর বছর পার হলেও ভাষানীতি চালু হয়নি। বিশ্বে প্রায় পাঁচ হাজার ভাষা এখনও টিকে আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে ইংরেজির প্রাধান্য যেটা ঔপনিবেশিক আমলে হয়েছে, সেই উপনিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারছে না মানুষ। মস্তিষ্কে যে উপনিবেশ তৈরি হয়ে আছে দশকের পর দশক ধরে, তা বদলাচ্ছে না। যেভাবে অরক্ষিত ভাষা হয়ে যাচ্ছে বাংলা, তাতে এর কাছে একটা সহজিয়া ভাষাকে ছাড়লে তার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। চতুর্দশ শতকে ল্যাটিন ভাষার পাশাপাশি কাস্তিলিয় ভাষার ব্যবহার বাড়ালে ল্যাটিন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। ভারতে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি পালি ভাষা এলে সংস্কৃত মৃত হয়ে আসতে থাকে। আমাদের শিশুরা মারদাঙ্গা সিনেমার ভাষা ব্যবহারে সাবলীল হওয়ায় হিন্দি ব্যবহার করছে। এখান থেকে সাবধান হতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টার ২০২২ সালের নভেম্বরের হিসাব বলছে, বিশ্বে প্রায় দেড়শ’ কোটি মানুষ এখন ইংরেজিতে কথা বলে। এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীনের মান্দারিন ভাষা, তৃতীয় ভারতের হিন্দি। এ দুটো ভাষার লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১১০ কোটি ও ৬০ কোটি ২২ লাখ। চতুর্থ হচ্ছে স্প্যানিশ (৫৪ কোটি ৮৩ লাখ), পঞ্চম ফরাসি (২৭ কোটি ৪১ লাখ) ও ষষ্ঠ আরবি (২৭ কোটি ৪০ লাখ)। আর সপ্তম অবস্থানটি হচ্ছে বাংলাভাষিদের, যাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৭ কোটি ২২ লাখ।
কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ক্ষমতার নিরিখে ভাষার সূচকে (পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনডেক্স র্যাঙ্কিং, ২০১৬) বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ভাষার অবস্থান যথাক্রমে ইংরেজি, চীনা, ফরাসি, স্প্যানিশ, আরবি, রুশ, জার্মান, জাপানি, পর্তুগিজ ও হিন্দি। শীর্ষ দশের তালিকায় বাংলা নেই। ভাষার ক্ষমতা নির্ধারণে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণে ভাষার সক্ষমতা, জ্ঞান ও গণমাধ্যম থেকে তথ্য আহরণের সক্ষমতা, ভৌগোলিক কূটনীতিতে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য, ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভাষার উপযোগিতা এবং সংলাপের ক্ষমতা। কোনও ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার অর্থনীতির এই ফারাকটা দূর করতে না পারলে ভাষার প্রসার কীভাবে সম্ভব? শুধু ব্রিটিশ কাউন্সিল ও বিবিসির প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা, তাদের প্রচার প্রসার ইংরেজিকে ক্রমশ রফতানিযোগ্য ভাষার শীর্ষে নিয়ে গেছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। একইভাবে শিল্প-সাহিত্যে ইংরেজি ও তাদের অনুবাদেও প্রভাবের বলয় থেকে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে ঔপনিবেশিক মানসিকতা, ইংরেজির প্রসার প্রচার এবং বিশ্বের যেকোনও ভাষার সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক সবখানে সবার আগে ইংরেজি প্রকাশনাগুলো পৌঁছায় বা অনলাইনে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে। তাহলে এই বলয় থেকে কীভাবে বের হওয়া যাবে? নিজের ভাষাকে পোক্ত করতে হবে, প্রসার ঘটাতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় লক্ষ করি যে বেশি ইংরেজি লেখক দার্শনিকদের লেখার উদ্ধৃতি দিতে পারি তাকে তত বিদ্বান ভাবি। আমাদের ভাষাভাষি লেখক, দার্শনিকদের গুরুত্ব খুবই কম। আমাদের মস্তিষ্কে উপনিবেশের ভূত থেকে যাওয়ায় উচ্চশিক্ষায় বাংলার ব্যবহার নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা একবার বলেছিলেন, ‘যখন আপনি কোনো ভাষায় কাউকে কিছু বলেন, তা তার মস্তিষ্কে পৌঁছায়, সে তা বুঝতে পারে। আর যখন তার নিজের ভাষায় বলেন, তখন তা তার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়।’ মাতৃভাষাকে তাই হৃদয়ের ভাষা বলেই মানেন ভাষাবিদরা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় ৭০টি (মতান্তরে ৪৫টি) আদিবাসীদের (ক্ষু নৃ-গোষ্ঠীর) ২৫ লাখেরও বেশি মানুষ বাস করে। হাজার বছরের সংস্কৃতি পরম্পরা ও ভাষিক ঐতিহ্য রয়েছে তাদের। সেসব ভাষা ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির রং ও রসে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে, দেশে বাংলাসহ মোট ভাষা রয়েছে ৪১টি। যার মধ্যে আদিবাসীদের (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর) ভাষা আছে ৩৩টি। এর মধ্য থেকে ১৪ ভাষাকে বিপন্ন ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভাষা গবেষকরা। একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে রাজবংশী, রাই, বাগদি, কোচ, হদি, কুঁড়ুখ, আদি মালতো ও ভালুর মতো আরও কয়েকটি ভাষা। বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে খাসিয়া, সাঁওতাল, মুন্ডা, মান্দি (গারো), ককবরক, লালেং (পাত্র), পালিয়া, মৈতেয় মণিপুরী, খুমি, বম, খেয়াং, পাংখো, লুসাই, ¤্রাে, চাক, ঠার বা থেক, মারমা, চাকমা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, সাদরি ও হাজং। এ ছাড়া সিং, কর্মকার, গন্ড, বেদিয়া, বর্মণ ও লোহার ভাষা প্রায় বিলুপ্তির পথে। ইউনেস্কোর সূত্র মতে, পৃথিবীতে কোনো ভাষায় কথা বলা মানুষের পরিমাণ যদি পাঁচ হাজারের কম হয় তাহলে সে ভাষাকে বিপন্ন ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশে বিপন্ন ভাষার সংখ্যা ১৪টি। বাংলা-ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার ক্রমাগত আগ্রাসনের কারণে সব আদিবাসী ভাষাই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসামসহ সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২৬ কোটি মানুষ এই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। এরপরও বাংলা ভাষার যে অবস্থা তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে পুঁজিবাদের কদাকার রূপ বাজার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ বাড়ছে। এতকালে বাংলা ভাষারও কোনো ভাষা নীতিমালা তৈরি হয়নি। ফলে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটছে তা ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। এক অঞ্চলের মানুষ চলে যাচ্ছে কোথাও রুটি-রুজির সন্ধানে। ফলে ভাষার অঞ্চল খালি হচ্ছে-হারাচ্ছে ভাষা বৈচিত্র্য-আঞ্চলিকতা। ভাষা নিয়ে মানুষ যেখানে যাচ্ছে, সে সেখানের ভাষায় কথা বলছে। সেখানেও সুর সহসা যায় না। এটা কলকাতায় গেলে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। কলকাতার ভাষার সঙ্গে সবাই দ্রুত তাল মেলালেও এলাকার মানুষ পেলে সে তার আঞ্চলিকতায় ফিরে যায়। এ অবস্থা খোদ ইউরোপ আমেরিকাসহ সব মানুষের বেলায়। তারপরও ভাষার বিবর্তনে ও পুঁজির অসম বিকাশের মধ্য দিয়ে ভাষা হারাচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষা-ভাষার প্রাণ। আঞ্চলিক ভাষাকে নির্বাসনে দিয়ে মান ভাষা টিকতে পারবে কিনা এটাও একটা বিষয়। মানুষের মতো ভাষারও সমাজ আছে- শ্রেণি আছে। সেদিক থেকে আঞ্চলিক ভাষা অচ্ছুত হলেও ভাষা তৈরির কারিগর। এটা না বুঝলে সংকটের মুখোমুখি হবে ভাষাই। তাই এখনই বিষয়টি চিন্তায় আনা দরকার।