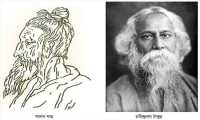literature » samoeky
সন্জীদা খাতুন : কৃতি ও কৃতিত্ব
বেগম আকতার কামাল
সন্জীদা খাতুন / জন্ম: ৪ এপ্রিল ১৯৩৩; মৃত্যু: ২৫ মার্চ ২০২৫
বহু পরিচয়ে গুণান্বিত সন্জীদা খাতুন মূলত একজন সাংস্কৃতিক লড়াকু ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি থেকে কী করে ইতিহাসগত পরিক্রমায় ও যাপিত জীবনে ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে হয় তার ন্যারেটিভ তিনি তৈরি করেছেন। আমরা ‘ন্যারেটিভ’ শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। কেননা এই ন্যারেটিভ আমিকেন্দ্রিক নয়, অপরতায় তথা সর্বনামের সাথে জোটবদ্ধ যাতে আছে আমাদের ইতিহাস-সময় ও শ্রেণিবর্গের ভাঙ্গাগড়া। সংস্কৃতি এই ভাঙ্গাগড়ার কেন্দ্র ও পরিধি- একইসঙ্গে। প্রশ্ন এই, কেন ও কীভাবে সংস্কৃতি কেন্দ্র-পরিধি হয়ে উঠল?
কোনো ব্যক্তি যখন একটি পণ্যবস্তু উৎপাদন করে তাতে লেগে থাকে তার শ্রম-কৃষ্টি, উৎপাদন পদ্ধতি, নৃতাত্ত্বিক পরম্পরা, ধ্যানজ্ঞান ইত্যাদি। পণ্য সবসময়ই বাজার সন্ধানী, বিনিময়যোগ্য। এটি যখন হাটবাজারে যায় তখন অন্যের পণ্যের সাথে মুখোমুখি হয়, বিনিময় হয়, অপরের ভোগ্য হয়। এর ফলে বাজারজাত পণ্যটি ও অন্যের সংস্পর্শজাত পণ্যটির মিথস্ক্রিয়া ঘটে তাতেই তৈরি হয় সংস্কৃতি। মনে রাখতে হবে এই পণ্যটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা তৈরি হয় বলে তার একটি মূল্য ও উপযোগিতা থাকে। সেটি যদি স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয়, শ্রেষ্ঠত্বের গুণবিচার দিয়ে মূল্যায়িত হয় তবেই তা সাংস্কৃতিক বলয় হয়ে ওঠে, সমাজ-মনস্তত্ত্বকে ও জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে। সন্জীদা খাতুনের কৃতি প্রধানত সংস্কৃতিকে ঘিরে, তাঁর কৃতিত্ব প্রতিভা ও শ্রমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে। তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা ও প্রতিভা এই কাঠামোতে নিজেকে যেমন গড়ে তুলেছে তেমনি সামাজিক রুচি ও অভিজ্ঞানকেও রূপ দিয়েছে। আমরা এই রূপদানের প্রশ্নে লক্ষ করি সন্জীদা খাতুনের নিজস্বী মুখশ্রী- যাকে বলতে পারি সেলফি (ংবষভরব)। এই নিজস্বী বা সেলফিই আজ ইতিহাস হয়ে আছে। কী এই ‘নিজস্বী’, কীভাবে কোন ভঙ্গিতে তিনি তা বিনির্মাণ করলেন?- সেটাই আমাদের ডিসকোর্স। যার পরিধিতে আছে তাঁর ছায়ানট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাদীক্ষা, সঙ্গীতচর্চা, অধ্যাপনা, সর্বোপরি ঐ সাংস্কৃতিক লড়াই। শুধু বাংলাদেশে নয়, তিনি ছড়িয়ে আছেন দেশের বাইরেও- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর পরিচিতি কম নয়। এর মূল লক্ষ্য হলো নিজের স্বাধীন-সত্তার পাশাপাশি অপর ব্যক্তির সত্তাকেও স্বাধীন করার সুকঠিন যাত্রাপথটি তৈরির দায়দায়িত্ব বহন করা। যাতে জড়িয়ে আছে স্বদেশ ও শ্রেণিবর্গ, চলমান ইতিহাসের গতি ও প্রগতি, আছে মানুষের নান্দনিক অবস্থান ও তা নিয়ে সংঘাত-সংগ্রাম।
মনোদর্শনের আলোকে তাঁকে বুঝে নিতে পারি তিনটি সূত্রে। তা হলো, অনুভূতি, ইচ্ছা ও জ্ঞান। অনুভূতিতে থাকে আবেগ-সংবেদন, থাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়ে চারপাশের প্রকৃতিজগৎকে আত্মভূত করার শক্তিবত্তা। আর ইচ্ছা হলো সেই শক্তিবত্তাকে সক্রিয় করে তোলা, কী করব বা করব না- সেই উপলব্ধিতে পৌঁছানো ও বোধে উপনীত হওয়া। এটিই স্বাধীন সত্তার সূচক, অনুভূতিকে বোধের মধ্যে নিয়ে গেলেই আমরা জ্ঞানের পরিসরে প্রবেশ করতে পারি। তাহলে অনুভূতি, ইচ্ছা ও বোধ- এই তিন সরণী দিয়ে আমরা জ্ঞানীয় সত্তায় পৌঁছাই যেখানে মনন থাকে, তত্ত্ব থাকে, ইতিহাস-সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া থাকে। সব মিলিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাকটিভি জম অনিবার্য হয়ে ওঠে। শিল্পীদের বেলায় এই অ্যাকটিভিটি স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গীতালয়, শিক্ষালয়, অনুসারীবৃন্দ গড়ে তোলায় নিয়োজিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বভারতী তার দৃষ্টান্ত। সন্জীদা খাতুনের ছায়ানট- নালন্দা স্কুল আরেক নমুনা। সঙ্গীতের মম্ময় সুরবাণীসাপেক্ষ যে পরিশীলন-বাক্সময় প্রকাশ তাকে অনুভূতি ও বোধ থেকে জ্ঞানসত্তায় উত্তীর্ণ করার প্রথম ধাপই অপরের জন্য শ্রোতাবর্গ ও সঙ্গীতকার তথা গায়ক ও প্রতিষ্ঠান-সংঘ তৈরি করা। এবং তাকে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন পুনরুৎপাদনের মধ্যে দিয়ে সাধন মার্গ করে তোলা। সন্জীদা খাতুনের অপরজনেরা ছিল বিপুল পরিসরে সংঘবদ্ধ ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাসিত মানুষেরা-শ্রেণিবর্গ নির্বিশেষে। যারা অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে- তা সে ধর্মীয় অনুশাসন, রাষ্ট্রের বিধান, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ- যা-ই হোকনা কেন, সব বাধাকে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করায়। তিনি এক্ষেত্রে সঙ্গীতের যরমযঃবহফ ংঢ়ববপয ধহফ সঁংরপধষ ধৎঃরপঁষধঃরড়হ-কে হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। একুশের গান, আমার সোনার বাংলা কিংবা কারার ঐ লৌহকপাট কিংবা আবার আসিব ফিরে এই বাংলার তীরে- ইত্যাকার গান হয়ে উঠেছিল ঐ হাতিয়ার। বিশেষ করে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি তিনি ’৭১-পূর্ববর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় শেখ মুজিবের ইচ্ছাক্রমে গাইতেন, গাইতেন শিল্পী অজিত রায়, যেটি ক্রমে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে ওঠে।
প্রশ্ন এই, সঙ্গীতচর্চা-সংঘপ্রতিষ্ঠান গড়া, যাপিত জীবনযাত্রায় এরকম স্বাধীনতা-মুক্ততার ক্ষমতা তিনি কীভাবে অর্জন করেছিলেন? বিশেষ করে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমানের বিকাশ-সংগ্রাম-মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতায়? একাডেমিকভাবে শিক্ষকতার ঘেরাটোপে? প্রথমেই স্পষ্ট করে আমরা বলতে চাই, সন্জীদা খাতুন নিছক নারী হিসেবে নিজের সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভাঙার কাজটা করেননি, করেছেন মানুষ হিসেবে। তাই তথাকথিত নারীবাদীদের দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, অথচ নারী হিসেবে সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক হার্ডল রেসেও তাঁকে দৌড়াতে হয়েছিল। তাঁকে ‘নারী’ হিসেবে বদনামের ভাগী হতে হয়েছে, কতিপয় সহকর্মীর ঈর্ষা ও অবজ্ঞার শিকার হতে হয়েছে। বিশেষ করে পিতা, কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) আত্মজা হিসেবে তাঁর মধ্যে কেউ কেউ অহংকার খুঁজে পেতেন। যুক্তিবাদ ও বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেনের আভিজাত্য, শ্রেণিসংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার আবহে সন্জীদা খাতুনের বেড়ে-ওঠাটা ছিল বুদ্ধিবাদী ও নান্দনিকতার মিথস্ক্রিয়া, এমন একটা আভা যা তাঁকে, নিছক লালিত্যের পরিবর্তে সহজ কাঠিন্যের, ছন্দ ও দ্বন্দ্বের স্বরায়ণ করে তুলেছিল। আর সে স্বরে মন্দ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান, সুর ও বাণীর ‘বেণীবন্ধন, তা যতটা না সুরমন্দ্রিত তারও বেশি স্বরলিপির নিখুঁত চর্চাধন্য, বলা চলে সঙ্গীতের ব্যাকরণ অনুসারে গানের চর্চা করার বাধ্যতা।
২.
এই গড়ে-ওঠার পর্বটা, আমরা প্রথমে একটু বুঝে নেব। পিতা কাজী মোতাহার হোসেন বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের- যা ইতিহাসে ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ নামে খ্যাত, ‘শিখা’ পত্রিকা ছিল যার মুখপাত্র তাতে যুক্ত ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের নামকরা অধ্যাপক, নেশায় ছিলেন ঝানু দাবা খেলোয়াড়, স্বভাবে আত্মভোলা একজন প-িত মানুষ। কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর সখ্য ইতিহাস বিদিত, নজরুল তাঁকে ‘মোতিহার’ সম্বোধন করতেন, তাঁকে কবি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রও লিখেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেনের এগার সন্তানের একজন হয়ে সন্জীদা খাতুন পিতা ও অগ্রজাদের বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবোধে যেমন লালিত হয়েছিলেন তেমনি একদিকে বোনেদের সঙ্গীতচর্চার আবহে নিজেও দীক্ষিত হতে থাকেন। শিক্ষাগ্রহণ করেন ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুলে। পরে ইডেন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে পড়াশোনা সমাপ্ত করে ১৯৫৪ সনে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে স্নাতকোত্তর শিক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। এই শিক্ষাগত পরিক্রমার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল সঙ্গীতচর্চার ধারাবাহিকতা ও নিজের শিল্পী-সত্তার বিকাশ।
তিনি শুরুতে নজরুলের গান গাইতেন, টেলিভিশনে গাওয়া প্রথম গানটিও ছিল নজরুল সঙ্গীত। নজরুলের বিচিত্র সুর সংযোজনা বিশেষ করে হিন্দুস্তানি দরবারি সাঙ্গীতিকতা প্রধান গানগুলি যেমন বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি সন্জীদা খাতুনকেও আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার দিকে মনোযোগী হন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হন। এর পটভূমিতে শুধু শান্তিনিকেতনে শিক্ষাগ্রহণের অভিজ্ঞতাই প্রধান কারণ ছিল না, ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাণী ও সুরের সম্মিলন ঘটানো; বিধায় সন্জীদা খাতুন তাতে খুঁজে পান ছন্দ-সুরের অতিরিক্ত কথার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। কথার খেয়ানৌকাই সুরের সরণী বেয়ে অনন্ত করে তুলত সঙ্গীতকে। কেননা মানুষের জ্ঞানের জগতে সবই বানিয়ে তোলা, মূর্ত, প্রাকৃতিক, কেবল গণিত ও সঙ্গীতের ভাষাই মৌলিক ও বিমূর্ত। সন্জীদা খাতুনের রবীন্দ্রচর্চায় আমরা এই অভিজ্ঞতা ও সত্য লাভ করি। তৃতীয় সূত্র হিসেবে ছিল তাঁর উচ্চারণভঙ্গিমা। নিখুঁত ব্যাকরণ অর্থাৎ স্বরলিপি বুঝে নিয়ে গান চর্চা করতেন তিনি, ফলে রক্ষিত হতো একই সঙ্গে সুরের শুদ্ধতা, বাণীর প্রাণসত্য, এই যে সুর বাণী ও উচ্চারণের প্রশিক্ষণ ও শুদ্ধতা রক্ষার দায়বদ্ধতা তা-ই সন্জীদা খাতুনের সাঙ্গীতিক উচ্চারণের- সঁংরপধষ ধৎঃরপঁষধঃরড়হ-এর অনুজ্ঞা। যা তাঁর কথোপকথনে, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে, ভাষণে এমনকি দৈনন্দিন কথাবার্তায়ও প্রকাশিত হতো, যা তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি ও ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিল। সঙ্গীত যেহেতু সুমিত রূপের কাঠামোতে থেকেও অনন্তের অভিসারী তেমনি তাঁর বাচনভঙ্গিও ছিল সুমিত, স্বচ্ছ ও ধীরলয়ের। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি তাঁর শারীরিক-মানসিক ব্যক্তিসত্তা সঙ্গীতশিল্পত্ব দিয়ে অন্তর্গঠিত। জীবন বাস্তবতা দিয়ে তিনি শিল্পী-ব্যক্তিত্ব গঠন করেননি, বরং শিল্পত্বের হাত ধরেই বাস্তব জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। শিল্পীকে বিশেষ করে সুরের আবেগ যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে গানের স্বরলিপি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করলেই আবেগের পায়ে বেড়ি পরানো সম্ভব হয়। সন্জীদা খাতুন সবসময় স্বরলিপিভিত্তিক গান গাইতেন বলে উচ্চারণ ও সাঙ্গিতিক ধ্যান- দুটোই ধরা দিয়েছিল। তাতে গানের তান, লয় ও ছন্দিত কথার মিথস্ক্রিয়া ঘটে যেত। শুদ্ধ উচ্চারণ করতেন ব্যাকরণ মেনে, গানও গাইতেন ব্যাকরণ মেনেই। ফলে কথার ব্যাকরণ ও গানের স্বরলিপি এক হয়ে যেত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম দিকের গায়কেরা যে স্বাধীনতা নিতেন সেক্ষেত্রে তিনি নিজের স্বকীয়তা আরোপ করতেন না। নিজেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে হারিয়ে ফেলতেন না, বরং গান হারিয়ে ফেলত অন্য গায়কের স্বকীয়তা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে এর কারণ হলো ঐ শুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গি ছাড়াও বিশ্বভারতীতে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য লিখিত ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ’ (১৯৮৫) ও ‘ধ্বনি থেকে কবিতা’ (১৯৮৮) বইদুটি। ভাবের ও কাব্যভাষার ঐশ্বর্য বুঝে নিয়ে ধ্বনির শক্তিবত্তায় তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার সচেতন প্রয়াসের ফল এই দুই বই। কাজেই তাঁর উপলব্ধি, চিত্ত, চরিত্র ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যে কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল তাতে অবধারিতভাবে মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছিল সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাংলাদেশের ’৭১-পরবর্তী পর্যায়ের সাংস্কৃতিক লড়াই যা রাষ্ট্রগঠনের রাজনীতির কোলে বেড়ে উঠছিল সেই ধারায় সন্জীদা খাতুন বাঙালিত্বের আত্মতা নির্মাণের দায়দায়িত্বর ভূমিকায় এসে দাঁড়ালেন। কেননা, সঙ্গীত চেতনার অন্তহীন দিগন্ত আর সংস্কৃতি জীবনের জাতির-রাষ্ট্রের অনুভূমি। নিজের এলিট শ্রেণিসত্তা ও শিল্পী-সত্তার সমীকরণ ঘটিয়ে তাঁকে ইতিহাসিত মানুষ করে তোলে চলমান সংঘর্ষশীল বাস্তবতা। শ্রেণিসত্তা আর ঐ শিল্পী-সত্তা- দুই-ই ধারণ করে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার দায়দায়িত্ব- গান আর লেখালেখি, ভাষণ ও প্রতিষ্ঠান গঠনের টানে তিনি মিশে গেলেন এদেশের ইতিহাসস্রোতে।
৩.
বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে ধর্ম ও ভাষার একটি বাইনারি আছে। আসলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকারের অংশীজন হওয়ার প্রশ্নেই, প্রথমত ধর্মকেন্দ্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও অচিরেই তা বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলন হয়ে উঠতে থাকে। এর কারণ পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির আধাসামরিক আধাঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালি মুসলমানের সংঘর্ষশীল চড়াইউৎরাই অবস্থাটি ছিল জটিল ও ইতিনেতি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাক্রম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতিলাভ, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও সংসদগঠন এবং পরে তা ভেঙে দেয়ার ফলে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনজারি ইত্যাকার ঘটনাক্রম আড়াল করছিল এদেশের শোষিত জনগণের দুরবস্থা। রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থাকলেও ঐ শোষণক্রিয়াটি ছিল অনুভূমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। বাঙালি যেহেতু কৃষিসংস্কৃতির মধ্যে বাঁচে ও মরে, তা আবহমান সময় জুড়ে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হলেও জীবনযুক্ত হয়ে থাকে, ফলে রাষ্ট্র্ক্ষমতার অংশী হওয়ার প্রশ্নে সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায় তার লড়াইয়ের অস্ত্র। সংস্কৃতির কোলেই রাজনীতির বোধবুদ্ধি চর্চিত হতে থাকে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণিও বেড়ে ওঠে, একটা বর্গ তৈরি করে। তৎকালীন বাঙালি বু্্দ্িধজীবীদের অর্গানিক করে তুলে আত্মবিকাশের পথ তৈরি হতে থাকে, এই পথ খুঁজে পায় ১৯৬১ সালের রবীন্দ্রজন্মশত বর্ষ-উদযাপনের মধ্যে, ইতোমধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা বলে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধকরণ, বাংলা হরফ পরিবর্তন, পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গীয় মূলধারার সাহিত্য বর্জনের ঘটনা ইত্যাদি বাঙালিত্ব বোধকে জাগিয়ে তোলে, সংঘবদ্ধ করতে থাকে যা রবীন্দ্রজন্মশত বর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। ষাটের দশকের পুরোটাই এই এগিয়ে যাওয়ার ঘনঘটায় পূর্ণ। নানা সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ, মননশীল ও সৃজনশীল লেখালেখির মধ্য দিয়ে আত্ম্স্বাধীন জাতিত্বের ন্যারেটিভ তৈরি হতে থাকে। রবীন্দ্রজন্মশত বর্ষ সফলভাবে উদযাপিত হয় সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও। এই সাফল্যের হাত ধরেই জন্ম হয় ছায়ানট প্রতিষ্ঠান, মূলত সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। তাতে জড়ো হতে থাকে এদেশের এলিট শ্রেণির বিদ্বজনেরা- কবি, লেখক, চিত্রশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, আবৃত্তি শিল্পী প্রমুখ। অর্থাৎ ছায়ানট যেমন সব গান শেখানোর প্রতিষ্ঠান তেমনি উদার মুক্তমনা বিদ্বজনেরও সম্মিলন-সংঘ হয়ে ওঠে। সামাজিক কর্মযজ্ঞে তাদের একত্র করে ছায়ানট পথযাত্রা শুরু করে। সন্জীদা খাতুন হন একজন কর্ণধার। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, সংঘগঠনের ক্ষমতা, বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাপিয়ে উঠছিল নিজের নিভৃত সঙ্গীতসত্তাকে, নিজে গান গেয়ে আনন্দ পাওয়ার চেয়ে তিনি বেশি শ্রম দিয়েছেন ছায়ানটের শিক্ষাদানে। তাই তাঁকে বলা যায় সঙ্গীতশ্রমী ও দীক্ষাগুরু, বস্তুত ছায়ানটের জন্মই হয়েছিল:
“বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখবার আন্দোলন হিসেবে, প্রথমেই ‘পুরানো দিনের গানের আসর’ হলো বিদ্যাপতি থেকে হিমাংশুদত্ত সুরসাগর পর্যন্ত ঐহিত্য স্মারক গীতিকারদের গান পরিবেশনের ভিতর দিয়ে। ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালির সম্মিলনের সুযোগ সৃষ্টি করা হলো।” (শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, সন্জীদা খাতুন, ২০২০)
-ইত্যাদি কর্মক্রিয়ার একদিকে ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির রাজনীতিকরণ, যেমন বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রতিবাদ, ১৯৬২ সালের ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রামের উপদ্রুত উপকূলের দুর্গত মানুষের জন্য অর্থসংগ্রহ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে সহযোগিতা ইত্যাদি। ১৯৬৫ সালের দাঙ্গায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে চাকরি থেকে বদলির ঘটনায়, সত্তরের বন্যায় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সম সঙ্গীত-সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের হাতিয়ার।
এই ধারণা সঠিক নয় যে, ছায়ানট কেবল রবীন্দ্রচর্চা করত বা করছে। এই প্রতিষ্ঠানে রাগসঙ্গীত, নজরুলগীতি, পল্লী গীতি, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিও সমভাবে চর্চিত হয়। এছাড়া শান্তিনিকেতনের আদলে সন্জীদা খাতুন ও অন্যরা ছায়ানটে বসন্ত ঋতু উদযাপন, শারদোৎসব, নবান্ন, বর্ষামঙ্গল- এসব ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবের প্রবর্তন ঘটায় এবং সবচেয়ে বড় যে অর্জন তা হলো ১৯৬৭ সাল থেকে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে রমনা বটমূলকে কেন্দ্র করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্মারক সৃষ্টি করে, যা বাখতিন-কথিত কানির্ভালের রূপ পরিগ্রহ করে। একাত্তর-পরবর্তী কালে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ চেতনা দিয়ে সন্জীদা খাতুন ছায়ানটকে একদিকে অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতির প্রতিরোধকামী সংঘ করে তোলেন অন্যদিকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারায় বাঙালি জাতীয় চেতনার শক্তিবত্তাকে প্রাণবান করে নিজের কর্মস্পৃহা অব্যাহত রাখেন। এ দেশের মৃত্তিকা-নদীজল-আকাশ, কৃষি সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর মনোভূমি ছিল এলিট শ্রেণিমাফিক, স্বকীয় রুচিসম্মত সিগনেচার তৈরি করলেও তিনি এটা বুঝেছিলেন যে জাতির রুচিবোধ, উন্নত বিকাশ ও বুদ্ধিবাদী চিত্ত গঠন করতে হলে প্রথমে দরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এরই দৃষ্টান্ত নালন্দা স্কুল, শক্তিবত্তা ও শারীরিক, সবল ব্যক্তিবর্গ তৈরির জন্য অন্যদিকে আয়োজন করা হয়েছিল ব্রতচারীর দল। অর্থাৎ উনিশ-বিশ শতকীয় বুদ্ধিবাদী চিন্তা ও চিত্তবিকাশই ছিল তাঁর আধেয়। যদিও তিনি বেড়ে উঠেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বঙ্গীয় রাজনীতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের ইতিনেতি সংঘাত-দ্বন্দ্বে তবু তাঁর আদর্শ ছিল সাংস্কৃতিক জাগরণ ও শিক্ষার বিকাশ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সহায়ক তাঁর শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।
যাঁরাই তাঁর সরাসরি শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁদের মধ্যে মেধাবীদের সহজেই শনাক্ত করে নিতেন, স্নেহের সম্পর্ক গড়ে তুলতেন, অন্যথায় ছিলেন দৃঢ়, কঠিন স্বভাবের অধ্যাপক। ব্যক্তিগত নানা বিপর্যয়-বিচ্ছেদ তাঁকে প্রহত করেছে কিন্তু কর্মযজ্ঞ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে কয়েকটি দিন তাঁর উদভ্রান্ত রূপ দেখেছি। ক্লাসে তিনি বিষাদে আচ্ছন্ন থাকতেন, একদিন তো অশ্রুও ঝরেছিল। তেমনি অশ্রুপাত করতে দেখেছি কন্যাসন্তান অপালার মৃত্যুতেও। প্রেমজবিবাহ সত্ত্বেও বিচ্ছেদ আর সন্তান হারানো এই স্ত্রীসত্তা ও মাতৃসত্তার শিকড় থেকে তাঁর নারীত্ব উপড়ে গেলেও সন্জীদা খাতুন সামলে উঠেছিলেন, নিজের মানবসত্তাকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ। মনে পড়ে ক্লাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের ২০১৭ নম্বর কক্ষেকোনো এক স্মরণসভায় তিনি বক্তৃতার পরিবর্তে গেয়েছিলেন- “তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই/কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ কোথা বিচ্ছেদ নাই”।
২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি তাঁর পঁচাশিতম জন্মবার্র্ষিক পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করেছিল। আমি সেখানে বক্তৃতায় আবেগবশে বলেছিলাম- ‘সন্জীদা খাতুন একজন মহামানবী’। তিনি বিব্রত হয়েছিলেন, বিরক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। এতটাই ছিল আত্মসম্ভ্রমবোধ, নীতিবত্তা ও অভিরুচি। স্পষ্টবাক অথচ ধীর স্থির কিন্তু হাঁটাচলায় দৃঢ়তা ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর শরীরীকাঠামো নিয়ে তিনি বাংলা বিভাগের করিডোরে হেঁটে যেতেন। ছিল না অবরোধ, নারীসুলভ বিব্রত ভঙ্গি বা লাজুকতার লেশমাত্র; অথচ আগেই বলেছি তিনি তথাকথিত নারীবাদী নন। ২০০১ সালে যখন পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হলো, মানুষ আহত-নিহত ভ-ুল হলো তখন তিনি দলবলবহ মিছিল করে শ্রোতাদের নিয়ে চারুকলায় এসে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। তাঁর সেই অনমনীয় দৃঢ়তা আজও স্মরণে তরবারি হানে।
৪
তাঁর লেখালেখির জগৎও ছোট নয়, ‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’সহ ঊনচল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিপুল কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব ভার সত্ত্বেও তিনি প্রচুর লিখেছেন, সভা-সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রথম গবেষণা গ্রন্থ : কবি সত্যেন্দ্রনাথ, (১৯৫৪)। অধিকাংশ লেখা রবীন্দ্র বিষয়ক, এছাড়াও আছে অন্যান্য সাহিত্য-সাহিত্যিক সন্বন্ধে তাঁর অভিমত। সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনাও অপ্রতিহত ছিল আমৃত্যুকাল অবধি, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশকাল নিয়ে চিন্তামূলক লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষা সম্পর্কে প্রীতিস্নিগ্ধ আলোচনাও কম নয়। বস্তুত এই কয়েকটি বিষয় ভাবনার বৃত্তে সন্জীদা খাতুন যতটা স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ততটা ক্রিটিক্যাল নন, আর্থসমাজ-কাঠামো, পরিবর্তনশীল শ্রেণিবর্গ, ক্ষমতায়ন-প্রশ্ন ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রশ্নগুলো তাঁর চিন্তাকে মেধাবী করে তোলেনি, যতটা করেছে ভাবুক। ভাববোধি দিয়েই তিনি চিন্তার অন্তরসার বুঝে নিবেন, চিন্তনের প্রতর্ক-তত্ত্ব-উপাত্ত নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী ন্যারেটিভ রচনার চেষ্টা তাতে অনুপস্থিত। দেশকাল-ইতিহাসের পটভূমি থাকলেও সেগুলোর বিশ্লেষণ-জটিলতা তাঁর লেখালেখিকে আচ্ছন্ন করেনি। বিশেষ করে ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ’ বা ‘ধ্বনি থেকে কবিতা’- এই দুটি গবেষণাধর্মী বই আবেগায়িত, স্নিগ্ধ ও সরলতায় ভরপুর। অন্তর্বিশ্লেষী নতুন তাৎপর্য বিনির্মাণের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, তবে পাঠক তাতে ভাবিত ও আবেগায়িত হবেন, কিন্তু নতুন জিজ্ঞাসায় ও যুক্তিশীলতায় আন্দোলিত কমই হবেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি :
“বিশ্বজগতের সুশৃঙ্খল ছন্দোময় গতি সম্পর্কে রবীন্দনাথের উপলব্ধির পরিচয় আছে তাঁর রচনায়। কবিতা আর গানে তার রূপায়ণ সর্বাধিক। কারণ ধ্বনির শিল্প হিসেবে কবিতা আর গানে সুর আর গতিছন্দ অপরিহার্য।... ‘বিশ্বনৃত্য’ কবিতা লিখেছিলেন স্বজাতির নিষ্প্রাণ নির্জীব ভাব থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আবেদন হিসেবে। “বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে/কে বাজারে সেই বাজনা/উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,/বিস্মৃত হবে আপনা”। ইত্যাদি। এই মন্ত্রধ্বনির বাদক হচ্ছেন নটরাজ। তাঁর ডমরুর তালে তালে ‘নৃত্য রত এবং সে-ধ্বনি আর নৃত্য বিশ্বজগৎকে নৃত্যচঞ্চল করছে-”(বিশ্ববীণা ও বিশ্বনৃত্য)।
‘কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা’ নিয়ে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ আছে। এই রচনাটিতে ভাষা বিশ্লেষণের বস্তুগত বিচার আছে, আছে পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতা। ধ্বনিকে তিনি কবিতার ভাবব্যঞ্জনার অভিসারী হিসেবেই সাব্যস্ত করেন এবং সংস্কৃত আলংকারিকদের ধ্বনিব্যঞ্জনাকে সমর্থন করেন পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিক ও নন্দনবিদের পরিবর্তে। অর্থাৎ ররীন্দ্রনাথের কাব্যসঙ্গীতের মর্মার্থ ও ধ্বনিব্যঞ্জনার আলোচনা একদিকে, আরেক দিকে জাতির চিত্ত-উদ্বোধনে রবীন্দ্রসৃষ্টি, দর্শন ও কর্মযজ্ঞের ভূমিকা নিয়েই সন্জীদা খাতুন বেশি অন্তর্মনস্ক। নজরুলের প্রেম ও নারী ভাবনা, গদ্যরচনা, পত্রাবলি ইত্যাদি সূত্রে নজরুলকে বিবেচনার প্রয়াস আছে। উদ্বৃতি:
“সন্দেহ নেই নজরুলের প্রেমবুভুক্ষা ছিল সমুদ্রপ্রমাণ কিংবা তারও অধিক,... তাঁর কৈফিয়ৎ, ‘কবি আর বুলবুল পাপ করে, তারা পাপের অস্তিত্বই মানে না বলে। ভুল করে ভুলের কাঁটায় ফুল ফোটাতে পারে বলে।’
নজরুল ভুল করে ফুল ফুটিয়েছেন বটে, কিন্তু বাগানের মালীকে তাঁর প্রিয় ‘স্বর্গের দেবতা’ হিসেবে অর্ঘ্য দিতে চায় যে, ... এই প্রত্যাখ্যান আর অবমাননার দুঃসহ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল নজরুলকে।... তবু স্বীকার করতে হবে অতল-গভীর এবং উত্তাল প্রেমের এই অভিজ্ঞতা নজরুলের বিশেষ প্রাপ্তি বটে।”
(পত্রাবলিতে কাজী নজরুল ইসলাম)
জসীম উদ্দীনকেও তিনি বিবেচনা করেন জীবন ঘনিষ্ঠ দেশি ‘মণিমানিক্য’ হিসেবেই। শিল্পকলা একাডেমিতে তিরিশের কবি বিষ্ণু দে-কে নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সন্জীদা খাতুন বিষ্ণু দে-র ‘ব্লাডপ্রেশার’ কবিতাটি আলোচনা করেছিলেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম বিষ্ণু দে-র সমাজনিষ্ঠ বামপন্থাকে তিনি চিহ্নিত করে কবিতাটিতে খুঁজে নেন সমাজের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাকে। এই পথে তিনি আর চর্চা করেননি। বরং রবীন্দ্রনাথ, স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমাজ আর বাংলা ভাষার গুণগরিমা নিয়েই প্রবন্ধ লিখে গেছেন- ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে, মু্িক্তযুদ্ধের শক্তিবত্তায় আর ভাষার ধ্বনিচরিত্র চিহ্নিতকরণে।
বস্তুত, লেখালেখির অব্যাহত ধারায় সন্জীদা খাতুনের ভূমিকা কতখানি তা বিশ্লেষণের ধারাটি ছাপিয়ে গেছে লেখনীর সততা ও বলবার কথাটিকে স্পষ্টতায় বলার স্বকীয়তা। আর সবকিছুকে অতিক্রম করে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব গায়কী, ছায়ানট প্রতিষ্ঠান, ব্রতচারী ও পিতাকে নিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন ইত্যাদি পরিশ্রমসাধ্য কর্মযজ্ঞ। সারাদেশে তিনি বিভিন্ন জেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন- যা নিয়মিতভাবে চর্চিত হচ্ছে। মনে পড়ে এমনি একটি সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের অনুষ্ঠানে আমি তাঁর সাথে দলবলসহ কুমিল্লার মতলবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি ঐ অঞ্চলের বয়স্ক আর ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম নিজ মিশনকে তুলে ধরে সবাইকে বরণ করে নেয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর আছে। বয়স্করা মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা-গান-নাচ দেখল, ছোটরা উজ্জীবিত হলো প্রাণচাঞ্চল্যে। আসার পথে শুনতে পেলাম দোকানে-দোকানে ঐ অনুষ্ঠানের রেকর্ডকৃত বক্তৃতা বাজচ্ছে, লোকজন ভিড় করে শুনছে। সন্ধ্যায় আমরা ক্লান্ত অবস্থায় ফিরছি কিন্তু সন্জীদা খাতুন ক্লান্তিহীন, যেন নতুন করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন। এই যে, স্বদেশের প্রাণের মধ্যে মিলে যাওয়ার শক্তি- যা গানে-কথায় সম্ভব তা-ই ছিল সন্জীদা খাতুনের ব্রতসাধনা। আমি এখানে তাঁর ‘বাংলাদেশের হƒদয় হতে’ পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসটি উহ্যই রাখলাম। সেটি তাঁর আরেক মহৎ কৃতি, মানসম্পন্ন লেখা প্রকাশের জন্য যে তাঁর আকুতি ও শ্রম আজও আমি স্মরণ করতে পারি।
আজ তিনি প্রয়াত। মেডিক্যালে নিজ দেহ উৎসর্গ করে গেছেন। যতই বিব্রত হোন জীবৎকালে, এখনও আমি বলব যে তিনি একজন মহামানবী-কৃতি ও কৃতিত্বে এদেশে এরকম দ্বিতীয়জন আর নেই। এই প্রবন্ধে আমি তাঁকে ছুঁয়ে গেলাম মাত্র। পরবর্তী সময়ে আরও সবিস্তারে বলার সম্ভাবনা নিয়ে এখানেই শেষ করছি।
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-

তিন প্রহরের শকুন
-

ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা
-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস