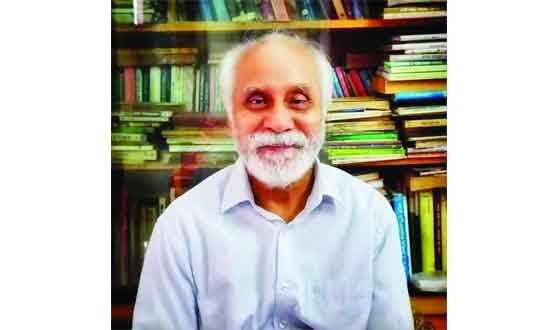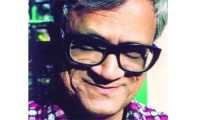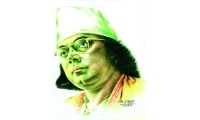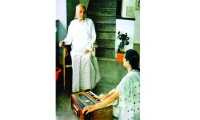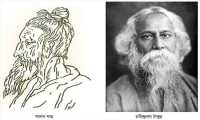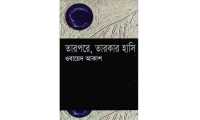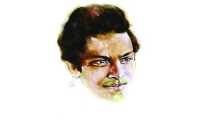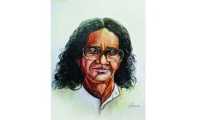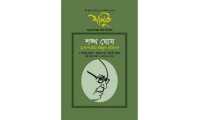literature » samoeky
কবি নূরুল হক
আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ
মোহম্মদ বিলাল
কবি নূরুল হক
বাংলা সাহিত্যে নূরুল হক একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি একাধারে মুক্তিযোদ্ধা এবং শিক্ষক। এই ত্রিবিদ পরিচয়ের মধ্যে নূরুল হক আমাদের কাব্যসাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। জীবনের মর্মযন্ত্রণা এবং আশার আলো দুটোই নূরুল হকের কবিতায় শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর কবিতাবলি উত্তরসূরীদের অনুপ্রাণিত করেছে। অর্থাৎ যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন, সেসবই তাঁর কবিতায় অনায়সে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ফলে তাঁর কবিতায় সাধারণ শব্দাবলি বা প্রাত্যহিক কাজের দৃশ্যাবলি মর্মলোকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবিশ্ব তৈরি করেছে। এর জন্ম মৃত্তিকার ভেতরে, কিন্তু ব্যঞ্জনা অসীমের দিকে বিস্তৃত। কবি নূরুল হক তাঁর জীবদ্দশায় ততটা পরিচিতি লাভ করেননি, যতটা তাঁর মৃত্যুর পরে চর্চিত হচ্ছেন। তাঁর কবিতার অনায়াস উচ্চারণ ও লাবণ্য পাঠককে কবিতার পর কবিতার দিকে নিয়ে যায়। এটি তাঁর কবিতার দূরগামী জীবনের ইঙ্গিত করে।
কবি নূরুল হক মূলত ষাটের দশকের কবি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছয়টি- সব আঘাত ছড়িয়ে পড়েছে রক্তদানায় (২০০৭), একটি গাছের পদপ্রান্তে (২০১০), মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত গল্প ও অন্যান্য কবিতা (২০১২),শাহবাগ থেকে মালোপাড়া (২০১৪), এ জীবন খসড়া জীবন (২০১৫), কবিতাসমগ্র (২০২০)। কবিতাসমগ্রতে অগ্রন্থিত কবিতা (৩৮টি), কৈশোরক ও প্রস্তুতি পর্বের কবিতা (৩৪টি) নামে আরও কয়েকটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিজীবনের শুরুর দিকে তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, মাঝখানে লম্বা বিরতিও ছিল। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি যখন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তাঁর সমকালীন কবিগণ যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতাপ অর্জন করেছেন। তিনি কি তাঁর সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন? আমার তো মনে হয়, তিনি কোথাও থেকে বীতরাগ হয়েছিলেন বলে ব্যাকফুটে বা নিভৃতলোকে চলে গিয়েছিলেন। পিয়াস মজিদ কর্তৃক গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার এবং শফিক হাসানের প্রবন্ধে কবি নূরুল হক নিজের কবিজীবন ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যে তথ্যাবলি পাওয়া যায় তাতেএরূপ ভাবনা একেবারে অমূলক নয়। আবার হয়তো তিনি নিজেই ছিলেন প্রচারবিমুখ এবং অনিয়মিত। নায়েম লিটুর সঙ্গে আলাপচারিতায় এ প্রসঙ্গে কবি নিজের কথা বলেছেন যাতে বিলম্বের কারণ ছাড়াও তাঁর মনোজগৎ ও কবিতাভাবনা সম্বন্ধে জানা যায়। কবি বলেছেন-
[...] কবিতায় নতুন কিছু যুক্ত করতে পারব না ভেবেই হয়তো সেখানে উপস্থিত থাকার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। [...] ‘কেনো লেখা যদি বাংলা সাহিত্যে কিছু সংযোজন না করে তাহলে সে লেখার দরকার কী? কোনো কোনো নামকরা কবির কাব্যগ্রন্থ কিনেও তো পড়ার মতো একটি পঙ্ক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে বাড়ি ফেরার আগেই বইটা নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসতে হয়। এরকম কাজ করে লাভ কী?’ [...] এরকম একটা মনোভাবের কারণেই লেখালেখি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। ফলে লেখার ক্ষমতাও একদিন আমার কাছ থেকে চলে গেল। (খেয়া, পৃ. ৭৬, প্রকাশকাল ১৪২৫ বঙ্গাব্দ )
উদ্ধৃতাংশটি নূরুল হকের কবিতাভাবনার কয়েকটি দিক নির্দেশ করে। যেমন- কোনটি কবিতা এবং কোনটি কবিতা নয় ইত্যাদি। এমনকী নিজের কবিতা সম্বন্ধেও একরকম বিচারবোধ কাজ করত তাঁর মনে। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় কবি নূরুল হকের কবিজীবনের বিশিষ্ট দিকসমূহ আলোচনা করা, এক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন তাঁর কবিতাবলি, সাক্ষাৎকার এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের তথ্য-বিশ্লেষণ। পুলক হাসান সম্পাদিত সাহিত্য-পত্রিকা খেয়া-র অগ্রহায়ণ ১৪২৫ সংখ্যাটি ছিল কবি নূরুল হক সংখ্যা। প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার এই লিটলম্যাগে কবি নূরুল হকের দুটি সাক্ষাৎকার, কবির জীবন ও কবিতা বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা সন্নিবেশিত হয়। কবি তখন জীবিত। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৪২৮ বঙ্গাব্দে খেয়া : কবি নূরুল হক স্মরণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতেও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধসহ সরকার আমিন কর্তৃক দুইপর্বে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। সরকার আমিন মূলত লাইভ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন যা পরিমার্জিত আকারে ‘নূরুল হক স্মরণ সংখ্যায়’ প্রকাশিত হয়েছিল। ফেইসবুকে প্রথম সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হয় ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে। দ্বিতীয়টি প্রচারিত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে।
‘খেয়া : কবি নূরুল হক সংখ্যা’য় খেয়ার পক্ষ থেকে পিয়াস মজিদ এবং নায়েম নায়েম লিটু আলাপ পরিচালনা করেন। সাক্ষাৎকার দুটির শিরোনাম ‘আলাপধারায় নূরুল হক’, ৪৯-৯২ সংখ্যক পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত হয়। পিয়াস মজিদের আলাপসূত্রে কবি নিজের মনোজগতের ভিত্তিমূল খোলাসা করে বলেন-
“আমার জন্ম গ্রামে। নেত্রকোণার ভাটি অঞ্চলে। বিস্তৃত হাওর সেই এলাকাটিকে ঘিরে রেখেছে। সেই হাওর আর আকাশ-ভরা জনপদে রাত্রিদিন লোকসাহিত্যের নানা আঙ্গিকের আসর লেগেই থাকত। বাতাসভরে থাকত সারিগান, জারিগান, কবিগান, কীর্তন, বাউলগান, ঘাটুগান, মেয়েলি গীত, গাইনের গীত, পুঁথিপাঠ, যাত্রাগান এবং গল্প-কথকতায়। বিশেষত জালাল উদ্দিন খাঁ, উকিল ?মুনশি, অন্ধ খুরশিদ, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ বাউল সাধকদের গান চারিদিকে জ্যোৎস্নাধারার মতো ভেসে বেড়াত। আমার গৃহশিক্ষক চারণ কবি রুকনউদ্দিনের কবিতায়ও মাটির মানুষের সুখদুঃখের কথা বেজে উঠত স্বতঃস্ফূর্তভাবে [...] চারপাশের সকল উপাদান আমার মানসলোক তৈরিতে সহায়তা করেছে।”
বাউলগণ সাধারণত সহজের সাধনা করেন, স্বভাবে ও কর্মে লালন করেন সহজিয়া ভাবনা, সারল্য তাদের জীবনের পাথেয়। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করে বলতে হয়, কবি নূরুল হকের মনোজগতে তৈরি করে দিয়েছিল শৈশবে দেখা বাউলঘরানার সহজিয়া ভাবনা। এজন্যে সারল্য তাঁর কবিতার শুধু ভূষণ নয়, ভেতরের সম্পদ।
সরকার আমিনের গৃহীত সংক্ষাৎকারটিতে কবির মানসলোকের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। সেটি তাঁর পিতার উপদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি অধ্যাপনায় যোগদান করেন। এটি ছিল সরকারি চাকরি, নিশ্চিত জীবনযাপনের পথ ছেড়ে দিয়ে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। একটা কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে সম্মুখ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ‘আপনি তো এটা কখনও জাহির করেননি।’ সরকার আমিনের একথার উত্তরে কবি নূরুল হক বলেন- ‘এটি জাহির করার কিছু নেই। আমার বাবা ইমাম ছিলেন। তিনি বলতেন, রাস্তা দিয়ে তুমি এমনভাবে হাঁটবে না যেন তোমাকে দেখে মানুষ রাস্তা ছেড়ে দেয়।’ যে মানুষ সরকারি কলেজের চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে একটা কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে লড়েছেন, কিন্তু সেটা জাহির করে কোনও সুবিধা নিতেই চাচ্ছেন না, তাঁকে অন্য ধাতুতে গড়া বলেই মানতে হবে। তাঁর সময়ের কবিদের থেকে তাঁর চিন্তার ধরন আলাদা। তিনি কবিতার পথে এমনভাবেই হেঁটেছেন যাতে তাঁর জন্যে রাস্তা ছেড়ে অন্যদের দাঁড়াতে হয়নি। এই মানসগঠনের জন্যই কি কবি নূরুল হক উচ্চকণ্ঠ হলেন না, বরং নিভৃতে সরে দাঁড়ালেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা থেকে? তাঁর কবিতার ভাবসম্পদ, বুননরীতি ও শব্দবিন্যাসের কৌশল তো শাশ্বত আসন দাবি করে এবং কালান্তরের পাঠক তাঁর কবিতাকে সেভাবেই গ্রহণ করেছে। নায়েম লিটু যাথার্থই বলেছেন- ‘তাঁর কবিতা নির্মেদ, বাহুল্য বর্জিত স্বতঃস্ফূর্ততার এক জাদুকরী প্রকাশ- অনিবার্য শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠককে নিয়ে যান ভিন্ন এক আবেশের পৃথিবীতে- যেখানে আষাঢ় মাসের হাওরে ঢেউয়ের গীতল ছন্দ (খেয়া, ২০৬ পৃ.)।’ নায়েম লিটুর সঙ্গে আলাপচারিতায় কবি নূরুল হকের জাগরণমূলক অর্থাৎ তৎকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের অভিঘাতের প্রেক্ষাপটে কবিসত্তার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। সে সময়ে অর্থাৎ ষাটের দশকের দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান, সাপ্তাহিক জনতা এবংকণ্ঠস্বর ও নাগরিক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তাঁর জাগরণমূলক কয়েকটি কবিতা প্রকাশিতও হয়। কিন্তু নূরুল হকের ভাবনা শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল সহজিয়া ঘরানায়, এখানেই তিনি বিশিষ্ট কবি।
আসলে কবিসত্তা কখনও মরে না। তাই অনিয়মিত থেকেও নূরুল হক পাঠকের মাঝে ফিরে এলেন পড়ন্তবেলায়। তখন জীবনের পড়ন্তবেলায় হলেও কবিতায় তিনি যুবাপুরুষের মতো দীপ্ত। তাঁর প্রথম কবিতার বই সব আঘাত ছড়িয়ে পড়েছে রক্তদানায় প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। তখন তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছে এবং তাঁর সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণ তখন খ্য্যতির চূড়ায় স্থাপিত। কী আঘাত ছিল তাঁর মনে যার জন্য এরকম একটি নাম বেছে নিয়েছিলেন কাব্যগ্রন্থের জন্যে? কবি নূরুল হককে যারা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, তারাই হয়তো এর রহস্যভেদ করতে পারবেন ভালো। কবি প্রয়াত হন ২০২১ সালের ২২ জুলাই। তাঁকে প্রণতি জানিয়ে তাঁর জীবন ও কর্ম মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকে প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা একাডেমি কর্তৃক ‘উত্তরাধিকার’-এর ‘কবি নূরুল হক সংখ্যা’ প্রকাশিত হয়। অবশ্য এটি আমার দেখা হয়নি। তবে কবির মৃত্যুর পর লিটলম্যাগ খেয়া-র ‘কবি নূরুল হক স্মরণসংখ্যায়’ শফিক হাসানের ‘নূরুল হক : শিল্পী-চারিত্র্য’ নামে একটি স্মৃতিগদ্য ছাপা হয়। প্রবন্ধটি কবির মৃত্যুর সপ্তাহখানেক বাদে সম্ভবত ৩০ শে জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের দৈনিক ‘খোলা কাগজে’ প্রথম ছাপা হয়েছিল ভিন্ন নামে। সে যাক। নূরুল হক সম্মন্ধে এটি একটি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ মনে করি। সেই স্মৃতিগদ্য থেকে জানা যায়, এ সময় কবি কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণের আড্ডার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। আজিজ সুপার মার্কেট, কাঁটাবন, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রপ্রভৃতির সংস্কৃতি-আড্ডায় সময় দেন। তখন তিনি খেয়া, প্রতিস্বর, বিহঙ্গকাল ইত্যাদি খ্যাতিমান লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
খেয়া-র নূরুল হক স্মরণ সংখ্যায় কবিকে ‘কবিতার সন্ত’ নামে অভিহিত করে পুলক হাসান একটি প্রবন্ধ লেখেছেন। এই অভিধাটি, আমার মতে, নূরুল হকের কবিতা ও কবিজীবনের সারাৎসার বহন করে। ওবায়েদ আকাশ তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন ‘নিমগ্ন দৃশ্যের কবি’ বলে। প্রবন্ধ লিখেছেন গোলাম ফারুক খান, মুজিবুল হক কবির, সৈয়দ কামরুল হাসান, সরকার মাসুদ প্রমুখ। এসবই মূল্যবান রচনা যা কবি নূরুল হকের জীবন ও সৃষ্টিকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করে। তবে নূরুল হক প্রকৃত অর্থেই ‘কবিতার সন্ত’ পুরুষ যিনি চ-ীদাসের মতো সাদামাটা ভাষায় কবিতা রচনা করে পাঠকের হৃদয়ের গভীরে জায়গা করে নিয়েছেন। তা না হলে, প্রথমপাঠেই কীভাবে নূরল হকের কবিতার প্রেমে পড়ে গেলাম? তখন করনাকালের লকডাউনজনিত অবসর ছিল। সিলেটের একটি বইবিপণীতে হঠাৎ করেই নূরুল হকের ‘কবিতাসমগ্র’ গ্রন্থটির ওপর চোখ আটকে যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কবিতা পড়ি। বলা যায়, প্রথম দর্শনেই তাঁর কবিতার প্রেমে পড়ে যাই, এমনকি সেদিনই ‘কবিতাসমগ্র’ কিনে নিই। এতে নূরুল হকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলি পাঠের সুযোগ পাই এবং ‘নূরুল হকের কবিতা : বিষয় ও শিল্পবোধ’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। এটা অবশ্য নূরুল হকের কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জার্নির তথ্য, তবে ভালোবাসার নিদর্শন তো বটেই।
সরকার আমিন কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকারের দিকে মনোযোগ দিলে কবি নূরুল হকের মনোজগত এবং সৃষ্টিকর্মকে বুঝতে পারার কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। নূরল হক সেখানে তাঁর প্রিয় কবিদের যে তালিকা দিয়েছেন তার প্রথম ও প্রধান জায়গাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, পরে আসছেন পাবলো নেরুদা, লোরকা প্রমুখ কবিগণ। আজতক আমাদের সাহিত্যে কবি ও অন্যরূপ সৃজনকর্মীদের ভাবলোক ও প্রকাশরীতির গড়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব অনেকটা ভিত্তিভূমির মতোই বিস্তৃত, এটার উপর দাঁড়িয়েই নিজস্ব সৃজনভুবন নির্মাণ করেছেন তাঁরা। কবি নূরুল হকও এই ভাবলোক ও প্রকাশরীতির ?উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো নিরীক্ষাধর্মিতার তাড়া নূরুল হকের ভেতরে নেই। তবু নূরুল হক কোথায় যেন অদ্বিতীয়- তাঁর কবিতা ছোটো ছোটো, তবে সেই স্বল্পায়তনের ভেতরে কবি এমনভাবে বাঁক পরিবর্তন ও ভাবান্তর উপস্থাপিত করেছেন যাতে একটি নিটোল কবিতাপাঠের আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের শেষার্ধে বলেছেন- ‘মনেরে আজ কহ যে/ ভালোমন্দ যাহাই আসুক/ সত্যরে লও সহজে।’ কবি নূরুল হক যেন এই দর্শনকে অন্তরে লালন করেছেন- প্রেমে-অপ্রেমে, অনুরাগে-অবহেলায় অবিচলিত শান্ত-স্নিগ্ধ মানুষ হিসেবে জীবনের বেদনাদীর্ণ চিত্রসমূহ চিত্রায়ন করে অগ্রসর হয়েছেন। এজন্যে তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায় দুঃখ ও বিবর্ণতার মুহূর্ত চিহ্নিত করার ঠিক পরক্ষণে, পরবর্তী চরণ বা স্তবকেই, জীবনের আননন্দময় অবস্থাকে নির্দেশ করেছেন। এ কাজটি তিনি করেছেন এক অদ্ভুত শক্তিতে, এ শক্তি তাঁর স্বভাবগত এবং সমকালীন অন্য কোনও কবির মধ্যে তা বিরল বা নেই বললেই চলে। কবিতায় আনন্দ-বেদনার পরিস্থিতিরে মধ্যে দূরত্ব, দুর্ভোগ বা কালগত সংযোগ প্রকাশ করতে তিনি কবিতার লাইন বা চরণ ভেঙে দিয়ে ভাবনার জন্য জায়গা ছেড়ে দেন যাতে পাঠক তার কল্পনার স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারেন। তাঁর ‘অনিদ্রা’ কবিতাটির কথা ধরা যাক। কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রথম দিনের সূর্য’ কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য বা অনুপ্রেরণার বিষয়টি যুক্ত বলেই মনে হয়। কিংবা দুটো কবিতা পাশাপাশি রেখে পাঠ করা যায়। কিন্তু ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো শোনায় না। যেমন-
অন্ধকারে
জানালা দিয়ে তাকাই,
বাইরে,
আকাশে।
দেখি
দূর কোনো তারায়
উসখুস করছে
কেউ।
আমি ঘুমুতে পারি না।
সারারাত।
শতাব্দী শতাব্দী কেটে গেলে
আবার তাকাই বাইরে
আকাশে-
আবার উসখুস করে কেউ।
অন্য কোনো তারায়।
(অনিদ্রা, মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত গল্প ও অন্যান্য কবিতা)
কবিতা বিষয়ে একটা দর্শন ছিল নূরুল হকের-কবিতা কোথা থেকে আসে? এক আলাপচারিতায় নূরুল হক বলেছেন, ‘যদি কবি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু লেখেন [...] কবির নিজের অভিজ্ঞতা, একবারে সোজাসুজি ফিলিং [...], চিন্তা করে লেখবেন, এটা নয় [...], একবারে নিজের ব্যক্তিগত অনুভব থেকে আসবে কবিতার ব্যাপারটা।’ আর কবিতার কাছে কী প্রত্যাশা? এরূপ প্রশ্নের উত্তর জীবনের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা তার সমার্থক বলেই নূরুল হক মনে করেন। সুতরাং বলতে হবে, নূরুল মনে করেন, কবিতা হবে কবির নিজের জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা যার মাধ্যমে জীবনের শুশ্রƒষা পাওয়া যায়। নূরুল হকের কবিজীবন আসলে জীবনের শুশ্রƒষার অপর নাম। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে তোষামোদি কারবার অবিদিত নয়, কিন্তু নূরুল হক তোষামোদিকে ঘৃণা করে কবিজীবন চর্চা করেছিলেন, তাই ‘উপরে উঠা’ বা পুরস্কার লাভের চিন্তা মাথায় নেননি। দুঃখবোধ নূরুল হকের কবিতায় ছিল এবং এইজন্যে তিনি কিছুটা নির্জনতাকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন।
কবি নূরুল হকের কবিতার আরেকটা বিশেষ দিক, স্বদেশ ও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। এই বোধ তাঁর কবিতাকে মহৎ করে তুলেছে। দেশ যখন দৈন্য-দুর্দশা বা বর্বরোচিত কর্মকা-ের দ্বারা বিপন্ন, স্বদেশ ভাবনা তখন তাঁর কাব্যের মৌল প্রেরণা ছিল। দেশের দুর্দশা কবিকে বিচলিত করে বলেই কবিতায় লেখেন, ‘দেশটা এখন আমার কাছে ভীষণ ভারি লাগে।’ রাষ্ট্র ও সমাজের রূঢ়তায় কবি কীরকম বিক্ষত হয়েছিলেন? জীবন ধারণের জন্য যে মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটানো অত্যাবশ্যক তার আকাল বা বঞ্চনায় কবি বিপন্ন বোধ করেছেন। এ অবস্থায় তিনি মনে করেন, নিজের জীবনকেই আধপোড়া কায়দায় পুড়িয়ে পুড়িয়ে প্রাচীন মানুষ যেমন মাংস ঝলসে খেতো তেমনি খেতে হবে জীবনের বাকি বেলাটুকু। এজন্যে কবি বলেছেন- নিজের জীবনকেই আধপোড়া কায়দায় পুড়িয়ে পুড়িয়ে/ খেতে হবে/ বাকি বেলাটুকু,/ দলিত আনন্দে প্রাচীন/ মানুষের আঙ্গনে ঝলসানো/ শিকার-করা মাংসের টুকরোর মত (‘আহার’, এ জীবন খসড়া জীবন)। এই দীর্ঘশ্বাস এবং যন্ত্রণার কথা ছাড়িয়ে তার কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে জীবনের জয়গান। তাঁর মতে, উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও বলতে হয়, ‘জীবন এক অপূর্ব দৃশ্য, যা দেখে মানুষ/ বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যায়।’ বাংলা কবিতাধারায় একথা অভিনব উচ্চারণ।
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-

তিন প্রহরের শকুন
-
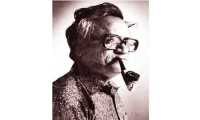
ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা
-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-
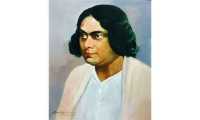
নজরুলের গল্প ও উপন্যাস