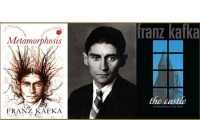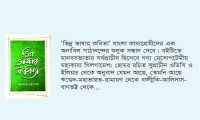সাময়িকী
বাস্তবের জাদু জাদুর বাস্তবতা
অমর মিত্র
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ / জন্ম : ৬ মার্চ ১৯২৭; মৃত্যু : ১৭ এপ্রিল ২০১৪
গত শতকের শেষ কুড়িটি বছর সমস্ত পৃথিবীই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থেকেছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির দিকে। সেইসব দেশের সাহিত্যের খবর আসতে আরম্ভ করেছে। গদ্য সাহিত্য, গল্প-উপন্যাসের লিখন প্রণালি তারা নিজেদের মতো করে খুঁজে নিয়েছেন, যা আমাদের এতকালের পাঠ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। আমরা অবাক হয়েছি। অনুবাদের মাধ্যমে একটু একটু করে পরিচিত হচ্ছি। আশ্চর্য একটি উপন্যাস আমাদের তাবত পাঠ অভিজ্ঞতাকে বদলে দিয়েছিল। নিঃসঙ্গতার একশো বছর। ১৯৮২ সালে এই উপন্যাস নোবেল পুরস্কার পায়। মার্কেজ ছড়িয়ে পড়েন সমস্ত পৃথিবীতে। তাঁর লেখার পদ্ধতি বা লিখনের আঙ্গিক জাদুবাস্তবতা এই শিরোনামে আমাদের কাছে এসে পৌঁছল। আমি আন্দাজ করেছিলাম, হয়ত তাঁর লেখার ভিতরে ফ্যান্টাসি আছে। পড়তে গিয়ে টের পেলাম ম্যাজিক রিয়ালিজম আর ফ্যান্টাসির ভিতরে তফাত বিস্তর। এক মুহূর্তের বিভ্রম আর জীবন ও সমাজের বাস্তবতাকে কল্পনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া এক নয়। এ যেন আধুনিক রূপকথা। এর বাস্তবতা মেলে আবার মেলে না। আসলে হার্ড রিয়ালিটি ক্লান্ত করে সত্য। তার আর নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। তাকে গার্সিয়া মার্কেজ মুড়েছেন এক কাল্পনিক বাস্তবতার ভিতরে। তা অলীকও নয়, আবার চারদিকের বাস্তবতাও নয় বুঝি। সেই বাস্তবতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা নয় যেমন, তেমনি তা বটেও। মুড়েছেন তিনি অনেক রকম গল্প দিয়ে, যে গল্প সত্য হয় না সরাসরি, কিন্তু ছড়িয়ে থাকে জনজীবনে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু গল্পের জাদু অবিশ্বাসীকেও নতমুখী করে তোলে। সেই সব অলীক কাহিনী কেমন করে ছড়িয়ে থাকে, না, অন্য এক রূপকথার মতো। আমি শালতোড়ার সেই পাহাড়ি গঞ্জে শুনেছিলাম এক অদ্ভুত গল্প। কোনো এক বছরে শিলাবৃষ্টির সময় নাকি পঞ্চাশ কেজিরও বেশি ওজনের এক শিলাখ- আকাশ থেকে পড়েছিল জঙ্গলের ভিতর। আর তা গলতে শুরু করলে অকালে শীত নেমে এসেছিল সেই গঞ্জে। আমার একটি গল্পে তা আছে। আমাদের রামায়ণ মহাভারত আর কথাসরিৎ সাগরে আছে এমন কত অবিশ্বাস্য কাহিনী। তাকে জীবন ও সমাজের সঙ্গে অন্বিত করেছেন পূর্বপুরুষ কাহিনী নির্মাতারা, লেখক-কথকরা। না করতে পারলে তা শুধুই গল্প। যে লেখক যেভাবে ভাবেন। ম্যাজিক রিয়ালিজম আপনি আপনার গল্পে একটু মিশিয়ে দিতে পারেন না। এটা সাহিত্যের এক নতুন আঙ্গিক। আবার এই আঙ্গিকেই যে ল্যাটিন আমেরিকার লেখকরা সকলে লেখেন, তা সত্য নয়। মার্কেজ যে সমস্ত ছোটগল্প লিখেছেন (সংখ্যায় ৩৯), তার অধিকাংশ কল্পনা আর জীবনকে জুড়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর জাদুবাস্তবতা ছিল না সমস্ত গল্পের বাস্তবতায়। কোনো গল্পে তা ছিল, কোনোটিতে তা ছিল না। আসলে তিনি যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবী, প্রকৃতি আর জীবন জড়িয়ে থেকেছে প্রবলভাবে। আমি আন্দাজ করি সমুদ্র পাহাড় অরণ্য নিয়ে যে প্রকৃতি, আর প্রকৃতির যে শক্তি, তাকে মান্য করতে জানতেন এই মস্ত লেখক। আমাদের ঠাকুমা দিদিমা’র গল্পে প্রকৃতি জড়িয়ে থাকত। ভূত-প্রেত নিয়ে বসবাস করতেন তাঁরা। মার্কেজ অনুভব করতেন প্রকৃতির অসীম শক্তির কাছে মানুষ কিছুই না। আমি একটি গল্পের কথা বলি, ক্রামোন্তনা। ক্রামোন্তনা একটি উত্তরের ভয়ংকর ঝড়োবাতাস। ভয়ানক তার শক্তি। সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দর এক জনপদ কাদাকেসে গ্রীষ্মের সময় এই ঝড় শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রামোন্তানা ব্যতীত কাদাকেসে গ্রীষ্মের সময়টি বড়ো মনোরম। এই সময় আফ্রিকার মরুপ্রান্তর থেকে তাপ ছড়াতে শুরু করলে, বহু ভ্রমণকারী কাদাকেসে আশ্রয় নেন। মূলতই তারা ইউরোপের মানুষ। এই গল্প আরম্ভ হয় অন্য এক শহর বার্সিলোনার এক পানশালায়। রাত দুটো। একটি ক্যারিবিয়ান যুবক গান গাইছিল সেখানে। আর তাকে ধরে টানাটানি করছিল জনাএগারো সুইডিশ যুবক। তারা তাকে কাদাকেসে নিয়ে যেতে চায় একটি অনুষ্ঠানের জন্য। সে যাবে না কিছুতেই। গল্প কথক, লেখক, গিয়েছেন কয়েক বন্ধুর সঙ্গে ওই পানশালায়। তিনি শেষ অবধি দেখলেন এগারো সুইডিশ যুবকের জেদের কাছে, শক্তিমত্তার কাছে ক্যারিবিয়ান যুবকটি হার মানল। তারা তাকে জোর করে পানশালা থেকে বের করে একটি গাড়িতে তুলল। ক্যারিবিয়ান গায়ক যুবকটি কিন্তু আসলে ছিল কাদাকেসের বাসিন্দা। কিন্তু গতবারে সে ক্রামোন্তোনা দেখে পালিয়ে এসেছে বার্সিলোনায়। আর যাবে না কাদাকেসে।
কিছুতেই না। ক্রামোন্তোনার অভিজ্ঞতা ভয়ানক, তাই সে যাবে না কাদাকেসে। লেখক বা গল্প কথক বছর পনেরো আগের কথা বলছেন তখন। ক্রামোন্তোনার অভিজ্ঞতা তখন তাঁর হয়নি তাই কাদাকেস সম্পর্কে ছিল অসম্ভব ভালো ধারণা। গ্রামখানি নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্য অতুলনীয় তখনো তাঁর কাছে। সেই অবকাশের সময় এসেছিল ক্রামোন্তোনা, ভয়ংকর সেই উত্তরের ঝড়। কী আক্রোশ তার। সেই আতঙ্ক যেন এখনো যায়নি। গল্পের অনেকটা অংশ জুড়ে কাদাকেসের বিবরণ। কেন সেই জায়গাটি সুন্দর তার কথা। তারপর ঝড়ের ভয়ংকরতা। গল্প এখানে প্রায় শেষ হয়ে আসে। শুধু একটি খবর দেওয়ার দরকার ছিল কথকের। সেই যে ক্যারিবিয়ান গায়ককে ধরে নিয়ে গেল বুদ্ধিভ্রংশ সুইডিশ যুবকেরা, তাদের অসর্তকতার সুযোগ নিয়ে সেই ভীতসন্ত্রস্ত যুবক ক্রামোন্তোনার কাছ থেকে বাঁচতে পাহাড়ের খাদে ঝাঁপ দিয়েছিল চলন্ত গাড়ি থেকে। মার্কেজ এইভাবে দ্যাখেন মানুষ আর প্রকৃতিকে। তাঁর আর একটি গল্প আছে এক নিদ্রিতা সুন্দরীকে নিয়ে। সেই গল্পেও আছে ভয়ানক তুষারঝড়ের বিবরণ। শতাব্দীর ভয়ংকরতম তুষারঝড়ে বিমানের উড়ালও বন্ধ। নিদ্রিতা সুন্দরীকে দেখার প্রাকৃতিক পটভূমি ছিল এমনই। এয়ারপোর্টের প্রতীক্ষালয়ে এত মানুষের ভিড় যে তুষারঝড়ে বিধ্বস্ত সেই প্রতীক্ষালয় থেকে বেরিয়ে আসতে হলো লেখককে। দুপুরেই টের পাওয়া গেল এক জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীতে পরিণত হয়েছেন তারা। সাত রেস্তোরাঁ, অজস্র কাফেটারিয়া, ফাস্টফুডের দোকানে অগণিত মানুষের লাইন। ঘণ্টাতিনেকে সব ফুরিয়ে গেল। বাচ্চারা কাঁদছে। আটকে যাওয়া যাত্রীরা যূথবদ্ধ জনতায় রূপান্তরিত। সকালে একঝলক দেখেছিল যে সুন্দরীকে, সে ওই জনতার ভিতরে আছে, এই ভেঙে যাওয়া জাহাজের ভিতরে কোথাও। কী অসামান্য না সেই গল্প। কী নির্ভার! পরদিন যখন এয়ারপোর্ট সচল হয়, সেই সুন্দরী ঘটনাক্রমে তার পাশে। যে সমস্ত পথ ঘুমিয়েই কাটাল। রাতের অন্ধকারে তারাভরা আকাশের ভিতর দিয়ে আটলান্টিক পার হচ্ছিল সেই বিমান। সুন্দরী ঘুমিয়ে আছে। অবতরণের আগেই তার ঘুম ভাঙে। এক্সিকিউজ মি, বলে সে নিজের পথ করে নিয়ে নেমে যায় বিমান থেকে। নিদ্রিতা সেই সুন্দরীর জন্য তার যাত্রাসঙ্গী যে অত আকুল হয়েছিল, তা জানলই না সুন্দরী। বড়ো কথা বলেনি গল্প, কিন্তু যে সূক্ষ্মতায় গিয়েছে তা, পাঠ শেষে শূন্য প্রকৃতিই থেকে যায়। সবটা মিলিয়েই দেখা হলো যেন। তুষার ঝড় থেকে এই শূন্যতা অবধি।
মার্কেজের গল্পের প্রকৃতির ভয়ংকরতা, কল্পনা ও বাস্তবতা, অলীকতা আমাদের গল্পের সঙ্গে সেইভাবে কি মেলে? অথচ সমাজটির গড়ন যেন আমাদেরই মতো। ঠাকুমা দিদিমা’র কাছে বড়ো হওয়া, ছেলেবেলায় শোনা রূপকথা, জনশ্রুতি, লোককাহিনী, কল্পনা সবই তাঁর লেখার সূত্র। আর ১০০ বছরের নিঃসঙ্গতার সূচনা কীভাবে ঘটেছিল তাও তো আমাদের জানা। গল্প বলতে হবে কীভাবে তা তাঁর পিতামহী তাকে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই তো লেখেন, সরলা এরেন্দিরা আর তার নির্দয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য সেই গল্প। চৌদ্দ বছরের নাতনি এরেন্দিরা শাদা তিমির মতো অতিকায় এক বৃদ্ধা ঠাকুমার সেবা করেই যায়। তারা থাকে মরুভূমির ভিতরে একটি প্রাচীন বাড়িতে। মাফিয়া আমাদিসের জারজ কন্যা এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমার এই গল্প, বাস্তব, কল্পনা আর স্বপ্ন আর জাগরণ- সবই ভেঙেচুরে এগোতে থাকে। মরু প্রকৃতির নির্দয়তার সঙ্গে এরেন্দিরার বুড়ি ঠাকুমার নির্দয়তা যেন মিলেমিশে যায়। এই মহৎ লেখকের রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করে যেন মহাপ্রকৃতি। সমুদ্র পাহাড় অরণ্য, মরুভূমি আর মরুভূমির বাতাস। চৌদ্দ বছরের এরেন্দিরা ঠাকুমাকে ঘুম পাড়িয়ে ঘুমের ভিতরে বুড়ির বলা কথা, নানান নির্দেশ শুনতে শুনতে গভীর রাতে বাকি কাজ সেরে ক্লান্ত শরীরে মোমবাতিটিকে টেবিলের ওপর রেখে ঘুমোতে যায় যখন, সেই জ্বলন্ত মোমবাতি দুর্ভাগ্যের মরু বাতাসের ঝটকায় পর্দায় গিয়ে পড়ে, আর তার ফলে আমাদিসদের (যারা আসলে ছিল মাফিয়া চোরাচালানকারী) সেই মরুপ্রাসাদ আগুনে ভস্ম হয়। এরেন্দিরার ওই দুর্ষ্কমের (!) জন্য। সেই ক্ষতিপূরণ করতে হবে চৌদ্দ বছরের এরেন্দিরাকেই। আরম্ভ হলো এরেন্দিরাকে দিয়ে ক্ষতিপূরণের কাজ। এই কাহিনী এক ভয়ংকরতার দিকে যাত্রা করা চৌদ্দ বছরের সদ্য প্রস্ফুটিত এরেন্দিরার সঙ্গে। এ হতে পারে, ওইটিই দস্তুর সেই মরুপ্রকৃতিতে। এরেন্দিরার ঠাকুমার ওইটিই জানা ছিল। এইটিই স্বাভাবিক। মরুপ্রকৃতির নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এরেন্দিরার ঠাকুমার নিষ্ঠুরতা মিশে গেছে এই গল্পে। সেই পিতামহী যেন মহাজাগতিক নিষ্ঠুরতা নিয়ে ক্ষতিপূরণের জন্য এরেন্দিরাকে ব্যবহার করতে থাকে। চৌদ্দ বছরের মেয়েকে শোধ করতে হবে ভস্মে যাবতীয় ক্ষতির দাম। এরেন্দিরা জানত এইটিই যেন স্বাভাবিক। এমনই হয়ে থাকে। বুড়ি ঠাকুমা বলেছে, ওই ক্ষতিপূরণের জন্য নাতনির একটি জীবনই যথেষ্ট নয়। সুতরাং এরেন্দিরাকে যেতে হয় অল্প বয়সে বিপত্মীক হওয়া হাড়-চামড়াসর্বস্ব সেখানকার এক দোকানদারের কাছে। ওই মরুদেশে কুমারীত্বর জন্য লোকটা ভালোই দাম দিয়ে থাকে। সে এসে এরেন্দিরার ঊরু দুটির শক্তি, পাছা এবং স্তনের মাপ নিয়ে একটা দর বলল। দরাদরি হয়ে দুশো কুড়ি পেসোয় তা স্থির হতে লোকটা এরেন্দিরাকে কঠিন হাতে দমন করে ভোগ করে। এরপর এরেন্দিরাকে ভোগ করে গাঁয়ের আরও লোক। ঠাকুমা তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে থাকে। গাঁয়ে যখন আয়ের আশা থাকে না, ঠাকুমা তাকে নিয়ে যাত্রা করে চোরাচালানকারীদের এলাকার দিকে। ঠাকুমা আর এরেন্দিরা, এরেন্দিরাকে নিয়ে ঠাকুমার ব্যবসা, এই গল্পে ওই বৃদ্ধা পিতামহী এক পুরাণ-প্রতীম চরিত্র হয়ে উঠেছে। ল্যাটিন আমেরিকার যে-কোনো দেশের আত্মা এরেন্দিরা, আর তার নিষ্ঠুর ভবিতব্য রচয়িতা ওই ঠাকুমা। মরুভূমির ভেতরে এরেন্দিরাকে নিয়ে তার ব্যবসা যতই ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে, তাঁবুর সামনে যত লাইন পড়তে থাকে, ঝুলিতে যত পেসো এসে জমা হতে থাকে, বুড়ি হয়ে উঠতে থাকে আরও ভয়ানক। এরেন্দিরা ছিল কুমারী মৃত্তিকার মতো, তাকে ব্যবহার করে করে, তাকে বিক্রি করে করে বুড়ি তার ক্ষতিপূরণ তুলে নিতে থাকে। সেই পিতামহ ঘুমের ভেতরেও যেন সমস্ত কিছু দেখতে পায়। তাকে এড়ানো বড়ো কঠিন। এরেন্দিরা ব্যতীত বুড়ি তার জীবন সে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বুড়ি নজরে নজরে রাখে। সমস্ত দিন তাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে যখন নিঃশেষিত, তখন ছাড় দেয়। এরেন্দিরাকে মিশনারিরা উদ্ধার করে তাদের আশ্রমে নিয়ে গেলেও বুড়ি কত কৌশলে তাকে ফিরিয়ে আনে। আর সেই মেয়েও জেনে গিয়েছিল ঠাকুমা ছাড়া তার বাঁচার উপায় নেই। সেই এরেন্দিরার প্রেমে পড়ে চোরাচালানকারীদের একজনের ছেলে ইউলিসিশ। মার্কেজ কি এক লৌকিক অলৌকিকে মোড়া কাহিনীই শুনিয়েছেন আমাদের? সেই ঠাকুমা এমনই শক্তিময়ী হয়ে ওঠে, তার মৃত্যুও হয় না বিষে। বিষ পান করেও সে তিন দিন ধরে গান গেয়ে যায়। তাকে মারতে চেয়েছিল এরেন্দিরা ও তার প্রেমিক। বুড়ি যেন রূপকথার রাক্ষসীর মতো হয়ে ওঠে। মৃত্যু নেই। তাকে মারার শক্তিই অর্জন করেনি এরেন্দিরার প্রেমিক। শেষ অবধি তাকে ছুরি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে হত্যা করে ইউলিসিশ। রক্তাক্ত ঠাকুমাকে স্পর্শ করে যখন এরেন্দিরা নিশ্চিন্ত হয় সে মরেছে, ঠাকুমা’র সোনার থলেটি হাতিয়ে প্রকৃত পরিণতর মতো এরেন্দিরা একা একা পালায়। সে বুঝি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে নিতে সোনার থলে হাতে ছুটতে থাকে শহরের মধ্য দিয়ে। ইউলিসিশ তাকে ডাকে, সে ফেরে না। ইউলিসিশের ডাক যেন সন্তানের ডাকের মতো শোনায়, সে ফেরে না। তখন সমুদ্র শেষ হয়ে স্বাভাবিক মরুভূমি শুরু হয়েছে। মাথা না ঘুরিয়ে জেলখানা, সোনার খনি, অভ্রের খনি পেরিয়ে গেল এরেন্দিরা। তীক্ষè বাতাস আর অশেষ সূর্যাস্ত পেরিয়ে সে ছুটে যায়। ওই উপমহাদেশের আত্মাকে চিনতে পারি আমরা। টের পাই এই বাস্তবতা আমার স্বদেশের বাস্তবতাও। অ্যালিগরি ধরা যায়। আমি এখনো ভুলিনি সেই অল্প বয়সে পড়া তলস্তয়কে। ক্রয়েটজার সোনাটা কিংবা ইভান ইলিচের মৃত্যু। এরেন্দিরার এই কাহিনী সেই রকমই আমার সঙ্গী হয়ে থাকল। মার্কেজ যে গল্প লিখেছেন, সেই গল্প আমাদের এই দেশে আপাতভাবে ঘটে না মনে হয়, শেষে মনে হয় এ আমার দেশেরই গল্প। অন্য কাহিনীই এই কথা বলতে পারত।
একটা দীর্ঘ গল্প “আমি শুধু একটি ফোন করতে এসেছিলাম” পড়তে পড়তে আন্তন চেখভের ওয়ার্ড নাম্বার সিক্সের কথা আবছা মনে এসে যায় সত্য, কিন্তু পরে যখন বুঝে নিতে থাকি সমস্তটা, স্তম্ভিত হই। কিছুই না। শুধু নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য অথচা কৌতুক অথবা কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনিই মারিয়াকে উন্মাদাশ্রমে ঢুকিয়ে দিল উন্মাদাশ্রমের গাড়ির পরিচালিকা। মারিয়ার গাড়ি রাস্তায় খারাপ হয়েছিল। সে ফিরছিল তার জাদুকর স্বামীর কাছে। সন্ধ্যায় তার সঙ্গে প্রোগ্রাম করতে বেরুতে হবে তাকে। গাড়ি হাইওয়ের ভেতরে খারাপ হলে মারিয়ার দরকার ছিল তার স্বামী সার্তুণোকে একটা ফোন করে খবর দেয়া, তার যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে গেছে। হাইওয়েতে কোন গাড়িই দাঁড়ায় না। মারিয়া খুব বিপদে পড়েছিল। টিপটিপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। তখন একটি বাস এসে দাঁড়ায়। মারিয়া ছুটে গিয়ে তার বিপন্নতার কথা জানায়। তার একটা ফোন করা দরকার। বাসের যাত্রীরা সবাই অন্ধকারে কম্বল মুড়ি দিয়ে আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল যার যার সিটে। মারিয়াকে তুলে নিল বাস। ঠা-ায় সে জমেও যাচ্ছিল। পরিচালিকা একটি মোটাসোটা মহিলা। তাকে মারিয়া একটি সিগারেট দেয়। তার সঙ্গে নিজের কথা বলে। সে চুপ করতে বলে মারিয়াকে। অবশেষে সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনের যাত্রা শেষ হয় সন্ধ্যার অন্ধকারে। বাস এসে পৌঁছল একটি প্রাচীন প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকার সম্মুখে। বাসের পরিচালিকা সকলকে নামিয়ে দেয় সেখানে। নিচে দাঁড়ানো রক্ষীরা বাসের যাত্রীদের টেনে-হিঁচড়ে নামায়। মারিয়াকে নেমে যেতে বলে সেই পরিচালিকা। মারিয়ার কাছ থেকে সে একটি সিগারেটও চায় নামিয়ে দেয়ার আগে। মারিয়া ভিজে প্যাকেটটাই দিয়ে দেয়। নামার সময় আবার জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে একটা ফোন করা যাবে কি? হ্যাঁ যাবে। উত্তর পেয়ে মারিয়া নেমে যায়। বাস চলে যায়। মারিয়া উন্মাদ আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পড়ে। আর বন্দি হয় সেখানে। উন্মাদ হিসেবে তার নাম রেজিস্টারে ওঠে। মারিয়াকে কি উন্মাদ ভেবেই বাসে তুলেছিল সেই পরিচালিকা রমণী। হতে পারে না। আবার উন্মাদ আশ্রমের পরিচালিকা হয়ে সে হয়তো স্বাভাবিক মানুষকে কল্পনা করতে পারে না। আবার এও হতে পারে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে সে স্বাভাবিক মারিয়াকে উন্মাদ আশ্রমে ঢুকিয়ে দিল। এটা তার কাছে যেন খেলার মতো। মারিয়ার কাছ থেকে সিগারেট চায়ও শেষে। কেন সে এই নিষ্ঠুরতার ভেতরে মারিয়াকে সমর্পণ করল? সে কি জানত না কী হতে পারে মারিয়ার ভবিষ্যৎ? না জেনে করল এই কা-টি? না কি জেনেই একটি কৌতুক! গল্পটি হাড় হিম করে দেয়। তার পরিণতি ভয়ংকর। উন্মাদাশ্রমের লোকজন জানত। বাস্তবে জাদু জাদুর বাস্তবতা। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতায় তাদের তুমুল আনন্দ। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয়, এমন ঘটনা, এই কৌতুক কিংবা নিষ্ঠুরতা ঘটেই চলে এইসব রাষ্ট্র শাসনকালে। উন্মাদ আশ্রম একটি স্বাভবিক মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে দিল, এই ঘটনাই তো অন্য কাহিনীর মোড়কে বিশ্বব্যাপী ঘটে চলে। এই কৌতুক বা এই দয়ামায়াহীনতা মানুষের ধর্ম। এরেন্দিরার ঠাকুমা হয়তো জানত না ওইটির ন্যায় অন্যায়। সেই মরুভূমিতে দুর্ভাগ্যের হাওয়া সমস্ত সময় বয়ে যায়, তাই যেন বয়েছিল এরেন্দিরার অতটা জীবনজুড়ে। মেয়ে মানুষ টাকা উপায়ের যন্ত্র, ঠাকুমার ভেতরে এই ধারণাটিই ছিল স্পষ্ট। আর এরেন্দিরা তো তার পুত্র আমাদিসের জারজ কন্যা। তাকে ওসব করতেই হবে। বুড়ির একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ধরা যায়। কিন্তু মারিয়ার ভবিতব্য যে নির্ধারণ করে দিয়ে মারিয়ার দেয়া সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বাসের সঙ্গে চলে গেল, তাকে চেনা যায় না। শুধুমাত্র ইচ্ছে হয়েছিল তার, তাই তাকে উন্মাদাশ্রমে ভরে দিল। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার অনুভূতিতে জারিত হয়ে যাই এই গল্পের ভেতরে প্রবেশ করে। মারিয়ার স্বামীর কাছে খবর পাঠাতে তাকে অনেক প্রতিদান দিতে হয়। হায় রে দুর্ভাগ্য। মারিয়ার স্বামীও বিশ্বাস করে ফেলে তার স্ত্রী উন্মাদ হয়ে গেছে। এইটা কেন ঘটেছিল, তা অনিশ্চয়তায় থেকে যায়। এই নতুন বিশ্বের শাসকের ধর্ম দেশের মানুষের স্বৈরাচারী শাসনে থাকার অভিজ্ঞতা সেই দেশের কথাসাহিত্যে নতুন আঙ্গিক দিয়েছিল যে তা মার্কেজ পড়লে ধরা যায়। মার্কেজের লেখার ভেতরে জীবন ও সময়ের অনিশ্চয়তাকে অনুভব করা যায়। এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার যেন মিল আছে। মিল আছে প্রকৃতির রোষের। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেলে তাই-ই হয়। খুব ছোটো একটি গল্প ‘মোনতিয়েলের বিধবা’র কথা বলি। হোসে মোনতিয়েল মারা গেলে সেই শহরের মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য। তারা ভাবত হোসে মোনতিয়েল হয় তো কোন নির্জন স্থানে কোনো আততায়ীর হাতে নিহত হবে। কিন্তু সেই ভয়ানক লোকটি মারা গেছে আচমকা, ক্রোধ সংবরণ না করতে পেরে। ডাক্তারের নিষেধ ছিল। মোনতিয়েলের স্ত্রী ভেবেছিল তার স্বামী রোগ শয্যায় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে মরবেন। তা হয়নি। মোনতিয়েল মারা গেলে শহর ভেঙে পড়েনি। লোকটাকে ভয় করত শহরবাসী। মনে মনে ঘেন্নাও। তার ছেলেমেয়েরাও আসেনি। দায়সারা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। মোনতিয়েলের বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেকেও যেন লোকসমাজ থেকে বিযুক্ত করে কফিন বন্দি করে ফেলল। সেই হলো মোনতিয়েলের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এই মহিলা অতি সাধারণ। মোনতিয়েল লোকটির কুকর্মে তার সায় ছিল না। তার উপরে নির্দেশ ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিরোধীদের শহর ছাড়া করতে হবে। হোসে মোনতিয়েল ছিল এক সাধারণ ভদ্র ব্যবসায়ী, সে হয়ে উঠল মেয়রের বিশ্বস্ত অনুচর। সে মেয়রের সঙ্গে বসে যাবতীয় হত্যার পরিকল্পনা করত। গরিব মানুষকে ময়দানে দাঁড় করিয়ে পুলিশ গুলি করত, আর ধনীদের ২৪ ঘণ্টা সময় দেয়া হতো শহর ছেড়ে যাওয়ার। সমস্ত দিন পাইকারি হত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা করত যখন মোনতিয়েল, তার স্ত্রী মৃত ব্যক্তিদের জন্য অশ্রুপাত করত। মেয়র চলে গেলে স্ত্রী মোনতিয়েলের সামনে এসে বলত, ওই লোকটা খুনি, যে করে হোক ওকে শহর থেকে বিদায়ের ব্যবস্থা করো সরকারকে বলে। মোনতিয়েল ক-বছরেই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছিল সেই গুপ্ত পুলিশের সার্জেন্ট মেয়রের সঙ্গী হয়ে। হত্যা, আতঙ্কগ্রস্ত করিয়ে শহর থেকে ধনীদের বিতাড়ন গরিব মানুষকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারা ইত্যাদি মোনতিয়েলের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল। একটা শহর, একটা দেশ যখন গুপ্ত পুলিশ বাহিনী, স্বৈরাচারীর দ্বারা শাসিত হয়, তখন কী হতে পারে তার খানিকটা স্বাক্ষর এই গল্প। মার্কেজের সমস্ত গল্পেই যেন সেই ছায়া ছড়িয়ে আছে। হোসে মোনতিয়েল কীভাবে মস্ত ধনী হয়ে উঠল, তা কোন দেশে সত্য নয়? এই মোনতিয়েলকে কি আমরা অন্য চেহারায় দেখিনি। আসলে মার্কেজ আমাদের গল্পই বলেছেন ওই দেশে বসে। মোনতিয়েলের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে শহরের মানুষ নিঃশব্দে শোধ নিচ্ছিল তাদের ওপর মোনতিয়েলের অত্যাচারের। মোনতিয়েলের যে ব্যবসা তার বেঁচে থাকার সময় রমরম করে চলত, তা আর চলছে না। উঠোনে দুধভর্তি পাত্রে দুধ পচে যাচ্ছে, চাকেই নষ্ট হচ্ছে মধু। খামারের অন্ধকার ভাঁড়ারে রাখা পনিরে পোকা জন্মাচ্ছে। এত কম সময়ে ওই শহরে কেউ অত বড়লোক হয়নি। মৃত্যুর পর মোনতিয়েলের বাড়িতে কেউ আসে না। ধন-সম্পত্তি নিয়ে যক্ষের মতো বসে আছে যেন তার বিধাতা। রাজনৈতিক ও গুপ্ত হত্যায় ভরা সেই সব দেশের গল্পে আমরা আমাদের দেশকেও চিনতে পারি গোপনে। সে ভাগ্যবান, ফ্রাঊ ফ্রিডা ভাগ্যিস তাকে স্বপ্নে পেয়েছিলেন। তারপর তার সঙ্গে লেখকের দেখা হয় বার্সিলোনায়। সেই সাক্ষাৎকারকে এখন তাঁর মনে হয় রহস্যময়। পাবলো নেরুদা সেদিন বার্সিলোনায় পা রেখেছিলেন স্পেন যাওয়ার পথে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মাতিলদে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় নেরুদা ফরাসিদের মতো শুধু রান্নার গল্প করে যাচ্ছিলেন। আর খেতে খেতে আচমকা তিনি লেখককে বলেছিলেন, পেছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে কেউ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। গল্পের বাস্তবতাকে তিনি এইভাবে জীবনের সত্যের মতো করে তুলতে পারেন। এখানে নেরুদার সঙ্গে দেখা হলো সেই স্বপ্ন ফেরি করা মহিলার। তর্জনীতে সাপের নকশার আংটির জন্য তাকে বহুদিন বাদে দেখেও চিনেছিলেন লেখক। নেরুদা যে জাহাজে এসেছিলেন, সেই জাহাজেই তিনি ছিলেন। কিন্তু তাদের দেখা হয়নি। তাকে অনুরোধ করতে তিনি এসে বসেছিলেন তাদের টেবিলে। মহিলাকে স্বপ্ন দেখার শক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করেছিলেন লেখক। তখন নেরুদা বলেছিলেন, স্বপ্ন কোনোদিন ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। পারে কবিতা। স্বপ্নের দৈবী শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। দুপুরে নেরুদা বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক ১৫ মিনিট বাদে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, তিনি বলেছিলেন, স্বপ্নে ওই মহিলাকে দেখেছেন। কী দেখেছেন, না ওই মহিলা তাকে স্বপ্নে দেখছেন, তাই। স্বপ্ন আর বিভ্রম তৈরি করেন নেরুদা। যে কথাটি বললেন, তা যেন বোরহেসের গল্প। বিকেলে সেই জাহাজের ডেকে দেখা হলো সেই ফ্রাউ ফ্রিডার সঙ্গে। তিনি ঠিক একই কথা বললেন। তিনিও স্বপ্ন দেখেছেন যে নেরুদা তাকে স্বপ্ন দেখছেন দুপুরে। এই বিভ্রমের ভেতরে গল্প ঢুকে যায়। গল্পটি আরম্ভ হয়েছিল হাভানার রিভিয়েরা হোটেলে। লাঞ্চ সারছিলেন লেখক। ঝলমলে দুপুরে আচমকা এই সামুদ্রিক ঢেউ আর ঝড়োবাতাস কয়েকটা গাড়িকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর তার চালক মহিলার হাতে সেই সাপের নকশা করা আংটি। মহিলা মারাই গেছেন। সেই মহিলা, যিনি কী করতেন, না স্বপ্ন দেখতেন। নিজের ভবিতব্যকে তিনি নিশ্চিত দেখতে পাননি। মার্কেজ ঠিক এমন, যার গল্পই যেন স্বপ্ন আর জাগরণের ভেতরে কোন এক মুহূর্তে লেখা হয়েছিল। তাকে পাঠ মানে গোটা ল্যাটিন আমেরিকা, আর তৃতীয় বিশ্বকে পাঠ। আর এই পাঠ একবারে শেষ হয় না। বারে বারে নতুন স্বপ্ন আর নতুন জাগরণ উন্মোচিত হয়ে যায় মার্কেজ পাঠে। বাস্তবের জাদু হয়ে যায় জাদুর বাস্তবতা। এইসব গল্প এই পৃথিবীর বাতাসে, আলোয় অন্ধকারে ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের ভেতরে লীন হয়েছিল। তাকে খুঁজে বের করেছেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।
-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ
-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা
-
সাময়িকী কবিতা
-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস
-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ
-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো
-

কবি নওশাদ নূরী
-

আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ