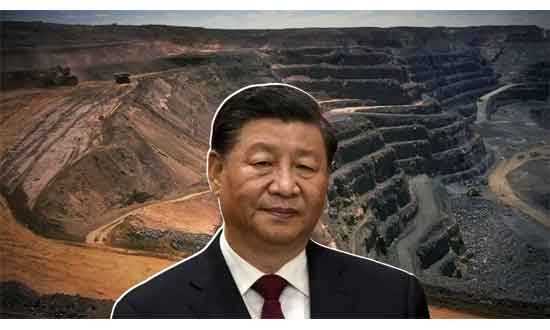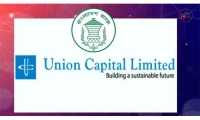news » business
বিরল খনিজ শিল্পে চীনের আধিপত্য একচেটিয়া
ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত
বর্তমানে বিরল খনিজের অধিকাংশ পরিমানই চীনের হাতে। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, কয়েক দশকের পরিকল্পনা, ভর্তুকি ও কৌশলগত অধিগ্রহণের মাধ্যমে চীন খনিজ উত্তোলন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সবচেয়ে সাশ্রয়ী উৎপাদক হিসেবে নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছে।
এই আধিপত্য বাণিজ্যেও প্রভাব ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে চীন এই বিরল খনিজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন সরাসরি অভিযোগ করেছেন- চীন ‘প্রভাব বিস্তার, নির্ভরশীলতা ও ব্ল্যাকমেইলের ধারা’ বজায় রেখেছে; প্রতিযোগীদের বাজার থেকে ছিটকে ফেলতে তারা এ কাজ করছে।
তথ্য বলছে, পশ্চিমা অভিযোগের পর রপ্তানি কিছুটা বাড়ালেও চীন এখনো কঠোরভাবে নজরদারি করছে, যাতে বিদেশে এই মৌলের মজুদ গড়ে তোলা না যায়। বর্তমানে বিরল খনিজ খননের ৭০ শতাংশ, প্রক্রিয়াজাতকরণের ৯০ শতাংশ আর চুম্বক তৈরির ৯৩ শতাংশই চীনের হাতে। অথচ দাম তুলনামূলকভাবে কম রেখে তারা নতুন প্রতিযোগীদের বাজারে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করেছে। ফলে পশ্চিমাদের বিকল্প সরবরাহ গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্লেষক গ্রেসলিন বাসকারান বলেন, চীন উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়ায় না, বরং বাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে প্রয়োজনমতো সম্পদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।
চীনের এই নিয়ন্ত্রণ এক দিনে হয়নি। ১৯৯০-এর দশকে শিথিল পরিবেশ আইন আর অগণিত ছোট ছোট খনির মাধ্যমে দেশজুড়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময়ে কৌশলগতভাবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের জিএমের ম্যাগনেট বিভাগ ও ফরাসি কোম্পানি ইউজিম্যাগ অধিগ্রহণ করে উৎপাদন ব্যবস্থা চীনে সরিয়ে আনে। ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে শেষ দুটি চুম্বক কারখানাও ২০১০ সালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।
জাপান তখন চীনের অনানুষ্ঠানিক রপ্তানি নিষেধাজ্ঞায় মজুত করতে শুরু করে। অন্যদিকে চীন পর্যায়ক্রমে এই খাত রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এখন চীনের দুটি বৃহৎ কোম্পানি-চায়না নর্দার্ন রেয়ার আর্থ ও চায়না রেয়ার আর্থ গ্রুপ পুরো শিল্প নিয়ন্ত্রণ করছে।
পশ্চিমা দেশগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। জি-৭ সম্প্রতি মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। লক্ষ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে চীনের অতি সস্তা চুম্বক পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। যুক্তরাষ্ট্র আরও এগিয়ে গিয়ে এমপি ম্যাটেরিয়ালসকে দ্বিগুণ দামে ধাতু কিনে দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রতিরক্ষা খাত ছাড়া উচ্চ মূল্যের বিকল্প পণ্যের চাহিদা সীমিতই থাকবে।
বিশ্লেষক গ্যারেথ হ্যাচের ভাষায়, পশ্চিমা কোম্পানির মন্ত্রই ছিল- যেভাবেই হোক সবচেয়ে কম খরচে পণ্য আনা। যখন সস্তা বিকল্প বাজারে আছে, তখন বেশি দামে কেন কিনবে?
চীনের আধিপত্য শুধু বিরল খনিজেই নয়- অনেক পণ্যের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে চীনের তৎকালীন নেতা দেং জিয়াওপিং বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে তেল আছে আর চীনের আছে বিরল খনিজ। এরপর ১৯৯০-এর দশকে শিথিল পরিবেশ আইন ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খননকার্য দ্রুত বেড়ে যায়। উত্তর মঙ্গোলিয়ায় হাজারো অবৈধ খনি থেকে হালকা বিরল খনিজ উত্তোলন শুরু হয়। দক্ষিণে ছোট ছোট খনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটির স্তর থেকে ভারী খনিজ আলাদা করত।’
চীন যেভাবে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নেয়: চীন শুধু খনিই নয়, পুরো মূল্যশৃঙ্খলেরও নিয়ন্ত্রণ নেয়। ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান চায়না ননফেরাস মেটালস ইন্ডাস্ট্রি কর্প ও বেইজিং সান হুয়ান নিউ ম্যাটেরিয়ালস, যার নেতৃত্বে ছিলেন দেং জিয়াওপিংয়ের দুই জামাতা- মার্কিন বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে মিলে জেনারেল মোটরসের (জিএম) ম্যাগনেট বিভাগ ‘ম্যাগনেকোয়েঞ্চ’ কিনে নেয়। এরপর তারা ফরাসি কোম্পানি ইউজিম্যাগের বিরল খনিজ বিভাগও অধিগ্রহণ করে। কয়েক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এতে শ্রমিকেরা চাকরি হারান এবং মেশিনগুলো চীনের তিয়ানজিন ও নিংবো শহরের কারখানায় স্থানান্তরিত হয়।
বিদেশি প্রতিযোগীদের হটিয়ে দিতে বেইজিং রপ্তানি কোটার পাশাপাশি করনীতি ব্যবহার করে। ম্যাগনেট শিল্প-বিশেষজ্ঞ জন অরমরড বলেন, ‘যখন গাড়ি কোম্পানি চুক্তি করতে চাইত, তখন চীনে গিয়ে দাম জিজ্ঞেস করলেই আমাদের সেই দামে নামতে হতো। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না।’
যখন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার নতুন খনি খনন শুরু হয় তখন বেইজিং উৎপাদন কোটা আরও বাড়িয়ে দেয়। এতে দাম কম থাকে। পশ্চিমা ও চীনা খনি কোম্পানি কেউই লাভ করতে পারে না। বিশ্লেষক বাসকারান বলেন, ‘চীন ইচ্ছাকৃতভাবে দাম চেপে ধরে রেখেছে। বিকল্প উৎস তৈরি না হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ- এটা ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক নয়। তবু চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো কম মুনাফা নিয়েই বিনিয়োগ চালিয়ে গেছে। এখন তারা বিশাল আকার ধারণ করেছে। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে, বিশেষ করে ধাতু প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে; এই প্রযুক্তি বিদেশে রপ্তানি করায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।’
জন অরমরডের মতে, চীনের দাম মেনে নেওয়া অসম্ভব। যারা চুম্বক কিনবে, তাদের বাড়তি দাম মেনে নিতেই হবে। কারণ, তথাকথিত চীনা বাজারদরের নিচে আর নামা যাবে না।
এ অবস্থায় পশ্চিমা দেশগুলো নানা প্রতিকার খুঁজছে। জুন মাসে জি-৭ দেশগুলো ঘোষণা দিয়েছে, তারা মান নির্ধারণের ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেবে। বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে চীনের অতি সস্তা চুম্বক পণ্যের সীমা টানা সম্ভব হবে। জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র আরও বড় পদক্ষেপ নেয়। তারা লাস ভেগাসভিত্তিক এমপি ম্যাটেরিয়ালসকে নিশ্চিত করেছে-নিওডিমিয়াম-প্রাসিওডিমিয়াম দ্বিগুণ দামে কিনে নেবে সরকার, এমনকি ভবিষ্যতের মার্কিন কারখানা থেকে উৎপাদিত সব চুম্বকও কিনে নেবে।
তবে প্রযুক্তি খনিজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেকনোলজি ম্যাটেরিয়ালস রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা গ্যারেথ হ্যাচের সন্দেহ আছে। তিনি মনে করেন, প্রতিরক্ষা খাত ছাড়া পশ্চিমা কোম্পানিগুলো চীন ব্যতীত বিকল্প উৎস থেকে বেশি দামে কেনার আগ্রহ দেখাবে না। তার ভাষায়, পশ্চিমা কোম্পানির নীতি হলো, যেভাবেই হোক সবচেয়ে কম খরচে পণ্য আনা। যখন বাজারে সস্তা বিকল্প আছে, তখন কেন বেশি খরচ করবে।
-

শাক-সবজির পর এবার আটা-ময়দার দাম বৃদ্ধি
-

‘মবের ঘটনা’ উদ্বেগজনক, গ্রেপ্তারদের মুক্তির দাবি জাসদের
-

জুলাই মাসে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় কমেছে ৪৩ শতাংশ
-

ডিএসইর বাজার মূলধনে যোগ হলো ১০ হাজার কোটি টাকা
-

আরও ১৫ কোটি ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক
-

মূল্যস্ফীতি ৩ থেকে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনার কাজ চলছে: বাংলাদেশ ব্যাংক
-

২৭ দিনে এলো সাড়ে ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়
-

ডিএসইর ফিক্স সার্টিফিকেশন পেল আরও ১৩ ব্রোকারেজ হাউজ
-

রাষ্ট্রকে কবজা করে সুবিধা নিয়েছিলেন পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা: সেলিম রায়হান
-

২৭ দিনে প্রবাসী আয় এল ২ বিলিয়ন ডলার
-

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুনাফা বেড়েছে ৭,৩০০ কোটি
-
জুলাইয়ে ৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা, ১৫ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতা
-

ওয়ালটনের নতুন প্রিমিয়াম অ্যান্ড্রয়েড ট্যাব বাজারে
-

সোনার দাম বেড়েছে
-
পুঁজিবাজারে এআই ব্যবহার করে প্রতারণা, বিনিয়োগকারীদের বিএসইসির সতর্কতা
-

ডিজিটাইজেশন না হওয়ায় সময়ের কাজ সময়ে হয় না: এনবিআর চেয়ারম্যান
-

ইসলামী ব্যাংক লভ্যাংশ দেবে না
-

তালিকাভুক্তির পর প্রথম ‘নো ডিভিডেন্ড’, লোকসানে প্রিমিয়ার ব্যাংক
-

বেতনের ৬ গুণ প্রণোদনা পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মীরা
-

জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ
-

বিমানকে ব্যবসা সফল প্রতিষ্ঠানে গড়ার প্রতিশ্রুতি নতুন চেয়ারম্যানের
-
হিমাগারে আলুর ন্যূনতম দাম কেজিতে ২২ টাকা নির্ধারণ
-

চীন প্লাস্টিক ‘ডাম্পিং’ করলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে: বাণিজ্যসচিব
-

বেসরকারি খাতে যাবে নগদ, এক সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি: গভর্নর
-

শেয়ারবাজারে পতন: লেনদেন, সূচক, শেয়ারদর সবই কমেছে
-

৩ বছর ‘ব্যবসা না থাকলে’ ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স নয়
-

সেমিকন্ডাক্টর খাতের উন্নয়নে চীনের সঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ
-

‘করলে সঞ্চয় ২০০ টাকা, সরকার দেবে ৪০০ টাকা’