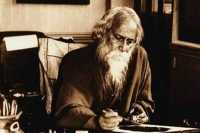উপ-সম্পাদকীয়
সাঁওতাল বিদ্রোহের চেতনা
মিথুশিলাক মুরমু
সাঁওতাল বিদ্রোহের চেতনাকে উজ্জীবিত ও উদীপ্ত করতে যে দু-একটি জায়গায় বিদ্রোহের নায়ক সিধু-কানুর ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, এটির মধ্যে বোচাগঞ্জ উপজেলার হাটরামপুর আদিবাসী পাড়া অন্যতম। নিজস্ব অর্থায়নে স্বাধীনতার শহীদদের আবক্ষমূর্তি খেলার মাঠের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। যোদ্ধাবেশে সিধু-কানুর হাতে রয়েছে আদিবাসীদের আদিমতম অস্ত্র তীর-ধনুক। মূলত, এটিই আদিবাসীদের আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের সম্মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তীরান্দাজ বাহিনীই।
সহজ-সরল আদিবাসী সাঁওতালরা দামিন-ই-কো অঞ্চলের গভীর অরণ্যকে পরিষ্কার করেছিল। অতঃপর ১৮২৩ খ্রি. কোম্পানির কর্তারা এই অঞ্চলের জমিকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। এবার আদিবাসী সাঁওতালদের পাশর্^বর্তী অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কারের লক্ষ্যে নিয়োগ দেয়া হয়। কোম্পানিরাজরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলÑ প্রথম তিন বছর খাজনা দিতে হবে না, পরে খাজনা দিতে হলেও তা খুবই সীমিত হারে ধার্য করা হবে। কোম্পানির লোভী কর্তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে ক্রমেই খাজনার ঊর্ধ্বগতির ধারা বজায় রেখেছিল। ভয়ঙ্কর হিং¯্র জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বসবাস উপযোগী করে তুললে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনে অনুমতি দেয়।
সাঁওতালদের চারপাশে গড়ে ওঠে গঞ্জ, সরকারি দপ্তরখানা, থানা ও আদালত প্রভৃতি। ঊনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ বারবার ঘটেছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর সাঁওতাল পরগণা জমিদারি এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সাঁওতালদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে জমির খাজনা আদায় করা হয়। পূর্বের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে তারা দামিন-ই-কো (বর্তমান রাজমহল পাহাড়তলী) এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অঞ্চল ছিল তখনকার ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। সাঁওতালরা আশা করছিল নতুনভাবে এখানে তাদের পক্ষে জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে কিন্তু জমিদার, মহাজন, সরকারি আমলা এবং বেপারিদের শোষণের হাত এখানেও বিস্তৃত হয়। ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ এবং ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে।
সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর নায়ক সিধুমুরমু জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ভগনাডিহি গ্রামে, আর কানু সিধু থেকে ৫ বছর ছোট অর্থাৎ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ভগনাডিহি সিধু-কানু, চাঁদ-ভৈরব, ফুলো-জানোদের নাড়িপোতা গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী সাঁওতালদের অবস্থা ও অবস্থান সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের অন্যতম স্বাধীনতাকামী বীরযোদ্ধাদের উত্তরসূরিদের সঙ্গে স্বল্প সময় কাটানোর প্রাক্কালে জানার চেষ্টা করেছি, আন্দোলনের চেতনার বিচ্ছুরণ ঘটলেও তারা কেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন! রাষ্ট্র, সরকার কিংবা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো কেউ-ই তাদের উত্তরসূরিদের সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পারেনি।
বাতির নিচেই অন্ধকার, এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সাঁওতাল পরগণার সর্বত্রই সিধু-কানু স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়; রাজপথ, পার্ক-উদ্যানের নামকরণ, ডাকটিকেট অবমুক্তকরণ এবং তাদের স্মৃতি ভাস্কর্য শহর-নগর-গ্রামে অসংখ্য নির্মিত হচ্ছে। ন্যায্য দাবি আদায়ের চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় করি কিন্তু উত্তরসূরি প্রজন্মের বিষয়ে যেন বিবেক অসাড় হয়ে যায়। ভাগ্যের নিমর্মতায় সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়করা ইংরেজদের জালে ধরা পড়েন। ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভগনাডিহির কাছে পাঁচকাঠিয়া বটবৃক্ষে বেলা পৌনে ২টা নাগাদ ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয় কানু মুুরমুুকে। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ¦ালিয় তুলব।’ ৪৫ মিনিট তার দেহটি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখার পর সেটিকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্বর ইংরেজ সরকার কানুর মৃতদেহটি তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দেয়ার সৌজন্য পর্যন্ত বোধ করেনি। বিশ^াসঘাতকদের সফলতায় বড়ভাই সিধু ধরা পড়েন ১ দিন আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং গুলি করে হত্যা করা হয়। বোধকরি, ইংরেজরা আন্দোলনের আলোকধারাকে নিভিয়ে দিতে সিধুর মৃতদেহকেও পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।
সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল চেতনার লড়াই, একপক্ষের রয়েছেÑ অর্থ, বিত্ত, অস্ত্র, বিদ্যা এবং ইংরেজ সরকারের সমর্থন। আর আদিবাসী সাঁওতালরা হৃদয়ে ধারণ করেছিল ন্যায্যতা, সত্য এবং অদম্য সাহস। অহিংসা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূচনা হলেও সেই ধারা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। তবে সমগ্র সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ সাহেবদের প্রতি সাঁওতালদের সম্মানবোধ, সৌজন্যতা এবং গভীর ভালোবাসাও ফুটে উঠেছে। তবে রাষ্ট্রনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। হাজারিবাগে বিদ্রোহের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ওই অঞ্চলের সাঁওতাল আদিবাসীরা বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। সাঁওতাল ও সিপাহিদের সম্মিলিত আন্দোলন ইংরেজদের পক্ষে এমনই গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করে যে, ডালটন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সিপাহি-আদিবাসী ঐক্য ইংরেজদের পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের কূটকৌশলের কাছে পরাজিত হতে হয়েছে, শিখ বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজরা বিদ্রোহী সাঁওতালদের দমন করতে সক্ষম হয়।
সাঁওতাল বিদ্রোহ বাংলার ভূখ-ের তেভাগা আন্দোলনকেও উদ্বেলিত করেছে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে শুরু হয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরব ছিল আন্দোলন। বর্গা বা ভাগ চাষিরা এতে অংশ নেয়। মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষি, একভাগ জমির মালিক এই দাবি থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। এর আগে বর্গা প্রথায় জমির সমস্ত ফসল মালিকের গোলায় উঠত এবং ভূমিহীন কৃষক বা ভাগ চাষির জন্য উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা আরো কম বরাদ্দ থাকত। যদিও ফসল ফলানোর জন্য বীজ ও শ্রম দুটোই কৃষক দিত। তৎকালীন পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন সংগটিত হয়। তবে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহীদ হিসেবে স্মরণীয় রয়েছেন দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলার তালপুকুর গ্রামের সমির উদ্দিন ও শিবরাম হাঁসদা। উল্লেখ্য যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি বালুরঘাট খাঁপুর গ্রামে পুলিশের প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষে শহীদ হন ২২ জন; এদের মধ্যে সাঁওতাল কমরেড হোপন মার্ডী, মাঝি সরেন, থোতো হেমব্রম, নারায়ণ মুরমু উল্লেখযোগ্য।
বাংলার ভূখ-ের সাঁওতালরা আজো নির্যাতিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত; বিদ্রোহের চেতনা টনটন থাকলেও শরীর নিস্তেজ, আত্মা দুর্বল। একবিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্র, সরকার আদিবাসীদের অব্যক্ত কথাগুলো উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ৩০ জুন ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস। দেশের আনাচে-কানাচে সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণার্থে আয়োজিত আলোচনা ও স্মরণ সভা থেকে সেই অবর্ণনীয় অভিব্যক্তিগুলোই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সাঁওতাল কবি লিখেছেনÑ
‘হুল’ মানে তেজ; আনা চেতনার/ ‘হুল’ মানে ভীত ভাঙা পরাধীনতার। / ‘হুল’ মানে জাগরণ দেশপ্রেম গড়ার/ ‘হুল’ মানে আগামীর স্বপ্ন, স্বাধীনতার।
[লেখক : কলামিস্ট]
-
ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী আমূল সংস্কার জরুরি
-
বরেন্দ্রর মাটিতে আমের বিপ্লব : সম্ভাবনা ও সতর্কবার্তা
-
অবশেষে ‘হাসিনা’ গ্রেফতার
-
স্ক্যাবিস সংক্রমণের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয়
-
বাস্তবমুখী বাজেটের প্রত্যাশা : বৈষম্যহীন অর্থনীতির পথে কতটা অগ্রগতি?
-
কৌশল নয়, এবার প্রযুক্তিতে সৌদি-মার্কিন জোট
-
সিউল : স্বর্গ নেমেছে ধরায়
-
নাচোল বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র সংগ্রহশালা : সাঁওতাল স্মৃতি কেন উপেক্ষিত?
-

অন্ধকার সত্য, শেষ সত্য নয়!
-
বিয়েতে মিতব্যয়িতা
-
এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বঞ্চনার কথা
-
রোহিঙ্গা সমস্যা : বাহবা, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়
-
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়
-
প্রযুক্তির ফাঁদে শৈশব : স্ক্রিন টাইম গিলে খাচ্ছে খেলার মাঠ
-
রমগদ্য : সিরাজগঞ্জে ‘ব্রিটিশ প্রেতাত্মা’
-
বামপন্থা : নীতির সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা
-
দাবি আদায়ে জনদুর্ভোগ : জনশিক্ষা ও সুশাসনের পথ
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন