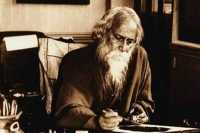উপ-সম্পাদকীয়
বাংলার মৃৎশিল্প
রাতিক হাসান রাজীব
বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শিল্প হলো মৃৎশিল্প। আবহমান গ্রাম-বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহন করে আসছে এই মৃৎশিল্প। মাটির নান্দনিক কারুকার্য ও মনের মাধুরি মিশিয়ে তৈরি করা এই শিল্পে ফুটে উঠে বাহারি নকশা। ‘মৃৎশিল্প’ শব্দকে ভাঙলে দুইটি শব্দ পাওয়া যায়, ‘মৃৎ’ শব্দের অর্থ মৃত্তিকা বা মাটি আর ‘শিল্প’ বলতে বোঝানো হয় সুন্দর ও সৃষ্টিশীল বস্তুকে। অর্থাৎ ‘মৃৎশিল্প’ বলতে বুঝায় মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে। ইংরেজিতে মৃৎশিল্পকে ‘পটারি’ বা ‘সিরামিক আর্ট’ নামে অভিহিত করা হয়। মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের বলা হয় ‘কুমার’ বা ‘কুম্ভকার’। কুমাররা বংশ পরম্পরায় দীর্ঘ সময় ধরে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।
মৃৎশিল্প মানুষের প্রাচীনতম আবিষ্কার। খ্রিস্টপূর্ব ২৯ হাজার থেকে ২৫ হাজার অব্দে নব্যপ্রস্তর যুগে এর সূচনা। ইতিহাস অনুযায়ী চীনের বিখ্যাত ‘থাংশান’ শহরে এই শিল্পের জন্ম। এ কারণে থাংশান শহরকে মৃৎশিল্পের শহর বলা হয়। চীনের পেইচিং শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পুর্বে থাংশান শহরের অবস্থান। এখানে পথে-প্রান্ত রে, পর্যটনকেন্দ্র ও পার্কগুলোতে মৃৎশিল্পের নানা কারুকার্যময় শিল্প দেখতে পাওয়া যায়।
আমাদের দেশেও এই শিল্পের ব্যবহার সেই আদিকাল থেকে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের উৎপত্তি মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে বগুড়ার মহাস্থানগড় খননের পর মাটির পাত্র পাওয়া যায়। ধামরাই মৃৎশিল্প বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত গ্রাম। ধামরাইয়ে বেশকিছু গ্রাম রয়েছে যেমন- কাগজিপাড়া, শিমুলিয়া পাল পাড়া, নোটুন বন্ধর ইত্যাদি। এই গ্রামগুলো তাদের মৃৎশিল্পের দক্ষতা ও বংশ পরম্পরায় পাল পরিবারের আবাসনের জন্য সুপরিচিত। মৃৎশিল্প প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম। মাটির নান্দনিক কারুকার্য ও বাহারি নকশার কারণে আদিকাল থেকে দেশে এর চাহিদা ব্যাপক। মৃৎশিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় নিমিষে তৈরি হয়ে যায় কারুকার্যময় সব জিনিসপত্র যেমন-মাটির পুতুল, ফুলদানি, বাসন-কোসন, হাড়ি-পাতিল, সরা, মটকা, সুরাই, পেয়ালা, পশু-পাখি, খেলনা, মাটির ব্যাংক ইত্যাদি।
মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি। এছাড়া উপকরণ হিসেবে দরকার জ্বালানি কাঠ, শুকনো ঘাস, খড় ও বালি। প্রধাণ উপকরণ মাটি হলেও সব ধরনের মাটি দিয়ে এই মৃৎশিল্প হয় না, প্রয়োজন পরিষ্কার এঁটেল মাটি। মাটির বুটনের ওপর ভিত্তি করে মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) বেলে মাটি- ঝরঝরে হয়, বালিকতার পরিমাণ বেশি, (২) দোআঁশ মাটি- বালি, পলি ও কর্দমকতা প্রায় সমান পরিমাণে থাকলে আঠালো হয় এবং (৩) এঁটেল মাটি- কর্দমকতার পরিমাণ বেশি থাকে, পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি এবং আঠালো হয়। এঁটেল মাটি বেশ আঠালো বলে এই মাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহার করা হয়।
মৃৎশিল্পের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও কালের বিবর্তনে আজ বিলীনের পথে। শিল্পায়নের যুগে ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য এই মৃৎশিল্প। এর পেছনের অন্যতম কারণ হলো-প্লাস্টিক পণ্যের সহজলভ্যতা। এছাড়া বাজারে যথেষ্ট চাহিদা মা থাকা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজের পরিধি বৃদ্ধি না করা, কাজের নতুনত্বের অভাব, আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের অসঙ্গতি, কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত মাটির মূল্য বৃদ্ধি, কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রী পরিবহনের সমস্যা। এছাড়া বর্তমানে প্লাস্টিক, স্টিল, ম্যালামাইন, সিরামিক ও সিলভারসহ বিভিন্ন ধাতব পদার্থের তৈরি তৈজসপত্রের নানাবিধ সুবিধার কারণে মৃৎশিল্পের বদলে এগুলো মানুষের পরিবারে জায়গা করে নিচ্ছে।
আগে যেখানে কুমারপারার লোকেরা ব্যস্ততায় দম ফালানো দায় ছিল তা আজ বিলীনের পথে। তবে বিলীনের পথে মৃৎশিল্পে জড়িত কেউ কেউ বাপ-দাদার স্মৃতিহিসেবে এখনো ধরে রেখেছে এই পেশা। আজও বৈশাখী মেলা, গ্রামীণ কিছু মেলায় পোড়ামাটির নানাবিধ কাজ, গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পুতুল, খেলনা, প্রতিমা, শো-পিসসহ অসংখ্য তৈজসপত্র দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও মৃৎশিল্পের জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘরে দেখা যায় সে সময়ের বাংলার কুমারপাড়ার চিত্র।
মৃৎশিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার সঙ্গে মিশে আছে গ্রামীণ বাংলার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকর্মকে টিকিয়ে রাখতে দরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি নানা ধরনের উদ্যোগ, তা না হলে অচিরেই হারিয়ে যাবে এক সময়ের অর্থনীতির চালিকা শক্তি ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি।
[লেখক : শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ]
-
স্ক্যাবিস সংক্রমণের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয়
-
বাস্তবমুখী বাজেটের প্রত্যাশা : বৈষম্যহীন অর্থনীতির পথে কতটা অগ্রগতি?
-
কৌশল নয়, এবার প্রযুক্তিতে সৌদি-মার্কিন জোট
-
সিউল : স্বর্গ নেমেছে ধরায়
-
নাচোল বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র সংগ্রহশালা : সাঁওতাল স্মৃতি কেন উপেক্ষিত?
-

অন্ধকার সত্য, শেষ সত্য নয়!
-
বিয়েতে মিতব্যয়িতা
-
এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বঞ্চনার কথা
-
রোহিঙ্গা সমস্যা : বাহবা, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়
-
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়
-
প্রযুক্তির ফাঁদে শৈশব : স্ক্রিন টাইম গিলে খাচ্ছে খেলার মাঠ
-
রমগদ্য : সিরাজগঞ্জে ‘ব্রিটিশ প্রেতাত্মা’
-
বামপন্থা : নীতির সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা
-
দাবি আদায়ে জনদুর্ভোগ : জনশিক্ষা ও সুশাসনের পথ
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”