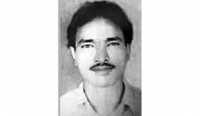opinion » post-editorial
আষাঢ়ী পূর্ণিমা : আত্মশুদ্ধির সাধনায় বুদ্ধের অনন্ত আলো
শতদল বড়ুয়া
আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র ও তাৎপর্যময় তিথি। এটি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; বরং ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা ও সমাজচিন্তার এক গভীর প্রতিফলন। বৌদ্ধ সমাজে এই দিনটি বহুমাত্রিক স্মৃতিচারণ, আত্মজিজ্ঞাসা ও পুণ্যসঞ্চয়ের দিন হিসেবে উদযাপিত হয়।
গৌতম বুদ্ধের জীবনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই পূর্ণিমা তিথির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদিন তিনি মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন, যৌবনে পরিবার ও বিত্ত-বৈভব পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগ করেন, বোধি লাভের পর বারাণসীর ইসিপতন মৃগদায় প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা প্রদান করেন। এই প্রথম ধর্মদেশনাই বুদ্ধবাণীর সূচনা, যা পরবর্তীতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।
এছাড়া এই দিনেই বুদ্ধ যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন, তাবতিংস স্বর্গে গমন করে মাতৃদেবীকে ধর্মদেশনা প্রদান করেন এবং ভিক্ষুসংঘকে বর্ষাব্রতের নির্দেশ দেন; যার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধ্যান ও সাধনার গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয়। বর্ষাব্রত পালনের প্রথা আজও সমানভাবে পালনীয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য এক ধ্যানমগ্ন আত্মশুদ্ধির সময়।
পুণ্যতিথির আচার-অনুষ্ঠান ও সমাজ-সম্পৃক্ততা আজকের আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সারাদেশের বিহারগুলোতে শুরু হয়েছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। ভোররাতে বিহার থেকে বিশ্বশান্তি কামনায় বিশেষ সূত্রপাঠের মধ্য দিয়ে দিনটি শুরু হয়। এরপর পঞ্চশীল ও অষ্টশীল প্রার্থনা, বুদ্ধ পূজা এবং সম্মিলিত বুদ্ধ বন্দনা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিহারগুলোতে দায়ক-দায়িকাদের অধিক উপস্থিতির কারণে একাধিকবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, গ্রামাঞ্চলে সাধারণত একবারেই পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং বুদ্ধ পূজা সম্পন্ন হয়।
এইসব আচার-অনুষ্ঠান শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সামাজিক বন্ধন, নৈতিক শিক্ষা এবং সামগ্রিক শুদ্ধাচারের অনুশীলন। আজকের দিনে বিশেষত শিশু-কিশোর ও তরুণদের বিহারমুখী করা, ধর্মচর্চার প্রতি উৎসাহিত করা এবং অহিংস, শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।
ভিক্ষুসংঘের পর্যায় ও ধর্মীয় জীবনচক্র ভিক্ষুসংঘ বৌদ্ধ ধর্মের ধারক ও বাহক। একজন শ্রমণ যখন উপসম্পদা গ্রহণ করে পূর্ণ ভিক্ষু হন, তখন থেকে শুরু হয় তার ‘বর্ষাবাস’ গণনা। এই বর্ষাবাসের ওপর ভিত্তি করে ভিক্ষুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়। এক থেকে নয় বছরের বর্ষাবাস প্রাপ্ত ভিক্ষু শুধুই ‘ভিক্ষু’ হিসেবে পরিচিত। দশ থেকে ঊনিশ বছর পর্যন্ত যারা ভিক্ষু জীবন যাপন করছেন, তাদের অনেক সময় ‘থেরো’ বলা হয়, যদিও ‘ভিক্ষু’ ও ‘থেরো’ পদবিগুলো নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ বছরের অধিক বর্ষাবাসপ্রাপ্ত ভিক্ষুরা ‘মহাথেরো’ বা ‘মহাস্থবির’ হিসেবে স্বীকৃত।
এখানে বয়স নয়, বরং বর্ষাবাসের সংখ্যা; অর্থাৎ ধর্মচর্চায় একনিষ্ঠ সময় হলো সম্মানের মাপকাঠি। তাই নব্বই বছরের একজন ব্যক্তি নতুন ভিক্ষু হলে তাকে একজন কিশোর কিন্তু অভিজ্ঞ ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হয়। এ এক অসাধারণ সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলার প্রতীক, যা বৌদ্ধ ধর্মের মহত্ত্ব প্রকাশ করে।
ভিক্ষু থেকে গৃহীজীবনে প্রত্যাবর্তন : একটি গভীরতর ভাবনা বৌদ্ধ সমাজে অনেক সময় দেখা যায় কেউ কেউ ভিক্ষু জীবন ত্যাগ করে আবার গৃহীজীবনে ফিরে যান। এ নিয়ে সমাজে নানা প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনা থাকলেও এটি একমাত্র তখনই প্রাসঙ্গিক হয় যদি সেই ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুশাসন ধারণ করে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। একজন সাবেক ভিক্ষু যদি পরিবারে ধর্মীয় নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবে তার ওই ধর্মজীবন মূল্যহীন নয়, বরং সমাজে আলো ছড়ানোর নতুন মাধ্যম।
বিদেশের কিছু বৌদ্ধপ্রধান সমাজে এমনকি একটি বরপক্ষের পাত্রকে নির্বাচনের সময় তার ‘ভিক্ষুজীবনের অভিজ্ঞতা’ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে ধরা হয়। তাদের বিশ্বাস, একজন ধর্মজীবী ব্যক্তি পারিবারিক দায়িত্বেও সংবেদনশীল, নীতিবান এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত হন।
তবে একসঙ্গে অনেক ভিক্ষুর গণহারে সংসারজীবনে ফিরে যাওয়া অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও গুরুবৃন্দের সতর্কতা, দিকনির্দেশনা ও সুচিন্তিত নীতিমালা প্রয়োজন।
আমরা সবাই যেন শুদ্ধচিত্তে, সদিচ্ছায়, সদ্ব্যবহারে বৌদ্ধ ধর্মের মহত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করি।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। দেশ হোক শান্তিময় ও সমৃদ্ধ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হোক আত্মজাগরণের নতুন সূচনা।
[লেখক : প্রাবন্ধিক]
-
নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য
-
আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে
-
জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে
-
পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা
-
সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত
-
অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স
-
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম
-
এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি
-
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ
-
ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে
-
রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”
-
কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা
-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’
-
স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য
-
ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি
-
ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য
-
তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
-
গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!
-
মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ
-
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি
-
হোক সবুজ বিপ্লব
-
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন
-
নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প
-
বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ
-
চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি
-
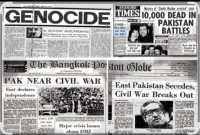
একাত্তরের গণহত্যা : সংখ্যার বিতর্ক নাকি দায় হালকা করার চেষ্টা?
-
রম্যগদ্য : ‘দালাল-ধন্বন্তরি-জীবন রক্ষাকারী...’