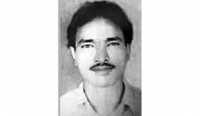opinion » post-editorial
পথশিশু ও বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির ব্যর্থতা
মতিউর রহমান
ঢাকা ও চট্টগ্রামের ব্যস্ত শহরগুলো, যা প্রায়শই প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতির কেন্দ্র হিসেবে চিত্রিত হয়, তাদের রাজপথের মধ্যেই সামাজিক উন্নয়নের বর্ণনার এক তীব্র বিরোধিতা বহন করে। আকাশচুম্বী ভবনের ছায়া এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের তীব্রতার মধ্যে, অসংখ্য পথশিশু এমন পরিস্থিতিতে বাস করে যা মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাঙনের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটায়।
এই শিশুদের উপস্থিতি কেবল একটি সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গভীর নৈতিক ব্যর্থতা যা সামাজিক চুক্তির পতন এবং এমিল ডুর্খেইমের তত্ত্ব অনুসারে অ্যানোমি অবস্থার উত্থানকে প্রকাশ করে। এটি টমাস হবস এবং জ্যাঁ-জ্যাক রুশো যে সামাজিক শৃঙ্খলার কল্পনা করেছিলেন তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যখন তারা সামাজিক চুক্তিকে একটি সংগঠিত এবং নীতিগত সমাজের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।
অ্যানোমি সম্পর্কে তার গুরুত্বপূর্ণ রচনায়, ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম সতর্ক করেছিলেন যে, সামাজিক রীতিনীতিগুলো যখন তাদের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তির আচরণকে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, তখন বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। সমাজের নিয়ন্ত্রক কাঠামো ভেঙে গেলে, ব্যক্তিরা একটি ভাগ করা নৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই অ্যানোমি বা আদর্শহীনতা দেখা দেয়।
বাংলাদেশের পথশিশুরা এই অ্যানোমি অবস্থার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রায়শই দারিদ্র্য, পারিবারিক সহিংসতা বা পরিত্যক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, এই শিশুরা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বহনকারী মৌলিক কাঠামো থেকে বঞ্চিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে নিয়ম প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রতিষ্ঠান, পরিবার, হয় অনুপস্থিত, অকার্যকর অথবা হিংস্র হয়ে ওঠে।
শিক্ষাব্যবস্থা, যা সামাজিকীকরণের দ্বিতীয় সুরক্ষা স্তর হিসাবে কাজ করা উচিত, প্রায়শই তাদের কাছে সহজলভ্য বা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না। রাষ্ট্র, তার কল্যাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, তাদের জীবনে প্রায় অদৃশ্য বলে মনে হয়, যা তাদেরকে ক্ষুধা, শোষণ এবং নিরাপত্তাহীনতার দ্বারা চিহ্নিত একটি নৃশংস অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করে। এই ধরনের সামাজিক শূন্যতায়, পথশিশুরা নৈতিক দিকনির্দেশনা বা সামাজিক সমর্থন ছাড়াই বেড়ে ওঠে যা অন্যরা গ্রহণ করে।
তারা অকাল প্রাপ্তবয়স্ক হতে বাধ্য হয়, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কাজ করে, মোড়ে মোড়ে ভিক্ষা করে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা ক্রমাগত হয়রানির সম্মুখীন হয়। তাদের জীবনে, সামাজিক সংহতি এবং যৌথ কল্যাণের আদর্শগুলো দূরবর্তী বিমূর্ততা বলে মনে হয়, দৈনন্দিন বেঁচে থাকার কঠোর বাস্তবতা দ্বারা আবৃত। ডুর্খেইম যুক্তি দেখান যে তাদের দুর্দশা বৃহত্তর সামাজিক অস্থিরতার লক্ষণ, যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে ছাড়িয়ে গেছে।
ডুর্খেইমের অ্যানোমি তত্ত্বের সাথে যুক্ত হয় সামাজিক চুক্তির ধ্রুপদী রাজনৈতিক দর্শন, বিশেষ করে ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস এবং ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাক রুশোর রচনা। হবস সামাজিক চুক্তিকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কল্পনা করেছিলেন যার মাধ্যমে ব্যক্তিরা, বিশৃঙ্খলা এবং সহিংসতার ভয়ে, তাদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু স্বাধীনতা সমর্পণ করে।
এর বিপরীতে, রুশো সামাজিক চুক্তিকে একটি সম্মিলিত চুক্তি হিসেবে জোর দিয়েছিলেন যা সাধারণ ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে একটি নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। হবসের বাস্তববাদ বা রুশোর আদর্শবাদের মাধ্যমেই হোক না কেন, সামাজিক চুক্তি ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ককে পূর্বাভাস দেয়। নাগরিকরা আইন মেনে চলে এবং সাধারণ কল্যাণে অবদান রাখে, যখন রাষ্ট্র তাদের অধিকার রক্ষা করে এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করে।
বাংলাদেশের পথশিশুরা এই চুক্তির লঙ্ঘনের স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এই শিশুরা সামাজিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসেনি, এমনকি এর শর্তাবলীও লঙ্ঘন করেনি। বরং, শুরু থেকেই তাদের এর সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। আর্থ-সামাজিক প্রান্তিক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে, তারা কখনোই রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা, শিক্ষা বা কল্যাণ উপভোগ করেনি।
এই আলোকে, পথশিশুদের অস্তিত্ব কেবল একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ নয় বরং একটি সাংবিধানিক ব্যর্থতা, যা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব এবং সুরক্ষার দাবির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রাষ্ট্র যখন তার সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তার নৈতিক এবং আইনি কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
পথশিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অনুপস্থিতি বাংলাদেশী সমাজের সম্মিলিত বিবেককেও ক্ষয় করে, যা ডুর্খেইমের সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। সম্মিলিত বিবেক বলতে সেই ভাগ করা বিশ্বাস, নৈতিক মনোভাব এবং মূল্যবোধকে বোঝায় যা একটি সমাজকে একত্রিত করে। যখন সমাজের বৃহৎ অংশ অর্থনৈতিক লাভ, রাজনৈতিক সুবিধা বা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুর্বল শিশুদের দুর্দশাকে উপেক্ষা করে, তখন এই ভাগ করা নৈতিক কাঠামো ভেঙে যেতে শুরু করে।
রাস্তার শিশুদের গাড়ির জানালায় ভিক্ষা করা, বাস স্টেশনে ঘুমানো বা ছোটখাটো শ্রমে লিপ্ত হওয়ার প্রতি জনগণের অনাকাক্সিক্ষত গ্রহণযোগ্যতা এমন একটি নৈতিক অসাড়তাকে প্রতিফলিত করে যা সামাজিক সংহতির কাঠামোকে ক্ষয় করে। এই শিশুদের ব্যর্থ করে সমাজ নিজেই ব্যর্থ হয়, সামাজিক জীবনের নৈতিক ভিত্তিকে ক্ষুণœ করে। এই নীরব উপেক্ষা কেবল শিশুদের বর্তমান দুর্দশাই নয়, বরং সমাজের ভবিষ্যৎ নৈতিক ভিত্তিকেও দুর্বল করে দেয়।
ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কারণ এটি কোনো সংকট নয় বরং একটি নিরন্তর অবহেলার প্রতিফলন। বছরের পর বছর ধরে, ধারাবাহিক সরকার, এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনগুলো পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলো এখনও খ-িত এবং অপর্যাপ্ত। আশ্রয়কেন্দ্র, ড্রপ-ইন সেন্টার এবং শিক্ষা কার্যক্রম, যতই মূল্যবান হোক না কেন, অভাবী মানুষের কাছে সামগ্রিকভাবে পৌঁছাতে পারে না।
মূল কারণগুলি মোকাবেলা করার কাঠামোগত সমাধানÑযেমন দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা, পারিবারিক সহায়তা এবং সর্বজনীন শিক্ষাÑএখনও অধরা রয়ে গেছে। এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতা রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সামাজিক অগ্রাধিকারের একটি গভীর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। জাতীয় বিতর্ক জিডিপি প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তরের উপর কেন্দ্রীভূত হলেও, পথশিশুদের নীরব দুর্ভোগ খুব কমই জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটি একটি জাতির অগ্রাধিকারের মধ্যে মৌলিক ত্রুটি নির্দেশ করে, যেখানে অর্থনৈতিক অর্জনগুলো মানব উন্নয়নের মৌলিক দিকগুলোকে ছাপিয়ে যায়।
পথশিশুদের দুর্দশা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি, যেমন জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার উপর জোর দেয়, তাদেরও চ্যালেঞ্জ করে। তার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের অধিকার সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হয়ে, জাতি বিশ্বব্যাপী তার নিজস্ব উন্নয়নমূলক আকাক্সক্ষা এবং নৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষুণœ করে। যখন একটি দেশ আন্তর্জাতিক ফোরামে মানবাধিকার এবং উন্নয়নের কথা বলে, অথচ তার নিজের অভ্যন্তরে অসংখ্য শিশু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এই সংকট কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, এটি বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশের অবস্থানকেও প্রভাবিত করে।
এই সংকট মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত সমাধান বা দাতব্য-চালিত হস্তক্ষেপের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। এটি সামাজিক চুক্তির পুনরুজ্জীবিতকরণের দাবি করে, যেখানে রাষ্ট্র তার মৌলিক দায়িত্বগুলোতে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং সমাজ তার সম্মিলিত বিবেককে জাগ্রত করে। নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই শিশু সুরক্ষাকে একটি আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে নয় বরং জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
পরিবার, স্কুল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামাজিকীকরণ এবং যতেœর কার্যকর এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য সমর্থন এবং সংস্কার করতে হবে। কল্যাণ রাষ্ট্রকে অবশ্যই এই শিশুদের বসবাসকারী অনানুষ্ঠানিক এবং প্রান্তিক ক্ষেত্রগুলোতে তার পরিধি প্রসারিত করতে হবে।
তাছাড়া, জনসাধারণের আলোচনাকে পথশিশুদের মানবতা এবং সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পরিবর্তন করতে হবে। তারা অপরাধী, বোঝা বা সামাজিক উপদ্রব নয়; তারা অধিকার এবং আকাক্সক্ষা সহ নাগরিক। তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মসূচিগুলি কেবল মৌলিক চাহিদা পূরণের উপর নয় বরং মর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং আত্মীয়তার অনুভূতি পুনরুদ্ধারের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।
এই সামগ্রিক পদ্ধতি রুশোর একটি নৈতিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণ সাধারণ কল্যাণে অবদান রাখে এবং ডুর্খেইমের জৈব সংহতির আদর্শের সাথে, যেখানে সমাজের প্রতিটি অংশ সমগ্রকে সমর্থন করে।
ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পথশিশুরা বাংলাদেশী সমাজের ব্যর্থতা এবং দ্বন্দ্বের প্রতিফলনকারী আয়না। তাদের দুর্দশা অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে, জাতীয় গর্ব এবং নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে ব্যবধান প্রকাশ করে। যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে এই শিশুরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়ে উঠবে, দারিদ্র্য, অপরাধ এবং বিচ্ছিন্নতার চক্রকে স্থায়ী করবে।
কিন্তু যদি সম্মিলিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাদের পুনর্বাসনকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি একটি রূপান্তরমূলক প্রকল্পে পরিণত হতে পারে, যা জাতির সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সদস্যদের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণ করবে এবং সামাজিক চুক্তির প্রতি বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করবে যা একটি জাতিকে একত্রিত করে। পথশিশুদের প্রতি আমাদের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া কেবল তাদের ভবিষ্যৎই নয়, বরং একটি জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব নৈতিক পরিচয়ও নির্ধারণ করবে।
[লেখক : গবেষক ও উন্নয়নকর্মী ]
-
নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য
-
আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে
-
জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে
-
পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা
-
সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত
-
অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স
-
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম
-
এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি
-
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ
-
ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে
-
রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”
-
কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা
-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’
-
স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য
-
ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি
-
ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য
-
তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
-
গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!
-
মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ
-
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি
-
হোক সবুজ বিপ্লব
-
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন
-
নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প
-
বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ
-
চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি
-
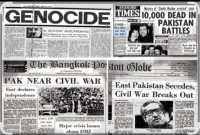
একাত্তরের গণহত্যা : সংখ্যার বিতর্ক নাকি দায় হালকা করার চেষ্টা?
-
রম্যগদ্য : ‘দালাল-ধন্বন্তরি-জীবন রক্ষাকারী...’