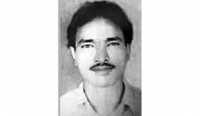opinion » post-editorial
আফ্রিকায় হঠাৎ কেন যুক্তরাষ্ট্রের ঝোঁক?
এম এ হোসাইন
একবিংশ শতাব্দীর ভূ-রাজনীতিতে একটি মধ্যাহ্নভোজও অনেক কিছু বলে দেয়। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আফ্রিকার পাঁচটি দেশেরÑগ্যাবন, গিনি-বিসাউ, লাইবেরিয়া, মরিতানিয়া ও সেনেগালÑনেতাদের সঙ্গে এমনই একটি সূক্ষ্ম অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক করেছেন। হাস্যোজ্জ্বল করমর্দন আর সৌজন্যমূলক কথাবার্তার আড়ালে ছিল এক সুস্পষ্ট বার্তাÑআফ্রিকার বিপুল খনিজ সম্পদের ওপর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে উঠেছে।
এই সম্মেলন দেখতে অনেকটাই রাশিয়া ও চীনের পূর্ববর্তী আয়োজনগুলোর মতো হলেও, পার্থক্য ছিল গভীরে। চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগ কিংবা রাশিয়ার সাহেল অঞ্চলে নিরাপত্তা জোটÑসবই কৌশলগত সফলতা পেয়েছে। অথচ ট্রাম্পের সম্মেলন ছিল একপ্রকার আত্মবিরোধী প্রচেষ্টাÑআফ্রিকাকে কাছে টানার চেষ্টার মধ্যেই ছিল অতীতের অবজ্ঞা, নীতি-অবিচার ও খোলাখুলি লেনদেনমুখী মনোভাবের ছাপ।
সম্মেলনের সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্তটি আসে যখন ট্রাম্প লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ বোয়াকাইকে জিজ্ঞেস করেন, “আপনি এত ভালো ইংরেজি কোথায় শিখলেন?”Ñবুঝতেই পারেননি যে ইংরেজি হলো লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রভাষা, আর দেশটি ১৯শ শতকের গোড়ায় মার্কিন সহায়তায় গঠিত হয়েছিল সাবেক আফ্রিকান-আমেরিকান দাসদের দ্বারা। এমন একটি দেশের ইতিহাসই যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই ইতিহাস ট্রাম্পের সামনে যেন অদৃশ্য।
অনেক আফ্রিকান বিশ্লেষকের চোখে এটি কেবল একটি নিছক ভুল ছিল না; বরং এটি ওয়াশিংটনের আফ্রিকা নীতিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি গভীর অজ্ঞতার প্রতীক। যেখানে চীন অভিজ্ঞ কূটনীতিক ও প্রকৌশলী পাঠিয়ে আফ্রিকান সরকারগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়শই শাসনব্যবস্থা নিয়ে উপদেশ দিতে আসে বা তারচেয়েও খারাপ, দম্ভ প্রদর্শন করে।
তবু এখন ওয়াশিংটন তার অবস্থান পাল্টাচ্ছে। আফ্রিকাজুড়ে পশ্চিমা প্রভাব হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটেÑবিশেষত মালি, বুরকিনা ফাসো এবং নাইজারে ফ্রান্সের মতো সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, তাদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু।
এই নতুন কূটনৈতিক আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে একটি শব্দÑ‘খনিজ’। আমন্ত্রিত পাঁচটি দেশ যদিও কূটনৈতিকভাবে প্রান্তিক, তবে তারা যে খনিজের অধিকারী, তা আধুনিক প্রযুক্তির প্রাণ। কোব্যাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, লিথিয়ামÑসবই দরকার ইলেকট্রিক গাড়ি, স্মার্টফোন বা সৌর প্যানেলের জন্য।
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সমস্যা হলোÑচীন অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। বিগত দুই দশক ধরে বেইজিং আফ্রিকাজুড়ে পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে, খনিজ চুক্তি করেছে, এবং “কোনো শর্ত ছাড়া” বিনিয়োগের এক মডেল প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আফ্রিকান নেতাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম কোব্যাল্ট ভা-ার এবং চীনা খনিশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যেই সেখানে সক্রিয়।
অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন শুরুতে আফ্রিকায় সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় এবং অভিবাসন নীতিও কঠোর করে। এখন তারা সে অবস্থান থেকে সরে আসছে, তবে খুব সীমিত লক্ষ্য নিয়ে। ট্রাম্পের জামাতা মাসাদ বুলোসের, যিনি ওই অঞ্চলে বিভিন্ন চুক্তির মধ্যস্থতা করেছেন এবং তারই নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র এখন নজর দিচ্ছে “অনাবিষ্কৃত এলাকা”Ñএর দিকে, অর্থাৎ এমন দেশগুলোতে যেখানে চীনের প্রভাব এখনো তুলনামূলকভাবে কম। গ্যাবনে ‘বানো-পাটাচ’ খনিজ প্রকল্প, যা ইউ.এস. ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশনের সহায়তায় পরিচালিত, সেটিকে এখন যুক্তরাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার কৌশলের একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
তবে দীর্ঘ সময়ের অনাস্থা, নতুন নিরাপত্তা হুমকি এবং সাহেল অঞ্চলে জিহাদি কার্যকলাপ এই বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। মালি ও নাইজারের মতো দেশ ইতোমধ্যেই পশ্চিমা বাহিনী তাড়িয়ে রাশিয়ার সঙ্গে নিরাপত্তা জোট গড়েছে। মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিপূর্ণ ও অনিশ্চিত পরিবেশ এড়িয়ে চলে, যেখানে আইন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেইÑসেই পরিবেশ আফ্রিকার বহু অংশেই বিরল।
আরও একটি অভিপ্রায় রয়েছে এই সম্মেলনেরÑঅভিবাসন। বিশেষ করে মরিতানিয়া ও সেনেগালের অভিবাসীরা, বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে। ট্রাম্প প্রশাসন এমন চুক্তি চাচ্ছে যাতে আফ্রিকান দেশগুলো অভিবাসন প্রত্যাবর্তন কিংবা তৃতীয় দেশে আশ্রয় প্রক্রিয়া গ্রহণে সম্মত হয়।
এই ‘লেনদেনমূলক নীতি’ ত্রুটিপূর্ণ। ওয়াশিংটনে নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু সামরিক সরঞ্জাম বা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিবাসন নিয়ে দরকষাকষিÑএই দ্বিমুখী কূটনীতি বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে। যেমন, চলতি বছর সেনেগালের নারী বাস্কেটবল দলকে মার্কিন ভিসা না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়। গত মাসে আফ্রিকান ব্যবসায়ী ও ক্রীড়াবিদদের ভিসা প্রত্যাখ্যান নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। এই মিলিত বার্তাÑব্যবসা করতে আসুন, কিন্তু মুক্তভাবে প্রবেশের আশা করবেন নাÑমার্কিন প্রস্তাবকে দ্বিচারিতার প্রতীক করে তোলে।
ট্রাম্পের আফ্রিকায় ঘুরে দাঁড়ানোর কৌশল তার পুরনো মন্ত্রের প্রতিফলন : “বাণিজ্য চাই, সাহায্য নয়”। আফ্রিকান নেতারা বিনিয়োগকে নির্ভরতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, এতে সমস্যা নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা কমিয়ে এনেছে এমন সময়ে, যখন স্বাস্থ্য ও নাগরিক সমাজের ওপর তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দ্য ল্যানসেট জার্নালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই সাহায্য কমানো হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। অপরদিকে, চীন ও রাশিয়া প্রাথমিকভাবে অবকাঠামো ও নিরাপত্তা দিয়ে মিত্রতা গড়ে তোলে, বিনিময়ে নৈতিকতার প্রচার নয়। এই ‘নন-ইন্টারফেরেন্স’ নীতি তাদের আফ্রিকায় দ্রুত বিস্তার ঘটাতে সহায়তা করেছে।
অনেক আফ্রিকান নেতার দৃষ্টিতে এই সম্মেলন যেন ছিল ধোঁয়াশার আবরণে মোড়া। প্রভাব হারিয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের একটি দেরিতে তৎপর হওয়ার চেষ্টামাত্র। লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন থেকে অপমানিত অবস্থায় ফিরেছে বলে মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৮ সালে ট্রাম্প আফ্রিকান দেশগুলো সম্পর্কে যে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, তার দাগ এখনও রয়েছে। শুধু ছবি তোলার সুযোগ ও খনিজ চুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই মন্তব্যের ক্ষত এত সহজে মুছে ফেলা যায় না ।
অবশ্য সম্ভাবনা এখনও আছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করে, সম্মানজনক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে, এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা করে কোনোরকম ঔপনিবেশিক মনোভাব ছাড়াই, তবে আফ্রিকায় পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন বিনয়, ইতিহাস সচেতনতা ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল, যা বর্তমানে ট্রাম্প-যুগের লেনদেননির্ভর কূটনীতিতে প্রায় অনুপস্থিত।
এই সম্মেলন ছিল কেবল একটি মধ্যাহ্নভোজ নয়, বরং একটি কৌশলগত সন্ধিক্ষণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পেরেছে, আফ্রিকা তাদের আর একচেটিয়া মিত্র নয়। চীন ও রাশিয়া কেবল দরজায় কড়া নাড়ছে না, তারা ইতোমধ্যেই প্রবেশ করেছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র সত্যিই প্রভাব ফিরে পেতে চায়, তবে খনিজ অনুসরণ করাই যথেষ্ট নয়। তাকে আস্থা পুনর্গঠন করতে হবে, প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং আফ্রিকাকে একটি পণ্য নয়, বরং সার্বভৌম অংশীদারদের মহাদেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
কী ঘটবে এরপরÑনতুন খনিজ প্রকল্প সফল হবে কিনা, অভিবাসন চুক্তি কার্যকর হবে কিনা, কিংবা নিরাপত্তা সহযোগিতা কতটা টিকবে, তা-ই ঠিক করে দেবে এটি নতুন এক যুক্তরাষ্ট্র-আফ্রিকা সম্পর্কের সূচনা কিনা, নাকি নিছকই প্রভাব পুনরুদ্ধারের এক অস্বস্তিকর, ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। আফ্রিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা কার আগে কে পৌঁছাবে তা নয়; বরং কে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে এবং কে মনোযোগ দিয়ে শুনবে আফ্রিকার কথা, এই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
[লেখক : প্রাবন্ধিক]
-
নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য
-
আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে
-
জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে
-
পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা
-
সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত
-
অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স
-
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম
-
এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি
-
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ
-
ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে
-
রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”
-
কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা
-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’
-
স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য
-
ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি
-
ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য
-
তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
-
গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!
-
মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ
-
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি
-
হোক সবুজ বিপ্লব
-
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন
-
নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প
-
বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ
-
চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি
-
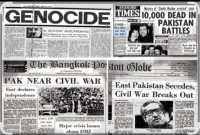
একাত্তরের গণহত্যা : সংখ্যার বিতর্ক নাকি দায় হালকা করার চেষ্টা?
-
রম্যগদ্য : ‘দালাল-ধন্বন্তরি-জীবন রক্ষাকারী...’