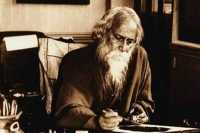উপ-সম্পাদকীয়
সাঁওতাল বিদ্রোহ
মনজুরুল হক

১.
৩০ জুন ছিল হুল দিবস। বাঙালিরা হুল চেনে না। বাঙালিরা বলি ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস’। ভারতবর্ষ ইংরেজের পদানত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোণে কোণে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়েছে। দামামা বেজে উঠেছে, কিন্তু সত্যিকারের বিদ্রোহ বা গণযুদ্ধ আরম্ভ করে সাঁওতালরা। সত্যিকারের গেরিলা যুদ্ধ করে ইংরেজদের শাসনকে আক্ষরিক অর্থেই চ্যালেঞ্জ করে সাঁওতাল বিদ্রোহ, তথা হুল। বিশেষত সিঁধু-কানু দুই ভাইয়ের ইতিহাস বিবৃত হলেও ওই এক পরিবার থেকেই ছয় ভাইবোন (সিধু, কানু, বিরসা, চাঁদ, ভৈরব, আর দুই বোন ফুলমনি এবং ঝানু মুর্মু) নেতৃত্ব দেয়। সংগঠিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। এদের ডাকে একত্রিত হয়েছিল চারশত গ্রাম আর সেই সব গ্রামের হাজার হাজার মানুষ।
২.
১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন সিদু-কানুর গ্রাম ভাগনাদিহিতে চারশত গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল সেই সভায় উপস্থিত হয়। এই সভার প্রথমে সিদু ও তাহার পর কানু বক্তৃতা করেন। দুই নায়কের বক্তৃতায় দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ ফাটিয়া পড়িতে থাকে। তাহারা একে একে বলিলেন- সাঁওতাল-জীবনের দুঃখের কাহিনী, ইংরেজ-জমিদার-মহাজন-পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী, জমিদার-মহাজনদের কাছে সাঁওতালদের সপরিবারে দাসত্বের কাহিনী, তাহাদের দ্বারা সাঁওতালদের স্ত্রী-কন্যার-ইজ্জতনাশের কাহিনী। অসহনীয় দুঃখ-লাঞ্ছনার ভারে পীড়িত, আজন্ম পদদলিত দশ সহস্র সাঁওতাল গর্জিয়া উঠিল। তাহারা সংকল্প গ্রহণ করিল।
৩.
যদিও সুপ্রকাশ রায়ের মতো ঐতিহাসিক লিখেছেন- ‘মূল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৮৫৫ সালে, কিন্তু উইকিপিডিয়া কোত্থেকে এরও আগের কিছু তারিখ উল্লেখ করে, যেমন- ১৭৮০, ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ সালেও সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়ছিল। আগেই বলেছি- এসব ছোট ছোট বিদ্রোহ আদতে বিদ্রোহ ছিল না। এগুলো ছিল আন্দোলন। কোনো একটা ইস্যুতে আন্দোলন। সত্যিকারের মহাবিদ্রোহ ওই ১৮৫৫ সালেই। এ সম্পর্কে আরও তথ্য- ১৮৫৫ সালেই যে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা তা নয়, এর আরও ৭৫ বছর আগে ১৭৮০ সালে সাঁওতাল জননেতা তিলকা মুরমুর (যিনি তিলকা মাঞ্জহী নামে পরিচিত) নেতৃত্বে শোষকদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল গণসংগ্রামের সূচনা হয়। তিনি সর্বপ্রথম সাঁওতাল মুক্তিবাহিনী গঠনের মাধ্যমে পাঁচ বছর ধরে ইংরেজ শাষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ১৭৮৪ সালের ১৭ জানুয়ারি তার তীরের আঘাতেই ভাগলপুরের ক্লিভল্যান্ড প্রাণ হারান। ১৭৮৫ সালে তিলকা মাঞ্জহী ধরা পড়েন এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ১৮১১ সালে বিভিন্ন সাঁওতাল নেতার নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এরপর ১৮২০ সালে তৃতীয়বার এবং ১৮৩১ সালে চতুর্থবার সাঁওতাল গণসংগ্রাম গড়ে ওঠে।
৪.
যাই হোক, ৩০ জুন তারিখের সমাবেশ হইতেই ‘সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া কলকাতাভিমুখে অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন কলকাতার দিকে এই বিপুল অভিযান আরম্ভ হয়। এই অভিযানে কেবল মাত্র নেতৃবৃন্দের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। সাঁওতালগণ গৃহ হইতে যে খাদ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল তাহা যত দিনে শেষ হয় নাই, ততদিন অভিযান সুশৃঙ্খলভাবেই চলিয়াছিল। কিন্তু রসদ শেষ হইবার পর পরিচালকহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র দলগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে। ইহার পর লুণ্ঠন অথবা বলপূর্বক খাদ্য-কর সংগ্রাম অপরিহার্য হইলে নেতারা দ্বিতীয় পন্থাই উচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সাধারণ সাঁওতালগণ অবলম্বন করে প্রথম উপায়টি।’
বিদ্রোহী বাহিনী পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাজারে মানিক চৌধুরী গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিৎ, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত নামে পাঁচজন কুখ্যাত বাঙালি মহাজন ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাঁওতালদের শোষণ-উৎপীড়ন চালাইতে ছিল। বিদ্রোহীগণ ইহাদের পাঁচজনকেই হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
৫.
আট মাসব্যাপী বিদ্রোহের শেষপর্যায়ে লেফটেন্যান্ট ফেগানের পরিচালিত ভাগলপুরে হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর হাতে সাঁওতালদের পরাজয় ঘটে। সিধুকে ভগনাডিহি গ্রামে গুলি করে হত্য করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের মহান নেতা কানুকে ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা ফাঁসি দেয় ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি (তাঁর বয়স তখন মাত্র ছত্রিশ বছর)। ৫২টি গ্রামের ২৫১ জনের বিচার হয়। তাদের মধ্যে সাঁওতাল ১৯১, ন্যাস ৩৪, ডেম ৫, ধাঙ্গড় ৬, কোল ৭, গোয়ালা ১, ভূঁইয়া ৬ ও রাজোয়ার ১। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব যে শুধুই সিধু-কানু বা চান্দ-ভাইরোরা দিয়েছেন তা নয়, ব্রিটিশ সেপাইরা ফুলো মুরমুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করে তার লাশ রেললাইনে ফেলে রেখে যায়। ইতিহাসের প্রথম বীরাঙ্গনা হিসেবে সাঁওতাল জাতিসত্তা তাকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।
অবশেষে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে সিধু নিহত হন এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে কানুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কার্ল মার্কস তার on Indian History-এ সাঁওতাল বিদ্রোহকে ‘গেরিলা যুদ্ধ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
৬.
আমার ৩১ মে তারিখে লেখা পোস্ট, যা আমার বই ‘উপমহাদেশের কৃষক বিদ্রোহ-ব্রিটিশবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গৌরব আলেখ্য’ থেকে কিছু অংশ-
‘একজন দারোগা অন্যায়ভাবে কতিপয় সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। পথে বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে আটক করিয়া তাহাদের নায়ক সিদু ও কানুর নিকট লইয়া যায়। এইভাবে কাজে বাধা পাইতে দারোগাটি অভ্যস্ত ছিল না। সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল : কে তুই সরকারি কার্যে বাধা দিস!’
একজন বলিল : ‘আমি কানু, এ আমার দেশ।’
দ্বিতীয় জন বলিল : ‘আমি সিদু, এ আমার দেশ।’
দারোগা পূর্বে কখনো এরূপ উত্তর শোনে নাই। সাঁওতাল জনতা ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল এবং নায়কদের নির্দেশে ধৃত সাঁওতালগণকে মুক্ত করিল। তৎক্ষণাৎ দুই ভ্রাতার (সিদু ও কানুর) মন স্থির হইয়া যায়। কানু চিৎকার করিয়া ঘোষণা করেন : ‘হুল (বিদ্রোহ) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শালের ডাল পাঠাইয়া দাও। এখন আর দারোগা নাই, হাকিম নাই, সরকার নাই। আমাদের রাজা আসিয়া গিয়াছে।’
‘রাজা-মহারাজদের খতম কর! দিকুদের (বাঙালি মহাজনদের) গঙ্গা পার করিয়া দাও! আমাদের নিজেদের হস্তে শাসন চাই!’
হুল বিদ্রোহ বা সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করব সাঁওতাল ভাষার কবি মনোজীত মুর্মুর লেখা ‘আলিঞ গে সিধু কানু’ শীর্ষক কবিতা দিয়ে-
আসেন মে ‘সার্জম সাকাম’ পটম গিরৗ/ আঠারশ পঞ্চান্ন সালেরে ৩০শা জুনরে হাতাওয়াবন কীরৗ। / সির্জও আবন হুল .../ সানাম মানমি কঃ তাঁহেন কানা চুমুল। / এন হঁবন তেঁঙ্গো না থারে থার, / বার জাঙা লাহাকাতে আড়াগাবন সেঁঙেল সার। / আলিঞ দ সিধু- কানু, / অড়ারে দ মিৎ চুপুৎ জমাঃ বানু, / এন হঁ বন সাব আ আঁ-সার, সাব আবন তাড়ওয়ারী-/ তুঞ কওয়াবন ইংরেজ, মাঃ কওয়াবন বায়রী। / মায়াম লিঁজি কানা যাওদিন, / এম হঁ ক হিজুঃ কানা সারাদিন। / মায়াম লিঁজি রেহঁ, জিইউ চালা রেহঁ, / সুখবন সাঁওয়ারা এনতে রেহঁ।
কবিতাটির ভাবানুবাদ
‘আমরা দুজন সিধু কানু’
আঠারোশ পঞ্চান্ন তিরিশে জুন/ নিয়ে যাও শালপাতায় মোড়া নিমন্ত্রণ। / বিদ্রোহ হলো শুরু হুল-/ বনবাসী জনগণ ভয়েতে আকুল। / বনমাঝে দাঁড়াইনু সবে সারে সার, / ঘরে ঘরে বাড়ন্ত খাবার দাবার। / সাহসে করিয়া ভর বাড়াইয়া জানু। / সদলে এগিয়ে যাই মোরা সিধু-কানু। / ধর ধনু-তীর, ধর তরবারি, / আগুনের ফলা ধর তাড়াতাড়ি-/ দাও বিঁধে, ফেল কেটে বৈরীসেনা কর শেষ। / সারা দিনমান করব রক্ত-স্নান, / জীবনের পণ- সুখেরই সন্ধান, / লক্ষ্য মোদের- দুঃখের অবসান, / চিরতরে হবে স্বাধীন মোদের দেশ।
[লেখক : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক]
-
ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী আমূল সংস্কার জরুরি
-
বরেন্দ্রর মাটিতে আমের বিপ্লব : সম্ভাবনা ও সতর্কবার্তা
-
অবশেষে ‘হাসিনা’ গ্রেফতার
-
স্ক্যাবিস সংক্রমণের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয়
-
বাস্তবমুখী বাজেটের প্রত্যাশা : বৈষম্যহীন অর্থনীতির পথে কতটা অগ্রগতি?
-
কৌশল নয়, এবার প্রযুক্তিতে সৌদি-মার্কিন জোট
-
সিউল : স্বর্গ নেমেছে ধরায়
-
নাচোল বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র সংগ্রহশালা : সাঁওতাল স্মৃতি কেন উপেক্ষিত?
-

অন্ধকার সত্য, শেষ সত্য নয়!
-
বিয়েতে মিতব্যয়িতা
-
এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বঞ্চনার কথা
-
রোহিঙ্গা সমস্যা : বাহবা, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়
-
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়
-
প্রযুক্তির ফাঁদে শৈশব : স্ক্রিন টাইম গিলে খাচ্ছে খেলার মাঠ
-
রমগদ্য : সিরাজগঞ্জে ‘ব্রিটিশ প্রেতাত্মা’
-
বামপন্থা : নীতির সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা
-
দাবি আদায়ে জনদুর্ভোগ : জনশিক্ষা ও সুশাসনের পথ
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন