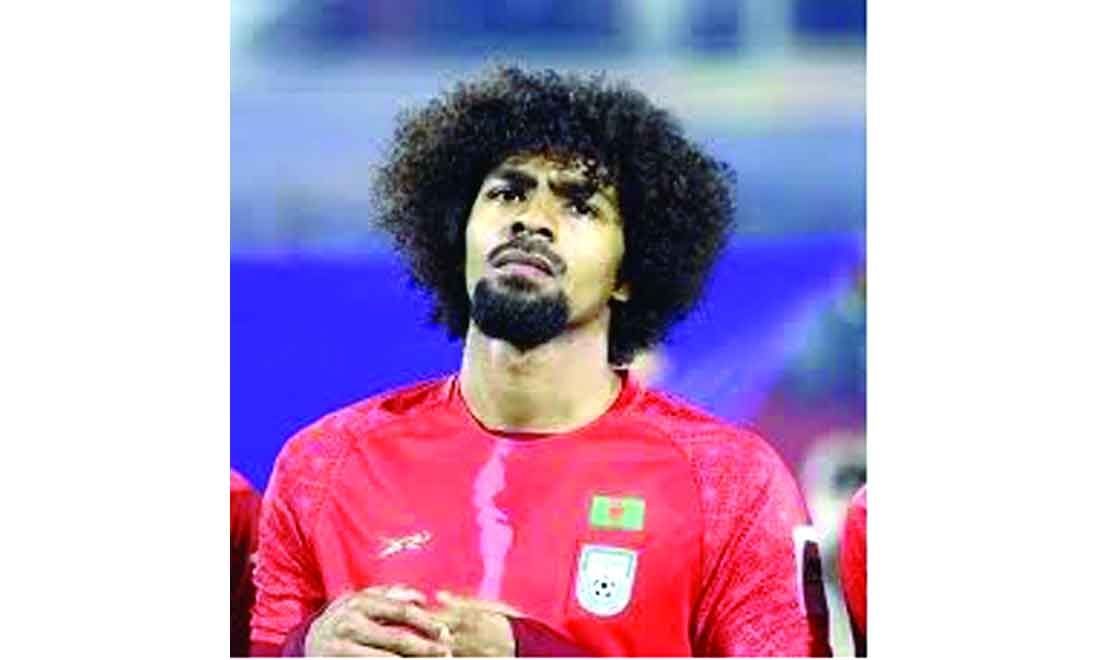পুরনো ঢাকার সেই বাড়িটি
চপল বাশার
পুরনো ঢাকার প্রায় শতাব্দীপ্রচীন একটি দোতলা বাড়ির কথা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। পুরনো ঢাকার দিকে গেলে বাড়িটি দেখতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় চলে যাই সেখানে, দেখতে চাই কেমন আছে বাড়িটি। তারপরেই ভুল ভেঙে যায়। ওটা তো আর নেই, ধ্বংস হয়েছে অনেক আগে।
আমি ২৬৩ বংশাল রোডের বাড়িটির কথা বলছি। সেখানে ছিল দেশের প্রাচীন দৈনিক সংবাদপত্র ‘সংবাদ’-এর অফিস। ১৯৫১ সালের ১৭ মে এই বাড়ি থেকেই ‘সংবাদ’-এর প্রকাশনা শুরু হয়। বাড়িটি তখনই ছিল যথেষ্ট পুরনো। পুরনো হলেও জরাজীর্ণ ছিল না ‘ইট-সুরকির মোটা দেয়াল ছিল মজবুত। কাঠের বাড়ি, কাঠের ছাদ, তার উপরে দোতলা। দোতলার সামনে ও পেছনের দিকে লোহার শিক দেয়া কাঠের রেলিং। নিচতলা উপরতলায় ছোটবড় সাত-আটটি ঘর। আসলে এটি ছিল আবাসিক ভবন। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর বাড়ির মালিক দেশ ত্যাগের সময় এটি হস্তান্তরিত হয়। এক পর্যায়ে গিয়াসউদ্দিন আহমদ নামে এক ব্যবসায়ী বাড়িটির দখল বা মালিকানা গ্রহণ করেন। পরে সেই ভদ্রলোক এই বাড়ি থেকেই প্রকাশ করেন দৈনিক পত্রিকা ‘সংবাদ’।
প্রথম দিকে ‘সংবাদ’ ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সমর্থিত পত্রিকা। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হলে পত্রিকাটি বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়, প্রকাশনা হয় বিঘিœত। সে সময় প্রয়াত আহমদুল কবির পত্রিকাটি কিনে নেন এবং ‘ঞযব ঝধহমনধফ খরসরঃবফ’ নামে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ‘সংবাদ’-এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। বংশাল রোডের বাড়িটির কিছু সংস্কার করে সেখানেই পত্রিকার অফিস ও ছাপাখানা রাখা হয়।
পত্রিকার মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর সম্পাদকীয় নীতিরও পরিবর্তন হয়। আহমদুল কবির প্রগতিশীল রাজনীতির অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। দলের প্রাদেশিক কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কৃষক সমিতির সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা ছিল। তার সহযোগী-সহকর্মীরাও প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এসব কারণেই বংশাল রোডের সেই বাড়িটি অর্থাৎ তৎকালীন ‘সংবাদ’ কার্যালয় বাম ঘরানার অনুসারীদের মিলনকেন্দ্র বা যোগাযোগ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।
‘সংবাদ’-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবির। তাঁর পরে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত একটানা ১৭ বছর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। জহুর হোসেন চৌধুরী আজীবন বাম ঘরানার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ‘সংবাদ’-এর মালিক/প্রকাশক আহমদুল কবির এবং সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, দু’জনেই প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার অনুসারী হওয়ায় পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিও সেই ধারার গড়ে ওঠে।
১৯৫৪ সালে মালিকানা পরিবর্তনের পর সংবাদ-এর নতুন যাত্রা শুরু হয়। সম্পাদক হিসেবে জহুর হোসেন চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী সংবাদ-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শহীদুল্লা কায়সারের নাম। তিনি জয়েন্ট এডিটর নামে একটি পদ প্রায় সব পত্রিকাতেই ছিল। সম্পাদকের পরেই ছিল তার স্থান। শহীদুল্লা কায়সার পত্রিকার সম্পাদক থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সব কাজই দেখতেন। তিনি নিজে সম্পাদকীয় ও কলাম লিখতেন। অন্যের লেখা সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় দেখে দিতেন। বার্তা বিভাগসহ পত্রিকার সব বিভাগ ও ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানও তাঁর ওপর এসে পড়েছিল। যদিও এত কাজ তাঁর করার কথা নয়, তবুও তিনি করতেন পত্রিকাটি চালু রাখার ও টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে।
শহীদুল্লা কায়সারকে সবাই শহীদ ভাই বলে ডাকতেন। সংবাদ-এর সহকর্মীরাও তাঁকে শহীদ ভাই বলতেন। অফিসের দোতলায় উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে তিনি বসতেন। সকালে অফিসে এসে প্রায় সারাদিন থাকতেন। ঐ ঘরে বসেই তিনি সবার সঙ্গে দেখা করতেন, কথা বলতেন। অফিসের লোক বা বাইরের অতিথি, সবার জন্যই তাঁর ঘরের দ্বার থাকতো খোলা। শহীদ ভাই ছিলেন পুরোপুরি বাম ঘরানার মানুষ। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। সংবাদ-এর জয়েন্ট এডিটরের দায়িত্ব নেয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকা- বা তৎপরতা ছিল প্রকাশ্য। কিন্তু তিনি তখনকার চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই ছিলেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি তার সাহিত্যচর্চাও চলেছে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখতেন। রাজনৈতিক কর্মকা-ের কারণে পাকিস্তানি শাসকরা তাঁকে কয়েকবার জেলে ঢুকিয়েছে।
জেলে গিয়েও তাঁর সাহিত্যচর্চা বন্ধ থাকেনি। কারাগারে বসেই তিনি কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস ‘সংশপ্তক’। এতে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে শোষিত-নির্যাতিত মানুষের সংঘাত বিরাট ক্যানভাসে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) দু’বার ধারাবাহিক নাটক হিসেবে প্রচারিত হয়েছে। তার আর একটি উপন্যাস ‘সারেং বৌ’ জনপ্রিয় ছিল। এটি নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ‘রাজবন্দীর রোজনামচা’ নামে তার আর একটি গ্রন্থও পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল। এছাড়াও তার আরও সাহিত্যকর্ম গ্রন্থিত হয়েছে।
আমি ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে ‘সংবাদ’-এর বার্তা বিভাগে শিক্ষানবিস হিসেবে যোগদান করি। সে সময়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে এমএ শেষ পর্বের ছাত্র। হাতে কলমে কাজ শেখা ও করার উদ্দেশ্যেই সংবাদ-এ ঢুকেছিলাম। নিউজ ডেস্ক ও রিপোর্টিং-উভয় বিভাগেই আমাকে দিয়ে কাজ করাতেন, বেতনও দিতেন। মাসে ১৫০ টাকা। আমার জন্য অনেক। গোপীবাগে আমার বাসা থেকে বংশালে ‘সংবাদ’ অফিসে যেতে রিকশা ভাড়া লাগতো ছ’আনা থেকে আট আনা (এখনকার ৩৭ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা)। রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপ দুই আনা, সিঙ্গারা দুই আনা, এক টাকা-দেড়টাকায় মাছ-ভাত বা মাংস-ভাত খাওয়া যেত। অতএব, মাসে দেড়শ’ টাকা পেয়ে আমি রাজার হালে ছিলাম। আমার নিজের হাতখচর ইত্যাদি ব্যয় মেটানোর পরেও বেশ কিছু টাকা বেঁচে যেত। সে টাকা দিয়ে মাঝে মধ্যে কাপড়চোড় কিনতাম, বই কিনতাম অথবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বসে খরচ করতাম।
তবে মাসিক বেতন পুরোটা একসঙ্গে পাওয়া যেত না। মাসের সাত তারিখে অর্ধেক বেতন দেয়া হতো সবাইকে। বাকি বেতন মাস শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে ভেঙে শোধ করা হতো। মাসের বেতন মাসেই শোধ করা হতো, বকেয়া থাকতো না, এজন্য সাংবাদিক-কর্মচারীদের বেতন নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না। সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। এজন্য কৃতিত্বটা শহীদুল্লা কায়সারের। তিনি মাসের বেতন মাস শেষ হওয়ার আগেই পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতেন। এ কারণে তিনি সাংবাদিক-কর্মচারীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন।
শহীদ ভাই মাঝেমধ্যেই বার্তাকক্ষে চলে আসতেন, বিশেষ করে বড় কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন। পরামর্শ দিতেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের উপকূলীয় বিরাট অঞ্চলে ধ্বংস্তূপে পরিণত করে। সেই ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় দশ লাখ মানুষের। সে সময় ‘সংবাদ’ তার সীমিত জনবল নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক প্রতিবেদন ছবিসহ প্রকাশ করেছে।
একদিন বরিশালের ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রখ্যাত শ্রমিকনেতা জসিমউদ্দীন ম-ল ‘সংবাদ’ অফিসে এলেন এবং সরাসরি শহীদুল্লা কালসারের ঘরে গেলেন। তিনি শহীদ ভাইকে জানালেন ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় যা দেখেছেন। শহীদ ভাই দেরি না করে জসীমউদ্দীন ম-লকে নিয়ে বার্তা কক্ষে এলেন। এসে দেখলেন, রিপোর্টার কেউ নেই। আমি চুপচাপ বসে আছি নিউজ ডেস্কে। তিনি আমাকে বললেন, ‘চপল, তুমি জসীম ভাইর ইন্টারভিউটা করো। তিনি ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় যা দেখেছেন, সব শুনে একটা রিপোর্ট লিখে আমাকে দেখাও।’
আমি তখনই জসীম ভাইকে নিয়ে বসলাম। তার কাছ থেকে যা শুনলাম তা ভয়াবহ, মর্মান্তিক। উপকূলে পানিতে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ ভাসছে। কচুরিপানার মতো। মানুষের লাশের সঙ্গে ভাসছে হাজার হাজার মৃত গবাদিপশু। লাশ উদ্ধার করে মাটিচাপা দেয়ার কেউ নেই। কোনো উদ্যোগও নেই। যারা বেঁচে আছে তারা খাবার পানি পাচ্ছে না, খাদ্য পাচ্ছে না, কোনো ত্রাণ তৎপরতা নেই। পানি ও খাবার না পেলে এরাও তো মরে যাবে। জীসম ভাইর বর্ণনা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। ঘূর্ণিঝড়ের পরে তখন ৫/৬ দিন পার হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ সরকার ও প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই।
জসীম ভাইর কাছ থেকে সব শুনে রিপোর্ট লিখতে বসলাম। কিন্তু কাগজের ওপর কলম চলতে চায় না। আমার মনের মধ্যে হাহাকার, যন্ত্রণা। তবুও সব যন্ত্রণা বুকের মধ্যে রেখেই কলমকে সচল করে লিখে ফেললাম মোটামুটি বড় এক রিপোর্ট। দোতলায় গিয়ে শহীদ ভাইকে রিপোর্টটি দিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে পুরো রিপোর্টটি পড়লেন। রিপোর্টের উপর দিকে কোনায় নোট দিলেন, এটি যেন প্রথম পাতায় ছাপা হয়। আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘ভালোই লিখেছ। এটা নিয়ে নিউজ ডেস্কে দাও। মানুষ মারা যাচ্ছে, সরকারের মাথাব্যথা নেই।’