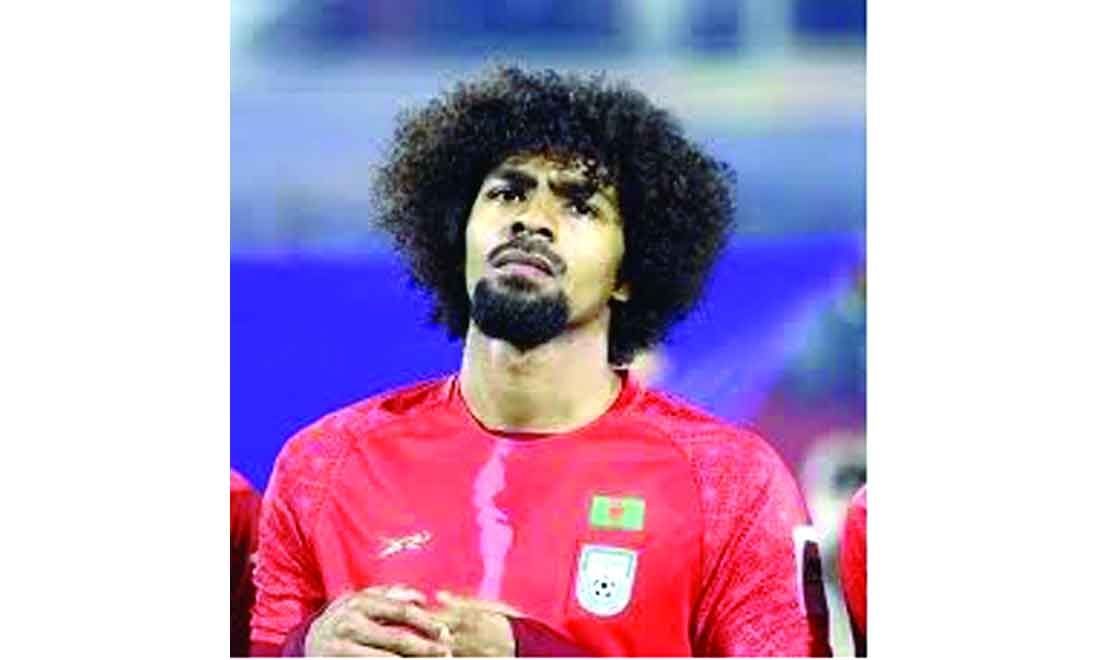গণমাধ্যম জাতীয় উন্নতির সহায়ক
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
গণযোগাযোগ গবেষকরা বিভিন্ন বিকাশশীল সমাজ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব দিয়ে থাকেন। এসব তত্ত্বে বলা হয়েছে, সুসংগঠিত গণযোগাযোগের সঙ্গে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এছাড়া জাতীয় উন্নয়নের জন্য গণমাধ্যমের বিকাশ অত্যাবশ্যক। আরও বলা হয়ে থাকে যে, গণমাধ্যমের বিকাশ থেকে একটি দেশের উন্নয়নের স্তর কী- তা বোঝা যায়। তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতির বেলায় এসব তত্ত্ব খাটে না বললেই চলে।
কয়েক দশক আগে ব্রিটিশ ভারতের একটি অংশ থাকা অবস্থায় বাংলাদেশে একটিও দৈনিক পত্রিকা ছিল না, রেডিও, টেলিভিশন অথবা চলচ্চিত্র তো দূরের কথা। তবে এখন এ দেশটিতে অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকাসহ অজস্র সাময়িকী রয়েছে। এছাড়া সারা দেশের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র থেকে বেতার ও একাধিক টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আর চলচ্চিত্র-শিল্পও যথেষ্টসংখ্যক চিত্র তৈরি করে যা দেশের প্রায় পুরো চাহিদা মেটায়।
এত অল্প সময়ের মধ্যে গণমাধ্যমের এই বিকাশের বেশ উল্লেখযোগ্য ছাপ বাংলাদেশের ওপর থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এদেশের আয়তন, জনসংখ্যা, উন্নীত সম্পদ, জীবনযাত্রার মান ও সাংগঠনিক স্তরের তুলনায় এর অনুন্নয়নের মাত্রা খুবই বেশি। এই পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির ব্যাখ্যা কী?
পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে, একটি দেশের সাধারণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষমতা গণমাধ্যমের ছিল। বিশিষ্ট গবেষকরা রিপোর্ট, নিবন্ধ ও বই প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে গণমাধ্যম জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করতে পারে। এভাবেই তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য গণমাধ্যম ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ সাধনের সুপারিশ করেছেন। উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ থাকায় এসব দেশের শাসকরা এই সুপারিশ সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। এরপর কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে, তাদের গণমাধ্যম ব্যবস্থার অনেক বিকাশ হয়েছে, কিন্তু কাক্সিক্ষত উন্নয়ন সাধিত হয়নি। এটা অবশ্য একটি ব্যাখ্যা মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি এটা প্রযোজ্য?
এর কোনো জবাব দেয়া কঠিন, কারণ বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থার বিকাশ নিয়ে কোনো সুশৃঙ্খল সমীক্ষা চালানো হয়নি। তাই এই লেখক বেশ কিছুকাল আগে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থার ওপর একটি সমীক্ষা চালানোর কাজ শুরু করেন এবং দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের বিকাশের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সম্পর্ক বের করার চেষ্টা চালান। বস্তুগতভাবে এ ধরনের সম্পর্ক বের করার অসুবিধার দিকটি উপলব্ধি করে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের দ্বৈত পদ্ধতিতে এই সমীক্ষা চালানো হয়। সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ছয়টি উন্নয়ন-নির্দেশক ও গণমাধ্যমের বিকাশের দুটি নির্দেশকের ৩০ বছরের পরিসংখ্যান সাজানো হয় এবং এর প্রতিনিধিত্বশীল পত্রিকা ও সম্প্রচার মাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। শেষতক গণমাধ্যমের বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে পরিসংখ্যানগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায়নি। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আমরা কোনো নিশ্চয়তা সহকারে এ কথা বলতে পারিনি যে, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশ দেশের উন্নয়ন স্তরে ছাপ পড়েছে। অনেক বছর পার হলেও এখনও যে ওই গবেষণালব্ধ তত্ত্ব অচল নয়- এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায়।
তাই এ কথা ধরে নেয়া যায় যে, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশ দেশের উন্নয়ন স্তরে কোনো অবদান রাখেনি, তবে এটা উন্নয়নের পথে কোনো বাধাও সৃষ্টি করেনি। গণমাধ্যম বিগত বছরগুলোতে বেশ বিকাশ লাভ করেছে, সম্ভবত একটি নতুন দেশ ও নতুন জনগণের তথ্যের বর্ণিত চাহিদা মেটাতে এই বিকাশ হয়েছে। আর এই দেশটি যাত্রা শুরু করেছে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা থেকে। গণমাধ্যমের এই বিকাশ ঘটেছে দ্রুত যা চোখে পড়ার মতো, এর মানও উন্নত। কিন্তু ইউনেস্কো সুপারিশকৃত মানের হিসাবে জনসংখ্যার তুলনায় এটা এখনও আশানুরূপ নয়। তবে গণমাধ্যমের বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো বিবেচনায় আনলে একে সম্ভবত যথেষ্ট বলেই গণ্য করতে হয়। তাই বাংলাদেশের গণমাধ্যম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উপযুক্ত অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়ে থাকলে তা কেবল বস্তুগত ত্রুটি নয়।
এটা সবাই জানেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণমাধ্যমের কেন্দ্রগুলো শহরাঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ বড় বড় সংবাদপত্র, প্রধান বেতারকেন্দ্র ও টেলিভিশন কেন্দ্র সবই রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। আর মাত্র গুটিকয়েক ছোটখাটো সংবাদপত্র, বেতারকেন্দ্র ও টেলিভিশন উপকেন্দ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, তবে সেগুলোও শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। ইদানীং স্যাটেলাইটের কল্যাণে অবশ্য কেবল টিভি অসংখ্য টিভি কেন্দ্র ঘরে নিয়ে আসে, তবে তারও মূল ওই শহরেই। উপরোক্ত সমীক্ষায় প্রচার মাধ্যমে বিকাশ ও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। এতে জানা যায়, প্রচারমাধ্যম প্রধানত শহরবাসীর উপকারে আসে, আর মোট জনসংখ্যার এরা মাত্র শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। অর্থাৎ সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক প্রচার মাধ্যমের বিকাশ থেকে তেমন একটা লাভবান হয় না। আসলে প্রচার মাধ্যম হয়তো তাদের কাছে পৌঁছতেই পারে না। আর এ ধরনের অবস্থা নিশ্চয়ই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের অবদানের ইঙ্গিত দেয় না।
উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোয় প্রচার মাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে আর সমাজ কাঠামোকে প্রভাবিত করার অন্যান্য কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে প্রচার মাধ্যমে কাজ করা উচিত নয়
প্রচার মাধ্যমের বিকাশ ও উন্নয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পর্ক দেখাতে ব্যস্ত হয়ে এই লেখক প্রচার মাধ্যমের বিয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের অবদান রাখার সামর্থ্য থেকে থাকলে তা সম্পন্ন করতে হবে এই বিষয়বস্তুর দ্বারাই। বিষয়বস্তুতে অবশ্যই উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক বাণী থাকতে হবে। কিন্তু দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে এ দিকটাকে সামান্যই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে এমন ধরনের বিষয়বস্তু স্থান পেয়ে থাকে যা দেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সামান্যই সম্পর্কযুক্ত। পল্লীর জনসংখ্যার দিকে এর দৃষ্টি নেই, আর রাজনৈতিক ও সরকারি বিষয়ের দিকেই ঝোঁক বেশি। সাধারণ শ্রোতা ও দর্শকদের বিবেচনা করলে, বেতার ও টেলিভিশনে, বিশেষ করে টেলিভিশনে উন্নয়নকে পত্র-পত্রিকার চেয়েও কম গুরুত্ব দেয়া হয়। দেখা গেছে যে, পল্লী এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করা সত্ত্বেও রেডিও কৃষকের প্রয়োজন, কাজ-কর্ম ও আশা-আকাক্সক্ষার সঙ্গে মিল রেখে উপযুক্ত বিষয় প্রচারে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে পত্র-পত্রিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ বলে মনে হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য যেসব সংবাদপত্রের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়েছে, সেগুলোতে কয়েক বছরের ব্যবধানে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর পরিমাণ অনেক বেড়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য এটা এখনও মোট বিষয়বস্তুর একটা ক্ষুদ্র অংশ। তবে বিশ্লেষণকৃত বিষয়বস্তুর দিকে ঘনিষ্ঠভাবে নজর দিলে দেখা যায়, উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশিরভাগ খবরই উন্নয়নের ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি তথা নেতিবাচক দিক অথবা অনুন্নয়নকেই তুলে ধরে। কেবল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমই উন্নয়নের ইতিবাচক দিকটাকে অধিকমাত্রায় তুলে ধরে। কিন্তু সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবর প্রচারসর্বস্ব হয়ে থাকে। আর এতে উন্নয়নের দিক বেশি পরিমাণে তুলে ধরা হলেও জনগণ তা গ্রহণ করবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে এ কথার সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে সামান্যই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশে সম্প্রচার ব্যবস্থা সব সময়ই সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবুও রেডিও অথবা টেলিভিশন কোথাও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় যথেষ্ট পরিমাণে তুলে ধরা হয় না। অবশ্য সম্প্রতি এক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সম্প্রচার ব্যবস্থার শক্তি ও সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে এর ব্যাপক বিকাশ লাভের দিক বিবেচনা করলে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় প্রচারে ঘাটতির কারণ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। সরকার প্রকৃত উন্নয়নের চেয়ে বর্তমান অবস্থা বহাল রাখতেই আগ্রহী।
জাতীয় উন্নয়নে ভবিষ্যৎ গণমাধ্যমের বৃহত্তর ভূমিকা রয়েছে, তবে গণমাধ্যম উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে না বরং তা সৃষ্ট হয় গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোয় প্রচার মাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে আর সমাজ কাঠামোকে প্রভাবিত করার অন্যান্য কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে প্রচার মাধ্যমে কাজ করা উচিত নয়।
প্রচার মাধ্যমের উপযুক্ত ভূমিকা আছে জনগণকে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করার। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উন্নয়ন-সুযোগকে চিহ্নিত করতে হবে ও তার কথাই সবার আগে বলতে হবে। জনকল্যাণের সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট উন্নতিসাধনের পর সত্যিকার উন্নয়ন হাতের মুঠোয় আসবে।
গণমাধ্যমে যে তথ্য প্রচারিত হবে তাতে অবশ্যই সমালোচনামূলক দিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। আর এভাবে প্রচার মাধ্যমের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ পর্যন্ত যোগাযোগ-বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত রয়েছে যোগাযোগের উপকরণ বিকাশের দিকে। প্রচারের বিষয়বস্তু তাদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বিষয়বস্তুই হচ্ছে যোগাযোগের মূল জিনিস, আর জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রচার মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহারের আসল কথাও এই বিষয়বস্তু।
এটা কীভাবে করা যাবে সে ব্যাপারে গণযোগাযোগ-বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা জানি না যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুর কতটা অংশকে উন্নয়নমুখী হতে হবে। তবে এটা দেখা গেছে যে, বর্তমান অবস্থায় থাকলে প্রচার মাধ্যমের বিষয়বস্তু কিছুই অর্জন করতে পারবে না। এই ধারা বদলাতে হবে আর পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানের ধরনই বদলে ফেলতে হবে। ব্যক্তিমালিকানার প্রচার মাধ্যম উন্নয়নকে উৎসাহিত করার ‘অলাভজনক’ কাজে খুব কমই আগ্রহ দেখায়। কোনো শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সরকারের পক্ষে তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচার মাধ্যমে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়কে অধিক পরিমাণে তুলে ধরা সম্ভব, কিন্তু এ ধরনের সরকার বিরল। আর এ ধরনের সরকার পাওয়া গেলেও তখন প্রশ্ন উঠবে যে, প্রচার মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাম্য হতে পারে কি? এটা এমনই এক প্রশ্ন- যার উত্তর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আজ হোক কাল হোক দিতেই হবে।