সাময়িকী
কালো রঙের আলো অথবা কিছু কোঁকড়ানো চুল
মুহিম মনির
মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে ঋতুর দেবদূত তার স্বেচ্ছালীলায় শাদা-কালো ধূসরতায় আড়াল করেছে আকাশকে। পেঁচিয়ে ফেলেছে সেই ফড়িঙটিকে, যে হয়তো হালকা সবুজ শাড়ি পরে, কড়ে আঙুলে ঘাসফুল জড়িয়ে, উড়ে বেড়াচ্ছিল ফুলের বনে, গাছের ডালে। দলে দলে ওড়া উচ্ছলতায় ভাটা পড়ায় কেঁদে উঠছে সে। সবুজ পাতায় পড়ছে তার চোখের জল। টলমল করছে টলে-পড়া লতার দল। অথচ তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে ন লোকজন। আমিও যাচ্ছি, তবে তাকিয়ে আছি ভিজতে থাকা মাঠের দিকে; কাঁটাল জঙ্গলে ফোটা ফুলগুলোর দিকে। আমার পাশে আছেন একজন; আরো আছেন আশেপাশে।
-কোথায় নামবেন?
-নাচোলে।
-নাচোলেই আপনার বাসা?
-জি।
-আমিও যাচ্ছি।
কেন যাচ্ছেন জানতে মন চাইল না। কোথাও দেখেছি বলেও মনে পড়ল না। তবু পরিচয়-চিহ্ন খুঁজলাম,
-কোনো আত্মীয়ের বাসায় কি?
-উঁউঁ... হু, বলতে পারেন।
-ওওও।
-আসলে একটা ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য যাচ্ছি।
বুঝতে পারছি, একটু আলাপ জমাতে চাচ্ছেন এই অল্প পরিচিত অথবা অপরিচিত মানুষটি। বিষয়টি ভালো হলেও ভালো লাগছে না। ধরে রাখতে পারছি না মনকে। সে এখন বৃষ্টিতে ভিজছে; খড়কুটোর সঙ্গে সাঁতরাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন জলকণা খেলা করছে হৃদয়-অলিন্দে। শব্দে শব্দে মুখরিত হচ্ছে সকল স্বপ্ন। এ সময় কি অন্যমনা হওয়া যায়?
-পরিচিত হতে পারি তো?
-হুম, নিশ্চয়।
-আমি আমিরুল ইসলাম কনক। রাবিতে ফোকলর পড়াই।
এবার আর যাই কোথায়? ‘রাবি’ শুনলেই মনকানন কেমন করে যে! প্রিয় ক্যাম্পাস তো বটেই; প্রিয় এক মানুষেরও নিক নেইম ছিল ‘রাবি’, যার খুব ইচ্ছে ছিল ফোকলরে পড়ার। তাই তাঁর শব্দগুলো তুলল অন্যরকম সুর। দূর-বহুদূর থেকে সরে এল মন। সমীহ করতে শুরু করল পাশের জনকে, কনক স্যারকে।
-তোমাকে ‘তুমি’ বলতে পারি তো?
-নিশ্চয় স্যার। আমিও এমনটি চাইছিলাম।
-কোথায় পড় তুমি?
আমি সাড়া দেয়া শুরু করলাম। আলাপচারিতাও চলতে লাগল। জানা গেল, তিনি যাচ্ছেন সাঁওতালদের বসন্ত-সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। নাচোল থানা থেকে আরেকটু দক্ষিণে গেলে শালবন দেখা যায়। কখনো যাইনি বলে জানতাম না, কয়েক ঘর আদিবাসী বাস করেন সেখানে। অথচ তাঁদের খোঁজ ঠিকই রেখেছেন রাবির এই অধ্যাপক। অনুষ্ঠানের কথা জানতে পেরে চলে যাচ্ছেন কিছু নোটস নিতে। অবশ্য এমন এক উদ্দেশ্য আমারও হয়েছিল একবার। ইচ্ছে করেছিল একটি গল্প লেখার। যখন জেনেছিলাম, ‘অভিগাতে লাং তাহে কানা’ মানে তোমাকে অনেক ভালোবাসতাম আমি, তখন তা গেঁথে দিতে চেয়েছিলাম কোনো এক গল্পের গায়ে। খসড়া মতো কিছু একটা লিখেওছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ করা হয়নি। না-হলেও হবে মনে হচ্ছে। মন বলছে, যাই, স্যারের সঙ্গে আমিও যাই। সরেজমিনে দেখে আসি; শালবন থেকে নিয়ে আসি আরও কিছু শব্দ, নিবিড় নৈঃশব্দ্য। যেহেতু আমারও কিছু দেখার আছে, দেখে কিছু লেখার আছে, সেহেতু সেইমতো প্ল্যানটা করেই ফেললাম। কিছু জিনিস জানতে চাইলাম, কিছুকিছু এমনিতেই জেনে গেলাম। নিজ থেকেই জানালেন তিনি। কথায় কথায় কিংবদন্তীই বানিয়ে ছাড়লেন সাঁওতালদের।
—এই যে তাদেরকে অনেকে অ্যাবরিজিনাল বা সেমি স্যাভেজ বলে, এটা কোনো কথা হল, বল? সাঁওতাল সাঁওতালই। একটি মহান জাতি। নৃবিজ্ঞানী মার্টিন ওরান্স যাদের সম্পর্কে বলেছেন, A tribe in search of a great tradition. একসময় ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করতেন বৈদিক সভ্যতাই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা। কিন্তু ১৯২৪ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানীর তৎপরতায় মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সেই দাবি খারিজ হয়ে যায়। আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই যে এখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।
—সে সভ্যতা কারা গড়েছিলেন?
—হুম, সেটাই তো কথা। কারা গড়ে তুলেছিলেন সেই সভ্যতা? নিঃসন্দেহে সাঁওতালেরা। সাঁওতালেরাই সেই সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। যদিও ঐতিহাসিকেরা সরাসরি স্বীকার করেন না। আবার অস্বীকারও করতে পারেন না। আরে আর্যরাই তো অশিক্ষিত ছিল। সাঁওতালদের সংস্পর্শে এসেই না সভ্য হতে শিখেছে। অথচ সেই শিক্ষক জাতিই কিনা...
একটা কল এলে রিসিভ করলেন তিনি। আমি আবার আমার চোখ দুটোকে ছেড়ে দিলাম। ছড়িয়ে পড়ল তারা। কী যেন খুঁজল সদ্যস্নাত মাটির বুকে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকালাম। তাঁদেরও একজন কী জন্য যেন তাকালেন। কিছু না বলে নীরবই থাকলেন। আমিও অব্যক্তে একে-ওকে দেখলাম; পড়লাম লাল-কালো কালিতে লেখা লেখাগুলো। ঠিক হাতের বামেই লেখা ‘এখানে ধূমপান নিষেধ, করিলে ১০০ টাকা জরিমানা’ লেখাটা পড়ছি দেখে তিনি বললেন,
—দেখেন দেখি কা-, ‘এখানে ধূমপান নিষেধ’ না-লিখে যদি একটু কষ্ট করে ‘এখানে ধূমপান করা নিষেধ’ কিংবা ‘এখানে ধূমপান নিষিদ্ধ’ কথাটা লিখত, তাহলে কীই-বা ক্ষতি হয়ে যেত? হয়তো একটু কালি বেশি লাগত। কিন্তু ‘করিলে’র বদলে ‘করলে’ লিখলে সেটাও পুষিয়ে যেত! হা হা...
আমিও হেসে উঠে দুএকটা কথা বললাম। জানতে চাইলাম,
—আপনার নাম?
—সুরেশ রায়।
—তাই? আমারও এক বন্ধুর নাম ছিল সুরেশ; সুরেশ টুডু। সেইরকম ফুটবল খেলত!
‘বাহ! বেশ তো!’ স্যার যোগ দিলেন, ‘এখন কী করে সুরেশ?’
—শুনেছি, পুলিশের চাকরি পেয়েছে। হাসিনা মুরমু নামেও একজন পড়ত, স্যার। তবে তার কথা জানি না।
—তুমি কি জানো, এই টুডু মুরমু এগুলো একেক গোত্রের একেক উপাধি?
—উপাধি?
—হুম, সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে ‘টোটেম’। এ টোটেম নিয়ে একটা গল্প আছে।
—বলেন স্যার প্লিজ!
শুরু করতে যাবেন এমন সময় একজন বাদামওয়ালা এলেন। একটু-আধটু আপত্তি সত্ত্বেও স্যার কয়েকশ বাদাম কিনলেন আমাদের জন্য। আরেকটু জমে উঠল আড্ডাটা,
—সাঁওতালদের বিশ্বাস মতে, তাঁদের আদি পিতামাতা হলেন পিলচু হানাম ও পিলচু বুড়ি। তাঁদের জন্ম হয় এক পাখির বাসায়। একসময় ঠাকুরজিউ মনে করলেন পৃথিবীতে আরও মানুষের দরকার। আর তাঁর এ ইচ্ছে পূরণে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। গোপনে হাড়াম-বুড়িকে চোলাই পান করালেন। চোলাইয়ে মাতাল হয়ে মিলিত হলেন; এবং এ থেকেই একে একে সাতটি পুত্র ও আটটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন তাঁরা।
—তারপর?
—তারপর তাঁদের ছেলেমেয়েগুলো বড়ো হয়ে উঠলে ঠাকুর পিলচু হাড়ামকে বললেন, ‘তুমি ছেলেদের নিয়ে সিংবীরে যাও।’ আর পিলচু বুড়িকে বললেন মেয়েদের নিয়ে মানবীরে চলে যেতে। তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠাকুরজিউ আবার তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিচয় ঘটালেন। সাত ভাই সাত বোনকে বিয়ে করল। সূচনা হল সাতটি বংশের-হাঁসদা, মুরমু, কিস্কু, হেমব্রোম, মারাণ্ডি, সরেন, টুডু। অবশ্য কোথাও কোথাও আরও পাঁচটি গোত্রের নাম জানা যায়— বেসরা, বাস্কে বেদিয়া, চোঁড়ে, পাঁওরিয়া। এদিকে নৈতিকতা ভুলে যেতে লাগল আদি সন্তানেরা। তারা কোনো আদেশ নিষেধ মানল না বলে সাত দিন সাত রাত অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি ঝরিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিলেন ঠাকুরজিউ। এরপর আবার পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়িকে আশীর্বাদ করলেন। এবং আবার নতুন সন্তানের জন্ম দিলেন এই আদি পিতামাতা।
—আদি পিতামাতা, মানে ইসলাম ধর্মমতে যেমন, আদম-হাওয়া?
—হুম, অনেকটা তেমনই। এ নিয়েও একটা মিথ চালু আছে।...
আগ্রহ পেয়ে বসেছে। চোখেমুখে জ্বলজ্বল করছে জানতে চাওয়ার আলোককণা। যেন ভূতে পাওয়া মানুষের মতো হয়ে গেছি। শুনে যাচ্ছি স্যারের কথা। তাঁর কথা কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে! সম্ভবত সেইখানে যেখানে মুরমু’র মুখ দেখা যায়। মনে পড়ে যায়, তার ছিল ঘনকালো রঙ; আর ছিল কোঁকড়ানো কিছু চুল। অনন্য ছিল ওর মুখের গড়ন। যদিও কোনো কামনা জাগায়নি, ওর সংস্পর্শে মনেও হয়নি, অন্নজলের বাইরেও কিছু চাই আমার; তবু এখন মনে হচ্ছে, সে-ই বসে আছে আমার কাছে। বলে চলেছে,
—...একসময় না পৃথিবীতে কেবল জল ছিল। জল আর জল। স্থল বলতে কিছুই ছিল না। দেবতারা স্বর্গ থেকে তোড়ে সুতাম বেয়ে স্নান করতে নামতেন। একদিনের কথা। ঠাকুরজিউ স্নান করতে এসেছেন। ঘাটে বসে অনেকটা ময়লা ছাড়ালেন। সেই ময়লা দিয়ে বানালেন দুটো পাখি—হাঁস ও হাঁসিল। মনের আনন্দে উড়তে লাগল পাখি দুটো। উড়তে উড়তে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও কোনো জায়গা পেল না যে একটু বসবে। তখন করল কি, বস-কি-বস ঠাকুরের হাতে এসেই বসল। এভাবেই দিন গেল, মাস গেল। একদিন সিঞ সাদম তেষ্টা মেটাতে মর্তে এলেন। জলপান করতে গেলেন আর অমনি তাঁর মুখের ফেনা গড়িয়ে পড়ল। হাঁস ও হাঁসিলকে সেই ফেনার ওপর বসতে বললেন ঠাকুর। তাঁর কথামতো তারা বসল। ফেনার সঙ্গে ভাসতে লাগল নৌকোর মতো। সে হোক, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁয় তো পেল। কিন্তু খাবার? সেটা পাবে কোথায়? তাই পুনরায় সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল তারা। তিনি তাদের দুঃখ বুঝলেন। সৃষ্টি করলেন স্থলভাগ। স্থলে এসে আটকে পড়ল ভাসমান ফেনা। সেই ফেনায় সিরম গাছের চারা বোনা হল। চারা বড়ো হয়ে উঠল। হাঁস-হাঁসিল বাসা বাঁধল সেই সিরম গাছের ডালে। ডিম পাড়ল; বাচ্চা ফোটাল। পাখির নয়; মানুষের বাচ্চা। একজন পিলচু হাড়াম, আরেকজন পিলচু বুড়ি।
—নাচোল চলে এসেছি, স্যার।
নাচোল। ‘নাচতে চল্’ থেকেই নাকি ‘নাচোল’, ইলা মিত্রর জন্য যে বলা চলে বিখ্যাত হয়ে গেছে, সে নাচোলেই পরপর কয়েকটা টাল সামলিয়ে নিজেকে স্থির করল ট্রেনটা। হুড়োহুড়ি শুরু করল লোকজন। যে যার মতো নামল-উঠল। আমরাও নামলাম দেশের এক বয়সাক্রান্ত রেলস্টেশনে। ভেজা শার্টের গন্ধে ভরে গেছে আলোয় উজ্জ্বল বাতাস। ঠেলাগাড়ির ঠনঠনানিও শোনা যাচ্ছে। এর-ওর কাছে ছুটে যাচ্ছে দু-তিনজন। আমার হাতে হাতব্যাগটা দিয়ে স্যার একটু একটা দোকানে গেলেন। হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলির ঠেলায় দূরেই দাঁড়ালাম আমি। হুড়টা কিছুতেই কমছে না। একজন সরছেন তো দু-জন ভিড়ছেন। এরইমধ্যে কে যেন কাকে ডাকলেন,
—সাম্য... সাম্য, এই যে আমি এদিকে।
তাঁর ডাকে এগিয়ে এল একজন। বয়সটা খুব জোর চৌদ্দ-পনেরো। মুখে মুগ্ধতার বদলে মোঁচ গজাতে শুরু করেছে। কাছে এসে বলল,
—কই সার?
—কী কই!
—আপনার ব্যাগ।
—আমার ব্যাগ! এই তোকে কে ডেকেছে রে?
—আপনিই তো সামু সামু কইহ্যা ডাকলেন।
এ-কথা শুনে রেগে গেলেন লোকটি। ততক্ষণে ধরানো সিগারেটটায় টান দিয়ে বললেন,
—যা ব্যাটা, ভাগ! আমি ডেকেছি সাম্যকে। আর তুই শুনেছিস সামু সামু? সব শালাই আসলে ধান্ধাবাজ!
কিছু মনে না করে তক্ষুনি আরেকজনের কাছে ছুটল ছেলেটি। ঘামের দামে কিনতে চাইল শাদা ভাত। স্বপ্নের সাপলুডু খেলতে থাকল পুরনো প্লাটফর্মে। যে যার কর্মে ডুবে থাকলাম। বেরুতে গিয়ে দেখলাম, কাজে-অকাজে ঝিঙের মতো ঝুলে আছে কয়েকটা বাল্ব। ওগুলো আলো দিলে হয়তো আরো চকচক করে উঠবে তেল চিটচিটে চামড়া। ভাড়া চুকিয়ে ভ্যানে চড়তে যাবেন এমন সময় স্যারকে বললাম,
—আমিও যাব, স্যার।
—যাবে তুমি? চল তাহলে দুজনেই যাই!
*
পথের মাথায় নামতে গিয়েই দেখলাম, একটি দল দাঁড়িয়ে আছেন। কারো হাতে মাদল, কারো হাতে মালা, কারো হাত খালি। করতালি দিলেন, মালা পরালেন, আনন্দ-কলরোল করতে করতে বরণ করে নিলেন ছোট্ট দলটি। তার মানে স্যার এমনি এমনি আসেননি; আমন্ত্রিত হয়েই এসেছেন। যখন জানলাম যে, এদের মধ্যে একজন পড়ে ফোকলরে তখন বাকিটা বুঝতে বাকি থাকল না। সনাতন নামের সেই সমবয়সীর সঙ্গে পরিচয় করালেন স্যার। আর আমাদেরও বন্ধুত্ব হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আমরা এগোতে থাকলাম শালবনের দিকে। ওখানেই বাহাপরব বা বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আলাপও চলছে সমান তালে,
—সবাই মনেহয় চলে এসেছে।
—তাহলে তো দেরি হবে না, না?
—না-হওয়ারই কথা।
কথা বলছি; এঁকে চলেছি পায়ের ছাপ। ছাপড়া চালার বাড়িগুলোর গলিতে একটা পুকুর পেলেও পেলাম না তেমন গাছপালা। দুএকটি দাঁড়িয়ে আছে, যাদের একটা-আধটা রীতিমতো কুঁজো হয়ে গেছে; ডাল ডুবিয়ে জলপান করছে। আশপাশও খাঁ খাঁ করছে চৈত্রের দাবদাহে। কে বলবে, ঘণ্টাখানেক আগেই বৃষ্টি হয়েছিল একবার? নাকি কেবল কাঁকনহাটের দিকেই হয়েছিল, এদিকে হয়নি? জানা হয়নি কারো কাছে। জানতে মন চায়নি; এখনো চাইল না। পৌঁছতেও বেশিক্ষণ লাগল না। ক’মিনিটেই গন্তব্যের গাছপাড়ায় পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, তিনটি ধনুক গাড়া আছে; ফুলফোটা শালের তলে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ঘর।
—এ ঘর দুটি দুজন দেবতার জন্য বানানো হয়েছে।
—যেমন?
—একজন গোসাইঞঁ; অন্যজন মংরেংকু।
—আর মুরগিগুলো?
—ওগুলো বলি দেয়া হবে।
আরেকটু কাছে গিয়ে দেখলাম, উঠোনের এককোণে কুলোয় রাখা আছে কিছু ঘাস সিঁদুর শালফুল। ধান-চালও আছে বলে মনে হল। বেশিক্ষণ যেতে-না-যেতেই শোনা যেতে লাগল, ‘মারা: বুরো ছুট রে... কৌ রে বালি ভিটারে... দিদি তিরি লিক লিক করে।’ এরই মাঝে পুজোর আয়োজন শুরু করলেন সর্দার। কুলোতে তুলে রাখা ধান-চাল-শাল আর একঘটি জল সামনে নিয়ে বসলেন। পড়তে থাকলেন, ‘জোহার এবে খানদো, মরেকু তুরেকু, আলেয়া আতু নুনুমতে...।’
যাতে আরো দেরি না-হয়ে যায় তাই রান্নাবান্নায় লেগে গেলেন লোকজন। আমি আর সনাতন একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। দেখলাম, শাল-শিমুলের গাছ, গাছের ডালের শুকনো পাতা, আলপনা-আঁকা ভাঙা-আধভাঙা ছোটো ছোটো বাড়ি, কিছু জীবন আর কিছু জীর্ণতা। সমাজ-স্বীকৃত শীর্ণতার মাঝেও সুখের সন্ধান পেলাম। খুঁজে পেলাম একজন সুতন্বিকে, যে আমাকে আকর্ষিত করল। সে আকর্ষণে কোথায় যে হারালাম! যেন চলে গেলাম কোনো বিকেলের কোলে, যেখানে চোখ মেলে হাসছে আলোরা; আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি। ও গাইছে, আমি শুনছি। আমাদের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে তুলোর মতো মেঘ; টুকরো টুকরো, শাদা শাদা, নীল সালোয়ারে ফুলতোলা ফুটফুটে মেঘ। সে মেঘ-মেয়েরা নিয়ে আসছে কত কত কবিতা,
‘গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম ‘সুন্দর’-
সুন্দর হল সে।’
সে সত্যিই সুন্দর, সমস্ত সুন্দরতার মালকিন সে, যার আভাসে আমি আভাসিত; ঘোরগ্রস্ত। অথচ এত ঘোরেও ধরা হল না ওই হাত। ধরার আগেই ধরা পড়ে গেলাম নতুন বন্ধুর কাছে। কী আর আছে লুকোনোর? তবু লুকোলাম। হাসতে হাসতে বললাম,
-কিন্তু সিঁদুরেই তো সমস্যা।
—সে অবশ্য ঠিক।
—তোমরাও সিঁদুর দাও তাহলে?
—আরে সবার আগে আমাদের মধ্যেই তো সিঁদুরের চল শুরু হয়। তুমি দেখবে, পুরাণে ঘট স্থাপনের কথা বলা হলেও কোথাও সিঁদুরের উল্লেখ নেই। বাংলার ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পণ্ডিতসহ অনেকেই সিঁদুর দানের বিষয়ে পৌরাণিক কোনো শাস্ত্র খুঁজে পাননি। ফলে সর্বপ্রথম পালযুগে প্রচলিত প্রথানুসারে ‘শিষ্ট সমাচারাৎ’ মারফত সিঁদুর দানের স্বীকৃতি দেন তাঁরা। অথচ তারও আগে থেকে সিঁদুরপ্রথা জনপ্রিয় ছিল হিন্দুদের মাঝে। এবং তা এসেছিল আদিবাসীদের থেকেই।
—আমি অবশ্য জানতাম না।
—এই সিঁদুর নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। শুনবে?
—নিশ্চয়।
সে আমাকে শোনায় সেই চার বন্ধুর গল্প। যাদের একজন ছিল কাঠুরে, একজন স্বর্ণকার, একজন তাঁতি আর একজন ছিল সিঁদুর বিক্রেতা। একবার এক দূর দেশের উদ্দেশে রওনা দিল তারা। আঁধার নেমে আসছে এমন সময় পৌঁছল বিশাল এক বনের কাছে। সিদ্ধান্ত নিল সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু যেহেতু জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে সেহেতু একসঙ্গে সবাই ঘুমাবে না। পালাক্রমে রাত জাগবে। তো প্রথমে জেগে থাকল কাঠুরে। সময় কাটাতে কাঠ কেটে খুব সুন্দর একটা মূর্তি গড়ল। অতঃপর ঘুমাতে গেলে শুরু হল স্বর্ণকারের পালা। স্বর্ণকার সোনা দিয়ে সাজাল নারীমূর্তিটিকে। তার পর তাঁতি এসে শাড়ি পরাল। আর সবশেষে সিঁথিতে সিঁদুর দিল সিঁদুর বিক্রেতা। অমনি মূর্তিটি কথা বলে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল অন্যদের। দেখল, স্রেফ কাঠের মূর্তিটি হয়ে গেছে নারী, অপূর্ব সুন্দরী নারী। কাঠুরে বলল, ও আমার। অন্যরাও ওকে আপন করে চাইল। তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল চার বন্ধুর মধ্যে। এমন সময় উপস্থিত হলেন স্বর্গের দেবতা। প্রত্যেকে তাঁকে সবকিছু খুলে বলল। দাবি করল প্রাণ পাওয়া প্রিয় নারীটিকে। দেবতা হাসলেন। বললেন,
—যে ওকে বানিয়েছে, সে ওর বাবা। যে স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়েছে, সে হচ্ছে মামা। ভাই হচ্ছে সে, যে শাড়ি পরিয়েছে। আর সবশেষে সিঁদুর দিয়ে প্রাণ দিয়েছে যে, সে তার স্বামী।
সিঁদুর আর সৌন্দর্যের মধ্যে হারাতে হারাতে হেঁটে এলাম এক বয়সী গাছের কাছে। একবার মনে হল, এটি একটি সিরম গাছ। জগতের ঝড়ঝাপটা সামলেও টিকে আছে গাছটি। বুকে বেঁধে আছে পাখির বাসা। এসব বাসায় ডিম পাড়ে পাখিরা; বাচ্চা ফোটায়। মানুষের নয়; পাখির বাচ্চা। মানুষের বাচ্চা বেরুবে এ বিশ্বাস আমার নেই। তারপরও এটা তো আর সেই আদিগাছ নয়; পাকুড় গাছ। প্রকাণ্ড প্লাস শ্রীহীন। কতদিন এভাবে থাকবে কে জানে। আমিও যে কতক্ষণ থাকব, বুঝতে পারছি না। গাঁয়ে-ঘরে ঘোরার কিছু আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আদতে আর কিছু টানছে না আমাকে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে, যাই না-হয়, চলেই যাই। যাবারও প্রস্তুতি নিলাম যখন বন্ধু বলল,
—এবার একটু যেতে হবে যে।
—কোথায় যাবে বলছ?
—ওই যে ওদের কাছে। রান্নায় হাত না-লাগালে কেমন দেখায়। বুঝতেই পারছ?
বুঝি না বুঝি, দাঁড়িয়েই আছি। খারাপ না-লাগলেও ভালো লাগছে না। স্যারের সঙ্গেও সময় কাটাতে পারছি না। তিনি তো শুরু থেকেই বড়োদের সঙ্গে আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। এটা-ওটা টুকে নিচ্ছেন। একবার মনে হল, ওদিকটায় যাই, একটু কথা বলি। কিন্তু কী মনে করে গেলাম না। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। শুনতে পেলাম, ঢোল বাজছে। কে যেন টানছে। ঝুমুর পায়ে নাচছে নারীরা, যারা খোঁপায় গেঁথেছে শাল-শিমুল ফুল, বাতাসে দুলছে তাদের কোঁকড়ানো চুল, গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তারা গাইছে। অথচ কে যেন বরফ ছুঁইয়ে জ্বর এনে দিচ্ছে। শরীরটা বার কয়েক কেঁপে উঠল। ভালো না-লাগাও শুরু হল বলে বলা চলে বেরিয়েই পড়লাম। স্যারকে বললাম। সম্মতিও পেলাম। কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চাইল না সনাতন। সে আমাকে একরকম জোর করেই নিয়ে এল বনের প্রান্তের ছোট্ট বাসায়। বলল,
—এ ঘরে বিশ্রাম নাও। খিচুড়ি রান্না হোক! খাবে; তারপর যাবে। আর চাইলে চোলাইও চলবে আজ। খেয়েছ কখনো?
—সে সাহস হয়নি, বন্ধু।
—সাহসটা একটু করেই দেখ না! মাতাল না-হলে, বল তো, মজা কি মেলে? হা হা...
আমিও হাসি। আর যাবার জন্য জোর করি না। সে ফিরে গেলে বিছানায় এলিয়ে দিই নিজেকে। থেকে থেকে শুনতে পাই, কোনো কোনো কোমল কণ্ঠের হাসি। কেন জানি মনে হয়, কাকে যেন রেখে এসেছি ওইখানে। সেই রমণীকেই কি, রমণাভিলাষী শরীরে কাঁপন তুলেছিল যে, কিছু বলেছিল চোখ মেলে? মনে পড়তে থাকে ওই মায়ামুখ। উঠে বসি একবার। আবার শুয়ে পড়ি প্রচ- মাথাব্যথায়। আমাকে ঘুম পাড়ায় কিছু স্বপ্ন। সেই স্বপ্নলোকে চাঁদ ওঠে। ঝরে পড়ে চাঁদের আলো। সে-আলোয় সে ফিরে ফিরে আসে। নিয়ে আসে শাড়িতে জড়ানো সেই সুন্দরতা, সেই পুরু ঠোঁট আর শাদা শাদা ফুল। সেই ফুল, যা গোলাপ হয়ে যায়, ছড়ায় কেয়া-কামিনীর আচ্ছন্নতা। সে-আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যাই।
—কী চায়?
‘কালো রঙের আলো চাই আর চাই কিছু কোঁকড়ানো চুল। আমার একটু চোলাই চাই, চম্পা। আমি পান করতে চাই।’ খ্বু করে চাই, চাই-ই তো; অথচ চাইতে পারি না।
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া
-

লোরকার দেশে
-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান
-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার
-
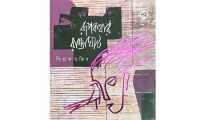
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
























