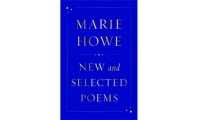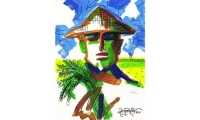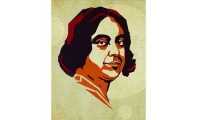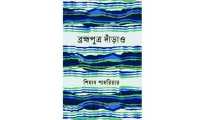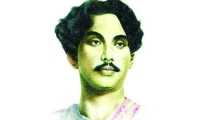সাময়িকী
‘মেঘের ভিতরে তুমি দ্যাখো কোন পাখির চককর?’
রুবী রহমান
বিয়ের পিঁড়িতে সৈয়দ শামসুল হক ও আনোয়ারা সৈয়দ হক
চলেছিলেন তিনি রজ্জুপথে। বড়ো অভাবনীয় আর ঝুঁকিপূর্ণ সেই পথ। বাংলাদেশের শিল্পানুরাগী মানুষেরা তাঁকে কবি সব্যসাচী নামে চিনেছিল। সব্যসাচী অর্জুনের মতোই তিনি ছিলেন লক্ষ্যে স্থির, একাগ্র। ‘জীবনের প্রচুর পকেট থেকে তিনি’ও রেখে গেছেন রাশি রাশি শব্দকুসুম। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যখন এই বাংলায় প্রায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যরুচি বিরাজ করছিল তখন তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। এক ঝাঁক তরুণ কবি, তরুণ লেখকের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি। এই তরুণদের হাতে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ভিত্তিভূমি আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা। নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল আলোয় আকাশ ছেয়ে তাঁরা ছিলেন মাথার ওপর। একে একে নিবেছে তারার বাতি। নক্ষত্রপাত ঘটিয়ে চলে গেলেন তিনিও, সৈয়দ শামসুল হক, এদেরই একজন। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, চিত্রশিল্পী-কি নন তিনি, শিল্প-সংস্কৃতির কোন প্রদেশে পড়েনি তাঁর পায়ের ছাপ!
সৈয়দ শামসুল হকের বয়ানে তারা ছিলেন ‘বাহান্নর সন্তান’। কী গভীর বিস্ময়, কী প্রগাঢ় উদ্দীপনা, কী নিগূঢ় দায়িত্ববোধ নিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁদের শিল্পযাত্রা। সেই পঞ্চাশের প্রথম প্রহরে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন এক নিবিড় ‘কবিসংঘ’। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, কাইয়ুম চৌধুরী- এঁরাই ছিলেন সেই কবিসংঘ। বাহান্নর চেতনা থেকে উদ্বোধন হয়েছিল তাঁদের শিল্পযজ্ঞের। তরুণবয়সে তাঁরা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বাংলা ভাষাকে রক্ষার গুরুদায়িত্ব। সেই সময়কার পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাহিত্যজগতে প্রকট ছিল মধ্যযুগীয় আবহ। তখনকার সেই তরুণ কবিসংঘ-সৈয়দ শামসুল হক যার কথা বলেছেন-সাহিত্য রুচিকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সাহিত্যে, কবিতায় তাঁরা আধুনিকতা আর সমকালীনতার সূচনা করেছিলেন। সেই প্রাণোচ্ছল তরুণেরা তাঁদের অপরিমেয় প্রাণশক্তি আর উদ্যম নিয়ে শিল্প সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছিলেন। তাঁদের সকল উদ্যোগ ছিল আনন্দে স্নাত। সৈয়দ শামসুল হক যখন তাঁদের মধ্যরাতে আড্ডা থেকে ঘরে ফেরার বর্ণনা দেন, তখন বোঝা যায় কত স্বতঃস্ফূর্ত, কত আনন্দময় আর কত শিল্পঘনিষ্ঠ ছিল সেইসব আড্ডা। সৈয়দ হক বলেন, ‘স্টেডিয়াম থেকে নবাবপুর রোড হয়ে প্রায় মধ্যরাত তখন আমরা দীর্ঘ আড্ডা দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম বাড়ির দিকে, তিনি (শামসুর রাহমান) আশেক লেনে, আমি লক্ষ্মীবাজারে, শহীদ কাদরী যাবে শিংটোলায়, কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছি ভিক্টোরিয়া পার্কের মোড়ে, এখান থেকেই বিচ্ছিন্ন হব আমরা-কবিতার পথেই কি?... আমি যদি জীবনানন্দ থেকে কয়েক পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে উঠেছি তো শামসুর রাহমান আবৃত্তি করে উঠলেন বুদ্ধদেব বসু থেকে, সহপথিক শহীদ কাদরী তখন অমিয় চক্রবর্তী থেকে বলে উঠলেন...’। এইমতো ছিল তাঁদের দিনানুদৈনিক শিল্প আড্ডা। আমার মতো লেখক, যে মহিলা, যার পক্ষে প্রায় অসম্ভব এরকম মধ্যরাতের শহরবিহার, তার জন্য নিতান্তই আকর্ষণীয় ও ঈর্ষণীয় এসব আড্ডা বৃত্তান্ত।
হক ভাই চলে যাবার দিন ছয়েক আগে হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। আধুনিক, স্মার্ট হক ভাইকে দেখে অভ্যেস হয়েছে আমাদের। এবারও তার ব্যত্যয় হয়নি। হাসপাতালের বিছানায় রোগীর পোশাকে শুয়ে আছেন কবি। মাস্ক-পরা ক্লান্ত মুখে হাতটি বাড়ালেন। কবি আমার বর নূরুল ইসলামকে নূরুল বলে ডাকতেন। বললেন, ‘নূরুলকে সেবার কুড়িগ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কী আবেগাপ্লুতই যে হয়েছিল।’ সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত গল্প ‘রক্তগোলাপে’র ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কবিপুত্র দ্বিতীয় সৈয়দ হক। কবিপতœী আনোয়ারা সৈয়দ হক হাসপাতাল কক্ষেই সেটি পাঠের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করেছিলেন। কবি-সম্পাদক মাহবুব আজীজ, কবি পিয়াস মজিদও সেই পাঠ প্রত্যক্ষ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সৈয়দ হক মন্দ্রস্বরে পাঠ শুরু করলেন তাঁর অনুবাদ। পাঠের আগে দ্বিতীয় তাঁর পূর্বকথন ধরনের বক্তব্যে তাঁর অনুবাদ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করলেন। প্রায় দু ঘণ্টা সময় লেগেছিল পাঠ শেষ হতে। এই দু ঘণ্টা কবি নিবিষ্টচিত্তে শ্রোতা হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এই আনুষ্ঠানিক পাঠে। কয়েকবার মনে হয়েছে ক্লান্তিতে তাঁর চোখের পাতা বুজে আসছে। কিন্তু ক্লান্তি-অবসাদ নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অতন্দ্র শ্রোতা হয়ে সচেতন থেকেছেন তিনি পাঠ-পর্বে। আমি আমার বর নূরুল ইসলামকে দেখেছিলাম মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিজ অভীষ্টের জন্য-অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য সচেষ্ট থাকতে। সেদিন হাসপাতালের ঘরে হক ভাইকে দেখে জানলাম এঁরা সকলেই যোদ্ধা, সকলেই বিপ্লবী। কবিতা-সাহিত্য-শিল্পের সাধনা আর সমাজ বদলের সাধনা একই পবিত্র সংগ্রামের এপিঠ-ওপিঠ। এই সকল প্রয়াসই মানুষের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ, মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। সাহিত্য রচনার প্রতিটি পর্যায়কেই সৈয়দ শামসুল হক সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমভাবে পবিত্র বলে বিবেচনা করেছেন। ওই কালব্যাধি শরীরে ধারণ করেও তাই তিনি নিষ্কম্প্র থেকেছেন। আমরা সেদিন দুই বা আড়াই ঘণ্টা পরে হাসপাতালের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আধুনিকতার উদ্গাতা সপ্রতিভ কবির স্মার্টনেসে এতটুকু চিড় ধরতে দেখা যায়নি। আমরা জেনেছিলাম সেদিন, মৃত্যুদুয়ারে দাঁড়িয়ে। তারপরেও নেপথ্যে কোথায় কোথায় যেন পঞ্চাশের প্রথম প্রহরের কবিসংঘের সেই নির্মল আনন্দ, মধ্যরাতের সেই অনাবিল উচ্চহাসির রেশ বেজে চলেছিল। এক প্রকৃত কবি আরেক মহান কবির বাণী ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’ মনে প্রাণে উপলব্ধি করবার প্রক্রিয়া বোধ করি শিখিয়ে দিয়েছিলেন হাতে ধরে। সেদিনকার তরুণ কবিসংঘের অনেকেই আজ গত হয়েছেন। মাথার ওপর থেকে সরে গেছে তাঁদের বরাভয় ছায়া। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে ‘হায়, তারা নাই, তারা নাই।’ তাঁরা তাঁদের কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে জানিয়ে গেছেন কালজয়ের তথ্য, অমরত্বের সমাচার। তাই আশ্বাস জেগে ওঠে, কবির প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখি : ‘থেকে যাবো কবিতার পঙ্ক্তি হাতে অপার কাঙাল ॥’
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-
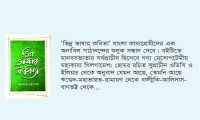
আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-
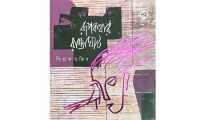
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
-
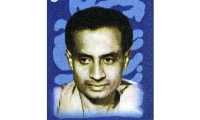
বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ বিষয়ভাবনা