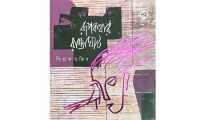সাময়িকী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বনির্মিত ও প্রান্তজনের কথাশিল্পী
বাদল বিহারী চক্রবর্তী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় / জন্ম : ১৯ মে, ১৯০৮; মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬
বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে উজ্জ্বলতর একটি নাম- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশবে লোকে যাঁকে আদর করে ডাকত কালো মানিক। এক বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যাঁর আবির্ভাব, ধূমকেতুর মতো যাঁর উত্থান, আবার অতি অল্প সময়েই জীবনের মধ্য গগন হতে উল্কার মতো যিনি পড়ে গেলেন- অজস্র তাঁর সাহিত্য-সম্ভার রেখে, তিনিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশবোত্তর জীবনের প্রতি পলে পলে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধকরা যে জীবনশিল্পী, ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ দুরন্তপনায় সিদ্ধ যে মানুষটি, সেই মানুষটিই রাতের পর রাত জোছনায় মগ্ন থাকতেন আড়বাঁশি বাজিয়ে; গাইতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত কিংবা অতুলপ্রসাদের গান। অমর এ সাহিত্যব্রতীর সাহিত্য সাধনা আর সংসার যাপন যেহেতু চরম অভাবের মধ্য দিয়ে কাটে, তাই তাঁর রচনায়, গল্প-উপন্যাসে নিজ জীবন কাহিনীর মতোই রূঢ় বাস্তব ও কঠিন চিত্র তিনি সুনিপুণ হাতে তুলে ধরেছেন।
কল্লোলীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা শুরু করা মানিকবাবু সক্ষম হয়েছিলেন মানবমনের গভীর জটিল মুহূর্তকে তুলে এনে মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা মগ্নচৈতন্যের অতলশায়ী বোধকে প্রকাশ করতে। কেননা, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব আর মার্কসীয় জীবন দর্শন ছিল তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। তাইতো তাঁকে নিয়ে ‘পুড়ে যায় জীবন নশ^র’ নামে গ্রন্থ লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য।
সাহিত্যক্ষেত্রে ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ নামে তিনি পরিচিত হলেও জন্মের পর থেকেই তাঁর যে দুটো নাম ছিল সেগুলো তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরজাসুন্দরী দেবীর চার ছেলেমেয়ের পর ১৯০৮ সালের ১৯ মে জন্ম হলো ঘুটঘুটে এক কালো ছেলের। গায়ের অমন রং দেখে আঁতুড় ঘরেই নাম দেয়া হলো ‘কালো মানিক’। গণক দেখিয়ে ঠিকুজিতে নাম রাখা হল অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সে নামেও কেউ কোনদিন ডাকল না। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধ করে নাম রাখলেন প্রবোধকুমার; অধরাই থেকে গেল পিতৃপ্রদত্ত নাম। এদিকে ভালোবেসে ‘কালো মানিক’ বলেই ডাকত সকলে। একদিন এ নাম থেকে ‘কালো’ শব্দটা ওঠে গিয়ে পড়ে রইল শুধু ‘মানিক’। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে ওই নামেই জীবনের প্রথম গল্প ‘অতসী মামী’ লিখে পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। যেহেতু রোমান্টিকতায় পূর্ণ ‘অতসী মামী’ গল্প, তাই বাবার দেয়া নাম-প্রবোধকুমারের বদলে ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ নাম দিয়ে তিনি ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা দফতরে গেলেন গল্পটি ছাপাতে। সেই সময় সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দফতরে ছিলেন না; ছিলেন সাহিত্যের আরেক দিকপাল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বিনোদ ঘোষাল অচিন্ত্যবাবুর লিখা স্মৃতিকথা তুলে ধরেন, “একদিন বিচিত্রার দফতরে কালোপানা একটি লম্বা ছেলে এল। বলল-গল্প এনেছি। বললাম, দিয়ে যান, সেই ছেলে লম্বা হাত বাড়িয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলল, এই যে রাখুন। এমন ভাব যেন এখুনি ছাপতে দিয়ে দিলে ভাল হয়। চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস চুঁইয়ে পড়ছে। গল্প জমা দিয়ে সে চলে গেল। আমি তারপর এমনিই গল্পে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ যে রীতিমতো দুর্দান্ত গল্প!”...বলা যায় পাঠক মহলে ঈর্ষণীয় সাড়ায় সেদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি তথা সাহিত্যাকাশের জ্যোতির্ময়।
মার্কস এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দর্শনে বিশ^াসী মানিকবাবু মনে করেন সমাজকে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে সমঝদার শিল্পীর নিখুঁত আঁকা সমাজচিত্র প্রয়োজন। তেমন একজন জীবনশিল্পীই পারেন তাঁর তুলি কিংবা লেখনীর মধ্য দিয়ে সামাজিক বিচ্যুতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বরূপ তুলে ধরে তা দূর করে শাসন-শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে। কিন্তু তাঁর মতো একজন রণক্লান্ত জীবনযোদ্ধা কি পেরেছেন তেমন একটি সমাজ গড়ার আবহ তৈরি করতে? হয়তো অনেকটা পেরেছেন, অনেকটা পারেননি। ভারতবর্ষের মতো দীর্ঘদিনের সামন্তবাদ-পুঁজিবাদ, কলোনিয়্যাল শোষণ ব্যবস্থার অচলায়তন ভাঙা সত্যিই দুরূহ। তবে তিনি কলম চালিয়ে গেছেন অহর্নিশ। তাঁর মতো একজন কলমযোদ্ধা আজীবন সাধারণ মানুষকেই তাঁর সাহিত্যে প্রধান ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, উপজীব্য করেছেন পূর্ববঙ্গের অতি সাধারণ মানুষ ও জীবনচিত্রকে। অবশ্য অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিক-কৃষক সর্বহারা মানুষদেরও নিখুঁত রূপালেখ্য ছিল তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর কালজয়ী আঞ্চলিক ভাষার উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আর ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-র কথা। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় উপন্যাস হিসেবে ধরলে ‘পদ্মানদীর মাঝি’র ক্রম প্রকাশ পায় চতুর্থ উপন্যাসে। লক্ষণীয় যে, সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একাধিক বিদেশী ভাষায় অনুদিত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস হলো ‘পদ্মানদীর মাঝি’। অনস্বীকার্য যে, এ দুটো উপন্যাসই পাঠকমহলে বেশি পরিচিত।
ভারতের উত্তরাখ- রাজ্যে অবস্থিত পশ্চিম হিমালয়ের উৎসমুখ থেকে নেমে আসা ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের ভিতর দিয়ে ‘গঙ্গা’ নামে প্রবাহিত অনেক আঁকাবাঁকা পথ ধরে যে নদী, তা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ‘পদ্মা’ নাম ধারণ করে যেন আরো ক্ষিপ্ত গতি লাভ করেছে। এ নদী বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। একে ‘কীর্তিনাশা’ বা ‘রাক্ষুসী পদ্মা’ও বলা হয়ে থাকে। কেননা, এর স্বভাব প্রকৃতিতে রয়েছে সর্বনাশা ভাঙন প্রবণতা ও প্রলয়ংকরী চিত্র। পদ্মানদীকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে নদীপারের নিম্নবর্ণের পাড়ার মাঝিদের ধীবরদের জীবনধারা ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটিতে তুলে এনেছেন মানিকবাবু। এ পাড়ার জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, কলহ-সংঘাত কিংবা প্রেম-প্রীতি সবই এ জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এদের জীবনের দিনাতিপাতকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। অসাধারণ নিখুঁত এক জীবনশিল্পের চিত্র। দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা, দু’বেলা দু’মুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা ধীবরদের একজন কুবের মাঝি। আর ওদিকে স্বামীকে ছেড়ে আসা কপিলা তার সম্পর্কে শ্যালিকা। কুবেরের সঙ্গে কপিলার নিষিদ্ধ অনৈতিক সম্পর্ক সংসারে এক জটিল মুহূর্ত তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি-“উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সস্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণি অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কণে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ”।...উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের বিক্রমপুর ও ফরিদপুর অঞ্চল-দেবীগঞ্জ ও আমিনবাড়ি গ্রাম। পদ্মার তীরবর্তী এ দুটো স্থানের নাম ছিল যথাক্রমে গোয়ালন্দ ও রাজবাড়ী। ধীবর সম্প্রদায় ছাড়াও উপন্যাসের আরেকটি বিচিত্র চরিত্র এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম-হোসেন মিয়া। নোয়াখালীর এই লোকটি বহুদর্শী ও বহু অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি। নোয়াখালীর সন্দ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রের বুকে তার আবিষ্কৃত ময়না দ্বীপ তার পত্তন নেয়া। রহস্যময় এ ব্যক্তির প্রভাব ও প্রবল শক্তিমত্তার কাছে বেচারা জেলেরা ছিল অনুগত ও অনন্যোপায়। ময়না দ্বীপটি ওখানকার মানুষদের কাছে যেন এক কল্পলোকের বার্তাবাহী স্থান। কৌশলী চতুর হোসেন মিয়ার ইশারায় যার মোহে আচ্ছন্ন মানুষ সেই অচেনা অজানা রহস্যময় জীবনকে বরণ করার জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে; যে পথের যাত্রী ছিল কুবের ও কপিলা।
প্রথমেই আসি ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র কথা। বস্তুবাদী দর্শনে বিশ^াসী হলেও সমাজের অদৃশ্য শক্তির সূতোটা যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই অদৃষ্টকে অস্বীকার করতে পারেননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দেখেছেন অসংখ্য স্থান-কালের মানুষগুলোর মধ্যে কার্যকারণ ও শেকলে বাঁধা নিয়তি। তেমনি এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে মানিকবাবুর ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে। এ গাঁয়ের জীবনগুলোর জটিল ও সমস্যাপূর্ণ চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি এখানে রোমান্সের মায়াকে পরিহার করে তুলে ধরেছেন এক দুঃখ-বেদনা দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ জীবনের কথা। উপন্যাসের প্রধান ও অনন্য পুরুষ চরিত্র শশী ডাক্তার। পল্লীগ্রামই তার কর্মক্ষেত্র। বজ্রাঘাতে হারু ঘোষের মৃতদেহ আবিষ্কারের দৃশ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু আর বিজ্ঞাননিষ্ঠ শশী ডাক্তারের মাটির টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দর্শনের শখের অতৃপ্ততা দিয়ে শেষ হয় এ উপন্যাসের। কলকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শশী (শহরের আত্মজনদের জন্য ব্যাকুল ও উদ্ভ্রান্ত হলেও) এক দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে গাঁয়ের জীবনপ্রবাহের প্রতি। যদিও শশীর কাহিনি নির্ভরই এ উপন্যাস, তবুও তার অস্তিত্বের শেকড় ও এর শাখা-প্রশাখা প্রোথিত হয়ে আছে অন্যান্য চরিত্রের ছোটবড় ঘটনার অনুষঙ্গে, এই জটিলতাকে সে অনুভব করে-পিতা, ভগ্নি, পরান-ভার্যা রহস্যময়ী কুসুম, নির্লিপ্ত উদাসীন কুমুদ ও তার অনুরূপ স্ত্রী মতির মধ্যে। অপরের বিবাহিত স্ত্রী কুসুমের প্রতি শশীর এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ যার বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু পূর্ণতা পায়নি কোনদিন। তাই বলা যায়, নিরাসক্ত অথচ জীবনের সঙ্গে সংবদ্ধ শশী যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রতিরূপ। এই শশীকেই কুসুমের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান থাকতে হয়েছে, নির্বাক সাক্ষী হতে হয়েছে যাদব প-িতের ‘স্বেচ্ছামৃত্যু’ নামক প্রহসনে। আবার মাতৃসমা সেনদিদির প্রতি এক রহস্যময় সম্পর্কের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি শশী দেখেছে ‘নিয়তি’ নামক অলীক সত্তার সুতো ছিঁড়ে জীবন-উপভোগের মহাযজ্ঞে বেরিয়ে পড়ার দৃশ্য, কুমুদ-মতির জীবনাগ্রহের প্রাবল্যে। তাই সহসা-ই প্রশ্ন জাগতেই পারে-পরিপাশের্^র স্থান-কাল-পাত্রের কে বা কারা পুতুল? কে-ইবা টানছে ওই পুতুলের সুতোটা ধরে!
ছোটবেলা থেকে ডানপিটে, দুরন্তপনায় সিদ্ধ মানিক স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় বরাবর ভাল রেজাল্ট করলেও (রাজনীতি বিশেষকরে কম্যুনিজম নিয়ে বেশি ঝোঁকে পড়ায়) বি,এস-সি,-তে পরপর দু’বার ফেল করে বসলেন। তখন তাঁর পড়াশোনার খরচ চালাতেন তাঁর বড়দা। ক্যারিয়ার গড়ার পাঠ রাজনীতিতে মনোনিবেশ করায় দাদা ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি লিখলেন, “তোমাকে ওখানে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়েছে, ফেল কেন করেছ, তার কৈফিয়ত দাও।” উত্তরে মানিক লিখে জানালেন যে গল্প, উপন্যাস লেখা এবং রাজনীতি তিনি ছাড়তে পারবেন না। তাতে আরও রেগে গেলেন দাদা। ভাইয়ের সাহিত্য চর্চার জন্য টাকা পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন দাদা। টাকা আর না-আসায় মানিকবাবু দাদাকে লিখলেন, “আপনি দেখে নেবেন, কালে কালে লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমার নাম ঘোষিত হবে।”... তিনি লিখেওছিলেন অজস্র গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম-উপন্যাস : দিবারাত্রির কাব্য, জননী, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, শহরতলী, অহিংসা, শহরবাসের ইতিকথা, চিহ্ন, চতুষ্কোণ, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী, আরোগ্য ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ : অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, সমুদ্রের স্নান, আজকাল পরশুর গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি।
একে তো আজীবন দুরন্তপনা, খামখেয়ালি, তার উপর য়োল বছর বয়সে মা-কে হারাবার পর আরও ছন্নছাড়া হয়ে গেল মানিকবাবুর জীবন। দাদার হাত ফিরিয়ে নেয়ায় শুরু হলো দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রকৃত লড়াই। ...নতুন জায়গা, আমহর্স্ট স্ট্রিটের একটি মেসে চলে এলেন মানিক। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিবারাত এক করে তিনি শুধু লিখে চলেছেন, ধর্ণা দিচ্ছেন প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে। নিজের শরীরের কথা না-ভেবে অমানুষিক পরিশ্রম ডেকে আনল ক্ষয়িষ্ণু জীবনের এক দুর্বিসহ রূপ। এক সময়কার কুস্তিলড়া, একসঙ্গে দশজনকে মোকাবেলা করা মানিক ভেঙে পড়লেন দিনকে দিন। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ মানুষের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখা তাঁর এক অমর উপন্যাস। সেই রচনায়ও এক প্রেরণা পান তিনি- যখন ১৯৩৩ সালে কলকাতায় এসেছিল এক বিখ্যাত পুতুলনাচের দল, তার দর্শন মুগ্ধতায়। সে মুগ্ধতা তাঁর লেখার উপকরণ যোগালেও লেখার নিবিষ্টতায় তিনি নিজের কথাই ভুলে যেতে থাকলেন। তাঁর ২৮/২৯ বছর বয়সে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাণান্ত সাহিত্য সাধনার এক পর্যায়ে তিনি দূরারোগ্য মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। ওদিকে পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন তাঁর প্রতি। নিজের রোগের সঙ্গে, চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে মুখোমুখি চলছিল দাঁতে দাঁত চাপা লড়াই। এমন এক অসহনীয় রোগ তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছিল না দুদ-। এক পর্যায়ে রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনি কী করবেন, ঠিক ছিল না। ফলে মদ্যপান শুরু করেন মাত্রাতিরিক্ত। সম্ভবত তাঁর অবিমৃষ্যকারী অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা করেই তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় ডাঃ বিধান রায়ের পরামর্শে। এত লেখালেখির পরও যখন সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন একটা চাকরি নিয়েছিলেন মানিক। কেননা, বাবাকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বরানগরের একটি ঠাসাঠাসি বাসায় একসঙ্গে থাকবেন বলে। কিন্তু বিধি বাম, কিছুদিন পরই চাকরিতে ইস্তফা।
দারিদ্র্য যে কী ভয়ংকর, তা মানিকবাবুর ডায়েরির একটি পৃষ্ঠা পড়লেই বোঝা যায়। এরই মধ্যে তাঁর স্ত্রী কমলা (ডাকনাম-ডলি) একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। আর সে প্রসঙ্গেই তিনি ডায়েরিতে লিখছেন, “বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল, বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করেছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।” ...কত হৃদয় বিদারক সমাধান! সংসারের এমন অবস্থায় তিনি আবার চাকরি নিতে মনস্থির করলেন। সাপ্তাহিক ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় পেলেনও কাজ। কিন্তু এখানেও টেকেননি বেশিদিন। তবু লিখে চলেছেন ; যুক্ত হলেন বামপন্থী ফ্যাসীবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের আন্দোলনে। তখনকার কলকাতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা রুখতে কখনও তিনি একাই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সেই আন্দোলন স্তব্ধ করতেই নেমে এল বামপন্থীদের ওপর চরম সরকারি দমননীতি। এক ভয়াল সঙ্কটে গোটা পরিবার। পরিবারের প্রত্যেকের ক্ষুধার্ত মুখের দিকে যেন আর তাকানো যাচ্ছিল না। নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে থাকলেন মানিক। অনন্যোপায় হয়ে দাদার কাছে কিছু ধার চেয়ে আবার লিখলেন। দাদা প্রত্যোত্তরে জানালেন আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয়- কাউকে তিনি টাকা ধার দেন না। ভাইয়ের সঙ্গে পাবলিশিং হাউজের ব্যবসাও পড়ে গেল মুখ থুবরে। এদিকে লিভার নষ্ট হতে থাকা মানিক (পুতুলনাচের পুতুল) বিপর্যস্ত, অনটনের নির্মম শিকার বড্ড অস্ফুটস্বরেই বলেছিলেন, ‘দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।”
দিনের পর দিন বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার অনিচ্ছা থাকলেও না নিয়েও পারছিলেন না। বন্ধুদের সহায়তায় বাড়িওয়ালার বাড়ি ভাড়ার মামলার তারিখ তিনি অগত্যা পেছাতে সক্ষম হলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর জীবনের আদালতের চূড়ান্ত রায় হয়তো শুনতে পায়নি কেউ। এমতাবস্থায় তাঁকে নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো প্রথমে ৩০ নভেম্বর, ১৯৫৬ এবং পরে ২ ডিসেম্বর। এদিন সম্পূর্ণ অবচেতন, জ্ঞান হারালেন তিনি। খবর পেয়ে কবি কমরেড সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছুটে এলেন হাসপাতালে। কিছুক্ষণ পরই অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথার’-র পুতুলকে। এবার আর বাড়ি অভিমুখে নয়। মহাপ্রস্থানের পথযাত্রা। ৩ ডিসেম্বর চারটেয় দীর্ঘদিন প্রাণান্ত লড়াইয়ের পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন আটচল্লিশ বছরের এক সংগ্রামী জীবন। শববাহী গাড়ির পালঙ্কে তোলা হলো তাঁর নশ^র দেহ। সুভাষবাবু শোকাতুরা লেখকপতœীকে অনেকটা অনুযোগেই বললেন, “বৌদি, এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেননি কেন?” তখন ম্লান হেসে বৌদি কমলা উত্তর দিলেন, “তাতে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।... সেটুকুও নেই যে ঘরে।”
বরেণ্য এই লেখকের অকালমৃত্যুতে তাঁর শেষ দুই দিনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা-“পালঙ্কসুদ্ধ ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হয় তখন একটা চোখ খোলা, একটা বন্ধ। শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপচে পড়ছে দু’পাশে...। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা এবং সাহিত্যিক! সামনে পিছনে দুই পাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভিড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না, কিছু ছিল না... জীবনে এত ফুলও তিনি পাননি। ”
বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন-
“ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে,
মালা জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল জমতে জমতে পাথর,
পাথরটা সরিয়ে নাও আমার লাগছে।”
আমরা বারবার ভারাক্রান্ত হয়ে যাই এই অকালপ্রয়াত লেখককের কথা আলোচনা করতে গিয়ে। আজ অশেষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এই বিদগ্ধ জীবনশিল্পীকে।
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব