সাময়িকী
ধারাবাহিক স্মৃতিকথা : ৮
স্মৃতির অতল তলে
আবদুস সেলিম
(পূর্ব প্রকাশের পর)
গত কিস্তিতে একটি অমার্জনীয় ভুল করেছি- যা এই কিস্তির শুরুতেই সংশোধন করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অনাবধানবশত আমার অতি প্রিয় শিক্ষক রাজিয়া খান আমিন-এর নাম ভুল লিখেছিলাম “রাজিয়া সুলাতানা খান আমিন” রূপে। এর কারণ আমার অবচেতন মনে আরও একজন “রাজিয়া” নামের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সাথে আমি দীর্ঘ দিন শিক্ষকতার কাজ করেছি- সরকারি কলেজে, ঢাকা ব্রিটিশ কাউন্সিলে, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, এবং অ্যাটজাংক্ট শিক্ষক হিসাবে অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর পুরো নাম রাজিয়া সুলতানা খান- অত্যন্ত মেধাবী এবং বন্ধুবৎসল। ইংরিজিতে ছোটগল্পের কয়েকটি প্রকাশনাও আছে তাঁর। যাইহোক, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক এবং শ্রদ্ধেয় রাজিয়া খান আমিন-এর পরিবারের কাছে মার্জনা প্রার্থী।
আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আবাসিক হবার অনুমোদন পাবার পরও হলে আবাসিক হতে পারিনি প্রায় এক মাস পর্যন্ত, সে কথা আমি আগেই লিখেছি। এর মূল কারণ অনেকেই এম. এ. পরীক্ষা দেবার পরেও রুম ছাড়তে গড়িমসি করতো কোনও চাকরি অনুসন্ধানের কারণে ঢাকাতে থাকার প্রয়োজনে। এটা তারাই করতেন যারা ঢাকার বাইরে থেকে পড়াশোনা করতে আসতেন, যদিও আমার চাইতে মেধাবী যারা ছিলেন তাদের আমার মতো এতদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। আমি কীভাবে হলে এসেছি সেকথাও আগের এক কিস্তিতে বর্ণনা করেছি যার পুনারাবৃত্তি করতে চাই না।
হলের সবারই মুরগির চ্যাপ্টা রান খাবার প্রতি আগ্রহ ছিল বিধায় অনেকেই বেশ তড়িঘড়ি দুপুরের খাবার খেতে চলে আসতো- তাদের মধ্যে অনেকেই সকালের নাস্তা না করে বারোটার ভেতর আক্ষরিক অর্থে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিত
হল-জীবন প্রাথমিকভাবে আমার জন্য তেমন সুখকর ছিল না, বলাই বাহুল্য। কারণ আমরা যারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত- অর্থাৎ কলেজে পড়া পর্যন্ত- বাড়িতে মায়ের স্নেহ ছায়াতে থেকেছি তাদের পক্ষে হঠাৎ করে স্বনির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমার ব্যাপারেও সেটা হয়েছে।
হলের জীবনযাপন সকল বিচারে বেশ বৈচিত্র্যময়। যেমন এতগুলো মানুষ একই বিল্ডিং-এ বসবাস করাটাই এক বিচিত্র ব্যাপার বৈ কি! সলিমুল্লাহ হলের দুটি “উইং”- ইস্ট এবং ওয়েস্ট। হলটি বিস্তৃতিতে যথেষ্ট বড় এবং মুসলিম এবং ইংরেজ স্থাপত্যের সংমিশ্রণে এক রাজকীয় স্থাপনা- এখনও আমি যখন ঐ হলের সামনে দিয়ে যাই সেই রাজকীয়তার স্পর্শ বাস্তব অনুভব করি। আমি বলতে পারবো না নির্দিষ্ট করে ঐ সময়ে আমরা কতজন ছাত্র আবাসিক ছিলাম, তবে সংখ্যাটি যে যথেষ্ট ভারি ছিল তাতে সন্দেহ নেই।
যা বলছিলাম, সলিমুল্লাহ হলের দুটি ভাগ, এবং ঐ দু’ভাগের সীমানির্দেশ করা আছে একটি লম্বা করিডোরের মাধ্যমে। দু’ভাগের মাঝ বরাবর, তখন, খোলা চতুষ্কোণ বাগানসহ লন ছিল- ছিল বলছি কারণ আমার জানা নেই বর্তমানে সেই বাগানসহ লনটি আছে কিনা। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর একবার বা দুবার হলে গিয়েছিলাম, তখনও ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর আর যাওয়া হয় নি। ইংরেজিতে বলতেই হয়: ও ৎবধষষু সরংং ঝ. গ. ঐধষষ!
কিন্তু ঐ সুখকর না থাকার জীবন থেকে আমারই অজান্তে কীভাবে অতিসুখকর জীবনে উত্তরণ ঘটলো তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। এত মানুষ এক সাথে থাকা এবং একটি ঘরে চারজন করে বসবাস করা, এর যেমন অ-সুখকর অভিজ্ঞতা আছে তেমনি এক রহস্যময় সুখও আছে। প্রতিটি মানুষ তার নিজস্বতা নিয়ে এক অনন্য সৃষ্টি। অথচ No man is an island. ফলে মানুষের সাথে মানুষের মিলেমিশে থাকার এক অপূর্ব চর্চার স্থান এই হলজীবন। রবীন্দ্রনাথ-এর কবিতার গভীর উপলব্ধি হয়েছে আমার এই হল-জীবনে আমারই নিজস্ব পথে: কত অজানারে জানাইলে তুমি/কত ঘরে দিলে ঠাঁই/দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু/পরকে করিলে ভাই...। আজ শিক্ষক হিসাবে যখন আমার ছাত্রদের রেফারেন্স লেটার দিই বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য তখন একটি কথা লিপিবদ্ধ করতেই হয়: She/He can mix with people easily. এই মানুষের সাথে সহজে মেশা যে জ্ঞান চর্চা, ভব্যতার চর্চা এবং সর্বোপরি সত্যিকারে মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য কত জরুরি তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।
সলিমুল্লাহ হল ঈস্টে আমি যে রুমে থাকতাম সেটি একটু ব্যতিক্রমী রুম ছিল- রুমটা ছিল তিনজনের জন্য, বা প্রচলিতভাবে আমরা যাকে বলি “থ্রি-সিটেড রুম”। আমার সাথে ছিল মোহাম্মদ জমীর আলী এবং আর একজন চট্টগ্রাম থেকে আসা স্নাতকোত্তর প্রিলিমিনারির ছাত্র (কোন বিষয়ের মনে করতে পারছি না)। আর ছিল হায়াত হোসেন। মোহাম্মদ জমীর আলী এবং হায়াত হোসেন সম্মন্ধে কিছু না লিখলেই নয়।
মোহাম্মদ জমীর আলী ছিল আইয়ুব খান-এর উন্মাদ ভক্ত- আইয়ুব খান কর্তৃক সৃষ্ট ছাত্রপ্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (এন. এস. এফ) মুসলিম হল শাখার প্রধান নেতা। ভীষণ নামাজি, উদ্ধত বক্তা- বিশেষ করে ভারত বিদ্বেষী- এবং অন্ধ আইয়ুব ভক্ত। মনে আছে আইয়ুব খান যখনই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সফরে অসতো জমীর উদ্দিন ভোর-সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজকালাম পড়ে (সে অবশ্য প্রতিদিনই ভোরে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে জোরেজোরে কোরআন শরিফ পড়তো), দাড়ি কেটে, গোসল সেরে মাথায় আইয়ুব-টুপি পরে প্রস্তুত হতো বিমানবন্দরে তার নেতা আইয়ুব খানকে স্বাগত জানাবার জন্য। জমীর আলী এসব সময়ে বারংবার ইংরেজিতে বলতো: My great leader is coming! আমি অবশ্য বলতে পারবো না এই স্বাগত জানাবার দৃশ্যটি বাস্তবে কেমন ছিল। অন্যদিকে হায়াত ছিল আমার ইংরেজি বিভাগেরই স্মার্ট সহপাঠীর অন্যতম। সে তখনকার সময়ের একমাত্র ক্যাডেত কলেজ- চট্টগ্রামে অবস্থিত ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। আমরা সবাই জানি এই কলেজ এবং পরবর্তিতে রাজশাহীর সারদাতে প্রতিষ্ঠিত (যে কলেজে আমার “আনুষ্ঠানিক” এবং “বৈধ” ভাবে অধ্যাপনা পেশায় হাতে খড়ি) আইয়ুব ক্যাডেত কলেজ পাকিস্তান সেনা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কঠোর নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হায়াত বেশ সিগারেট পান করতো, মেয়েদের ভেতর সে দারুণ প্রিয় একটি নাম ছিল, তার মুখেই একাধিক মেয়ের সাথে তার সম্পর্কের গল্প শুনেছি- সত্যমিথ্যা বলতে পারবো না। চট্টগ্রামে তার বাবা পেশাতে আইনজীবী ছিলেন বলে মনে পড়ছে।
তো, এহেন কলেজে পড়াশোনা করা হায়াত হোসেন যে কতটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী, “বোহিমিয়ান”, বামপন্থী চিন্তাতে উদ্বুদ্ধ, এবং পাকিস্তান বিরোধী, আইয়ুব বিরোধী, মুসলিম লীগ বিরোধী ছিল তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়। মোহাম্মদ জমীর আলী এবং হায়াত হোসেন- এই দুই বিপরীত মেরুর দুটি মানুষ একই ঘরে কীভাবে সহ-বাস করতে পারে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি- আর একেই আমি বলেছি “প্রতিটি মানুষ তার নিজস্বতা নিয়ে এক অনন্য সৃষ্টি”, এবং সেই অনন্যতাটাই হলো জীবনের বৈচিত্র্য।
একবার মনে আছে এমন এক গোলযোগের সময় আমি রুমেই ছিলাম- সম্ভবত এমন কোনো গোলযোগ হবার আভাস আগে ছিল না- আকস্মিকই ঘটেছে- হঠাৎ সারোয়ার ঘরে ঢুকে জানতে চাইলো হায়াত-এর সিট কোনটা, এবং আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বিছানাপত্র, জামাকাপড় লনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল
জমীর আলির সাথে হায়াত-এর খটমট লেগেই থাকতো। বিপরীতে আমি ছিলাম নির্বিবাদী নিরীহ মানুষ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে- আগেই বলেছি- গোবেচারা লাজুক ছাত্র ছিলাম। আমার সাবলীল ইংরেজি বলার অভ্যাস তখনও রপ্ত হয় নি। অন্যদিকে আমার চাচাত ভাই সাদুল্লাহ এবং হায়াত স্বচ্ছন্দ অনর্গল ইংরেজি বলতে পারদর্শী ছিল। যে কোনো মেয়ের সাথে সজেই বন্ধুত্ব করতে পারতো।
যেমন বলছিলাম, হায়াত এবং জমীর ছিল দুই মেরুর মানুষ। এ দুজনের জীবনযাত্রা নিয়ে অনেক “অ্যানেকডোট” আছে যার সবটা বর্ণনা করা সম্ভব নয় শালীনতা এবং সমসাময়িকতার কারণে। এন. এস. এফ., অর্থাৎ মোহাম্মদ জমীর-এর দল, মারামারি এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করায় বেশ পারদর্শী ছিল এবং এমন মারামারি হাঙ্গামা হলে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও ঘটতো- তবে এটাও ঠিক এখন যতটা ঘনঘন ঘটে ঠিক ততটা ঘনঘন ঘটতো না। হলে যখন এমনটা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিত তখন জমীর আলী এবং তার স্যাঙ্গাত সারোয়ার আমাকে এবং আমার চাচাত ভাই সাদুল্লাহকে আগেই বলে রাখত যেন আমরা ঐ দিন এবং ঐ রাতে হলে না থাকি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো প্রায় প্রতিবারই আমাদের রুমটি এই তা-বের শিকার হতো শুধু মাত্র হায়াত-এর জন্য। এন. এস. এফ-এর মারকুটেরা হায়াত-এর জামা-কাপড়, বিছানাপত্র এবং বইখাতা সামনের লনে ছুঁড়ে ফেলে দিত। হায়াত রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল, ছাত্র ইউনিয়ন করতো- আমিও করতাম, কিন্তু তার মতো অত সক্রিয় ছিলাম না বা হতেও পারিনি- কারণটা বোধগম্য। আমাদের সময় ছাত্র ইউনিয়ন একটিই ছিল- মেনন, মতিয়া ভাগাভাগি ছিল না। সেটা হয়েছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর।
একবার মনে আছে এমন এক গোলযোগের সময় আমি রুমেই ছিলাম- সম্ভবত এমন কোনো গোলযোগ হবার আভাস আগে ছিল না- আকস্মিকই ঘটেছে- হঠাৎ সারোয়ার ঘরে ঢুকে জানতে চাইলো হায়াত-এর সিট কোনটা, এবং আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বিছানাপত্র, জামাকাপড় লনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমাদের সময় ইংরেজি সাহিত্যের মূল পাঠ্য বইয়ের অনেকটাই যোগান দিত ঢাকা ব্রিটিশ কাউন্সিল। এই বইগুলো আমাদের বিভাগে ভর্তি হবার সাথেসাথেই প্রত্যেকের নামে ইস্যু করা হতো এবং তিন বছর পর অনার্স পরীক্ষা শেষ হলে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ফেরত দিতে হতো। যে ঠিক মতো ফেরত দিতো না তার রেজাল্ট আটকে (withheld) রাখা হতো।
হায়াত-এর বিছানাপত্র এবং জামাকাপড় নিয়ে আমার তেমন কোনো উদ্বেগ ছিল না যতটা ছিল তার বইগুলো নিয়ে, কারণ বইগুলো দেশে সহজলভ্য ছিল না এবং সেগুলো ফেরত না দিলে অনার্স পরীক্ষার পর তার রেজাল্ট withheld হয়ে থাকবে। আমি ফলে দ্রুত চিন্তা করে সারোয়ারকে বলেছিলাম ওই সবগুলো বই আমার, এবং সে আমার কথা সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়ে বইগুলোকে রেহাই দিয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম না এসব বইয়ের কোনটিই শেষপর্যন্ত হায়াত-এর কোনো কাজে লাগবে না। রহস্যটি ক্রমশ জ্ঞাতব্য।
আমাদের হলের- যেমনটা সব হল-হোস্টেলেই হয়- খাবারের মান ছিল সাদা কথাতে গড়পড়তা- কিম্বা বলা যায় বেশ নিম্ন মানের। পানির মতো নির্জলা ডাল সারাটা দিনই খাবার টেবিলে মজুদ থাকতো- যার ভেতর অনেক সময়ই মাছি-পিপড়াসহ অনেক পোকামাকড় হাবুডুবু খেতে খেতে প্রাণত্যাগ করতো। দিনে মাছের ঝোল- বিশেষ করে যে মৌসুমে যে মাছ সবচাইতে সস্তা মিলতো, যেমন বর্ষা কালে ইলিশ মাছ- শুনেছি তখন অনেক সময়েই চার/ছয় আনাতে একটা ইলিশ পাওয়া যেত। সেই ইলিশ ঐ মৌসুমে প্রতি দুপুরের খাবারেই মিলতো, এবং আমরা যারা একটু দেরিতে খেতে অভ্যস্ত ছিলাম তারা হিমশীতল ইলিশ মাছ এবং তরল জলীয় ডাল ঠাণ্ডা ভাতের সাথে বেস্বাদ গিলতাম। এমনটা হবার ফলে ইলিশ মাছের প্রতি আমার এক বিশেষ বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়, এবং এখনও মনেপ্রাণে, চিন্তাচেতনাতে খাঁটি বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও আমি ইলিশ মাছ খেতে তেমন পছন্দ করিনা- কেমন একটা আঁশটে গন্ধ মানসিক প্রক্রিয়াতে আমার নাকে প্রবেশ করে।
রাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুরগি দেয়া হতো, কালেভদ্রে গরু বা খাসি। হলের সবারই মুরগির চ্যাপ্টা রান খাবার প্রতি আগ্রহ ছিল বিধায় অনেকেই বেশ তড়িঘড়ি দুপুরের খাবার খেতে চলে আসতো- তাদের মধ্যে অনেকেই সকালের নাস্তা না করে বারোটার ভেতর আক্ষরিক অর্থে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিত। তবে সারা মাসের এই দৈন্য আহার প্রক্রিয়ার একেবারে উল্টো চিত্র ছিল “ইম্প্রুভড ডায়েট”-এ এবং “ফিস্ট”-এ। মাসে দুটি “ইম্প্রুভড ডায়েট” এবং একটি “ফিস্ট” হতো। এবং এ দুটিতে যে পরিমাণ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পরিবেশন করা হতো তা পেয়ে আমরা যার পর নাই খুশি হতাম এবং সারা মাসের দৈন্য সহজেই ভুলে যেতাম। অথচ ১৯৬৩ সালে আমাদের দুবেলা খাওয়া এবং ওই দুটি “ইম্প্রুভড ডায়েট” ও একটি “ফিস্ট” বাবদ মাসপ্রতি পঁইত্রিশ টাকা দিতে হতো যা ১৯৬৬ সালে আটষট্টি টাকায় উন্নিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, আমাদের মানবিক বিভাগে দেড়মাসিক বেতন ছিলো এগারো টাকা যদিও হিসাবটা দেড়মাসিক কেনো ছিল জানি না।
আমাদের মাসে এক শ’ থেকে দেড়শ’ টাকা লাগতো সব খরচ মেটাবার জন্য যার ভেতর ঐ মেস চার্জ, সকালের নাস্তা, লন্ড্রি খরচ, পুরুষালী টইলেট্রিজ যেমন পেস্ট, সাবান, দাড়ি কাটার সরঞ্জামাদি, কিছু প্রসাধনী (এটি সবার না, যেমন আমি তেমন ব্যবহার করতাম না শুধুমাত্র শীতকালে স্নো এবং অলিভ অয়েল বা শর্ষের তেল ছাড়া। তবে সাদুল্লাহ খুব সৌখিন ছিল। সে স্নো-পাউডার এবং পারফিউম এবং মাঝেমধ্যে ডেডোরেন্ট, যদিও এটি তদানীন্তন সময়ে তেমন সহজলভ্য ছিল না, বেশ ব্যবহার করতো।) হায়াত-এর এসব বালাই ছিল না। সে বেশ সুদর্শন দীর্ঘ পুরুষ ছিল। স্মার্ট, সুদর্শন এবং দীর্ঘদেহী পুরুষের প্রতি নারীদের আকর্ষণ থাকাটাই স্বাভাবিক বলে আমি ওই বয়সে ধরেই নিয়েছিলাম। কারণ আমি দেখেছি সাদুল্লাহকেও (সেও “হ্যান্ডসাম” এবং স্মার্ট ছিল তার পোশাক, কথাবার্তা এবং অনর্গল ইংরেজি বলার কারণে) মেয়েরা বেশ পছন্দ করতো। হায়াত ছিল প্রাকৃতিকভাবেই পৌরুষ স্বভাবের।
আমাদের হলে একটি ক্যান্টিন ছিল মূল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সামনে গেটের কাছে হাতের ডান দিকে। এখানে আমরা দুবেলা নাশতা করতাম- সকালে এবং বিকেলে। নাশতা করতে সাধারণভাবে চার থেকে ছ’আনা থেকে আট আনা লাগতো। তখন দশমিক মুদ্রার চল শুরু হয়ে গেছে। ফলে হিসাবটা হতো ঐ মুদ্রাতেই। সাধারণ নাশতার মেনু ছিল দুটি পরটা, সজি/ডাল, একটি ডিম পোচ/ভাজি এবং এক কাপ চা। অনেকে দুটি ডিম পোচ বা ভাজি খেতে চাইতো। অবশ্য বিকল্পে বাটার-টোস্টও পাওয়া যেতো। কিছু ছাত্র ঐ ভাজা ডিমে প্রচুর পেঁয়াজ এবং মরিচের দাবি থাকতো, এবং কেউ কেউ আবার ভাজির ভেতরটা যাতে তরল থাকে তার অর্ডারও করতো। বিকেলের নাশতাটা ছিল ঐচ্ছিক। সবাই এটা খেত না, পরিবর্তে রাত আটটার ভেতর রাতের খাবার খেয়ে নিত। তবে আমাদের চয়েস ছিল বিভিন্ন ধরনের। হল ক্যান্টিনে পেতাম বুঁদিয়া, সিঙ্গাড়া, পুরি ইত্যাদি। আমাদের কিছকিছু ছাত্রের স্বাদ বদলের ইচ্ছে হতো মাঝে মধ্যে এবং ফলে হেঁটে চলে যেতাম বকশীবাজারের দিকে রেল ক্রসিং পেরিয়ে ক্যাফে রাজ-এ। তখন ঢাকার মূল রেল স্টেশন ছিল ফুলবাড়িয়াতে। রেললাইনটা আমাদের হলের পাশ কাটিয়ে বকশীবাজার মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে দিয়ে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত ছিল। এখানে আমি প্রতি বিকেলে আসতাম আসলে আমার সাত-আটটি স্কুলে পড়া বন্ধুদের সাথে- যাদের অনেকেই ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তো- তাদের সাথে আড্ডা দিতে। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা।
মুরগির চ্যাপ্টা রান খাওয়াটা যে লাভজনক সেটা বুঝেছি বিলম্বে। আসলে যে সাইজের মুরগি আমাদের দেয়া হতো তার সারা অঙ্গে “ঢেউ” ছিল না- অর্থাৎ মুরগিগুলো ছিল জীর্ণ শীর্ণ। একমাত্র স্থান যেখানে কিছুটা অন্তত স্থুল মাংস পাওয়া যেত সেটি হলো ওই চ্যাপ্টা রান। আমিও সেই চ্যাপ্টা রান শিকারী হয়ে গেলাম সময়ে। কিন্তু এন. এস. এফ. পা-াদের জন্য এই চ্যাপ্টা রান আলাদা ভাবে সংরক্ষিত থাকতো তা তারা যখনই খেতে আসুক না কেনো। আসলে আমার সীমিত জ্ঞান থেকে মনে হয়েছে রাজনীতির স্বৈরাচারিতার মুখ যতটা ছাত্র রাজনীতিতে সংক্রামিত ও প্রকট হয়েছে তা বোধহয় আর কোথাও তেমনভাবে হয়নি। তবে একথাও ঠিক আমাদের সময় এর তীব্রতা তেমন ছিল না এবং সুস্থ ছাত্ররাজনীতির তখন আধিপত্য ছিল বলেই ষাটের দশকে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তারা অনেক ঐতিহাসিক মাইল ফলকের মতো ঘটনা ঘটাতে পেরেছি। আরও একটি বিষয় হলো, আইয়ুব খান-এর মতো সামরিক ফাসিস্তরা আসলে আমাদের রাজনীতির ধারাকে দূষিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করেছে- যার অনেকটাই স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সংক্রামিত হয়েছে।
সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রবেশ পথের ডান ও বাম পাশে দুটি টেনিস কোর্ট ছিল যে দুটি দেখে আমার বাবা ভীষণ উৎফুল্ল হয়েছিলেন। আমি একাধিকবার বলেছি উনি ভীষণ “স্পোর্টস ফ্যান” ছিলেন, নিজেও টেনিস খেলতেন। ফলে সপ্তাহখানেক পরে ময়মনসিংহ থেকে উনি একটি টেনিস রেকেট কিনে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমি যেনো টেনিস খেলি। দু’একদিন যদিও হেলেছিলাম, কিন্তু আমার প্রিয় খেলা ছিল ক্রিকেট। আমি স্কুলে এবং কলেজে দলের অধিনায়ক ছিলাম, ভাল বল করতে পারতাম। কয়েদিন পর আবিষ্কার করলাম আমার রুমের বাইরেই একটি ক্রিকেট প্র্যাকটিস নেট আছে এবং কয়েকজন সাথীও পেয়ে গেলাম প্রাকটিস করার জন্য যার ভেতর অন্যতম ছিলেন আইয়ুব কাদরী। আইয়ুব কাদরী ইংরেজি বিভাগেই পড়তেন, আমার সম্ভবত দু’বছরের সিনিয়র ছিলেন। পরবর্তীকালে উনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং এক সময় স্বাধীন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন। আমি যখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনারত তখন তার ছেলে আমার ছাত্র ছিল এবং ফলে আইয়ুব কাদরীর সাথে আমার আবার অনেক আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছিলো।
আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের হয়ে ইন্টারইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে একাধিকবার খেলেছি। এই টিমে আইয়ুব কাদরীও খেলেছেন, এবং টিমের অধিনায়ক ছিলেন রাজা আলী, নিয়াজ জামানের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, বর্তমানে অবসরে) বড় ভাই। রাজা আলী পাকিস্তানে চলে যান এবং সম্ভবত বর্তমানে সেখানেই বসবাস করছেন। নিয়াজ জামান-এর মেইডেন নাম ছিল নিয়াজ আলী। উনারা দুই ভাইবোনই ভীষণ মেধাবী। নিয়াজ আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে স্কার্ট পরে সাইকেল চালিয়ে ক্লাস করতে আসতেন।
এভাবে ক্রমশ আমি হল জীবনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে হল-জীবনের প্রারম্ভ আমার মোটেও পছন্দ ছিল না। হলের আবাসিক ছাত্র, খাবার, ক্যান্টিনের নাশতা, বন্ধুদের সাথে আমার আড্ডা, হায়াত-জমীর-এর ঠেলাঠেলি, আইয়ুব-পাকিস্তানের রাজনীতি এবং তার ফলে হলে উত্তেজনা, হলের লনে ক্রিকেট প্র্যাকটিস এসবই এক সময় আমাকে আবিষ্ট করে ফেলে এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলকে আমি আমার মনের কোটরে স্থান দিয়ে ফেলি আজীবনের জন্য। এখনও হলের সামনে দিয়ে যাবার সময় আমি অশ্রুসিক্ত হই ঐ ভালবাসারই টানে।
তবে হলের আখ্যান এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া
-

লোরকার দেশে
-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান
-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার
-
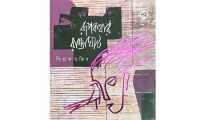
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
























