সাময়িকী
ছোটগল্পের অনন্যস্বর হাসান আজিজুল হক
অনন্ত মাহফুজ
“আমি যখন এখানে এলাম... আমি একটা করবী গাছ লাগাই। ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।” দেশভাগের পর এপারে চলে আসা এক পিতার শেষ জীবনে মেয়ের দেহোপার্জনের ওপর বেঁচে থাকার এইসব রূঢ় বাস্তবতার গল্পে হাসান আজিজুল হক বাংলা কথাসাহিত্যে নিজের ঘরানার ভিতর দিয়ে প্রায় স্পর্শের বাইরে চলে যান। তাঁর সমান্তরাল করে কিংবা পিছনে ফেলে দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছেন, এমনটি তো আর দেখা যায় না। তাঁর সাহিত্য কোনো একক বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। নিরলসভাবে নিজেকে বার বার ছাড়িয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়ে গল্প, উপন্যাস কিংবা গদ্যে ভাষার এক কারুকার্যময় শব্দহীন ¯্রােতের মতো প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি করেন। গদ্য ও কবিতার মধ্যে তিনি কখনো পার্থক্য খুঁজে পেতেন না।
‘শকুন’ গল্প দিয়ে হাসান আজিজুল হক প্রবেশ করেন কথাসাহিত্যে, সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকায় ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় গল্পটি। রাঢ় বঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা অবিকল তুলে আনলেন সংলাপে। কোনো কিছুর মৃতদেহ নিয়ে কুকুরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সম্ভবত পরাজিত এক শকুন লোকালয়ে এসে মাটিতে পড়ে গেলে সে কিছু কিশোরের খেলনা হয়ে ওঠে কিংবা আক্রোশের শিকার হয়। তারা শকুনের মধ্যে অঘোর বোষ্টমের প্রতিবিম্ব দেখে। ছেলেদের টানাহ্যাঁচড়ায় মরে পড়ে থাকে শকুনটি। শত শত শকুন নামে। পাশে পড়ে থাকা একটি অপরিণত মানবশিশুর মৃতদেহের লোভে শকুন নামতে থাকে। হাসান আজিজুল হক ছোটোগল্পের পলিশ করা অবস্থাটা টেনে সরিয়ে দিলেন যেন। প্রথম গল্পেই পাঠকদের সামনে বর্ণনা, সংলাপ ও বিষয়ে নতুন এক গল্পের জগৎ তুলে ধরেন তিনি। ‘শকুন’ প্রকাশের পর সে-বছরই পূর্বমেঘ পত্রিকায় ‘একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে’ গল্প প্রকাশের পর একজন অসামান্য শক্তিধর কথাসাহিত্যিকের আগমনের বিষয়ে পাঠক ও সাহিত্য বোদ্ধারা সচেতন হন। এই দুটি গল্পসহ দশটি গল্প নিয়ে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে।
আত্মজা ও একটি করবী গাছ পাঠকের ভাবনাকে আবারও আঘাত করে। এ গ্রন্থের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ আমাদের বিমূঢ় করে রাখে। আমরা দেখি ধর্মকে জাতি আখ্যা দিয়ে স্বার্থ আদায়ের জন্য উপমহাদেশ কেটে দুই ভাগ করে ফেলার পর এ বাংলায় চলে আসা এক বৃদ্ধের বেঁচে থাকার গল্প
আত্মজা ও একটি করবী গাছ পাঠকের ভাবনাকে আবারও আঘাত করে। এ গ্রন্থের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ আমাদের বিমূঢ় করে রাখে। আমরা দেখি ধর্মকে জাতি আখ্যা দিয়ে স্বার্থ আদায়ের জন্য উপমহাদেশ কেটে দুই ভাগ করে ফেলার পর এ বাংলায় চলে আসা এক বৃদ্ধের বেঁচে থাকার গল্প। হঠকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী এলিট ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর ষড়যন্ত্রের সাথে বৃটিশ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশভাগের রক্তক্ষরণ বুকে ধারণ করেন হাসান। করবীর বিচি থেকে অসাধারণ বিষ হয় বলে হয়তো নিজের মেয়ের জন্মের সময় সে একটি করবী গাছ লাগায় বৃদ্ধ। তারপর এক বিষময় জীবনযাপন। আত্মজার শরীর বেচে উপার্জন, করবীর বিচি থেকে তৈরি হওয়া বিষ, ঠেলে বয়ে চলা একটা জীবন, সব একাকার হয়ে যায়। ফেলে আসা যবগ্রাম, শৈশব, কৈশোর, চেনা মাটির গন্ধ, বন্ধু-স্বজন ছেড়ে আসা একটা জীবনের চাপা বেদনাবোধ হয়তো বয়ে বেড়াতেন হাসান আজিজুল হক।
হাসানের গল্পের রূপক-সাংকেতিকতা আরও জোরে মোড় নেয় তার তৃতীয় গল্পগ্রন্থ জীবন ঘষে আগুন-এ। ‘জীবন ঘষে আগুন’ গল্পে বাংলার ভূমিহীন তেঁতুল বাগদীদের সংগ্রাম ও কষ্টের জীবনের সাথে প্রাচীন উপকথার জীবন যুদ্ধের সমান্তরাল বয়ে চলাকে উপজীব্য করে লেখা এ গল্পে হাসান নিজেকে আরেকবার অতিক্রম করে যান। হাজার বছর ধরে ভূমিহীন মানুষের জীবনে ধর্মের কাহিনিসমূহ বাঁচার অধিকার আদায়ের চেতনাকে দুর্বল করে দেয়। তবে শোষণের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ জমা হয়। তারা প্রতিবাদী হয়। উঁচু শ্রেণির ঘণ্টাবাবু নিম্নবর্গের রমণী কালীর অসহায়তার সুযোগ নেয়। নিম্নবর্গের সচেতন মানুষেরা মুখ বুঁজে এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারে না। যুবক মনোহর প্রতিবাদী হয়। সে ঘণ্টাবাবুকে হত্যা করে। মনোহরের সংগ্রামী চেতনা তাকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেছে। আসন্ন সংগ্রামে সে তার কর্তব্য স্থির করে রাখে। এ গ্রন্থের আরেক গল্প ‘খাঁচা’ পুনরায় দেশভাগের গল্প।
এরপর হাসান আজিুজুল হক লেখেন নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫), পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১), আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮), রোদে যাবো (১৯৯৫), মা মেয়ের সংসার (১৯৯৭), বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প (২০০৭)। সমাজ ও রাজনীতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিশ^ সাহিত্য, সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার প্রবন্ধ আমাদের ভাবনার জায়গা প্রসারিত করে। কথাসাহিত্যের কথকতা (১৯৮১), চালচিত্রের খুঁটিনাটি (১৯৮৬), অপ্রকাশের ভার (১৯৮৮),সক্রেটিস (১৯৮৬), অতলের আধি (১৯৯৮), একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা (২০০৫), ছড়ানো ছিটানো (২০০৮), বাচনিক আত্মজৈবনিক (২০১১), চিন্তন-কণা (২০১৩), রবীন্দ্রনাথ ও ভাষাভাবনা (২০১৪) ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থে হাসান আজিজুল হক মানুষ, জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশে সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মানুষের সমস্যা ও বিকাশ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও তথ্য প্রকাশ করেছেন।
দীর্ঘ সময় ধরে অসামান্য সব গল্পগ্রন্থ, নিবন্ধ লেখার পর হাসান লেখেন দেশভাগের ওপর এক মহাকাব্যিক উপন্যাস আগুনপাখি যা ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়।
উত্তমপুরুষে লেখা আগুনপাখি এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের গল্প। এ গল্প বয়ানের ভিতর দিয়ে হাসান আজিজুল হক তুলে আনেন দেশভাগের আগের ভারত উপমহাদেশ, তদানীন্তন রাজনীতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানবিক বিপর্যয় ও অবক্ষয়। গ্রামীণ জনপদের এক প্রান্তিক নারীর জবানিতে এখানে উঠে এসেছে তার সমাজ-সংসার, স্বামী-সন্তানদের সাথে তার সম্পর্ক ও চিন্তার পার্থক্য। উপন্যাসের কথক ও মূল চরিত্র এ নারীর মানসিক দৃঢ়তা উপন্যাসের আসল শক্তি। উপন্যাসের শেষে তার স্বামী পরিবার নিয়ে পাড়ি দিতে যান পাকিস্তানে বা পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি তার জন্মস্থান, তার বেড়ে ওঠা, নিজের হাতে গড়া সংসার ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। তিনি থেকে যেতে চান শ্বশুরবাড়ির ভিটেতেই। স্বামীর ধমক, পুত্র-কন্যার আবেগঘন আকুতি- কিছুই তাকে টলাতে পারে না। দেশভাগের পর বিপর্যস্ত মানুষ উদ্ভ্রান্তের মতো আশ্রয় খোঁজার দলে যুক্ত হননি তিনি। ধর্ম আর স্বার্থের সমীকরণের খেলায় দেশভাগ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এই নারী প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেন।
তার দ্বিতীয় উপন্যাস সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩), আরেক সংগ্রামী নারীর আখ্যান। হাসানের এ উপন্যাসটিও যেন নারীর দীর্ঘ এক যাত্রা, ষোলো বছর বয়সে যে যাত্রা শুরু হয় কিশোরী সাবিত্রীর। ঘটনাটি গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের, ১৯৩৮ সালের। ধর্ষিত সাবিত্রীর মামলার আদালতের সাক্ষ্য থেকে সাবিত্রীর সংক্ষুব্ধ, গ্লানি আর ঘৃণার জীবন, সমকাল, অমানবিকতা, রাজনীতি। হাসান উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন সাবিত্রীকে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে। নারীর অপমানের জীবনের ছবি আঁকার অক্ষমতা কিংবা অপূর্ণতা ক্ষমা না করলে লেখক হিসেবে সেই কষ্ট বয়ে বেড়ানোর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী আছে?
শেষের দিকে হাসান মনোযোগ দেন তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো লিখে রাখতে। ফিরে যাই ফিরে আসি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। স্মৃতিকথার দ্বিতীয় অংশ উঁকি দিয়ে দিগন্ত পাঠকের হাতে আসে ২০১১ সালে। আমরা দেখি, স্মৃতিকথার প্রথম অংশে হাসান আজিজুল হক ফিরে আসেন শৈশবে অথবা শৈশবই সমস্ত বিত্তবৈভব নিয়ে ফিরে আসে হাসান আজিজুল হকের কাছে। ফিরে-আসা শৈশবের খুঁটিনাটি উঠে আসে ফিরে যাই ফিরে আসি স্মৃতিগ্রন্থে। হাসান আজিজুল হককে জানবার তীব্র বাসনা পোষণ-করা হাজার হাজার পাঠক লেখকের সঙ্গে ফিরে যান বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে। হাসানের শৈশবের সঙ্গে পাঠকের শৈশবের মিল-অমিলের তুলনা চলে। পাঠকও তার সঙ্গে স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হন।
স্মৃতিরা মূলত কষ্টদায়ক। স্মৃতি স্বভাবত অতীত। হয়তো তাই স্মৃতির কাছে ফিরে যাবার বাসনা থাকে, দায়ও থাকে। যে শৈশবের রেখাচিত্র হাসান তাঁর গ্রন্থে আঁকেন তা তো কেবল পাঠককে কিছু একটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। এর পশ্চাতে ধাবমান থাকে অনেক কথা, অনেক কষ্ট। শৈশবের যবগ্রামের কাছে ফিরে যাবার তীব্র কষ্ট হাসানকে তাড়া করে। প্রিয় ধুলো-বালির গ্রাম এখন তার কাছে অথবা আমাদের সবার কাছে ভিন্ন একটা দেশের সীমানার মধ্যে। যেখানে মন চাইলেই চলে যাবার সুযোগ থাকে না। কাগজে-কলমে যাকে আর নিজের বলে দাবি করবার কোনো উপায় থাকে না।
হাসানের জন্ম ১৯৩৯ সালে, অবিভক্ত ব্রিটিশ-ভারতে। উপমহাদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাবার একটা তোড়জোড় তখন ব্রিটিশদের মধ্যে। ছেড়ে যেতে হবে এই সত্য মেনে নিয়েও ভারত উপমহাদেশ যাতে তাদের আঙুলের ইশারায় চলে সেই চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। সুবিধাবাদী এলিটদের দল কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ ভাগাভাগি নিয়ে দর কষাকষি করছে ব্রিটিশদের সঙ্গে। মুসলমান আর হিন্দু মূলত দুটো জাতি, এই দুর্বোধ্য এবং অমানবিক দর্শন সাধারণ মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। হাসানের বয়স তখন সাত। তারপর ইতিহাসের সবচেয়ে পরিকল্পিত ট্রাজেডির একটি ঘটানো হয় ১৯৪৭ সালের আগস্টে, উপমহাদেশ বিভক্তির নামে স্বার্থের কাটাছেঁড়া, বাংলাকে কেটে দুই টুকরো করা।
ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া ভারত তখন মূলত হিন্দু আর মুসলমান এই দুই ধর্মানুসারিদের থাকবার জায়গা, দুটো আলাদা জায়গা মাত্র। হাসান আজিজুল হক ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতে কাটান আরও কয়েক বছর। ১৯৫৪ সালে তিনি চলে আসেন খুলনায়। খুলনার দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হন তিনি। প্রায় পনের বছর তিনি কাটিয়ে আসেন বর্ধমানে, কাটোয়া, নিগণ আর যবগ্রামে। বাংলার অযৌক্তিক এবং স্বার্থভিত্তিক বিভাজন, যবগ্রাম থেকে খুলনা, যৌবন ছুঁই ছুঁই করে চলে আসার তুমুল কষ্ট তার রচনায় আসবে সেই তো স্বাভাবিক। আগুনপাখিতে তার ভিতরে বহু-লালিত সেই কষ্টের কিছুটা আমরা বের হতে দেখি। আসলে এটি কেবল একজন হাসান আজিজুল হকের কষ্ট নয়, রাজনীতির স্বার্থের মারপ্যাঁচে পড়ে যাদের তখন এপার-ওপার করতে হয়েছিল তাদের এবং একটি জাতি ও সংস্কৃতি বিভাজনের সুদূর প্রসারী প্রভাবের বিষয়টি যারা মানতে পারেননি তারা সবাই হাসানের কষ্টটাকে ভাগ করে নেন। সেই হাসান আজিজুল হকের কাছে পাঠকের অনেক জানবার থাকে, অনেক প্রত্যাশা থাকে। বাংলা সাহিত্যকে তাঁর বোধের গভীরতায় ছুঁয়ে যাবার পরও হাসানের অতৃপ্তির সঙ্গে যোগ হয় আমাদের প্রত্যাশা। তিনি তখন লিখতে বসেন ফিরে যাই ফিরে আসি।
ফিরে যাই ফিরে আসি মূলত আত্মকথা, আত্মজীবনী নয়। শুরু করেছেন যবগ্রামে নিজের জন্ম দিয়ে। যবগ্রামে তার ফেলে আসা শৈশবই দেখতে পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে। বাকি জীবনের কথাও পাঠক পেয়ে যাবেন পরে এরকম একটি আশার মধ্য দিয়ে ফিরে যাই ফিরে আসি শুরু অথবা শেষ হয়।
ত্রিশের দশকের শেষপ্রান্তে ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দিনটিকে হাসান তার জন্মদিন হিসেবে উল্লেখ করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের মানুষ সন্তানের জন্ম বিষয়ে সচেতন থাকবেন না সেই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম হাসান আজিজুল হকের বেলায়। তার পিতা, সংসারের মেঝ সন্তান, নিজ ও আশপাশের গ্রামে প-িত এবং সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম সন্তান জন্মের সময় তার ব্যাপক উৎসাহ ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। ষোলো বছর বয়সে তার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হলে তার পিতা ‘চিরদিনের মতো দুমড়ে-মুচড়ে যান’। তারপর ‘সারাজীবনেও তিনি আর এই ভাঙাচোরা পৃথিবীকে সোজা করতে পারেন না’। ফলে নবজাতক হাসান তার কাছে ‘অযোগের ভূত’ হয়ে আসেন এবং তার জন্ম তারিখ, জন্মক্ষণ কিছুই তিনি লিখে রাখেন না। এর যে খুব বেশি প্রয়োজন আছে তাও হয়তো নয়। গ্রন্থের শুরুর দিকে লেখক হয়তো তাই বলেন, “আমার ধারণা জন্মদিন জানা, মৃত্যুদিন জানার মতোই সত্যিই জরুরি নয়। বরং জানা থাকলেই মুশকিল। আমি আমার মৃত্যুদিন জানি এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর তী হতে পারে? জীবনের দামই তো তাতে কমে যায়, বৈরাগ্য এসে চেপে ধরে, কি হবে আর ধড়ফড় করে? মৃত্যুর ফাঁদে আটকা পড়ার দিনকাল যখন জানাই আছে। মৃত্যুদিন জানার মানে হচ্ছে হেরে যাবার, বিলুপ্ত হবার দিনক্ষণ জেনে ফেলা। তেমনি জন্মদিন জানাও হচ্ছে বিশ্রী ব্যাপার।” তবু মায়ের কাছ থেকে নিজের জন্মদিনটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান লেখক। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় যদিও তার জন্মদিন লেখা হলো দোসরা ফেব্রুয়ারি, উনিশ শো ঊনচল্লিশ, হাসানের মতে তার জন্মদিন ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দিন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, “স্মৃতিকে কতটা পিছনে নেওয়া যায়? নিশ্চই চেতনার পিছনে নয়। আমার ধারণা শুধুমাত্র চেতনাতেও স্মৃতি নেই, যদি থাকেও তা আধো-অন্ধকারেই ডুবে থাকে। আত্মচেতনা থেকেই স্মৃতির শুরু। জন্মের পর থেকে চেতনা আছে, গূঢ় রহস্যময় চেতনা- কিন্তু স্মৃতি নেই।”
চেতনা-আত্মচেতনার মাঝখানের জায়গাটিতে ফিরে যেতে চান হাসান। কারণ “সারাজীবন মানুষের কোনো না কোনো একটা অর্থ খুঁজতেই কেটে যায়, সে বুঝতেও পারে না।... জ্ঞানে-অজ্ঞানে এই খোঁজটুকুর জন্যেই মানুষের সমস্ত বাঁচাটা অন্যের মুখাপেক্ষি হয়ে যায়। একেবারে একা হলে সে থাকে অতিষ্ঠ। অন্যের কাছে সে যায়; সুখে যায়, দুঃখে যায়, ধনে-সম্পদে দারিদ্র্যে অভাবে যায়, প্রীতিতে যায়, অপ্রীতিতেও যায়।” আর এই যাওয়ার শুরুর কথা তিনি বলেন ‘ভোরবেলাকার চোখে’।
কী বলেন তিনি? অনেক কথা বলেন। যতটা নিজের কথা, তার চেয়ে বেশি তখনকার যবগ্রাম আর গ্রামের মানুষের কথা। শৈশবে দেখা মানুষ আর মানুষের কর্মকা-ের কথা। সব কথা তিনি বলেন একজন শিশুর মতো করেই। বলা যায় কথা শুরু করেন বাড়ির বাইরের একটি পরিত্যক্ত ঘরের কথা দিয়ে। যে ঘরে তিন শো বছর আগে মরে যাওয়া একজন পীর থাকেন। মজার ব্যাপার হলো হিন্দু আর মুসলমান সবার কাছেই তিনি নমস্য। হিন্দুরা ডাকে পাঁচু ঠাকুর বলে আর মুসলমানরা বলে পীর। তার খাদেম মুসলমান অথচ নানা জাতীয় মানত নিয়ে আসে হিন্দুরা। পাঁচু ঠাকুরের কাছে সন্তান লাভের জন্য মানত করে হিন্দু রমণীরা। তবে মুসলমানরা আসে না। কেন আসে না তা অবশ্য আমরা জানতে পারি না। একবিংশ শতকে ধর্মের মারাত্মক বিভাজন, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে শত্রুতা তখন খুব একটা কল্পনা করা যেত না, বিশেষ করে হাসানের যবগ্রামে।
চমৎকার একটি তথ্য এখানে পাওয়া যায়। যবগ্রামে আলাদা কোনো গোরস্তান নেই। কেন নেই তার একটা উত্তর তিনি দিয়েছেন। হয়ত গাঁয়ের মানুষ মৃতদের আলাদা কোথাও পাঠিয়ে দিতে চায় না কারণ মৃতরা সব শূন্য করে চলে গেছে এ-রকম ভাবে না তারা। থাকুক তারা জীবিতদের আশেপাশে।
যবগ্রামে ধানের উৎপাদনের বাইরে রবিশস্য তেমন একটা হয় না। কৃষিজীবীর সংখ্যা বেশি বলে পেশা-বৈচিত্র্য কম। ফলে নাপিত বা কামারদের বেশ কদর থাকে। দুই ঘর নাপিত আর এক ঘর কামার। ইচ্ছে হলে কেউ তার কর্মটি করে, ইচ্ছে না হলে করে না। এই তো এই নিয়ে জীবন যবগ্রামের মানুষের। আর তাই হয়ত হাসান বলেন, “ভারি একঘেয়ে জীবন আমাদের। আজকের দিনটা ঠিক কালকের মতো। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, খেলা-ধুলো প্রত্যেক দিন ঠিক এক রকম। মনে হতো, আলাদা আলাদা এক একটা দিন কাটাচ্ছি না আমরা প্রত্যেকদিন একটা দিনই কাটিয়ে যাচ্ছি।” এই বৈচিত্র্যহীনতা প্রতিদিনের খাবার-দাবারেও। পোশাক-আশাকেও।
দুরন্ত শৈশবে প্রথম পাঠশালার অভিজ্ঞতা বামুনগাঁয়ের দত্তবাড়ির বৈঠকখানায়। প্রথম শিক্ষক রণ মাস্টার। জোলের মাঠ পেরিয়ে বামুনগাঁয়ে দত্তদের শৌখিন বৈঠকখানায় কবে হাসান প্রথম পাঠ শুরু করেছিলেন তা অবশ্য তিনি মনে করতে পারেননি। পারার কথাও নয়। রণ প-িতের এই পাঠশালা বেশি দিন চলেনি বলে রণ মাস্টার যবগ্রামে চলে আসেন দাশু মাস্টারের পাঠশালায়। এইখানে সকালে একবার আর বিকালে একবার পাঠশালা বসে। অনেকটা আধুনিক স্কুলগুলোর ডে আর মর্নিং শিফটের মতো। মজার তথ্যটি হলো, এই পাঠশালায় একটিও মেয়ে নেই। সবাই ছেলে কারণ হিন্দু অথবা মুসলমান কেউ তাদের মেয়েদের গাঁয়ের পাঠশালায় পাঠাত না।
আর এই স্কুলে এসে হাসান আজিজুল হকের শৈশবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের কূটচাল, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ জাগিয়ে তুলবার প্রচেষ্টাগুলো বাংলার গ্রাম-গঞ্জগুলোকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে না পারলেও আচারিক দিক দিয়ে একটা পার্থক্য বোধ হয় থাকেই। দাশু মাস্টারের ছেলেকে মুখের আধ-খাওয়া চকলেট দেওয়ার পর বাড়িসুদ্ধ একটা হুলস্থুল পড়ে যায়। তাদের সবার মুখে মোটামুটি একটাই কথা- গেল গেল সব গেল। কিন্তু আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে হয়ত-বা শাস্ত্রের বিধানের বাইরে গিয়ে অনেক প্রাগ্রসর একজন ব্যক্তির মতো দাশু মাস্টার বলেন, “শিশু, শিশু, ওরা দেবদূত, কিছুতেই কিছু হবে না।” ‘ভোরবেলাকার চোখে’র অল্প কয়েক বছরের সময়ে একটি মৃত্যু দেখেন হাসান। সংসারকে চারদিক থেকে আগলে রাখেন যে মানুষটি, হাসান আজিজুল হকের দাদি, মারা যান। জায়গাটা খালি থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসা ফুফু জায়গাটা দখল করেন। দাদির সম্পর্কে পড়তে গিয়ে আগুন পাখির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আগুন পাখির কথকের কথা। দাদির সঙ্গে কোথাও যেন মিল আছে তার।
তাহলে সত্যিই কি একঘেয়ে শৈশব হলো হাসান আজিজের? প্রায় সত্তর বছর আগের বর্ধমানের একটি গ্রামে আর কত বৈচিত্র্য থাকে? অথবা এরচেয়ে বৈচিত্র্যময় আর কী হতে পারে? ছয় সাত বছর ধরে চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেখানে হয়তো খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারেনি, হয়ত মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল কেবল কিছু বিমান। তবু চৈত্রের শুষ্ক খটখটে রাঢ়ের গাঁয়ে আদতেই কি কিছু নেই? আছে, ফিরে যাই ফিরে আসিতে শরতে সমতলে বয়ে-যাওয়া নদীর শান্ত স্রোতের মতো বর্ণনার ভিতর দিয়ে তার দেখা পাওয়া যায়। হাসান নিজেই বলেন, “সত্যি, কি ভুল কথা যে ভালো লাগে না এই দেশ! মাঠঘাট সব মরুভূমির মতো, কেবলই ধুলো আর বালি ওড়ে, আর ছাই ছাই, মেটে মেটে রং ছাড়া আর কোনো রংই চোখে পড়ে না। না, ঠিক নয় এসব কথা। একটু সময় তো দিতে হবে দেখার জন্য।”
এ গ্রন্থের ভূমিকায় শেষে লেখক বলেন, “মৃত্যু পর্যন্ত একনাগাড়ে সেই যাওয়াটার সকালবেলা এখন। সূর্য কেবল উঠছে।” সুখে অথবা দুঃখে, নির্মাণ অথবা ধংসে মানুষই মানুষের কাছে যায়। সেই যাওয়ার ভোরবেলা এখন। হাসান আজিজুল হক লেখক হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, একজন দার্শনিক হিসেবে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, আমরা শুধু সেই বহুপ্রজ জীবনের কথাগুলো শুনেছি। হাসান আজিজুল হক কৈশোর, কৈশোর পেরিয়ে যৌবন, বর্ধমান ছেড়ে খুলনা, ভারত বিভাজন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন তুলে ধরেন স্মৃতিকথার দ্বিতীয় অংশ উঁকি দিয়ে দিগন্তে।
গল্প ও উপন্যাসে হাসান একটি স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে প্রবেশ করেছিলেন। তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তা আরও শাণিত হয়েছে। অবাক করা বিষয় হলো, তার স্মৃতিকথা কোনোভাবেই একরৈখিক বর্ণনা নয়। এখানে গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়, নাটকীয়তা থাকে। তার স্মৃতিকথাও কথাসাহিত্য। স্মৃতিকথার একটি সুবিধা হলো, শেষ থেকে ওপরের দিকে তাকানো যায়। ফলে তার দুই স্মৃতিকথা তাকে বোঝার সুযোগ করে দেয়। পাঠক এক পরিপূর্ণ শিল্পীকে চিনে নিতে পারে।
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া
-

লোরকার দেশে
-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান
-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার
-
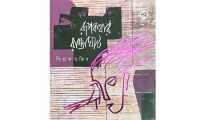
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
























