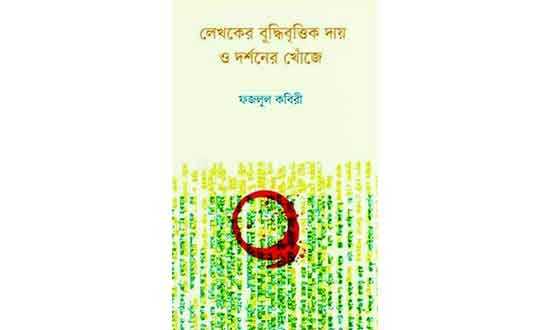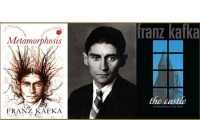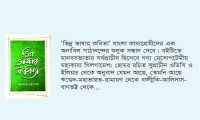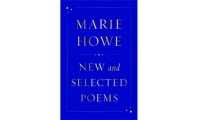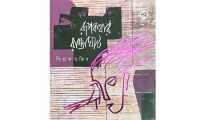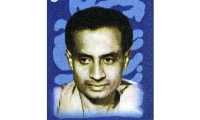সাময়িকী
প্রসঙ্গ : লেখকের বুদ্ধিবৃৃত্তিক দায় ও দর্শনের খোঁজে
খালেদ হামিদী
বইটি অনন্য কেন? এরকম বিশেষণ তো সিদ্ধান্তের মতো যা কোনও গ্রন্থালোচনার শেষাংশে উল্লেখ্য কিংবা প্রথাবদ্ধ ‘রচনা’য় লেখা ‘উপসংহার’ তুল্য। প্রথানুগত আলোচনা-সমালোচনা এ-মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য নয়, এই প্রবন্ধগ্রন্থটি পাঠের অভিজ্ঞতারই সারাৎসার শ্রদ্ধেয় পাঠকদের জানাতে চাই কেবল। এ জন্যেই বইটির অনন্যতা প্রথমেই স্বীকার্য। লেখক ফজলুল কবিরীর এই বই এখনও পর্যন্ত কীভাবে অদ্বিতীয়? এ-গ্রন্থ অতুলনীয় এ জন্যে যে, ক্ষমতার তাঁবেদার ও বই-বাণিজ্যে সফল দুই লেখক-গোষ্ঠীর বহুবিধ ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে, যতদূর জানি, এ যাবৎ আর কোনো লেখক বই প্রকাশ দূরে থাক, একটা প্রবন্ধও লেখেননি, করেননি সাহিত্যিক ভাষায় প্রতিবাদও। সমাজের অন্য অনেক মানুষের মতো নবীন-প্রবীণ অধিকাংশ লেখকই যে বিশ্বব্যাপী ‘বিজয়ী’ পুঁজিবাদের করাল গ্রাসেই একই সঙ্গে আত্মবিস্মৃত ও জনবিচ্ছিন্ন আমাদের লেখক তা শনাক্ত করেন এই বইয়ে, তাও প্রায় প্রথমবারের মতোই। চিহ্নিত কেবল নয়, তিনি এই বাস্তবতার বিশদ চিত্র তুলে ধরেন ৩২টি পর্বে। ফলে সংশ্লিষ্ট নানা অনুষঙ্গের মতো বিরাজমান অনেক করুণ, ক্ষোভ-জাগানিয়া ও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উল্লেখ তিনি করেন যৌক্তিক মন্তব্যযোগে।
এবার আসে বইটির দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠার প্রশ্ন। হ্যাঁ, তিনি নির্দিষ্ট কারোর নামোল্লেখ না করেও অপরিমেয় সৎ সাহসের সঙ্গে লেখক নামধারী পুঁজিবাদের সুবিধাভোগী অনুচরদের শ্রেণিচরিত্র উন্মোচন করেছেন অসম্ভব দার্ঢ্যযোগে। এর বিশেষণ দুর্র্ধর্ষ না হয়ে আর কী হতে পারে? উপর্যুক্ত নানা অনুষঙ্গরূপ পরিস্থিতিগুলো কী কী? দুয়েকটা এমন: জনপ্রিয় বা চটুল সাহিত্যের বাজার রমরমা হওয়া, বিস্ময়কর প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে প্রকৃত সাহিত্যের প্রতি প্রায়ই পাঠকের বিমুখতা, ক্ষমতার পদলেহী লেখকদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ, সব মিলিয়ে নানাভাবে সাহিত্যের পণ্যায়ন ইত্যাদি।
তাই বলে আমাদের লেখক কি শুধু কী চান না তা-ই বিশদ করেন এই ব্যতিক্রমী বইয়ে? অবশ্য কার্ল মার্কসও কী চান না তা ব্যাখ্যা করতেই আয়ু নিঃশেষ করেন, যা চান তার বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়ণের সময় তাঁর মেলে না। না, ফজলুল কবিরীও যদিও প্রকৃত লেখকের দর্শন ও স্বপ্নের কথা বারবার বলেন, কিন্তু সেই স্বরূপ উন্মোচনের দিকে অগ্রসর না হলেও তিনি সাম্যের কথা বলেন, আলোচ্যমান গ্রন্থে অন্তত দু’বার। এ-প্রসঙ্গে তার চেয়েও ঢের গভীর ও বিস্তৃৃতরূপে, নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে, সত্যিকার পরিচয় তুলে ধরেন প্রকৃৃত লেখকের। তাঁর অধীত মহৎ সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জ্ঞান এ ক্ষেত্রে তাঁরই সহায়ক হয় সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে। যেন তিনি দস্তইয়েভস্কি, মার্কেস, বোদলেয়ার, মানিক, জীবনানন্দ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাথে পথ হেঁটেছেন বহুকাল, পৃথিবীর পথে। (উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে মার্কেস ছাড়া আর কারো নাম তিনি উল্লেখ না করলেও।)
বইটি আমি দাগিয়ে দাগিয়ে, অনেক পৃষ্ঠার বামে-ডানে নোট টুকে টুকে পড়েছি। এতে বাণীপ্রতিম অমোঘ উচ্চারণ রয়েছে অনেক। এখানে সেগুলো উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে হচ্ছে বক্ষ্যমাণ গদ্যের শুরুর ঘোষণা অনুযায়ী। তবে অবশ্যউল্লেখ্য যে, কবিরীর ভাষা বেশ পরিণত। উদ্ধৃতি-ভারাক্রান্ত নয়, প্রাঞ্জল, কিন্তু তবুও পরিপক্ব। তাঁর অধীত বিদ্যার পশ্চাৎভূমির বিশালতা তাঁকে পাথরতুল্য বিশুষ্কতার পরিবর্তে যেন দিয়েছে বিশুদ্ধ হাওয়ার অফুরান অম্লজান, অশেষ প্রাণপ্রাচুর্য। এই প্রাণের স্ববৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠাই তো প্রকৃত লেখকের অন্বিষ্ট। তবে একই কথা বা বক্তব্যের, শব্দ ও বাক্যের ভিন্নতাযোগে, পুনরাবৃত্তি যে ঘটেনি তা নয়। এ ক্ষেত্রে কথাকে নানাভাবে ভাষায় পল্লবিত করবার ক্ষমতাও প্রশংসনীয়।
লক্ষণীয়, কবিরী লেখক বলতে কথাসাহিত্যিকদেরই বুঝিয়েছেন। কবিদের বা কবিতার প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে অনুল্লেখিত। যদিও, সকল লেখক কবি নন, কিন্তু সকল পূর্ণাঙ্গ কবিই লেখক। আরেকটা কথা, তিনি বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে পাঠের গুরুত্ব বোঝাতে চমৎকারভাবে আর্নস্ট ফিশারকে উদ্ধৃত করেন। বইয়ের কোনো অংশে প্লেখানভ, ব্রেখট, বেঞ্জামিন প্রমুখের নন্দনতত্ত্বের ঋণ স্বীকারের সুযোগ ছিল কি? তবে এ বই তিনি লিখেছেন কিছুটা কথা বলার ধরনে, মূলত তরুণ লিখিয়েদের উদ্দেশে। বইটি পড়ার সময় মনে হয়, শুধু নবীন নয়, অপেক্ষাকৃত প্রবীণদেরও কেউ কেউ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শুনতে শুনতে তাঁরই সাথে হাঁটছেন। কবিরীর বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এ বই প্রকাশিত হয়। তিনি কথাসাহিত্যিক। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও সাহস অনেকে অর্জনে সক্ষম হন না বয়স বিরাশি হলেও। এই বইখানা তাই নবীন লেখকদের জন্যে শিক্ষণীয় তো বটেই, অনেক প্রবীণের জন্যেও অনুসরণীয়। বাক্যটা উল্টো করে বললেও তা-ই।
তিনি একটা বাক্যে ‘উন্নয়নের’ সমালোচনা করায় কারো ভ্রম হতে পারে যে, তিনি সুবিধাভোগী লেখক বলতে শুধু বিগত সরকারের তাঁবেদারকেই বুঝিয়েছেন। না, আরেকটা বাক্যে, সব সরকারের আমলের ওরকম অলেখকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে আবার এমন কবি-লেখকও আছেন যাঁরা লেখাযোগে বাংলা একাডেমির একাধিক প্রকাশনায় ঠাঁই পেয়েছেন মাত্র প্রচলিত সম্মানীর বিনিময়ে।
যাই হোক, ফজলুল কবিরীকে যাঁরা তরুণ লেখক গণ্য করেন তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের অনগ্রসরতাহেতু বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হতে পারেন। কে তাঁদের বলবে, স্টাডিজ ইন আ ডায়িং কালচারসহ আরও দুর্দান্ত কিছু বইয়ের লেখক ক্রিস্টোফার কডওয়েল মাত্র তিরিশ বছর বয়সে কেন স্প্যানিশ ন্যাশনালিস্টদের হাতে নিহত হন? তাছাড়া আমাদের প্রবীণ ভালো লেখকগণও প্রাগুল্লিখিত বই-বাণিজ্য বিষয়ে নীরব কেন? অথচ ১০ কোটিরও অধিক কপি বিক্রি হওয়া ই. এল. জেমস্-এর ফিফটি শেডস অফ গ্রে উপন্যাস সম্পর্কে সালমান রুশদি লেখেন: ‘এতোটা কুলিখিত প্রকাশিত কিছু আমি কখনোই পড়িনি।’ (১ম সূত্র: দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ; ৩০ এপ্রিল ২০১৩; ২য় সূত্র: মদীয় ২য় প্রবন্ধগ্রন্থভুক্ত গদ্য: জনপ্রিয়, অজনপ্রিয় ও প্রভাবক বই; না কবিতা হাঁ কবিতা; ফেব্রুয়ারি ২০১৬)
আমাদের দেশে ফজলুল কবিরী একা প্রাসঙ্গিক আরও অনেক জরুরি কথা উপরে আলোচিত বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। শুভ পাঠ।
লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক দায় ও দর্শনের খোঁজে; ফজলুল কবিরী; প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৩; প্রকাশক: দ্বিমত পাবলিশার্স; চট্টগ্রাম
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব