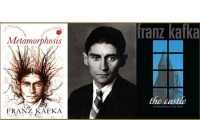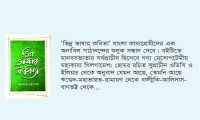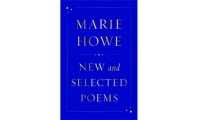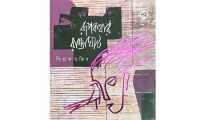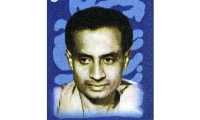সাময়িকী
সিকদার আমিনুল হকের গদ্য
সিকদার আমিনুল হকের প্রাণিপ্রীতি
হেমন্তেও ভিন্ন বসন্ত
১
আমরা যারা ষাটের দশকের কবি, রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশের বিশাল ঐশ্বর্য ও বিশ্ব-কবিতার ছিটেফোঁটা স্বাদ প্রথম দিকে আমাদের কাছে এদেশের চল্লিশের কবিদের হাত দিয়ে পৌঁছায়নি। চল্লিশের কবিদের সাধনা ছিলো বিক্ষিপ্ত, নিরক্ত ও উদ্দেশ্যহীনÑ সত্যের খাতিরে সেটা বলতেই হয়Ñ শামসুর রাহমান পঞ্চাশের কবি হয়েও তিরিশের কবিতার স্বাদ ও গন্ধ আমাদের পৌঁছে দিলেন।
মনে পড়ে, শামসুর রাহমানের ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ দেখার আগে তাঁর কোনো কবিতার সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিলে না। সম্ভবত সেটাই স্বাভাবিক। আমরা থাকতুম মফস্বলেÑ নিজেদের গোপন খাতায় রাত জেগে অসংখ্য বাজে কবিতা (অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ছায়া) লেখার সাথে সাথে আধুনিক কবিতার চেয়ে আধুনিক গদ্য-সাহিত্য, অর্থাৎ উপন্যাস ছোটগল্পের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিলো বেশি। অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেবÑ অর্থাৎ কল্লোলের গল্প-লেখকরা পৌঁছলো সবার আগে।
কবিতাও পৌঁছেছিলো, তবে অনেক পরে, প্রায় না জেনে, না বুঝে, আকস্মিকভাবে একদিনেই কিনে ফেরেছিলাম, বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ কবিতা, তাঁর সম্পাদিত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ সংকলন, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, এরকম আরও কিছু বই। তবে সত্যের খাতিরে বলতে হয়, ‘কবিতা’ পত্রিকার কিছু বাঁধানো সংখ্যা ছিলো কলেজে; রবীন্দ্রনাথের ও নজরুলের প্রতাপ বহন করছি তখন, স্বভাবতই জীবনানন্দের কিছু কিছু কবিতা ছাড়া, চোখ আর মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি কারুরই কবিতা। একটু আলাদা স্বাদ। একটু আলাদা তার গন্ধ ও ভিন্ন তার শরীরের পূর্ণতাÑ এটুকুই মাত্র। হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার মতো, মনের প্রস্তুতি তখনও ছিলো না।
ঢাকায় এসেছি ষাটের প্রথম দিকে। ততদিনে কবিতা লিখবো, কবি হতে হবে, এমন একটা শক্তি মনে মনে নিশ্চয়ই অর্জন করে নিয়েছিÑ এবং তারই সূত্র ধরে আকাশে-বাতাসে আমার মতো কবিতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনতে পায় এমন ক’জনের সাথে পরিচয়ও হলো। তাদেরই কারো মুখ থেকে সেই প্রথম শুনলাম কবি শামসুর রাহমানের নাম। দুর্দান্ত কবি, তিরিশের কবিদের ধরবার মতো শক্তি ও সাধ্য নিয়েই বাংলা কবিতার সঙ্গে এসেছেন এই কবি। তখনও পর্যন্ত, একটি মাত্রই তার বই, ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’Ñ কিন্তু সেই একটি বইয়ের খ্যাতি, যশ ও স্বীকৃতি একালে আটটি বই লিখেও পাওয়া যায় না। কোন এক বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী হবে হয়তো, সে-বই চটপট সংগ্রহ করে পড়তে উপদেশ দিলেন। বললেন, আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতা তারই অভিভাবকত্বে আত্মপ্রকাশ করেছে সবেগে ও উচ্চকণ্ঠে।
সত্যিই তাই, কেবলমাত্র নতুন স্বাদের কবিতায়ই নয়, শোভন প্রকাশনার উজ্জ্বলতায় তার পাশে দাঁড়াতে পারে, এমন কোন বই তখনও পর্যন্ত আমরা এ দেশে দেখিনি। আর কি সব টাটকা কবিতা! মাথা থেকে পা পর্যন্ত রোমান্টিক, কিন্তু আবার বল্গাহীনও নয়; মেধা, মনন, নাগরিক বৈদগ্ধ্যে তা আশ্চর্য সংযম ও সংহতিতে মুখর-নীরব।
এই-ই হচ্ছে বাংলা কবিতা, এই কবিতাই আমাদের লিখতে হবে; শামসুর রাহমান দূর থেকে আমাদের কাফেলার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেনÑ প্রকাশ্যে না হলেও আমরা মনে মনে তাঁর নেতৃপদ মেনে নিলাম। এবং যত দূর জানি, আজও পর্যন্ত তাঁর হাত থেকে তা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।
২
এরপর শামসুর রাহমান এগিয়েছেন, আমরাও যার যার শক্তি অনুযায়ী এগিয়েছি। তিরিশের কবিরা তখন আমাদের কাছে অনেক বেশি স্পষ্ট, ঘনিষ্ঠ ও অধিগম্যÑ এবং শামসুর রাহমানও তাই। প্রথম কাব্যগ্রন্থই তাঁকে জয়ের ও যশের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে : সেই যে যাত্রাশুরু সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসেরÑ ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’র পরে এলো ‘রৌদ্র করোটিকে’, ‘বিধ্বস্ত নীলিমা’, ‘নিরালোকে দিব্যরথ’Ñ তা আর ক্ষণকালের জন্যে থামেনি। কখনো-সখনো পথের ক্লান্তি ছিলো, এবং ক্ষণিক আত্ম-বিস্মৃতির মুহূর্তে পুনরুক্তির ত্রুটি। কিন্তু শামসুর রাহমান মুহূর্তেই আমাদের সব সংশয়, দুশ্চিন্তা আর ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছেন।
যদিও তার প্রেমের কবিতা ও মননের কবিতাই আমাকে আবিষ্ট করে বেশি, তবু বলবো, আমাদের রাষ্ট্রীয় সংকটে তার ‘প্রয়োজনের কবিতাগুলি’ আমাদের দেশের কবিতা পড়ে না বা পছন্দ করে না, এমন লোককেও আলোড়িত করেছে।
দেশ স্বাধীনের অস্পষ্ট চিন্তায় যখন আমরা আন্দোলিত, সেই সময়ের এক একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা রাশি রাশি আত্মপরিচয় ও আত্মজিজ্ঞাসার কবিতা পেলাম তাঁর কাছ থেকে। তার পর এলো স্বাধীনতার যুদ্ধ, কবি আরেকবার নির্ভুলভাবে অন্ধকারে আলোর সাহস দেখালেন।
আমাদের সংকট কাটতেই চায় না। গণতন্ত্রকে সামনে রেখে সেনাকর্তারা বহুদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের শাসন ও অপকৌশলের সাহায্যে শোষণ। এসব অপরাধ, মানুষের প্রতি অমর্যাদা অথবা মনুষ্যত্বের প্রতি আঘাত সব কবিকে একই রীতিতে আন্দোলিত করবে, তা আমি বিশ্বাস করি না। কবিতা যেমন অনেক রকমের, কবিও তেমনি নানা রুচির ও নানা ধরনের হতে পারেন। জগতের সাহিত্যের দু’রকম প্রমাণই আছে। নেরুদা, লোর্কা, সার্ত্র, মায়াকোভস্কি, এলুয়ার, আরাগঁরা যদি থাকেন একদিকে, তবে অন্যদিকে রিলকে, হ্যোন্ডার্লিন, বোদলেয়ার, র্যাঁবো ও ভের্লেনরা কোনভাবেই ছিলেন না রাজনীতিমনষ্ক। আমাদের বাংলা কবিতাতেই জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেবের বিপরীতে আছেন বিষ্ণু দে, সুভাষ ও সমর সেনরা।
শামসুর রাহমানকে দেখেছি, অসুস্থ শরীরে নিছক জনতার দাবির জন্যে লেখায়, বক্তৃতায়, মঞ্চে আসীন থেকে অ-মানুষিক পরিশ্রম করতে। ছুটে গিয়েছেন দূরে-দূরান্তরে, মফস্বলে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেÑ এবং দেশের বাইরে তো বটেই।
শুধু কবি, ঘনিষ্ঠভাবে কবি : এই পরিচয়ের প্রতি তার লোভ আগেও ছিলো না, এখনও নেই। তাঁর কর্মক্ষেত্র বিশাল। জীবনের সকল দিকে সমান আগ্রহ ও তৃষ্ণাÑ এমন সম্ভবত আমাদের সময়ে আর কারো মধ্যে নেই। নিরন্তর চাপ সত্ত্বেও তাঁর উজ্জ্বল চেহারা কখনো ম্লান হয় না। ভদ্রতা, বিনয়, সৌজন্যÑ এই সব কিছুতেই দেখেছি আমরা তাঁর ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারি না। তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফেরার দৃষ্টান্ত বিরলÑ অনেক সময় মনে হয়েছে আমরা তাঁর অতিরিক্ত সহ্য ক্ষমতার ওপর চাপ দিচ্ছি, যা মন ও স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল নয়। এই জন্যেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর সময় ও সৃষ্টিশীল বিশ্রামকে কোনদিনই বেশি ক্ষতি করতে চাইনি। আমার মতে, কবি বা ভাবুকমাত্রই দূর থেকে শ্রদ্ধা ও সঙ্গী হওয়ার যোগ্য।
৩
জীবিকা, জীবন, রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ, প্রতিরোধের নেতৃত্বÑ এসব যথাযথ পালন করেও শামসুর রাহমান সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন। তাঁর আছে প্রতিভা, লেখার ক্লান্তিহীন ক্ষমতা, চিন্তার বিস্তৃতি এবং জানা আছে শব্দের গন্ধ। অবিশ্বাস্য, কিন্তু কবিতার পর কবিতা, দিনের পর দিন অকল্পনীয় গতিতে তিনি লিখেছেন। সমকালীন কোন বড় ঘটনা বা দুর্ঘটনাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নিÑ লেখার পরিমাণ দেখলে যে কেউ সেই সৃষ্টিকে চেষ্টাহীন কিংবা স্বভাব কবিতার শ্রেণিতে ফেলতে চাইবেন।
কিন্তু কবিতা পড়া যার কাছে কেবল কোন শৌখিন কাজ নয়, তিনিই জানেন, কত শক্ত তাঁর হাত, কবিতার কলা-কৌশলের ওপর কী বিশাল অধিকার তার করায়ত্ত, প্রকরণের কত জটিল অলিগলির ভেতর দিয়ে পৌঁছে যান গন্তব্যে।
একালের কবিকে যে নানা বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, জানতে হয় মানুষের অর্জিত চিন্তা, তত্ত্ব ও বহুবিধ তথ্য; কবিকে যে দ্রষ্টা হতে হয়, শিখতে হয়, অন্তত আঙুলের ডগায় রাখতে হয় অজস্র দেশি-বিদেশি শব্দ, কিংবদন্তি, পুরাণÑ শামসুর রাহমানের মনোযোগী পাঠক তা অল্প অগ্রসর হলেই টের পেয়ে যান। অসংকোচে বলবো, তার মতো শব্দের সঞ্চয় একালের আর কোন কবিরই নেই। আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, এঁরাও আলস্য ও ভ্রান্তি কিংবা অমনোযোগের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দত্রুটি কিংবা শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেনÑ কিন্তু শামসুর রাহমান ছন্দকে বিন্দুমাত্র টলতে দেননি। তাঁর চিত্রকল্প ও উপমা সর্বদা জীবন্ত, উক্তির অর্থ বিশ্ব-বিস্তৃত, দৃষ্টির স্বচ্ছতা আধুনিক ও নাগরিক; প্রথম পঙ্ক্তি থেকে শেষ পঙ্ক্তি পর্যন্ত একটি নিটোল সমগ্রতায় মূল্যবান। আমি তার একটি অতিসাধারণ কবিতাও পড়ে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত একটি উজ্জ্বল উপমা কিংবা একটি চিত্রের সূক্ষ্মতা অথবা একটি অভাবিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের আলোড়নের প্রাপ্তি আমাদের কবিতাটিকে খারিজ না করতে বাধ্য করে।
দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কবিতার এত তীব্র ঘনিষ্ঠতা, আর কোন কবিই তৈরি করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ, কলামের সংখ্যাও প্রচুরÑ কিন্তু এসব প্রয়োজন ও উপলক্ষের রচনা বলে কবিতার ঘনতা তাতে নেই। কবিতাই তার প্রকৃত ক্ষেত্র। গ্রন্থ থেকে গ্রন্থ, অজস্র কবিতা তিনি রচনা করেছেন। লেখার প্রাচুর্য আমাদের মুগ্ধ করে, তাঁর নতুন আবিষ্কার ও জয় আমাদের শক্তি ও সাহস জোগায়।
আবু সয়ীদ আইয়ুব তিরিশ-পরবর্তী প্রধান কবি হিসেবে তাঁকে যে নির্বাচন করেছেন, এ নিয়ে এখন আর বিতর্ক নেই। প্রতিপক্ষেরা শক্তি বা আল মাহমুদকে দাঁড় করাতে পারেন; সাহিত্যে এরকম ভুল বা শিথিল সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে হয়- কিন্তু তাদের গভীরতা ও বিস্তারের ক্ষেত্রটি খুব ছোট বলেই আমাদের কাছে অধিক তীক্ষè মনে হয়। কিন্তু শামসুর রাহমানের কবিতা বিশাল এক চিত্রের মতো, বিপুল তাঁর পরিধি, কোন এক ক্ষুদ্র অংশের উজ্জ্বলতা ও আলোতে তাঁর মহত্ত্ব ও বিরাটত্বকে ধরা যাবে না। একটু দূর থেকে, সম্পূর্ণ চিত্রটি দৃষ্টিতে ধরতে পারলে আমরা বুঝবো অত্যন্ত প্রজ্ঞা, স্বচ্ছ জ্ঞান, আর প্রকৃত দ্রষ্টার শক্তি না থাকলে একজনের পক্ষে প্রায় পাঁচ দশকের আর্তি, দ্রোহ, স্বপ্ন, প্রেম, কল্পনা, মেধা, মনন ও তারুণ্যকে আলিঙ্গন করা সম্ভব নয়।
অতিরঞ্জন নয়, শামসুর রাহমান একালের অনেক কবির কাজ তিনি নিজে একাই করে গেছেন। এতে তাঁর স্বাস্থ্য আর আয়ুর ওপর চাপ পড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বড় কবি তারাই, যাদের কণ্ঠস্বর সময়ের অন্য কবিদের অক্ষমতা অথবা গৌণ শক্তিকে মূর্ত করে বা মূর্ত হতে সাহায্য করে।
৪.
প্রতিভা ও রূপ প্রায়শই বিপরীত কেন্দ্রে অবস্থান করে। বায়রন, শেলী, রবীন্দ্রনাথ এঁদের প্রতিভাকে আরও অগ্রসর করে দিয়েছে এঁদের ভুবনমোহিনী রূপ। কিছুটা খর্বকায় হলেও সুদর্শন শামসুর রাহমান ভিড়ের মধ্যেও অত্যন্ত আলাদাÑ যা চট করে চোখে পড়ে। শুভ্র, কেশ, নম্র কণ্ঠস্বর, সৌজন্য, ভদ্রতা, বিনয়- এসব গুণাবলীর কোনটাতেই আমরা তাকে হারাতে পারিনি। নারীর মৃদুতা তাঁর সৌজন্যে ও আলাপচারিতায়; কিন্তু চরিত্রের বা সংকল্পের দৃঢ়তায় তিনি এক ভিন্ন মানুষ। যখন, কোন দুর্লভ মুহূর্তে, তাঁর সান্নিধ্যে যাবার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে, দেখেছি এক অভিজাত স্নিগ্ধতা। আমাদের সমকালীন অধিকাংশ কবিদের স্থূলতার পাশে, রুচির এই উচ্চতাকে কবি হিসেবে তাঁকে আরো আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্বময় করেছে।
তাঁর কাছে আমাদের ঋণ, তাঁর বিপুল সৃষ্টিশীলতার ঐশ্বর্য ও কৌলীন্য হয়তো খুব সন্নিকট সময়ের কারণে আমাদের কাছে এখনও ততো স্পষ্ট ও নিশ্চিত হচ্ছে না; কিন্তু আজ থেকে কয়েক দশক পরে তিনি নিঃসন্দেহেই আদায় করে নেবেন তাঁর প্রতিভার সংশয়াতীত প্রাপ্ত স্বীকৃতি। [সংক্ষেপিত]১৯৯৩
ভাবুক শিখরে-
কবিতার পাটক, পাঠকের কবিতা
সম্ভবত ঠাট্টা করেই আজও বাংলাদেশকে ‘কবি ও কবিতার দেশ’ বলে উল্লেখ করা হয়। বাঙালি প্রচ-ভাবেই আবেগপ্রবণ জাতি; আলস্য তার মজ্জাগত, স্বপ্ন আকাশচুম্বী কিন্তু কর্মস্পৃহা সেই তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল ও বলতে গেলে প্রায় প্রচ্ছন্ন।
ফলে, কারা যেন আবিষ্কার করেছিলেন, বাঙালির বৈষয়িক পতনের অনেকটাই কবিতার জন্যে, আবার যদি তার কিছুমাত্র গৌরব এই বিশ্বে অর্জিত হয়ে থাকেÑ তবে সেই অবদানের অনেকটা কৃতিত্বই কবিতার।
উপরের যা কিছু বলা হলো, এর সবটাই ভুল চিন্তা, অসার অভিজ্ঞতা আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্ররোচনা। কথাটা আমি এজন্যে বললুম যে, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, চিত্রকলা, দর্শন, মানব-সভ্যতার বিকাশের অপরিহার্য এসব আলোকিত অংশের কারু চেয়েই কবিতা কম কঠিন বিষয় নয়। অত্যন্ত জটিল এর সাধনা, সিদ্ধি প্রায়শই আকাশকুসুম। Ñকেননা, অনেকেরই কবিতা লেখার আয়োজন ও দক্ষতা অর্জন শেষ করতে না করতেই আয়ুর দরোজায় ডাক এসে পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত স্মরণীয় প্রতিভা ছাড়া মাঝারি প্রতিভার পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্য ও সার্বভৌমত্ব পেতেই সময় লাগে কম করে তিরিশ বছর কিংবা তারও কিছু বেশি সময়।
অবশ্য বাংলা কবিতায় (আমি বাংলাদেশের কবিতাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি- ষাট দশকের পরে কয়েকজন শিক্ষিত ও প্রকৃত ভাবুকের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, এখন অবশ্য উল্টো হাওয়ারই প্রবল প্রতাপ। তিরিশের কবিরা কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সৃজনী ক্ষমতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও জানতেন, স্বভাব-কবিতা লেখার ক্ষমতা বস্তুত পাগলামিরই রকমফের।
ইস্কুলের বালক থেকে আঠারো বছরের কিশোরীর ‘মন কেমন করা’ কবিতা মুখে মুখে রচনা করার এক উদ্দাম প্রতিযোগিতা (যাকে অতিরঞ্জিত করে বলা হয় লিরিক) শুরু হয়েছে গত দুই দশক কিংবা তিন দশক থেকে। উর্দু গজলের আকৃতিও এরকমই ছোট; বিষয়ও প্রধানত প্রেম; ঈশ্বর কিংবা অদৃষ্ট। কিন্তু সে-সব কবিতার বহুমুখী ব্যঞ্জনা, উক্তির দ্ব্যর্থক গন্তব্য ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য ও সংযত নির্যাস এদের রচনায় নেই। হাল্কা ভাবনা-তরল ভাষায়, চপল উচ্ছ্বাসে বলা হয় বলেই এসব কবিতার পাঠক বেশি।
আমার আপত্তির কারণ এ জন্যে নয় যে, ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ভালো পাস করা ছাত্রের প্রিয় কবি হবেন হেলাল হাফিজ, কি রুদ্রÑ সেই ছাত্রের বয়স, অভিজ্ঞতা, অপূর্ণ চৈতন্য ও প্রায় অ-জাগ্রত শিল্প ধারণায় সেটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যারা সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা শিক্ষিতের দাবিদার; মার্জিত রুচি ও সুচর্চিত সংস্কৃতি যাদের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই কাম্য; তারা কীভাবে উপরোক্ত অর্বাচীন বালকদের সঙ্গে এই বালক-শোভন রচনারই আজকাল পৃষ্ঠপোষক। যদি তাই-ই না হতো, তবে উপরে উল্লিখিত একজন তথাকথিত কবির শিথিল ও অশিক্ষিত রচনার পাঁচ-ছ’টি সংস্করণ হয় কীভাবে। কেন, (মৃতের প্রতি সম্মান দেখিয়ৈই বলছি, যদিও সৃষ্টি সর্বদাই আক্রমণের কিংবা প্রশংসার বস্তু; তার স্রষ্টা জীবিত কিংবা মৃত, যাই হন না কেন!) রুদ্রের অপরিণত ও গড়পড়তা রচনাশক্তিকে কবিত্ব আখ্যা দিয়ে তার অকাল-প্রয়াণকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা হয় উৎসব ও উচ্ছ্বাসের পোশাক পরিয়ে।
অনেকেই বলবেন, ইস্কুল কিংবা কলেজের ছাত্রদের জন্যে সহজবোধ্য লেখা কি আগে ছিলো না? এর জবাব, হ্যাঁ ছিলো। জয়েস, ফকনার, কুন্ডেরা, লোর্কা বা প্যার্সের কবিতা এই সদ্য জাগ্রত পাঠকেরা পড়বে; এতটা উগ্র জবরদস্তি প্রয়োগের মত নির্বোধ আমি নই। যেমন মোহন সিরিজ, গোয়েন্দাগল্প কিংবা নীহাররঞ্জন, গেলবার বয়স ইস্কুলের জীবনটুকুই। তাতে লজ্জার কিছুই নেই; এভাবেই ভবিষ্যতের জন্যে পড়ার শক্তি সঞ্চয় করার পথটাই স্বাভাবিক ও যথার্থ। তাই সদ্য সদ্য ইস্কুল উত্তীর্ণ ছাত্রের যদি শামসুর রাহমান কিংবা আল মাহমুদের কবিতা প্রিয় না হয়; যদি প্রচ- দুর্বোধ্য মনে হয় জীবনানন্দের কবিতা এবং সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে বিরাট ধ্বনিসর্বস্ব অন্ধকার; তবে আমি তার সেই ব্যর্থতায় অবাক হবো না। কিন্তু যারা সাবালক পাঠক, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজা পেরিয়ে সমাজের অগ্রগামীদের দলে পড়ার প্রাথমিক গৌরবটুকু অর্জন করেছেনÑ কিংবা সেই সব অধ্যাপক, যারা প্রকৃত সৃজনশীলতার অভাবে অপরিপক্ব সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনুর্বরতার অভাব পুষিয়ে নিচ্ছেন বা সভা সমিতি সভাপতিত্ব কিংবা এ ধরনের ক্রিয়াকা-ের সঙ্গে জিড়তÑ তারাও যখন পরের মুখে ঝাল খেয়ে এই সব দুগ্ধপোষ্যদেরই স্বীকৃতি দিচ্ছেন দ্বিধাহীন চিত্তেÑ তখন সমাজ পতনের এই নিদারুণ দৃষ্টান্ত আমাদের মহা ভাবনায় ফেলে।
না হয় এদের কথাও বাদ দিলাম। দেশের রাজনীতি, দর্শন, চলচ্চিত্র, সঙ্গীতÑ সবক্ষেত্রেই এখন নিকৃষ্টদের প্রবল উপস্থিতি ও প্রভাবÑ কিন্তু যারা নিজেরাই লেখক, কবি, অন্তত সেই স্বীকৃতি ও যশের জন্মে উৎসর্গিতÑ তাদের রুচি, বিচারের ক্ষমতা, তৃষ্ণা ও পক্ষপাতও যখন এই ‘জনপ্রিয়’ ও চলতি হাওয়ার সাহিত্যের পক্ষে; তখন বুঝতে হবে, অবশিষ্ট সম্ভাবনারও মৃত্যু আসন্ন। কেননা উঁচুদরের সাহিত্যের, সমকালীন শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের আবিষ্কারক সব যুগেই প্রধানত সেই কালের লেখকরাই। এ জন্যেই যথার্থ বড় কবিকে হতে হয় কবিদের কবি; বড় লেখককে লেখকদের লেখক। সাহিত্যের আদর্শ তৈরি হয় তাদের হাতে; মাঝারি ও সর্বশেষ মানের লেখক-কবিরা সেই আদর্শের অনুসরণ করে অর্জিত সম্পদের বিস্তৃতি ও সংগ্রহ বাড়ান। কিন্তু দু’একজনকে বাদ দিলে (কিন্তু তারাও আত্মরক্ষার বর্ম রচনা করে নিশ্চুপ থাকাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন) সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে লেখক-কবিদের, বিশেষ করে কবিদের রুচি, শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে ভয়াবহ। এই অতি তরুণ কবিযশপ্রার্থীদের সাহস, বিবেক ও উঁচু আদর্শের চাপ তো নেই-ই বরং এরা অত্যন্ত প্রচার লোলুপ। যে কারণে জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীন বিকাশের চেয়ে এরা সহজেই স্বীকার করে নেন দাসত্ব ও অসার দিনগত পাপক্ষয়ের ফাঁদ। এরা প্রতিষ্ঠিত মান (যা গড়তে কিংবা পড়ে অর্থ উদ্ধার করতে মেধা, চিন্তা ও যুক্তি লাগে না) প্রত্যক্ষ করেই বুঝে নেন, কী করে জনরুচি কিংবা ‘পাঠকের কবিতা’ লেখা যায়। এক্ষেত্রে যেহেতু নিয়ন্ত্রণ করার কোন নিয়ম নেই এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাত্রই বাংলা সাহিত্য রচনায় স্বাধীন-সেহেতু মুদ্রিত রচনা মাত্রই প্রচারের প্রত্যাশায় বাজারে আসে।
নিঃসন্দেহেই যাদের এতকাল কবিতার পাঠক বলে আমরা ভাবতুম, যেমন, প্রাপ্তবয়স্ক, বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য বহনে সক্ষম, পরিশ্রমী, বিচিত্র বিদ্যার অধিকারী, তৃষ্ণার্ত, সৌন্দর্যের প্রভাবে প্রসারিত-রুচি ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যে নিজে সৃষ্টিশীলতায় নাহলেও মননে ও অর্জনে প্রায় করিই কাছাকাছি; তারা, দুঃখজনক হলেও আজ নিরুদ্দেশ। পার্থিব লালসায় এদের দৃষ্টি আজ অন্যদিকে। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে পরিশোধিত চৈতন্যের যে ভাবুক শিখর রচনা করেন কবিরা; এদের কাছে তা পাগলামীরই নামান্তর।
শুনেছি, স্থুল ও নিম্নমানের চলচ্চিত্রেরও চাহিদা আছে, যমন আধুনিক যুগে টেলিভিশন এসেছে এই স্থূলবুদ্ধি মানুষদের বিনোদনের জন্য এক চাহিদা থেকে; কাউকে তৃপ্তি দ্যায় রতি-প্রলুব্ধকারি রগরগে রম্যপত্রিকা; সেই সঙ্গে বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্যে স্নায়ুউত্তেজক প্রভাতী পত্রিকা কিংবা সংবাদপত্রÑ ঠিক একইভাবে সমাজে থাকবে অতি নিম্নমানের ও নিম্নস্তরের পাঠকের মনতুষ্টির জন্যে একদল কবি, যারা দাবি মাত্রই রচনা করে দেবেন পাঠকের জন্যে অতি সরল ও সহজপাচ্য কিছু পংক্তি... অন্য কিছু না হোক, আকৃতির কারণেই যাকে লোকে কবিতা বলে শনাক্ত করে। কবিতা এদের কাছে, এই যাযাবর পদ্য রচয়িতাদের চেতনায় বিলাসের উপকরণমাত্র। কিন্তু প্রকৃত ও মুষ্টিমেয় কবিরা এদের জন্যেই উপেক্ষা ও নির্যাতন সহ্য করবে আরও বহুকাল। অন্তত এই শতাব্দী পূর্ণ করার আগে নতুন সূর্যোদয়ের ন্যূনতম আশাও দেখতে পাচ্ছি না।
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব