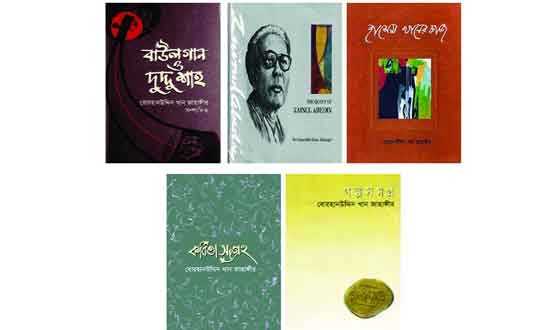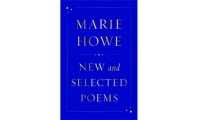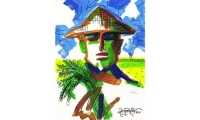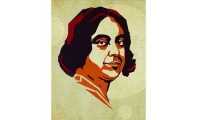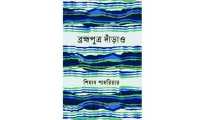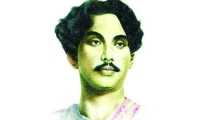সাময়িকী
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যে একটা দিগদর্শন স্পষ্ট। সে হচ্ছে সাহিত্যের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক নয়। সাহিত্যের একটা দিক হচ্ছে কলোনির সময়, অপরটি হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর সময়। এই দুই সময়কেই বোঝার জন্য দরকার কলোনিয়াল এবং স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। এই দুই মিলিয়ে সাহিত্যে কলোনিয়াল অ্যাডভেঞ্চার এবং এই দুই মিলিয়ে কলোনিয়াল সাহিত্যের স্বরূপ এবং বাংলাদেশি সাহিত্যের উত্থান। কলোনিকালের লেখক পাকিস্তানি কলোনি কাল এবং ব্রিটিশ কলোনি কালের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এসব তত্ত্বের মধ্যে আছে শ্বেতাঙ্গদের সভ্যতার মিশন এবং পাকিস্তানিদের ইসলামীকরণের মিশন, সে জন্য দু’ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রয়াসকে যুক্তিশীল করা হয়েছে। কলোনিয়াল অভিজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে, সাহিত্যের সমাদর্শিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ, এই বিশ্লেষণে যুক্ত বাংলা সাহিত্যের কলোনিয়াল এবং রেসিয়াল উপাদানগুলো। কলোনিয়াল উপাদানগুলো এসেছে পাকিস্তানি এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে। রেসিয়াল উপাদানগুলো এসেছে শ্বেতাঙ্গ শাসন বনাম বাঙালি জনজীবন, শ্বেতাঙ্গ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব বনাম বাঙালি জনজীবনের নিকৃষ্টতা, বাঙালি জনজীবনের মধ্যে ক্রিয়াশীল আবার হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব বনাম মুসলমান সমাজের নিকৃষ্টতা; আবার বাঙালি জনজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বনাম পাহাড়ি, আরণ্যক সমাজের নিকৃষ্টতা। সাহিত্যে কলোনিয়াল এবং রেসিয়াল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নেহাতই অভিজ্ঞতার ভিন্নতা নয়, এখানে স্পষ্ট শ্রেষ্ঠ সমাজের নিকৃষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা। এই ঘৃণা মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা, একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী নিকৃষ্ট মানুষগুলোর অধিকারহীন জীবনযাপন। কলোনিয়াল সমাজে বাঙালিদের কতক অংশ ‘ইংরেজ’ হওয়ার চেষ্টা করেছে, তেমনি বাঙালিদের কতক অংশ ‘পাকিস্তানি’ হওয়ার চেষ্টা করেছে, তেমনি পাহাড়ি ও আরণ্যক জনগোষ্ঠীর কতক অংশ ‘বাঙালি’ হওয়ার চেষ্টা করেছে।
কলোনিয়াল সমাজ সে জন্য কলোনাইজড জনসমষ্টির যারা কলোনাইজার (ক্ষেত্র বিশেষে ইংরেজ, পাকিস্তানি, বাঙালি) তাদের প্রত্যাখ্যান কেবল নয়, এই বিরোধ কিংবা বিষম অবস্থানে উচ্চারিত গভীর এক নির্ভরশীলতার বোধ। এই বোধে উচ্চারিত যারা আদিবাসী, ইংরেজদের চোখে বাঙালি, কিংবা পাকিস্তানিদের চোখে বাঙালি কিংবা বাঙালিদের চোখে পাহাড়ি ও আরণ্যক জনগোষ্ঠী হচ্ছে নষ্টামির অন্তঃসার, এই নষ্টামি থেকে উৎসারিত দূষণ, অন্যদিকে কলোনাইজার জনসমষ্টির মধ্যে ক্রিয়াশীল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধ। কলোনাইজার জনসমষ্টি ক্ষমতার জোরে কেবল শাসন করেছে তাই নয়, কলোনাইজড জনসমষ্টির তুলনায় তারা নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ।
কলোনিয়াল সমাজের সাহিত্যে অন্তঃশীল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কিংবা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কিংবা বাঙালিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা কিংবা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার আকাক্সক্ষা। এই আকাক্সক্ষার মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থান বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থান দুই ধরনের। প্রথমত, এ সব আন্দোলন হয়েছে গণমানুষের সমর্থন নিয়ে। দ্বিতীয়ত, এ সব আন্দোলনে গণমানুষের অংশগ্রহণ ন্যূনতম। এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, শিক্ষিত রাজনৈতিক এলিটরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কিংবা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কিংবা বাঙালিদের বিরুদ্ধে পপুলার সমর্থন ব্যবহার করেছে, কিন্তু এ এলিটদের কোনো আকাক্সক্ষা ছিল না কলোনিয়াল আমলের কিংবা (স্বাধীনতা-উত্তর আমলের) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন করা কিংবা যে জনসমষ্টিকে তারা শোষণ করেছে তাদের সঙ্গে ক্ষমতার শেয়ার করা। এই এলিটদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল (অথবা আছে) কলোনিয়াল আমলাতন্ত্রের হাত থেকে নিজেদের কাছে ক্ষমতা বদলি করা। এলিট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যকার এই প্রভেদ, তফাত, ব্যবধানের অর্থ হচ্ছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন গণমানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি।
লেখকের প্রজেক্ট হচ্ছে সাহিত্য নির্মাণ করা। যে সাহিত্য কলোনিয়াল সমাজ ক্ষেত্রে উৎসারিত এবং স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে প্রবাহিত সে প্রজেক্টে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রেসিয়াল এবং নৈতিক সমস্যাগুলো ঘুরে ঘুরে বারে বারে আসে। কলোনিয়াল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে সাস্কৃতিক আইডেনটিটি তৈরি হবে কীভাবে? সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি হচ্ছে নিজের সত্তা এবং অন্যের সত্তার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা, নিজেদের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সম্মান তৈরি করা। এই সম্মান বাংলাদেশের মতো মাল্টিরেসিয়াল সমাজে কত দূর পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব। এখানে লেখকের সঙ্গে তার সমাজের প্রকৃত আইডেন্টিফিকেশনের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে রাষ্ট্রসৃষ্ট আইন-কানুন, সমাজসৃষ্ট তার রং, তার বর্ণ, তার শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা নিকৃষ্টতার দ্বন্দ্ব। এই সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে, কখন কোন অর্থে জাতীয় বাঙালি সাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে। মাল্টিরেসিয়াল সমাজে জাতীয় সাহিত্য তৈরি হয় না, তৈরি হয় কলোনিয়াল সাহিত্য; যার মধ্যে ক্রিয়াশীল ইউরোপিয়ান সাহিত্য, পাকিস্তানি ধর্মমনস্ক সাহিত্য, শ্রেণি সাহিত্য। কলোনিয়ালিজমের অবসান দরকার সব অর্থে, যাতে করে জাতীয় চেতনা এবং সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়।
নিজের সত্তা এবং অন্যের সত্তার মধ্যে তার সম্পর্ক সাহিত্য এবং সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক, জাতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে মতাদর্শ। এই মতাদর্শ হচ্ছে জীবন্ত সম্পর্কের পরিশীলিত স্বরূপ। যদি কোনো মতাদর্শ অসম্পূর্ণ থাকে, সেক্ষেত্রে সাহিত্য কিংবা সাহিত্যের কোনো টেক্সট তা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম। নান্দনিকতা কিংবা নান্দনিক কোনো কাজ সমাধানহীন সামাজিক বৈপরীত্যের সমাধান করতে পারে কাল্পনিক কিংবা ফর্মাল সম্পর্ক উদ্ভাবন করে। সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রশ্নে এই কথাগুলো মনে রাখা দরকার।
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-
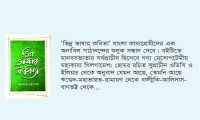
আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-
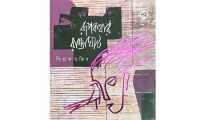
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
-
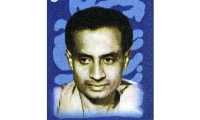
বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ বিষয়ভাবনা