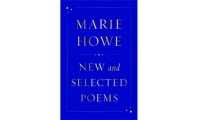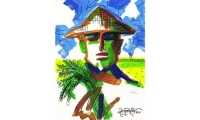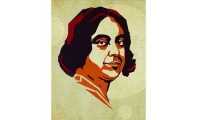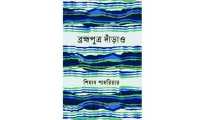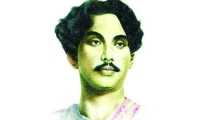সাময়িকী
উপন্যাসের জন্মবীক্ষা
রকিবুল হাসান
ইতালিয়ান লেখক জিওভান্নি বোকাচ্চিও
আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সকল আশা-আকাক্সক্ষা-বেদনার সাহিত্য-রূপ উপন্যাস।১ কিন্তু উপন্যাসের জন্মকাল নিয়ে নানামাত্রিক আলোচনা আছে। সেসব আলোচনাতে সঠিক সময়কাল নিয়ে মতবিরোধও আছে। উপন্যাসের জন্মের সঠিক সময়কাল নির্ণয়ে এখনো মতবিরোধ নিষ্পন্ন হয়নি। উপন্যাসের সঠিক অবকাঠামো তৈরির আগে অনেককাল ধরেই উপন্যাসের-স্টাইলে কিছু রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো উপন্যাস না হলেও উপন্যাসের ইঙ্গিত বহন করে। ইতালির বোকাচ্চিওর দেকামেরন, ইংল্যান্ডের চসারের ক্যান্টারবারি টেলস্, ফ্রান্সের রাবল্যের গারগানতুয়া ও প্যাঁতাগ্রুয়েল এবং স্পেনের মিগুয়েল দ্য সেরভান্তেস’র ডন কিকসট্ দ্য লা মাঞ্চা- এই পাঁচটি গ্রন্থ সেই নিদর্শন বহন করে। এ পাঁচটি গ্রন্থের কোনোটিই যথার্থ উপন্যাস নয়। কিন্তু উপন্যাসের ইঙ্গিত গ্রন্থগুলোতে লক্ষণীয়। উপন্যাসের বীজবপন মূলত এ গ্রন্থগুলোতে নিহিত। আর এ গ্রন্থগুলোর চারজন লেখকই ছিলেন ইউরোপের প্রথম আধুনিক শিল্পী। এসব লেখক তাঁদের গ্রন্থে ‘মধ্যযুগীয় রোমান্সের অবিশ্বাস্য কল্পলোকের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্য ও অবাস্তব জীবনকে তীক্ষè ব্যঙ্গের শরাঘাতে ও যুক্তির নির্মম খোঁচায় বাস্তবভূমিতে ধরাশায়ী করা হয়েছে। ইউরোপের মানুষের সামনে এঁরা এক নতুন পৃথিবীর ছবি তুলে ধরলেন।’২ উপন্যাসের ইঙ্গিত দিয়ে যে-সব গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে, সে-সবের উপর দাঁড়িয়ে উপন্যাস সৃষ্টির পথ এগিয়ে গেছে আরো খানিকটা পথ। আর তা অবকাঠামোগতভাবে যেমন, তেমনি বিষয়বস্তুতেও। বিশেষ করে উপন্যাসের প্রাথমিক সূচনা লক্ষ্য করা যায় ষোলো, সতের ও আঠার শতকে। এটি ঘটে স্পেন ও ফ্রান্সে। বিষয়বস্তুতে যুক্ত হয় বিজ্ঞান-কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার-উপাখ্যান, রম্য ও প্রেম। এসবের ভেতর গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায় বাস্তবচেতনা, মানবসম্পর্ক ও সংসারমুখিতা। যেখানে ঘোষিত হয়েছে বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তির জয়। আর এর মূলমন্ত্রক ছিলেন ‘ফ্রান্সে মিশেল দ্য মঁতেন, ভোলত্যের, রুশো, দিদেরো এবং স্পেনে লেসেজ। এঁদের রচনায় মানুষের আত্মবিশ্বাসের কথা প্রথম উচ্চারিত হয়। বিজ্ঞানকে মানুষের জীবনকে উন্নত করতে এবং রহস্যময় অধ্যাত্ম স্বর্গের পরিবর্তে স্পষ্টরূপে ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেতনাবোধ তৈরি করে। এর মাধ্যমেই ইউরোপের মানুষের জীবনে ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’- এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইউরোপের জীবনের দিগন্ত আরো প্রসারিত হয়। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং এশিয়া-আমেরিকার জলপথের সন্ধান এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। আর উপন্যাসের জন্ম ঘটে মূলত তখনই।
আঠারো শতকে শিল্পবিপ্লব ঘটে, আবিষ্কার হয় মুদ্রণযন্ত্রের। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে উদ্ভব ঘটে সাময়িক পত্রিকার এবং এটি দ্রুত প্রসারতা লাভ করে। এতে করে উপন্যাসের ব্যাপারটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসে বিষয়বস্তুর যেমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তেমনি ঘটতে থাকে উপন্যাসের কাঠামোগত পরিবর্তন। এই ধারাতে জন্ম ঘটে বানিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস (১৬৭৮), ডানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশো (১৭২৭), জনাথান সুইফটের গালিভারস্ ট্রাভেলস (১৬২৭)। এ উপন্যাসত্রয়ে নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত হয় বাস্তব জীবনের গল্প; উপন্যাসের ভিত্তি তৈরিতে যা অবিশ্বাস্য এক ভূমিকা রাখে। উপন্যাসের পথ উন্মুক্ত হয় মূলত এখান থেকেই। বিশেষত এই তিনটি গ্রন্থের মাধ্যমে। এ ধারাতেই আবির্ভূত হন রিচার্ডসন, ফিলডিং, স্মোলেট ও স্টার্ন। রিচার্ডসনের পামেলা (১৭৪০), ক্লারিসা হার্লো ও স্যার চার্লস গ্রান্ডিসন, হেনরি ফিলডিং’র জোসেফ অ্যান্ড্রুজ (১৭৪২), ও টম জোন্স (১৭৪৯), এস্মালেটের রোডরিক র্যান্ডম (১৭৪৮), পেরিগ্রিন পিকল (১৭৫১) ও হামফ্রি ক্লিঙ্কার (১৭৭১) এবং স্টার্নের ট্রিস্ট্রাম স্যান্ডি (১৭৬০-৬৭) ও আ সেন্টিমেন্টাল জার্নি (১৭৭৩)- ইংরেজি সাহিত্যে এগুলো ছিল প্রাথমিক উপন্যাস। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ত্রিশ বছর সময়কালের মধ্যে। ইংরেজি উপন্যাসের বুনিয়াদী ভিত্তি মূলত রচিত হয় এঁদের হাতেই। ইংরেজি উপন্যাস-সাহিত্যের স্থপতি হিসেবেও এঁদেরকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এঁদের হাতের ইংরেজি উপন্যাসের মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর উনিশ শতকে ইংরেজি উপন্যাসের বিকাশের দুর্দান্ত এক সময়কাল। উনিশ শতক হয়ে ওঠে উপন্যাসের শতক। পৃথিবীজুড়েই উপন্যাসের বিশাল রাজত্ব গড়ে ওঠে। উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক ‘স্বর্ণশতক’ হিসেবে অভিহিত হতে পারে। উনিশ শতকে উপন্যাসের যে বিকাশ ঘটেছিল এবং যেসব মহাশক্তিশালী ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অন্য আর কোনো শতকে তা আর সম্ভব হয়নি। এসব বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উপন্যাস-সাহিত্যকে সেসময় এতো সমৃদ্ধ করে গেছেন, পরবর্তীতে তাঁদের এ ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-বিকাশের ধারাতেই উপন্যাস পথ হেঁটেছে। যা আজো এক অপার বিস্ময় হয়ে আছে। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডে উনিশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীখ্যাত বিভিন্ন ঔপন্যাসিক। ফ্রান্সের সেসময়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্তাঁধাল, বালজাক, আলেকজান্ডার ডুমা, জর্জ সাঁ, ভিক্টর হুগো, গুস্তাব ফ্লোবের, এমিল জোলা, আলফাঁস দোদে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতালিতে আবির্ভূত হন জিওভান্নি ভের্গা। স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসমারিয়া দ্য পেরেডা, হুয়ান ভালেরা, বেনিতো পেরেজ গালদোস। রাশিয়ার নিকোলাই গোগোল, ইভান তুর্গেনেভ্, লিও টলস্টয়, দস্তভয়েস্কি, আন্তন চেখভ। ইংল্যান্ডের জেন অস্টেন, ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, জর্জ মেরিডিথ, টমার্স হার্ডি, ব্রন্টে ভগিনীত্রয় এবং আমেরিকার নাথানিয়েল হথর্ন ও হানমেন মেলভিল। এসব বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির ওপর নির্ভর করে বিশ শতকে উপন্যাস জনপ্রিয় সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ শতকের উপন্যাসের বিশেষ দিক ছিল লেখকের আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটি। সেসময়ে বিখ্যাত সব লেখকেরা উপন্যাসকে তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। জীবননিষ্ঠা, জীবনজিজ্ঞাসা, সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবতার ভিত্তির ওপর উপন্যাসের নতুনমাত্রা জন্মলাভ করে। পাঠকের কাছেও যা নতুন আস্বাদনে পরিণত হয়। সেই কারণে পাঠকের আগ্রহমাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশ^সাহিত্যে উপন্যাসের জনপ্রিয়তার প্রথম দিকটি এ পর্যায়েই চিহ্নিত হয়।
বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই। দীর্ঘদিন বাংলা উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্য বেশ শক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণে বাংলা উপন্যাসের সফল যাত্রা ঘটে। সময়কাল হিসেবে আঠারো শতকের ইংরেজি উপন্যাসকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি। একথা স্বীকার্য যে, বাঙালির নিজস্ব সম্পদ লোকসাহিত্য, রূপকথা, উপকথা, কিস্সা-গল্প, বীরত্ব-কাহিনি নির্ভর হয়ে সেসময় উপন্যাস নির্মিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশশাসনের একটি পর্যায়ে নগরজীবনের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটতে থাকে। ভারতবর্ষ তথা বাঙালি সমাজবাস্তবতায় পুঁজির প্রতিক্রিয়ায় নাগরিক উপকরণের সূত্রপাত ঘটতে থাকে বৃটিশশাসনের গোড়া থেকেই নানাভাবে। মুসলমানদের যে বাস্তবতা তৈরি হয় তা অনেকাংশে উপেক্ষিত ও অবহেলিত জীবনপ্রয়াস। সমাজ-অর্থনীতি বা অনাদৃত পরিবেশে কোনোভাবেই আধুনিকতার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা সম্পন্ন হয়নি। পুঁজির প্রবাহের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। বিপরীতে হিন্দু মধ্যবিত্ত ইংরেজ সহযোগিতা বা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়সমূহ সহজাত বাস্তবতায় গ্রহণ করে। ফলে এ সম্প্রদায়ের ভেতরে যোগ্য ব্যক্তি তথা দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি হয়। নবজাগরণের প্রবাদপুরুষ হিসেবেই তারা পরিগণিত হতে থাকেন। তাছাড়া মেধা ও যোগ্যতার কমতি ছিল না এসকল মনীষীদের। ভারতবর্ষ তথা বাংলার যাবতীয় কর্মকা-ের পথিকৃৎরূপে তারা পরিগণিত হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ সকল মনীষীর হাতেই সমাজ সংস্কার, নগরভিত্তি বা রূপায়ণ পুনর্গঠিত হওয়ার ঘটনা শুরু হতে থাকে। তবে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি মুসলমানরা সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’র (১৭৯৩) ফলে বঙ্গদেশের ভূমিব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সংখ্যার হিসেবে বাঙালি মুসলমান জমিদার বাঙালি হিন্দু জমিদারের চেয়ে কখনই বেশি ছিল না। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই সংখ্যা আরো হ্রাস পায়। কারণ, এই নতুন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে পূর্বতন জমিদারেরাই জমিদারি হারিয়েছিলেন। কিন্তু পুরনো হিন্দু জমিদারের বদলে যেভাবে নতুন হিন্দু জমিদারশ্রেণির উদ্ভব ঘটে, বাঙালি মুসমানদের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। কেননা, ভূমিতে বিনিময়যোগ্য অর্থের সংস্থান তাদের ছিল না। ফলত তাদের মধ্যে এভাবেই সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা কমে যেতে থাকে। যার জন্য পুরো ব্যাপারটাই এরকম দাঁড়ায় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নতির অর্থই হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের অধোগতি।’৩ ফলশ্রুতিতে মুলমান নেতৃত্ব তৈরি হয়নি। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সচেতনতাও গড়ে ওঠেনি। এ কারণে, সাং¯ৃ‹তিকভাবে তারা থেকে যায় নিরাবলম্ব। যাবতীয় বিষয়-ব্যবস্থাপনায় ধরা পড়ে অসংলগ্নতা। আধুনিকতা অর্জনের পথে মুসলমানদের ঘটে অমোচনীয় বিপর্যয়। ভাষা-সাহিত্য সং¯ৃ‹তির পাদপীঠে তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের অসহায়ত্বই প্রতিপন্ন হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাকে ঘিরে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশ বিরাজমান ছিল সেখানে মুসলমানরা প্রকৃতার্থে বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকদের নানামাফিক মন্তব্য থাকলেও প্রকৃত সত্য এই যে, বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও প্রসারের সামূহিক বাস্তবতায় মুসলমানদের কোনো কৃতি পরিলক্ষিত হয় না। গদ্যের নির্মিত ও অর্জিত আধুনিকতার সঙ্গে মুসলমানরা জড়িত থাকতে পারেননি বলা চলে। সেক্ষেত্রে তারা তৈরিও ছিলেন না। এছাড়া ধর্মীয় শাস্ত্রাচারে বা সংস্কার বিশ্বাস তাদের এতই বদ্ধমূল করে রেখেছিল যে, সেখানে আধুনিকতার বিবিধ উপাদানসমূহকে গ্রাহ্য করতে তারা কিছুতেই সক্ষম ছিলো না। বস্তুত ধর্মের রীতি-নীতি আর আধুনিকতার সঙ্গে তাদের বিরোধ ও বাধা দুটোই ছিল। ফলে আধুনিকতা অর্জনের পথে তারা কিছুতেই এগোতে পারেনি। গদ্য উৎপত্তির এ পর্বে যখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) মতো লেখকরা সামাজিক নকশাধর্মী (ংড়পরধষ ংশবঃপয) রচনাসমূহে মনোনিবেশ করেছেন এবং কথাসাহিত্যের বাস্তবতা উন্মোচিত হচ্ছে বা পথ তৈরি হচ্ছে তখন মুসলমানরা এসব থেকে দূরে স্থিত আছেন। তারা মূল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত। ধর্মোন্মাদ বা প্রতিক্রিয়াশীলতার বেশে খোলাফায়ে রাশেদিনের রাজ্যকে পুনরাবর্তন বা ফিরে যাওয়ার জেহাদে শামিল হতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ পর্যায়ে বেশ কিছু কারণ চিন্তাবিদদের দর্পণে উঠে আসে। যেমন, মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, প্রত্যন্ত গ্রামে স্থিতি, নাগরিক সংস্পর্শ না থাকা, কুসংস্কার আর শাস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশীল মনের আশ্রয়, আধুনিকতার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ, ইংরেজি শিক্ষার অবহেলা ইত্যাদি। ফলে গদ্যরচনার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য উপাদান আবিষ্কারে তারা অনুপস্থিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। গদ্যের অস্তিত্বের ভেতরে যে নগরায়ণ ভাবনা, আধুনিকতার উন্মেষ, প্রগতিচেতনার উত্থান, ব্যক্তিচরিত্রের উন্মোচন, প্রতিরোধী ও সাহসী চরিত্র সৃষ্টি, সংস্কার বা দ্বিধাকে অস্বীকার করে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ তৎপরতা সবকিছুই এগিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু সেটি মুষ্ঠিমেয় শিক্ষিত হিন্দুর ভেতরে চললেও তা জনপ্রিয়তার দৃষ্টিতে সম্মুখগামী হতে পারেনি। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কিছু স্কেচধর্মী নাটক যেমন রচিত হয়, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনুবাদ হয় এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পুননির্মাণও চলতে থাকে। এ পুনর্পাঠে সাহিত্যে উন্মোচিত হতে থাকে নতুন জীবন-বীক্ষা। সেখানে সমাজ সংস্কার বা শাস্ত্রীয় ধর্মাচার বিপুলভাবে ভাঙনের মুখে পড়ে। যুক্ত হয় জীবনের আলোকিত ও উন্মত্ত সত্যসমূহ। এ পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক নকশার ভেতর থেকে শিল্পপ্রয়াসের বার্তা উন্মোচিত হতে থাকে।
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-
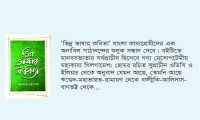
আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-
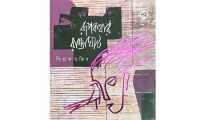
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
-
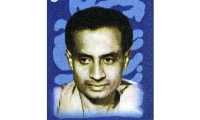
বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ বিষয়ভাবনা