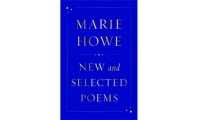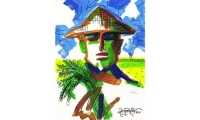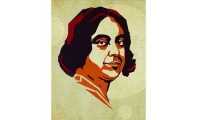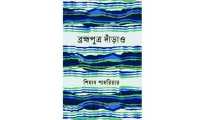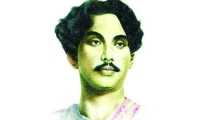সাময়িকী
বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি পর্যবেক্ষণ
কামরুল ইসলাম
শিল্পী : রাজিব রায়
বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং বাঙালি সংস্কৃতির রয়েছে দীর্ঘ পথপরিক্রমা। তা কখনো সুখের, দুঃখের কিংবা রক্তক্ষয়ের, জয়ের কিংবা পরাজয়ের। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে এগোতে হয়েছে বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে। অল্পকিছু দেশি শব্দ নিয়ে তো আর এ ভাষা বিকাশ লাভ করেনি, নানা উৎস থেকে আহৃত হয়েছে বহু শব্দ। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাও একটি মিশ্রভাষা। নানা জাতিগোষ্ঠীর মুখের ভাষা যোগ হয়েছে এই ভাষায়। নতুন নতুন শব্দের সংযোজনে ভাষার সৌন্দর্য বাড়ে। ইংরেজি ভাষার দিকে তাকালেই সেটি সহজেই বোঝা যায়। ভাষা প্রাণ পায় এই আহরণে এবং শিল্পসাহিত্যে তার ব্যাপক ব্যবহারে ভাষা গতিশীল হয়। বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা- যা একটি বোঝাবুঝির জগতের সাঁকো তৈরি করে। দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। অঞ্চলভেদে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। বদলে যায় শব্দের রূপ। ভাষা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। কয়েক শ’ বছর আগে বাংলা ভাষার যে অবস্থা ছিল, আজকে কিন্তু আর সেরকম নেই। আগামী কয়েক শ’ বছর পরে আজকের এই রূপ আর থাকবে না। পৃথিবীর যে কোনো ভাষাই নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, বিকশিত হয় তখনই, যখন সেই ভাষায় সৃষ্টি হয় উচ্চমার্গের সাহিত্য।
বহু দ্রাবিড় শব্দ তৎসম শব্দ রূপে বাংলা ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বহু তামিল কানাড়িসহ ভারতবর্ষের অনেক ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। মনে রাখতে হবে, যে ভাষার গ্রহণ করবার ক্ষমতা যত বেশি সেই ভাষা তত শক্তিশালী। চীনা ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার খোঁজ পাওয়া যাবে এ ভাষায়। মুসলিম বিজয়ের পর প্রচুর আরবি-ফার্সি তুর্কি শব্দ এ ভাষায় ঢুকে পড়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম ভাষা। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় সপ্তম শতকে। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। চর্যাপদ প্রাচীন বাংলার কাব্য বা সাহিত্য। চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচনা করেছিলেন কাহ্নপা। তিনি ১৩টি পদ রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ ও কবি। পুরা নাম কৃষ্ণাচার্য পাদ। পরে তিনি সহজিয়া মতে দীক্ষা নিয়ে সিদ্ধাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ছাড়াও আরো অনেক পদকর্তার নাম জানা যায় যারা খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পদগুলো রচনা করেন। কোনো কোনো গবেষক খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পদগুলো রচিত হয়েছে বলে মনে করেন। চর্যাপদকে চর্যাগীতিও বলা হয়। হরপ্রসাদশাস্ত্রীর মতে, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি লুইপা। কিন্তু ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি শবরপা। উল্লেখ্য, ১৯০৭ সালে ড. হরপ্রসাদশাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এটি সম্পাদনাও করেছিলেন ড. হরপ্রসাদশাস্ত্রী। ২৩ বা ২৪ জন চর্যাপদকর্তার (সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ) পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদ বা চর্যাগীতি মূলত বৌদ্ধ গান বা দোহা। দুর্বোধ্যতার কারণে চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়।
প্রাচীন বঙ্গালের এই বাংলা ভাষা আজ বিশ^দরবারে স্থান করে নিয়েছে তার ব্যাপক ব্যবহার এবং সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে। তামিল, তেলেগু, মালায়লাম, কানাড়ি প্রভৃতি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। আর্যগোষ্ঠীর আদিভাষা বৈদিক সংস্কৃত বিবর্তিত হয়ে কালক্রমে বাংলা, হিন্দুস্তানি, মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বলেছেন- Bengali is a member of the Indic group of the Indo Iranian or Aryan Branch of the Indo-European family of Language. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন- ‘অনুমিত হয় যে, আর্যগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আর্যভাষা গ্রহণ করে, প্রাচীন সংস্কৃত হতে প্রথমে পালি ও প্রাকৃত, এবং পরে অপভ্রংশ, এই তিনটি ভাষার উৎপত্তি হয়। অপভ্রংশ হতে বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।’ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ‘বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে লিখেছেন- ‘বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নয়, দূর সম্পকের আত্মীয় মাত্র’। সংস্কৃত থেকে বাংলার উৎপত্তি- এই চিরাচরিত ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে বাঙালি প-িতদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন- ‘মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলার উৎপত্তি’। মাগধী প্রাকৃতের পূর্বতর রূপ হচ্ছে গৌড়ী প্রাকৃত। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ‘গৌড়ী প্রাকৃত হতে গৌড়ী অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে’। বাংলা ভাষার পূর্বপুরুষ হলো প্রোটো-গৌড় বাংলা, যা এসেছিল প্রোটো-গৌড়-কামরূপ ভাষা থেকে, সেটি আবার এসেছিল মাগধী প্রাকৃত থেকে। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। সুতরাং, এ নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। আদমশুমারি ১৯১১ অনুযায়ী ভারতের সর্ববৃহৎ একক জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ছিল বাংলা। তখন ৪ কোটি ৮৩ লাখ ৬৭হাজার ৯শ’ ১৫ জন ভারতীয় মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি।
১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে এই কলেজটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৮০১ সালে এই কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় এবং উইলিয়াম কেরি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য উইলিয়াম কেরি কলকাতায় এসেই রামরাম বসুর কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেন এবং তার সাহায্য নিয়ে বাইবেলের অনুবাদের কাজে হাত দেন।তিনি তার বিভাগে কয়েকজন বাঙালি প-িতকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার বিবর্তনে উইলিয়াম কেরির অবদান অনস্বীকার্য। একজন খ্রিস্টান মিশনারি ফাদার উইলিয়াম কেরি এবং অন্য মিশনারিরা অনুধাবন করেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য এই ভাষার চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। উইলিয়াম কেরি রচনা করেন বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘কথোপকথন’ (১৮০১)। পরে ১৮১২ সালে প্রকাশিত হয় ‘ইতিহাসমালা’। বাংলা ভাষার প্রতি তার ভালোবাসার অনেক নিদর্শন রয়েছে। ১৮১৮ সালে উপমহাদেশে বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশের কৃতিত্ব কেরি সাহেবের। তিনি ‘কথোপকথন’ লিখেছিলেন কথ্যভাষায় এবং বাংলা গদ্যের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তকে ভারতীয় অন্য সকল ভাষার চেয়ে বাংলা যেন পিছিয়ে না থাকে, অবহেলিত না হয়, সেব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বাংলায় গদ্যপাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক তিনি। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁর সংগ্রামকে আমাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাবিস্তার এবং বিজ্ঞানশিক্ষার বিষয় নিয়ে তিনি জোরালোভাবে প্রস্তার উত্থাপন করেছিলেন।
১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড কর্তৃক ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ‘আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’। ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজিতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। পরে তিনি ১৮৩০ সালে ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ করে নাম দেন ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’। ১৮৩৩ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রামমোহন প্রথম ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ রচনায় সাধু ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এই সাধু ভাষাকে প্রাঞ্জল, গতিশীল, সুমধুর, ছন্দোময় এবং কিছু নির্দেশনার মাধ্যমে অনায়াসে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন ঈশ^রচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যে কারণে তাঁকে বাংলা সাধু ভাষার জনক বলা হয়। তিনি বাংলা গদ্যেরও জনক। বাংলা ভাষায় চলিত রীতি প্রবর্তন করেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ এই চলিত ভাষাকে বিকশিত করেছেন নানাভাবে। আজকে যারা লেখালেখি করছেন, কেউই আর সাধু ভাষা ব্যবহার করেন না। তবে কিছু আইন-বিধিতে এখনো সাধু ভাষার প্রচলন দেখা যায়।
মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০) সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ সময়ের প্রথম কবি বড়– চ-ীদাস রচনা করেন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউসুফ-জুলেখা’, মুকুন্দরাম ‘চ-ীমঙ্গল কাব্য’ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচনা করেন ‘অন্নদামঙ্গল’। তিনি অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি। চন্দ্রাবতী ছিলেন মধ্যযুগের প্রথম বাঙালি মহিলা কবি। তিনি রচনা করেন মলুয়া (কাব্য),‘দস্যু কেনারামের পালা’ এবং পিতার আদেশে বাংলায় রামায়ন (অসমাপ্ত) রচনা করেন। আব্দুল হাকিম রচনা করেন ‘নূরনামা’ কাব্য। তিনি আরবি ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষার প-িত ছিলেন। তিনি একজন ভালো অনুবাদকও ছিলেন। আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) বাংলা ভাষাকে সম্মানিত করেছেন, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় পাই যখন তিনি বলেন- ‘যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। / সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥/ দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়। / নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥’ (বঙ্গবাণী)।
বাংলা ভাষার মধ্যে এমন এক সম্মোহনী শক্তি রয়েছে, যা পৃথিবীর খুব কম ভাষায়ই আছে। যখন শুনি- ‘মোদের গরব মোদের আশা / আ-মরি বাংলা ভাষা’ তখন আমাদের চিত্ত আন্দোলিত হয়, আমরা দূর স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাবার আনন্দে উদ্বেলিত হই, ভাষা যেন সেই মন্ত্র। এই ভাষাকে একটি বিশেষ জায়গায় তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইউনেস্কোর জরিপ অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাষা হলো বাংলা। ভাষা নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে, সেই পরিবর্তনের মধ্যেও একটি শৃংখলা থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, ‘আমি যে ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়ম রচনা নহে; নিয়ম প্রণয়ন নহে; নিয়ম আবিষ্কার। ভাষার মধ্যে অজ্ঞাত অপরিচিত নিয়ম বর্তমান আছে; সেই নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নিয়ম সকল ভাষাতেই আছে।... কেননা অনিয়ত, শৃঙ্খলারহিত ভাষা চিন্তার অগোচর।... নিয়ম সাহিত্যের ভাষাতেও আছে, লৌকিক ভাষাতেও আছে। কথাবার্তার ভাষা অনেকটা বন্ধন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতই কি তাহা শৃঙ্খলাবর্জিত? অসম্ভব।... কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের রোধ হয় না। ভাষার পক্ষেও সেই একই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তন রোধ করিতে পারেন নাই।’
যে ভাষায় যত বেশি অন্য ভাষার সাহিত্য অনূদিত হয়েছে, সেই ভাষাও তত উন্নত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার এই আধিপত্য এবং পরাক্রমশালী হয়ে ওঠার মূলে অনেক কারণের মধ্যে একটি হলো সারা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় ইংরেজিতে অনুবাদ। ইংরেজিতে অনূদিত না হলে তা বিশ^জগতে পরিচিতি পায় না। আমাদের বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিক-জীবনানন্দ দাশ কিংবা আরো অনেক কবি-সাহিত্যিক অনেক ভালো লিখেও তাঁরা নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি তাঁদের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ না হওয়ার কারণে। বলে রাখা ভালো, কোনোকিছু কেবল ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় অনূদিত হলেই চলবে না, তার ব্যাপক প্রচারও দরকার। আমাদের দেশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, শহীদুল জহির ফিকশনের ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ করেছেন। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী বাংলা কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ পৃথিবীর অন্যতম শেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এর পরে বাংলাদেশে আর এরকম উচ্চমানের উপন্যাস লেখা হয়নি। বাংলা ভাষার এইসব গুণী লেখকদের গল্প-উপন্যাস কিংবা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদের মাধ্যমে সারাবিশে^ ছড়িয়ে দেবার দায়িত্বটি বাংলা একাডেমি নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির কাজ হলো ভালো বেতন/ সম্মানী দিয়ে ভালো অনুবাদকের সাহায্য নেওয়া। এটাও ঠিক যে আমাদের দেশে হাতেগোনা কিছু ভালো মাপের অনুবাদক রয়েছেন।
ইংরেজি, ফরাসি কিংবা স্প্যানিশ ভাষা জানলেই যে সে অনুবাদ করতে পারবেন- তা একেবারেই সত্য নয়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়নে সারা দুনিয়ার সাহিত্যের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকতে হবে আর সেজন্যেই অনুবাদ সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। অনুবাদ, সে আক্ষরিক ((Word for word), ভাবানুবাদ (Idea for idea) কিংবা সৃষ্টিশীল অনুবাদ (Transcreation) যা-ই হোক না কেন, কাজটি খুবই পরিশ্রমের। এর জন্য দরকার অনুবাদকের ভাষাগত প্রস্তুতি, দীর্ঘ অনুশীলন এবং বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ-অলংকার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা। যে লেখকের লেখা অনুবাদ করা হবে, কোনো অনুবাদককে অবশ্যই জানতে হবে, সেই বিদেশি লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তার দর্শন, তার রাজনীতি এবং সেই সাংস্কৃতিক আবহ যার মধ্যে সে হয়ে উঠেছে। পঠন-পাঠনের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশযোগ্য লিটারেরি ল্যাংগুয়েজ।
হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন-
“কোনো ভাষা শুধু মৌলিক সাহিত্যে সমৃদ্ধ হতে পারে না। যে-ভাষা যতো ধনী, তার অনুবাদ সাহিত্যও ততো ধনী। আমাদের ভাষায় যা নেই, তা হয়তো আছে জর্মন ভাষায় বা ফরাসি ভাষায়। তাই আমাদের ভাষাকে আরো ঋদ্ধ করার জন্যে আমরা অপর ভাষা থেকে অনুবাদ করি। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। তাঁরা অনুবাদের আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছিলেন। হিন্দু কবিরা সাধারণত অনুবাদ করেছিলেন তাদের পুরাণ কাহিনীগুলো, মুসলমান কবিরা অনুবাদ করেছেন ফারসি হিন্দি থেকে রোমাঞ্চকর কাহিনী।... মুসলমান স¤্রাটদের উৎসাহে বাংলা ভাষায় মহাভারত রামায়ন অনূদিত হতে পেরেছিল। অনুবাদ সাধারণত করেছেন হিন্দু কবিরা।” ( লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী)।
অনুবাদের মাধ্যমে ভিন্নভাষী লেখকদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হয়, ভাষা ও সংস্কৃতির বিনিময় হয়। কলোম্বিয়ার ঔপন্যাসিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের বিখ্যাত উপন্যাস ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড’ লেখা হয়েছিল স্প্যানিশ ভাষায় এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এই উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন গ্রেগরি রাবাসা এবং ইংরেজি সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এই উপন্যাসের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। অনেকের মতে, উপন্যাসটির স্প্যানিশ ভার্সনের চেয়ে নাকি ইংরেজি ভার্সনই বেশি সুখপাঠ্য হয়েছিল। বলা বাহুল্য ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষার মধ্যে একটি সুসম্পর্ক রয়েছে। ইংরেজিতে অনূদিত না হলে এই বিখ্যাত উপন্যাসটি পৃথিবীর বহুসংখ্যাক মানুষই পাঠের সুযোগ পেতেন না।
২.
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল সা¤্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ১১৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারা রাজত্ব করেছিলন। স¤্রাট পদে আসীন হন গোপাল। মূলত বাংলা ও বিহার অঞ্চল ছিল এই সা¤্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে এই সা¤্রাজ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বাংলার ইতিহাসে এই যুুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। উল্লেখ্য, তাদের সময়ে প্রাচীন বাংলা ভাষার উন্নয়ন ঘটে। চর্চাপদ পালযুগেই রচিত হয়েছিল। শিল্পকলা ও স্থাপত্যে প্রভূত উন্নতি ঘটে পাল শাসন আমলে। পালবংশ ৪০০ বছর শাসন করেছিল। তাদের সা¤্রাজ্য তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অতীশ দীপঙ্কর এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। অনেক মঠ-মন্দির তারা নির্মাণ করেছিলেন। নালন্দা, সোমপুর বিহারের কথা আমরা জানি, যেগুলো পাল আমলের নিদর্শন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরা দ্বাদশ শতাব্দীতে পালদের পরাজিত করে সেনবংশের গোড়াপত্তন করে। সেন আমলে বাংলা ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। এসময়ে বাংলা ভাষার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। নি¤œবর্ণের হিন্দুরা ছিল নানাভাবে অত্যাচারিত। রাজভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সংস্কৃত চর্চা-ই হয়েছে মূলত। সংস্কৃতকে তারা দেবতার ভাষা মনে করতেন। এবং তারা এ-ও ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলা মানুষের ভাষা, এই ভাষায় যারা অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণ শ্রবণ করবে তারা রৌরব নরকে স্থান পাবে। এ সময় অবধি এ ভাষা উচ্চবিত্তের সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠেনি এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখেই এর অস্তিত্ব টিকে ছিল। ১২০৩ সালে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করলে পটভূমি পালটে যায়। অত্যাচারিত নি¤œবর্ণের হিন্দুরা তাদের এই বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছিল এবং তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।
মুসলিম বিজয়ের পর মানুষ এ ভাষার চর্চায় উৎসাহী হয়েছে এবং সে সময়ে আরবি-ফারসি শব্দের আত্তীকরণ বাংলা ভাষাকে বিকশিত করেছে। পরবর্তীতে দীর্ঘ দিনের মুসলমান শাসন আমলে এ ভাষার চর্চা ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। মুসলমান সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এবং বিশেষ করে হোসেন শাহী আমলে এ ভাষার বিকাশ এবং বৈষ্ণব রচনার দ্বারা এর উন্নয়ন একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ বিষয়ে প-িত গবেষক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন-‘হীরা কয়লা খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভেতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিতে থাকে, বাংলা ভাষা তেমন কোন শুভদিন শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে ছিল। মুসলিম বিজয় সেই শুভদিন শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল।’ (বাংলা ভাষার ওপর মুসলমানদের প্রভাব: শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন)।
বৃটিশ বেনিয়ারা উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রারম্ভেই চেষ্টা চালিয়েছে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের সাম্রাজ্য বিস্তারেরও। এ কথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষার, বিশেষ করে আধুনিক বাংলা গদ্যের চর্চা হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, বৃটিশরা নির্মোহভাবে এই বাংলাচর্চার সুযোগ দেয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে সিভিলিয়ানরা এদেশে এসেছিলেন তাদেরকে এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয় শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে তাদের শাসনকার্য চালাতে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। এছাড়া তারা চেয়েছে ভারতীয়দের তাদের নিজের ভাষা শেখাতে। কারণ কোনো জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রথম শর্তই হলো আধিপত্যবাদীর নিজ ভাষারও আধিপত্য বিস্তার এবং বিজিত জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভেতর থেকে ধবংস করে দেওয়া। বৃটিশদের সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শনেরও চালান এসেছে তাদের আগমনের সাথে সাথে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই আমদানী শিল্প-সাহিত্যের আধুনিক দিগ¦লয়ের সাথে আমাদের অন্বিষ্ট করেছে, যদিও তথাকথিত এই আধুনিকতা আমাদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং উপনিবেশবাদীদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়েছিল আমাদের সামাজিক জীবন ও জীবনবোধের সবকিছু- শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা ভাষার আয়োজনও। কলিম খানের মতে, ‘ইউরোপ কেবল ভারতে উপনিবেশই স্থাপন করেনি। ভারতীয়দের জীবনের সর্বত্র তার ভাষায়, আচার ব্যবহারে, মনে, জীবিকায় শিল্পে সাহিত্যে এককথায় সমগ্র জীবনযাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করছিল।’ কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা চলেছে।
বিদ্যাসাগর শেক্সপিয়ার অনুবাদ করেছেন, বঙ্কিম স্কট আত্মস্থ করেছেন, মাইকেল মধুসূধন দত্ত তো একেবারে খ্রিস্টানই সেজে গেলেন একদা এক মোহে এবং নিজ ভাষাকেও অবজ্ঞার দুঃসাহস দেখালেন। বলতে গেলে তাঁর এই মোহ-ই বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে মুক্তি দিয়েছে, বাংলা ভাষারও উৎকর্ষ সাধন করেছে। পাশ্চাত্যের নাটক, কবিতার অভূত গ্রহণ এবং বাংলা কাব্যের তো বটেই, তিনি বিদ্রোহটা দেখিয়েছেন সুদৃঢ়ভাবেই বাংলা ভাষার মন্থর মেজাজের বিরুদ্ধে,অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং প্রথম বাংলা ভাষায় ট্রাজেডি রচয়িতা হিসেবেও তিনি সর্বাগ্রের। বাংলা ভাষার ভা-ারে যে ‘বিবিধ রতন’ রয়েছে তা বুঝতে পেরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় তিনি তাঁর অদম্য সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন। রামমোহনের প্রতিবাদী চরিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে বাংলা গদ্যের যে বিকাশ, তাকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের ইতিহাস হতে পারে না, যদিও তাঁর ভাষা লোকভাষার স্পর্শ পাইনি। রামমোহন বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করেছেন বিপর্যয়ের হাত থেকে। বিদ্যাসাগরের, সংস্কৃত বাদে, (সংস্কৃতের প-িত হয়েও) সাধারণের মুখের ভাষাকে লেখ্য ভাষার রূপ দিয়ে তাকে গদ্যের বাহন করে ভাষার বিকাশকে বাংলা গদ্যের একটি সৌভাগ্যের পর্যায়-ই বলতে হবে। তার হাতে এই ভাষা সাবলীল প্রবাহমানতা অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার মূল ভূমিকে সৌকর্য দান করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে উপযুক্ত জায়গায় পৌছে দিয়েছেন, যেখান থেকে তা ফুলে-ফলে নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, ‘রামমোহন বঙ্গ-সাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তব্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন।’(আধুনিক সাহিত্য: বঙ্কিমচন্দ্র)। আর সেই পলিস্তরেই নানাভাবে ফসল ফলালেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এবং অন্যরা।
ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে তার একটি ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, “কিন্তু অধীনতার ভিতরেও বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছিল, সেটি ছিল স্বাধীনতার জন্য সাধনা।... জয় ছিল বাংলা ভাষার চর্চায়, ইংরেজিকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে ব্যবহার করে। ভিক্ষুকের মতো নয়, প্রভুর মতো। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম- এঁরা কেউ ইংরেজি কম জানতেন না এঁরা ইংরেজিতে লিখেছেনও, পরে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার পেলেন সেও তো তাঁর নিজের করা বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের জন্যই,...। তাঁদের কা-জ্ঞান ছিল, আর ছিল দেশপ্রেম, যে জন্য তাঁরা বাংলার পথে এসেছেন, জেনেছেন সেইখানেই সিদ্ধি, ওই পথেই মুক্তি- যেমন তাঁদের সৃষ্টিশীলতার তেমনি তাঁদের দেশবাসীর (ভাষা ও স্বাধীনতা)।”
কলিম খানের মতে, “উপনিবেশের ফলে ‘বাংলা ভাষা বাস্তবিকভাবে তার সাম্রাজ্য হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় পরিণত হয়।” বাংলা ভাষা প্রাকৃতজনের মুখে মুখে বেঁচে থেকেছে অনেক কাল এবং বিকশিত হয়েছে, এ ভাষার প্রবাহমানতা কখনো রুদ্ধ করতে পারেনি কেউ। বাংলা ভাষা ঔপনিবেশিক সময়েও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল এবং তার আধুনিক হয়ে ওঠায় উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ের চিন্তকরা যে হারানোর কথা ভাবছেন, তা আসলে একধরনের পাওয়াও বটে। তবে পাশাপাশি একথা মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা নেই যে, উপনিবেশ বাংলা ভাষাকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে অনেকখানিই বাধাগ্রস্ত করেছে, তার ব্রাত্যবিকাশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগোতে দেয়নি। বিচিত্র প্রতিবন্ধকতায় বাংলা ভাষার ডানায় আরো শক্তি এসেছে এবং ভাষার কারণেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। একটি ভাষাভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। স্বাধীনতা অর্থবহ হলে, গণতন্ত্রের কাঠামো সুদৃঢ় হলে ভাষাও স্বাধীন হবে, আরো বিকশিত হবে। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বাধীনভাবে চলতে হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আনতে হবে গণতন্ত্র চর্চার ব্যাপকতা। আর ভাষা যে সমষ্টিনির্ভর, জ্যাক দেরিদার এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। (আগামী সংখ্যায় পড়ুন)
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-
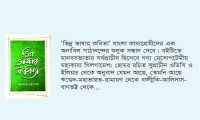
আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-
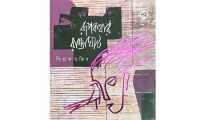
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও
-
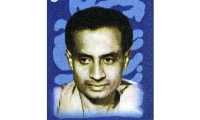
বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ বিষয়ভাবনা