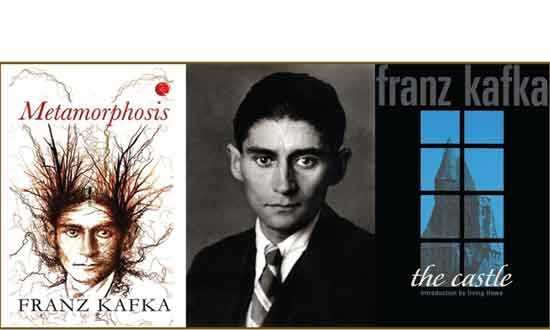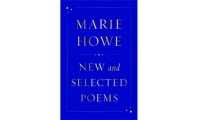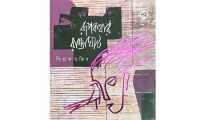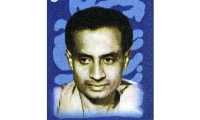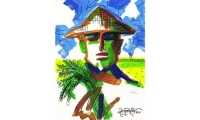সাময়িকী
কাফকাকে পড়া, কাফকাকে পড়ানো
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
ফ্রান্স কাফকা / জন্ম: ০৩ জুলাই ১৮৮৩; মৃত্যু: ০৩ জুন ১৯২৪
এক কাফকা-আলোচক, জশুয়া কোহেন, তাঁর “কাফকাকে পড়ার আনন্দ ও শাস্তি” প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছেন, “কাফকাকে নিয়ে কিছু লেখা আর চীনের প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে এটি সম্বন্ধে কিছু বলার মধ্যে পার্থক্য নেই। সত্য মেনে নিয়ে যা করা যায়, শুধু দেয়ালটির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখানো যায়।” এই সংকট আরেকটু গভীর হয় কাফকাকে পড়াতে গেলে। তখন চীনের দেয়ালটা অদৃশ্য হয়ে যায়, তার জায়গায় দৃশ্যমান হতে থাকে কাফকার ক্যাসলটি, যাকে বাংলায় আমরা দুর্গ বলতে পারি, যদিও ওই নামের উপন্যাসে সেই দুর্গ ঠিক দুর্গ নয়- বস্তুত দুর্গের স্থাপত্যে একে ফেলা যায় না, কেননা, দ্য ক্যাস্ল-এর (জার্মান ভাষায় ডাস শ্লস্) এক ইংরেজি অনুবাদক এন্থিয়া বেল আমাদের জানান- এবং উপন্যাসের মনোযোগী পাঠক মাত্রই একমত হবেন- “এই ক্যাস্ল আসলে অনেকগুলি দালানের সমষ্টি, যেগুলির মাত্র কয়েকটি দু’তলা, কিন্তু বেশি ভাগই আরো নিচু আর ঘনবদ্ধ। আপনি যদি না জানতেন যে এই সমষ্টির নামই ক্যাসল, তাহলে আপনি ধরে নিতেন, এটি আসলে ছোট একটি শহর।” কাফকাকে পড়াতে গেলে পাঠের আনন্দ ও শাস্তির সঙ্গে যোগ হয় তাকে কতটা বোঝা গেল না গেল, সেই অনিশ্চয়তা অথবা অতৃপ্তি। তাঁকে পড়ানোর আনন্দ-বেদনা-অনিশ্চয়তার সঙ্গে বিস্তর মিল আছে কধভশধবংয়ঁব বা কাফকিও রহস্য-ভীতি-হতাশা আর অনিশ্চয়তাবোধের, যার অবস্থান কাফকার দর্শনের গভীরে। তাঁর গল্প বা উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের দিকে তাকালে চোখে পড়বে, তাদের অনেকেরই বাস যেন সেই দুর্গ তথা ঘনবদ্ধ শহরের অলিগলিতে, যেগুলোর শুরু বা শেষ নেই, পৌঁছে দেয়ার মতো কোনো গন্তব্যও যাদের নেই। এগুলির একটিতে পা দিয়ে কিছুটা পথ গেলেই ঘরের ঠিকানা মানুষ ভুলে যায়, অথচ সবসময় তার মনে এমন এক অলীক ধারণা জন্মাতে থাকে যে, যেন চাইলেই ঠিকানা হারানো সেই ঘরে পৌঁছানো যায়। গলির জীবন বাস্তব, তাতে আহার-নিদ্রা-যৌনতা আর জীবনযাপনের সব কৃত্য-অনুষঙ্গই বর্তমান, শুধু সেই জীবনটা প্রকৃত অর্থে কখনো যাপন করা হয় না, কারণ সেই প্রকৃত একসময় নানান রহস্য, ভীতি আর প্রতিকারহীন উদ্বেগে অপ্রকৃত হয়ে যায়। একটা গলি যদি গোলকধাঁধার চরিত্র নিয়ে তাতে পা-রাখা মানুষটাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, তাহলে স্বাভাবিকতার সংজ্ঞাই তো পাল্টে যায়। প্রকৃত বলতে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর এক নির্মাণকে আমরা শুধু প্রত্যক্ষণ আর ইন্দ্রিয়ের হিসেবে ফেলেই মাপি, অথচ ইন্দ্রিয়গুলিতে যখন জট লাগে, প্রত্যক্ষণ অস্পষ্ট করে একটা ঘোলাটে জগৎ বাস্তবকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকে, যখন একজন অভিযুক্ত কেউ তার কাজে, কথায় ও আচরণে নিজেকে অভিযোগের যোগ্য করে তুলতে থাকে, যখন এক পরিবার-অন্ত তরুণের মনুষ্য চেহারাটা একটা পোকার রূপ নিয়ে তার পরিবার আর অফিস-কর্তাকে ধোঁকা দিতে থাকে, তখন প্রকৃত বলতে যা থাকে, তা হয়ে দাঁড়ায় এক নিখাদ কাফকাত্ব, যা কাফকা নিজেও যে বুঝে উঠতে পেরেছিলেন, তা নয়। তিনি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন কিনা, সেই খবর আমরা জানি না। তাঁর গল্প-উপন্যাসে উত্থাপিত কিছু জটিল প্রশ্নের সমাধান খোঁজার পরিবর্তে তিনি তা ক্রমাগত মুলতবি করে গেছেন। শেষ পৃষ্ঠায় এসেও এই প্রশ্নগুলি একদিকে উত্তর খোঁজার কিছু সম্ভাবনা মাত্র রেখে যায়, যদিও এই ঘোষণাও একই সঙ্গে তারা দিতে থাকে- উত্তর খুঁজে লাভ নেই, প্রশ্নটাই বরং বোঝার চেষ্টা করুন। সমাধান নাস্তি।
কাফকাকে পড়াতে গেলে এই প্রশ্নগুলির একটা সমাধান যখন শিক্ষার্থীরা চায়, এবং এর উত্তরে যখন শোনে, প্রশ্নটা যেন ঠিক কি, অথবা, প্রশ্নটা আবার একটু করে দেখা যাক, তখন তাদের হতাশ হওয়ারই কথা। তবে কাফকাকে পড়ানোর একটা আনন্দ, হতাশা ছাপিয়ে প্রশ্নগুলিকে বোঝার এবং নিজের মতো করে সেগুলিকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টাটা যখন তাদের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, তখন কাফকাত্বের ভারটা অনেকটাই সহনীয় হয়ে ওঠে। সোজা উত্তরের চাইতে এই ঘুরানো পথে পাওয়া উত্তর, অন্তত কাফকার ক্ষেত্রে, অনেক বেশি ফলদায়ক।
একটু আগে কাফকা-দর্শন বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আসলে কাফকা-পাঠজনিত একটি অভিজ্ঞান, যা এই ক্রমশ ক্রূর আর মূঢ় হতে থাকা পৃথিবীর ছোট-বড় সব সমাজের, সংগঠনের আর প্রতিষ্ঠানের শক্তিকে বুঝতে অনেকটাই সাহায্য করে। এটি কাফকাকে পড়ানোর একটা ছোটখাটো তৃপ্তিও বটে- ছোটখাটো, যেহেতু এই অভিজ্ঞান যে ছবিটা আমাদের সামনে তুলে ধরে, তা কুড়ি শতকের বিখ্যাত আইরিশ-ইংরেজ শিল্পী ফ্রান্সিস বেকনের ছবিগুলির মতোই মোটেও স্বস্তিকর নয়। কাফকার মতো খুব কম লেখকই আছেন, যাঁদের নামের সঙ্গে তাঁদের গল্প-উপন্যাস বা কবিতায় বর্ণিত জগৎ এমন এক অদ্ভুত সমীকরণের গাঁটছড়াতে আটকা পড়ে যায় যে, ওই জগতের প্রকৃত-অপ্রকৃত, শারীরিক-মনস্তাত্ত্বিক, সমকালীন-চিরকালীন দ্বন্দ্বগুলি আমাদের চেতনাকে অধিকার করে রাখে। আর এই অধিকার করে রাখার পেছনে থাকে আমাদের সামষ্টিক স্মৃতিতে জমা আতঙ্ক আর উদ্বেগের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতি আর সমরনীতি, বর্ণবাদ আর ধর্মীয় উন্মাদনার দূষণ, বৈষম্য আর বঞ্চনা, কায়াহীন অথচ নির্মম আমলাতন্দ্র এবং পুরুষতন্ত্রের শাসন আর সহিংসতা যা এর প্রধান অস্ত্র। এসবের যোগফল যে আতংক, অনিশ্চয়তা আর অবসাদের জন্ম দেয়, তা যদি মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানুষের করার কী থাকে?
কাফকা কঠিন বটে, কিন্তু সেই কঠিনেরে ভালোবেসেছি বিশ^বিদ্যালয় জীবনে তাঁকে প্রথম পড়ার পর থেকেই। উনিশ শ’ ষাটের সেই আশ্চর্য দশকে জগৎটা আমাদের সামনে তাঁর চিন্তার সক্রিয়তার পথগুলি খুলে দিয়েছিল। আমরা প্রতিদিন মার্ক্সের সঙ্গে তর্কে জড়াতাম, জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আলাপ করতাম, ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী মার্কিন তরুণদের মিছিলে যোগ দিতাম, বিট কবি আর বিটল্স্-এর সামনে বসে তাদের দুনিয়া কাঁপানো কবিতা পড়তাম/গান শুনতাম। আমাদের মার্ক্স আর সার্ত্র পড়া ছিল খুবই অপ্রতুল, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রাজপথে ভাঙ্গা সাইকেল নিয়েই নেমে পড়তে কুণ্ঠাবোধ করতাম না। তাতে কিছুটা পথ তো অন্তত পাড়ি দেয়া গেছে। সেই পথের মোড়ে মোড়ে দেখা পেয়েছি নিৎশে-হেগেল-হাইডেগারকে, ব্রেখট-ক্যামু-ভার্জিনিয়া উলফ আর জেডি সেলিঙ্গারকে। শিক্ষক হওয়ার পর এঁদের এক দলকে পড়িয়েছি, অন্য দলের দর্শন-চিন্তাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছি। এঁদের অনেকের দর্শন এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, যদিও এঁরা সবাই সেই বুঝে ওঠার একটা আমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কাফকা যেন সেই আমন্ত্রণটা ক্রমাগত মুলতবি করে রাখেন। ভাবটা এমন, বুঝতে চাইলে বোঝো, তবে এখনই না। আরো ক’টা দিন যাক। তোমার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাতে আরো কিছু সামান জমুক।
কাফকার মতো অতটা কঠিন না হলেও নানা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন আলবেয়ার ক্যামু আর মিলান কুন্ডেরা, টি এস এলিয়ট (বিশেষ করে তাঁর ফোর কোয়ার্টেটস-এ) এবং সাম্যুয়েল বেকেট। কিন্তু এলিয়টের পড়ো জমিতে- যাতে পাঠক তার ভ্রমণ শেষে হিমালয়ের নিচে এসে বৃষ্টির দেখা পায়- কাফকার সেই অনিশ্চিতির ভীতি নেই, কুন্ডেরার পৃথিবীর পালানোর পথগুলি সব রুদ্ধ অথবা অদৃশ্য হয়ে যায় না, বেকেটের গডোকে বুঝতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় না, এবং ক্যামুর অন্ধকার অস্তিত্ববাদও একসময় ব্যক্তির মুক্তিকে অসম্ভব করে তোলে না (তাঁর দ্য আউটসাইডার/স্ট্রেঞ্জার উপন্যাসের মিয়েরসো যখন ফাঁসির মঞ্চকে বেছে নেয়, যেহেতু সে সত্যকে তার মতো করে আঁকড়ে ধরেছে, তার মুক্তি ঘটে প্রদোষের আলোয় আলোয়)। সেই তুলনায় দ্য ট্রায়াল এবং দ্য ক্যাস্ল-এর জোসেফ কে এবং মি: কে অথবা “দ্য মেটামরফসিস” গল্পের গ্রেগর সামসার কোনো মুক্তি নেই, তাদের পথগুলিও অনির্দিষ্ট (এবং শঙ্কার বিষয় হলো, এই পথগুলিতে হরহামেশা আমরাও চলছি, অথবা ধরে নিচ্ছি আমরা চলছি) তাদের গন্তব্য ক্রমাগত দূরে হারিয়ে যেতে থাকে, এবং তাদের পৃথিবী মোড়ানো থাকে এক পরিত্রাণহীন কুয়াশায়, যা ভেদ করে বাস্তবের একটা বিভ্রম উঁকি দেয় বটে- যে বাস্তবে মানুষ খায়দায়, ঘুমায়, কাজ-উপার্জন করে, শরীরের নানা ক্ষুধা মেটায়- কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমাট বাঁধা কুয়াশাটা আর কাটে না।
দ্য ট্রায়াল গল্পে এক সুন্দর সকালে জোসেফ কে-কে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো, কোনো এক অপরাধে, যা তাকে গ্রেপ্তার করতে আসা দুই লোক জানালো না- তারা নিজেরাও জানে কিনা বোঝা গেল না- এবং যা জানার চেষ্টাতেই কে’র এই পৃথিবীতে বাকি ক’টা দিন কেটে গেল। যে মামলাটার কথা উপন্যাসের শিরোনাম ঘোষণা দেয়, সেই মামলাও চলল একটা না-মামলার মতো। এবং অবাক কা-, এই মামলায় তার যে দ- হলো, যা মৃত্যুদ- বটে, কিন্তু মৃত্যুদ- থেকেও যা আরো ভীতিকর, তার শেষ রায়টা সে বিচারকের মুখ থেকে নয়, তার আগে এক পুরোহিতের কাছ থেকেই শুনে নিল। কে’র সমস্যা হলো, একে তো সে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটাই ঠিক কী, তা জানে না, বরং আইন এ ব্যাপারে কী বলে তাও কিছুতেই পরিষ্কার নয়। আর মামলার নিয়মগুলিও ক্রমাগত বদলায়। এজন্য আইনকে সে বিশ^াস করে না, আদালতকে না, কোনো প্রতিষ্ঠানকে না, পুরোহিতের গীর্জাকেও না। পুরোহিতের সঙ্গে সে যখন আলাপ করে, কোনো সিদ্ধান্তে আসার জন্য নয়, বরং এরকম আলাপকে যেহেতু মানুষ গুরুত্ব দেয়, সে জন্য, পুরোহিত তাকে বলে, “তুমি এ সত্যটা বুঝতে পারছ না, রায়টা হঠাৎ করে আসে না, মামলা চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা রায় তৈরি হয়ে যায়।” কিন্তু কে’র সমস্যা তো এই ‘সত্য’ নিয়ে। এই সত্য তো কোনো প্রতিষ্ঠানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরোহিত তাকে আবার বলেন, “না, সবকিছুকে সত্য বলে তোমোকে ধরে নিতে হবে না, তুমি বরং সত্যকে একটা প্রয়োজনীয়তা হিসেবে ধরে নিতে পারো।” কে’র মনে পুরোহিতের কথাটা বিষাদ ছড়ায়। হ্যাঁ, সে বলে “এই মিথ্যাটাকে দুনিয়ার নিয়মে পরিণত করা হয়েছে।”
সত্য-মিথ্যার ফারাক যখন মসলিনের কাপড় থেকেও চিকন, সত্যই যে এক বিরাট মিথ্যা না, তার প্রমাণটা কোথায়? সত্য বলে যে মিথ্যাটাকে- যাকে প্রয়োজনীতার মোড়কে বৈধতা দেয়া হয়েছে- দুনিয়ার আইনে পরিণত করা হয়েছে, তা আমাদের যে কোনো আদালতের বারান্দায় একবেলা ঘুরে এলে মানুষের একিন হবে। কাফকা এই কঠিনের শিক্ষাটা আমাকে দিয়েছিলেন বলে আমিও কোনো প্রতিষ্ঠানে সত্য খুঁজি না। আমলাতন্ত্র যে মিথ্যাকে আইনি সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে দুনিয়া চালাচ্ছে, সেই মিথ্যাকে আদালতের চত্বরে বসানো ভাস্কর্যে উদযাপিত বিচার দেবির ভুল নিক্তিতে প্রতিদিন তুলে দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের কথা, মিডিয়ার কথা, একাডেমিয়ার কথা বাদ দিন, পরিবারের ভেতর এই সত্য-মিথ্যার হাঁসজারু প্রতিদিন যে অলীক ডিম পাড়ে, তা হন্যে হয়ে সবাই খুঁজতে লেগে যায়।
এক শিক্ষার্থী একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, সত্যটা তাহলে কী? আমি তাকে আরেক ফ্রান্সিস বেকনের কাছে যেতে বললাম, যিনি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ছিলেন ইংলন্ডের বরেণ্য দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মননশীল লেখক, এবং তাঁর রচনাবলি থেকে “অফ ট্রুথ” রচনাটি পড়তে বললাম। রচনাটি বেকন এইভাবে শুরু করেছেন, সত্য কী? গলায় ঠাট্টা মিশিয়ে হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে উঠে গেলেন। হাকিম প্রশ্নটা করলেন বটে, কিন্তু তিনিও কাফকার মতোই জানতেন, এই সত্য খোঁজা আর খড়ের গাদায় হারানো সুঁই খোঁজা একই জিনিস, যেহেতু এটি এক অদৃশ্য, কল্পিত প্রপঞ্চ। যদি সেটি বাস্তবে থাকত, তার প্রভাবটা ব্যক্তিতে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে পড়ত। তা কি আদৌ পড়েছে, কোনোকালে? দ্য ট্রায়াল যতটা দুর্ভেদ্য এক পৃথিবীর ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যায়, এবং আমরা এই গোলকধাঁধার চক্রে প্রায় দিশেহারা কে’র সঙ্গী হই, আমরা টের পাই, তার এই জীবনে কোনো সুবিচার সে পাবে না, ‘সু’ জিনিসটাই তো থাকে ক্রমাগত ঠাট্টা করতে থাকে, বিচার তো আরেক পাকচক্র। উপন্যাসজুড়ে কে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখায়, উদ্ধত আচরণও করে, যৌনতায় স্বস্তি খোঁজে, কিন্তু কোনো পথের দিশা পায় না। তার এই চক্রবৃদ্ধিতে ক্রমশ অসম্ভব হতে থাকা কোনো সমাধান-আশা শেষ হোঁচটটা খায় তার জন্মদিনে, যা তার মৃত্যুদিনও। সেই দিন সন্ধ্যায় দুই মৃত্যুদ- বহালকারী লোক তাকে ধরে নিয়ে যায় এক কোয়ারিতে যেখানে তাকে মারা হবে। চাঁদের আলোয় কে হাঁটে, এবং উদ্ভট এক জগতে তার জন্মদিন-মৃত্যুদিনের জটপাকানো নির্মমতায় আহত হতে হতে নিহত হবার পথে এগোয়। উপন্যাসের এই শেষ অধ্যায়টি খুবই সংক্ষিপ্ত, তার জীবনে ইতিটানা ৩১তম জন্মদিনটাকে করুণাহীন করে তোলার জন্য হয়তো, অথবা এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টিতেই যে আছে একটা উপন্যাসের ব্যাপ্তি, যেমন কোনো হাতের অর্ধেক সমান কোনো বনসাই বৃক্ষে যেমন থাকে আস্ত এক বটগাছ, তা বোঝাবার জন্য, কে জানে, কিন্তু এই অধ্যায়ের শেষে এসে কে’র মনে হলো, “যেন কোনো সারমেয়র” মতো তার জীবন, অথবা মরণ, অথবা উভয়ই। সে দেখতে পাচ্ছে, তার দুই আইনি খুনি আজ সন্ধ্যায় কোনো অপেরায় যাওয়ার জন্য সেজেছে, মাথায় তাই টপ হ্যাট পরেছে আর তাদের ব্যবহারেও আছে প্রচুর সৌজন্য। কিন্তু তাতে কী? কুত্তার মতো যে মরে, তার লজ্জাটা তো তার জীবন ছাপিয়ে দীর্ঘদিন থেকে যায়।
দ্য ট্রায়াল-এর শেষ অধ্যায়টা এখনও আমাকে অনেক ভাবনার, অনেক প্রশ্নের সামনে নিয়ে যায়। কে’র মৃত্যুর জন্য কাফকা তার জন্মদিন কেন বেছে নিলেন, তার দুই ঘাতককে কেন অপেরা দর্শকের সাজ পরালেন। জীবনটা কি তাহলে একটা অপেরা, সংক্ষিপ্ত, এক সন্ধ্যাতে শেষ হওয়া গীতি-নাটক? দুই ঘাতক আসলে কে? আমি বুঝতে পারি, কাফকা তাঁর সব লেখায় অনেক প্রশ্ন তোলার জায়গা রেখে যান। নিজে অনেক প্রশ্ন তোলেন, অনেক প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন অথবা উহ্য রাখেন, অনেক প্রশ্ন যেন পাঠক তোলেন, সেই আশা করেন। না, পাঠকের কথাটা হয়তো ভুল বলা হলো, যেহেতু তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাক্স ব্রডকে তাঁর সব পা-ুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন। তাহলে তিনিই কি সেই পাঠক ছিলেন (প্রত্যেক লেখক তাঁর প্রথম পাঠকও বটে), যিনি বুঝেছিলেন, অকারণ প্রশ্নের ভার কেন বইবে পাঠক তাঁহার? কিন্তু আমার এক শিক্ষার্থী পাঠক একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, জোসেফ কে কুকুরের মতো মৃত্যুকে যে লজ্জা বলে ধরে নিল, তাতে কি প্রমাণ হলো না, ওই লোক কুকুরকে ইতর ভাবে? কেন ভাবে? কুকুর মানুষ থেকেও বিশ^স্ত, বন্ধুসুলভ, উপকারী। বরং সে যদি বলত, কুকুরের মতো, এই গৌরব আমার মৃত্যুকে ছাপিয়ে যাক, তা কি ভালো হত না? আর শেষ যখন এই উপন্যাসটি পড়াই, মিলেনিয়াল প্রজন্মের কাছে প্রকৃতিচিন্তাটি যখন গুরুত্ব পাচ্ছে, সাহিত্যতত্ত্বের বাজারে ইকোক্রিটিসিজম ঢুকে পড়েছে, এক শিক্ষার্থী আমাকে প্রশ্ন করল, জোসেফ কে’র ঘাতকরা ওকে কেন এক স্টোন কোয়ারিতে নিয়ে গেল? তা কি এই কোয়ারির একটা প্রতীকী রূপের কারণে? কোয়ারি, আমরা জানি এমন এক এলাকা যাতে খোঁড়াখুঁড়ি করে মাটির ভেতর থেকে পাথর ইত্যাদি তোলা হয়। এজন্য ডায়নামাইটও ব্যবহার করা হয়। আমাদের এই সময়ে প্রকৃতি ধ্বংসের জন্য এক্সট্র্যাকশন মাইনিং কে দায়ী করা হচ্ছে। কাফকাও কি বুঝেছিলেন, কে’র প্রতি প্রতিষ্ঠানের, রাষ্ট্রের, আমলাতন্ত্রের নির্মমতার একটা চমৎকার সাযুজ্য হতে পারে এই বোয়ারিতে তাকে ছুরি মেরে খুন করার ঘটনাটি?
আরেক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ছিল এই- জোসেফ কে একসময় ক্ষিপ্ত হয়ে ভেবেছে, কুড়িটি হাতে সে জগতের সঙ্গে লড়বে। তাকে যখন দুই ঘাতক বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে, একটা পুলের উপর দিয়ে তাদের যেতে হয়। ‘কে’ ভেবেছে, দু’দিকে তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকা একজনের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে সে নিজের বুকে বিঁধিয়ে দেবে। কেন সে একথা ভাবল? সে তো পারত ছুরিটা নিয়ে একজন, এমনকি দু’জনের বুকে বিঁধিয়ে মিথ্যা মামলা, মিথ্যা রায়কে ভুল প্রমাণ করে অন্তত কিছুদিন মুক্ত বাতাসে নিঃশ^াস নিতে? সে কেন আত্মহত্যার বিরুদ্ধে এত যুক্তি দেখাবে, তার বিশ হাতের লড়াইয়ের ক্রোধটাইবা কোথায় গেল? সে কি তাহলে জানে, তাকে আটকের কারণটা আসলে কী? সেখানে কি সে ধরা খেয়ে গেল?
কাফকা না পড়ে তো আর কাফকা পড়ানো যায় না, কিন্তু যতবার কাফকা পড়েছি, ততবার কাফকা পড়ানোর কষ্ট কমেছে আমার। আমিও, কাফকার মতোই, শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তুলতে উৎসাহ দেই। একসময় দেখতে পাই, অনেক উত্তর তারা নিজেরাই দিচ্ছে। অথবা আমার শর্তযুক্ত উত্তর মেনে নিজেদের মতো উত্তরও খুঁজছে। শর্তটা থাকে এই, আমি সম্ভাব্য একটা উত্তর দিচ্ছি। এর মতো দশটা উত্তর থাকতে পারে। অথবা আরো বেশি। তাদের খুঁজে নিতে হবে। না নিলেও আপত্তি নেই। উত্তরগুলি যেহেতু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না, সিদ্ধান্তকে মুলতবী করে দেয় মাত্র। (আগামী সংখ্যায় পড়ুন)
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-
সাময়িকী কবিতা
-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন
-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-
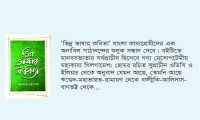
আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য