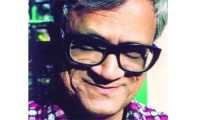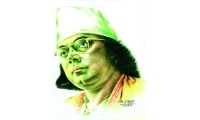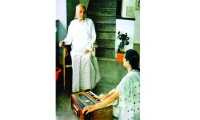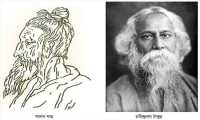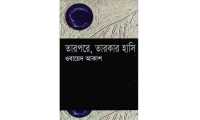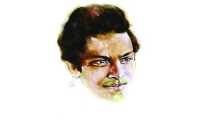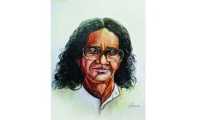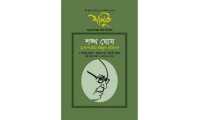literature » samoeky
ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী ১২
লোরকার দেশে
চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ
(পূর্ব প্রকাশের পর)
গ্রানাদায় বেড়ানোর সময় নাতাশা বলেছিল, সাগর দেখব। তখন যে শহরটির কথা মনে পড়ল তা পাশের মালাগা। সে শহরেই এখন আসলাম সাগর দেখতে দেখতে, আর সাগর পাড়ি দিতে দিতে মেলিইয়া থেকে মালাগা। দুটি শহর ভূমধ্যসাগরের দুই পারে। একটি আফ্রিকায়, অপরটি ইউরোপে। তবে দুটিই স্পেনে।
মালাগা‘কোস্টা দে সল’অঞ্চলটির রাজধানী, আর তার সবচেয়ে বড় শহর-বন্দর।
মালাগার পাবলো পিকাসো বিমান বন্দর থেকে শহরে হোটেলে পৌঁছতে আধা ঘণ্টা সময় লেগে গেল, যদিও দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার।
হোটেলটি শহরের এক ব্যস্ত এলাকা কায়ে আলামোছ-এ। নাবিল ও নাতাশা পরিবেশটি পছন্দ করল না। বলল, আমরা এখানে থাকতে চাই না। সাগরের পাড়ে সৈকতের এক হোটেলে থাকব। বললাম, অবশ্যই থাকবে। তবে আজকে নয়, কাল। আজ এখানে থাকি, হোটেলের কাছাকাছি যা দেখার আছে তা দেখে নিই। সৈকতের হোটেলগুলি একটু দূরে, তাই কাল যাব। এ হলো টাইম ম্যানজমেন্ট। তারা দুজনে সানন্দে রাজি হয়ে গেল।
হোটেলে চেক ইন করে আমরা বরাবর ঘুরতে বের হই- এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। মোড়ের এক তাপাস বারে হালকা কিছু খেয়ে গেলাম একটু হাঁটতে, কাছাকাছি-‘প্লাছা দে লা মেরছেদ’- শহরের প্রধান প্লাজা। নীল কৃষ্ণচূড়ার সারির নিচে অনেকগুলি বেঞ্চিতে বসে কেউ বিশ্রাম নিচ্ছেন, কেউ খাচ্ছেন, কেউ পড়ছেন। একটি বেঞ্চি একটু আলাদা মনে হলো। সাদা মার্বেলের। তার ওপর একজন বসে আছেন একাকী। কবিগুরুর ভাষায়, ‘দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে’। কাছে যেতেই দেখলাম আর কেউ নন, স্বয়ং পাবলো পিকাসো বসে আছেন পায়ের উপর পা তুলে। বাম হাতে একটি খাতা। ডান হাতে পেন্সিল। তাঁকে নাবিল ও নাতাশা ‘হাই’ বলে অভিবাদন করল। বেঞ্চিতে তাঁর পাশে বসে ছবি তুলল। পাবলো পিকাসোর পূর্ণাঙ্গ আকারের এ ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য স্মরণ করিয়ে দিল মালাগা হচ্ছে তাঁর জন্মভূমি। নাতাশা বলল, এখানে অবশ্যই পাবলো পিকাসোর জন্মভিটা থাকবে, যা হবে এক মিউজিয়ম। নাবিল যোগ করল- কাছাকাছি কোথায়ও থাকবে পাবলো পিকাসোর নামে পার্ক, সাথে মনুমেন্ট। তারা হয়তো গ্রানাদায় তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকেই তা বলছে।
নাবিল ও নাতাশার অনুমান পুরোপরি ঠিক। পাশেই পিকাসো বাগিচা-‘হার্দিনে দে পিকাসো’- এ শিল্পীর স্মরণে নির্মিত এক সবুজ চত্বর। এর মাঝে থেমে আছে শহরের সব কোলাহল। দেখলাম এক ¯িœগ্ধ সবুজ, অনুভব করলাম এক নিবিড় শ্রদ্ধা। একটু হেঁটে সবাই গেলাম অনুপম এক ভাস্কর্যের সামনে। পাবলো পিকাসোকে নিবেদিত ভাস্কর মিগেল অরতিজ-এর শিল্পকর্ম। এখানেও ছবি তুলতে নাবিল-নাতাশার আপত্তি থাকল না। নাবিল বলল, মালাগা হচ্ছে পিকাসোর শহর, যে রকম গ্রানাদা হচ্ছে লোরকার।
কাছের এক বাড়ী, ঠিকানা: ১৫ প্লাছা দে লা মেরছেদ-এ জন্ম নিয়েছিলেন পাবলো পিকাসো। তা এখন এক যাদুঘর-‘কাসা নেতাল দে পিকাসো’। এখনো তা খোলা আছে, তাই টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম সবাই।
তিন তলা দালানের প্রথম তলায় বাস করেছেন হোসে রুইস ব্লাসকো ও মারিয়া পিকাসো লোপেজ ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। এখানেই ২৫ শে অক্টোবর ১৮৮১ সালে জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র ছেলে পাবলো রুইস পিকাসো; পিকাসো পদবিটি তাঁর মায়ের কাছ নেয়া। পাবলো পিকাসোর ‘পিকাসো’, আর ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার ‘লোরকা’- দুটিই মায়ের পদবী। এ দুজন নিজেদের খ্যাতির সাথে সাথে মায়ের নামকেও সারা বিশ্বে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন।
‘কাসা নেতাল দে পিকাসো’ এসে আমরা দেখলাম সে স্থানটি, যেখানে বিশ্বখ্যাত শিল্পীর জন্ম, শিশুকালে হাঁটা, বেড়ে ওঠা।আরো অনেক কিছু দেখলাম- পিকাসো ও তাঁর পরিবারের।
চিত্রশিল্পী বাবা চাইলেন পিকাসোকে তাঁর মতো করে গড়ে তুলবেন। তাই ছেলেকে রঙ-তুলি-ক্যানভাসে শেখাতে লাগলেন চিত্রকর্ম। আর পরিচিত করালেন আন্দালুসিয়ার ঐতিহ্যের সাথে। শিশু পিকাসোকে নিয়ে দেখতে যেতেন ষাঁড়ের লড়াই। চিত্রকর্ম ও ষাঁড়ের লড়াই- এ দুয়ের কি তড়িৎ প্রভাব! পিকাসো আঁকলেন তাঁর প্রথম চিত্র ‘করিদা’ বা ‘ষাঁড়ের লড়াই’। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক বুল ফাইটার প্রবেশ করছে লড়াইয়ের রিং-এ। শুরু হবে ষাঁড়ের সাথে লড়াই। দর্শকরা তাকিয়ে আছে উৎসাহ ও উত্তেজনায়। শিশু পিকাসো রঙ ও রেখায় তা করে তুললো জীবন্ত। এ চিত্র আঁকার সময় পাবলো পিকাসো ভাল করে কথা বলতেও শেখেনি। কারণ তখন তার বয়স মাত্র ৮ বছর। সে ছিল ১৮৮৯ সাল। পিকাসো ঠিকই বলেছেন: ‘প্রত্যেক শিশুর মাঝে রয়েছে এক শিল্পী।’
‘কাসা নেতাল দে পিকাসো’ শুধু পিকাসো ও তাঁর পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন নয়। এখানে রয়েছে দু’শয়ের মতো শিল্পীর সাতশ’র বেশি চিত্রকর্ম; পাবলো পিকাসোর বিভিন্ন সময়ের আঁকা ছবি তো আছেই। জন্মভিটা থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে রয়েছে তাঁর চিত্রকর্মের আলাদা সংগ্রহশালা-‘মুজেও পিকাসো।
পিকাসো’র শহরে এসে ‘মুজেও পিকাসো’তে যাওয়া হবে না, তা ভাবাই যায় না। অবশ্য এর মধ্যে আমরা তাঁর অনেক চিত্রকর্ম দেখেছি তাঁর জন্মভিটার যাদুঘরে। তবে পিকাসোর ছবির যেন শেষ নেই, তাই আমাদের দেখারও বিরাম নেই। একজন বলল, পিকাসোর ছবির আরো বড় সংগ্রহশালা হচ্ছে বার্সেলোনার পিকাসো মিউজিয়ম। তা পরে ভাবা যাবে, এখন ঘুরে দেখা যাক কাছের মিউজিয়মটি।
পরিবারের দান করা পিকাসোর ২৮৫টি চিত্রকর্ম দিয়ে মুজেও পিকাসো নির্মিত হয় ঐতিহাসিক ভবন বুয়েনাভিস্তা প্রাসাদে- যা ষোড়শ শতাব্দীর এক মনোরম আন্দালুসীয় স্থাপত্য। এ প্রাসাদের বেসমেন্টে রয়েছে মালাগার ইতিহাসের বিভিন্ন প্রতœতাত্ত্বিক নিদর্শন, আর ওপরের দুটি তলায় রয়েছে পাবলো পিকাসোর চিত্রকর্ম।
নাবিল, নাতাশা ও ফারজানা- কেউ ইতিহাস দেখতে গেল না। ইতিহাসের জন্য তাদের সময় নেই, হয়তো কিছুটা আছে বর্তমানের জন্য। তারা চলে গেল চিত্রকর্মের গ্যালারিতে। আমি একাই ইতিহাসের নিদর্শন দেখতে নিচে বেসমেন্টে ঢুকলাম। এখানে রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস- যা গ্রিক, রোমান ও আরব সংস্কৃতির মিশ্রণ- মালাগায় ৩০০০ বছর ধরে মানুষের বসবাসের ইতিহাস, তা বেরিয়ে পড়ে মাটি খোঁড়াখুঁড়ির সময়, প্রাসাদ থেকে জাদুঘরে রূপান্তরে।
মালাগার ইতিহাসের পথে এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষে আমিও যোগ দিলাম পিকাসোর গ্যালারিতে। এখানে রয়েছে পিকাসোর আট দশকের শিল্পকর্মের সংগ্রহ- কি বিপুল সৃষ্টিশীলতা, অপার তার প্রাচুর্য ও অসীম তার বৈচিত্র্য সব সৃষ্টিকর্ম মাত্র একজন মানুষের, যিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক শিল্প আন্দোলনের এক পুরোধা।
১৯০১ সালে পাবলো পিকাসো মাত্র ১০ বছর বয়সে পরিবারের সাথে মালাগা ত্যাগ করেন। এরপর এখানে আর বাস করেননি, শুধু দু-একবার বেড়াতে এসেছিলেন। এর প্রায় ১০০ বছর পরে ২০০৩ সালে চালু হয় ‘মুজেও পিকাসে’া- এ শহরের শ্রেষ্ঠ সন্তানের নামে তাঁর চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা- যাকে নিয়ে মালাগা শহরে ঘটে এক আশ্চর্য রূপান্তর, এর কেন্দ্র হয়ে ওঠেন পাবলো পিকাসো- তাঁর ছবি দেখার জন্য নামে মানুষের ঢল, শহরে শুরু হয় নব উদ্দীপনা।
মুজেও পিকাসো-এর আশে পাশে চিত্রকলার সারি সারি দোকান, আর পিকাসোর হাজারো ছবির হরেক সাইজের প্রিন্ট। অনেক ছবি আবার মূল ছবি দেখে হাতে আঁকা- আসল না নকল, তা বোঝাই কঠিন। আমরা পিকাসোর বিখ্যাত কিছু ছবির প্রিন্ট নিলাম, তার মাঝে করিদা ও গোয়ের্নিকা তো আছেই।
মুজেও পিকাসো দেখা শেষ করে আমরা সবাই বসলাম কাছের এক তাপাস বারে- একটু খাওয়া, একটু বিশ্রামের জন্য। বিশ্বখ্যাত পাবলো পিকাসোর জাদুঘর দেখে কারো মাঝে কোনো আনন্দ, উচ্ছ্বাস দেখলাম না। বরং মনে হলো সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। তারপরও জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগল? নাবিল ও নাতাশা প্রায়ই একই সাথে, একই সুরে বলল, ভালো লাগেনি। ভাল লাগা, না লাগা, এরা সরাসরিই বলে দেয়, আমাদের মতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে না। আমার একটু আগ্রহ হলো জানার, কেন ভাল লাগেনি। নাতাশা বলল, আমার পছন্দ ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং, আর প্রিয় শিল্পী ক্লদ মনে ও তাঁর ‘ওয়াটার লিলি’। পাবলো পিকাসোর ছবিগুলি অন্য রকম, ঠিক বোঝা যায় না। নাবিল বলল, ভ্যান গগ আমার প্রিয় শিল্পী- আর তার ‘স্টারি নাইট’ আমার সবচেয়ে প্রিয় আর্ট। পাবলো পিকাসোর ছবিগুলি এ রকম নয়। ফারজানা বলল, রেনোয়া আমার প্রিয় শিল্পী। তাঁর অনেকগুলি ছবি, যেমন ‘স্প্রিং বুকে’, ‘মাদাম মনে এ্যান্ড হার সান’ আমি পছন্দ করি। পাবলো পিকাসো একটু জটিল।
চিত্রকলা বিষয়ে আমার জ্ঞান সীমিত, তাই কথা বেশি বাড়ালাম না। তবে বুঝতে পারলাম, চারপাশের চেনা জগতই তারা দেখতে চায় পরিচিত রূপে, তাকে ভেঙ্গেচুরে নয়। এটা কি সেই বিখ্যাত ইমপ্রেশনিজম? আমিও একই ধারার। তবে তা আরো মাটিছোঁয়া। আমার কাছে চিত্রশিল্পী মানেই জয়নুল আবেদিন- যার রঙ-তুলিতে ধরা পড়েছে বাংলার চিরায়ত রূপ অনন্যভাবে। মাটির, মানুষের, জীবনের- কী সব অসাধারণ ছবি!নবান্ন, নৌকা, সংগ্রাম, মনপুরা ৭০- আরো কত কী! আমার তো জয়নুলের চোখ দিয়েই বাংলাকে দেখা- সে চোখে অন্য কিছু কি ভাল লাগবে?
ঘুরতে ঘুরতে এরপর আমরা এলাম এক রাস্তায়, নাম- এল পাছাহে দে চিনিতাস। তার এক কোনায় বেশ ভিড়। দেখলাম এক ট্যুরিস্ট গাইড তার দলকে এক ভবনের সামনে কী সব দেখাচ্ছে। ভিড়ের সাথে মিশে আমরাও তা দেখতে লাগলাম। ভবনের সদর দরজায় বড় করে লেখা আছে- এল কাফে দে চিনিতাস, তার নিচে মোজাইকে খোদিত ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকারর এক কবিতার অংশ, স্পেনীয় ভাষায়, নাবিল চট করে গুগলে অনুবাদ করে নিল ইংরেজিতে, আমি করলাম বাংলায়:
পাকিরো তার ভাইকে বলল:
তোমার চেয়ে বেশি সাহসী আমি,
আরো বড় বুলফাইটার
আরো বেশি জিপসি।
এ ক্যাফেটির নামে কবিতার শিরোনাম: ‘এন এল ক্যাফে দে চিনিতাস’-এর মানে ‘ক্যাফে দে চিনিতাস এর মাঝে’।
ট্যুরিস্ট গাইডকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে গেলাম, কেউ কিছু বলল না। গাইড বলে যাচ্ছে এ ক্যাফের ইতিহাস, ১৮৫৭ সালে যা চালু হয়। আগে এর নাম ছিল ক্যাফে ক্যানতানতে দে চিনিতাস- তা ছিল এক ফ্ল্যামেনকো স্টুডিও। এটা হয়ে ওঠে কবি ও শিল্পীদের আড্ডার একটি প্রিয় জায়গা। এখানে অনেকেই আসতেন, তার মধ্যে নামকরা হলেন ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, পাবলো পিকাসো ও সালভাদর দালি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়, ১৯৩৭ সালে, এটা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ছিল ৮৭ বছর। এর ঐতিহ্যের কথা ভেবে অনেক সংস্কার করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে- এখন থেকে মাত্র ৪ মাস আগে- তা আবার চালু করা হয়। তবে এখন আর ফ্ল্যামেনকো স্টুডিও নয়, শুধুমাত্র রেস্তোরাঁ, নাম- ক্যাফে দে চিনিতাস।
ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল লোরকাকে, তিনি ডান হাতে কলম ও বাম হাতে এক নোট বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পূর্ণ আকারের এ ভাস্কর্যটি বসানো হয়েছে বারের মাঝখানে। বুল রিংয়ের আদলে গোলাকার করে বানানো বারটি, যার মাথার উপর শোভা পাচ্ছে কর্ডোভার এক হ্যাট। চারপাশের দেয়ালে রাখা আছে শিংসহ ষাঁড়ের মাথা, যা মনে করিয়ে দিচ্ছে ষাঁড়ের লড়াইকে। মেঝেতে রাখা আছে ব্যারেল ও জগ। সব মিলিয়ে বুল রিংয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। লোরকার ভাস্কর্যটির পাশে মুদ্রিত আছে তাঁর ‘এন এল ক্যাফে দে চিনিতাস’ কবিতাটির পুরো রূপ:
ক্যাফে দে চিনিতাস এর মাঝে
পাকিরো তার ভাইকে বলল:
“তোমার চেয়ে বেশি সাহসী আমি,
আরো বড় বুলফাইটার
আরো বেশি জিপসি।”
ক্যাফে দে চিনিতাস এর মাঝে
পাকিরো বলল ফ্রাসকুয়েলোকে:
“তোমার চেয়ে বেশি সাহসী আমি,
আরো বড় বুলফাইটার
আরো বেশি জিপসি।”
পাকিরো তার হাতের ঘড়ি
খুলে বলল:
“এই ষাঁড়টিকে মরতে হবে
সাড়ে চারটার আগেই।”
রাস্তার ঘড়িতে যখন চারটা বাজে
তখন তারা ক্যাফে ছেড়ে চলে যায়।
পাকিরো তখন রাস্তায়
পোস্টারের বুলফাইটার।১
নাবিল বলল, এখানেও ইতিহাস, আর ভাল লাগে না। আমি একটু সান্ত¡নার সুরে বললাম, তুমি এসব না শুনলেও হয়। তার চেয়ে বরং তোমরা দুজন খাওয়ার মেন্যু দেখে কিছু অর্ডার দিয়ে দিতে পার। এটা একটা রেস্তোরাঁ, আমরা এখানে ডিনার সেরে নিতে পারি। আমার জন্য অর্ডার দাও গ্রিলড ফিশ- স্যামন, সার্দিন, ম্যাকারেল- যাই হোক। সমুদ্র পাড়ের শহরে মাছ সবচেয়ে উপাদেয়। ফারজানা বলল, আমার জন্যও তাই। নাবিল ও নাতাশা খুশি মনে চলে গেল। আমি আর ফারজানা গাইড ও ইতিহাসের পেছনে ঘুরতে থাকলাম। একটু পরে নাবিল নাতাশার সাথে যোগ দিলাম।
যখন ডিনার শেষ করলাম, তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতে চলল। নাতাশা বলল, গুগল সার্চ করে আমি বের করেছি এক সুন্দর জায়গা- কায়ে লারিওস। এটি মালাগার সবচেয়ে বড় শপিং সেন্টার। চল আমরা সেখানে যাই।
খুব কাছেই‘কায়ে মার্কেস দে লারিওস’- সংক্ষেপে কায়ে লারিওস। বহু আধুনিক ভবন, আর বড় রাস্তা ও চওড়া চত্বরে ঘেরা শহরের প্রাণকেন্দ্র। বিশাল আয়তাকার চত্বর ঘিরে আছে ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, বার, সুদৃশ্য বুটিক শপ প্রভৃতি। বিশ্বখ্যাত সব ব্র্যান্ডের পারফিউম, পোশাক, জুতা, স্যুটকেস, অলংকার ইত্যাদির দোকান। মনে হচ্ছে নিউ ইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউ দেখছি, সেখানে ঘুরছি।
কদিন আগে ছিল ক্রিসমাস, এখনো তার সাজসজ্জা শোভা পাচ্ছে কায়ে লারিওস এর ল্যাম্পপোস্টে, রাস্তায়, ভবনে। আমরা তা সব দেখছি হেঁটে হেঁটে। ধীরে ধীরে বাড়ছে রাত, সাথে বাড়ছে মানুষের ভিড়। এর মাঝে কয়েকজন ছেলে মেয়ে এসে চত্বরে একটু জায়গা করে নিল। এরপর বসালো সাথে আনা কটি স্পিকার, আর শুরু করল ফ্লেমেনকো নৃত্য-গীত। নাচ-গানের ছন্দ তীব্রতর হতে লাগল। সাথে বাড়তে লাগল চারপাশের মানুষের উচ্ছ্বাস। ঘণ্টাখানেক পর নাচ-গানের ছন্দ ও শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।
এরপর শুরু হলোস্ট্রীট শো-এর প্রস্তুতি। দলপতি ডমিনগাজ, একজন স্পেনীয় সুপুরুষ- তার দলের চারজনকে বলল চারদিকে যেতে, আর দর্শকদের বলল, জায়গা করে দিতে। এভাবে তারা মাঝখানের খালি জায়গাটি করল আরো বিস্তৃত। প্রায় ৪০ ফিট বাই ১৫ ফিট। তার চারপাশে দর্শক গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডমিনগাজ অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। দর্শকদের বুঝিয়ে দিল সে কী করতে যাচ্ছে। ১০ জন বাছাইকৃত দর্শক মাঝখানে লাইন করে দাঁড়াবে আর সে লাফ দিয়ে তাদের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। কী হয় দেখা যাক!
ডমিনগাজ বর্ণনা করল দর্শকদের বাছাই করার নিয়ম। পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশ থেকে দুজন করে মোট ১০ জনকে নেয়া হবে। কোনো দেশ থেকে একজনের বেশি হতে পারবে না। আর হবে বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন বয়সের লোকজন- অর্ধেক নারী, অর্ধেক পুরুষ। ডমিনগাজ বলল, আমি পুরো পৃথিবীকে এখানে আনব, কারণ স্পেনে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে লোকজন বেড়াতে আসে। এটা হবে বন্ধুত্বের এক প্রদর্শনী। ডমিনগাজ কথা বলে চমৎকার, তার অঙ্গভঙ্গিও দৃষ্টিনন্দন, তাই সবাই মোহিত হয়ে যাচ্ছে। সময়ের দিকে কারো খেয়াল নেই।
আমার মনে ভয় ঢুকে গেল-যদি আমাদের কাউকে ডাকে। পরে ভাবলাম, ভয়ের তেমন কিছু নেই। ডাক পড়লেই যাব। নাবিল ও নাতাশা তো আগ্রহী হয়ে আছে, যেতে বললেই যাবে।
ডমিনগাজ একে একে ১০ জন দর্শককে বাছাই করল। তারা ৫ মহাদেশের ১০টি দেশ থেকে আগত দর্শক- মরক্কো, নাইজেরিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া- মাঝখানে সারি করে দাঁড় করাল। তারপর তাদেরকে দেয়া হলো ৩টি শর্ত- তারা নড়তে পারবে না, শব্দ করতে পারবে না, চোখ খুলতে পারবে না। এসব শুনে ৩ জন বলল তারা তা মানতে পারবেনা। ডমিনগাজ নতুন ৩ জনকে বাছাই করে আনল। পুরো ব্যাপারটি দেখে দর্শকদের উত্তেজনা বাড়তে লাগল। কীভাবে ঘণ্টাখানেক সময় চলে গেল, বোঝাই গেল না। চমৎকার এক শোম্যানশিপ দিয়ে ডমিনগাজ দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখল। এর মধ্যেই কয়েক হাজার লোক জমে গেল এ শো দেখতে। তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে শুধু ডমিনগাজকে দেখছে, তার কথা শুনছে। হাজার লোকের মাঝে পিনপতন নিস্তব্ধতা- একমাত্র ডমিনগাজ-এর কথা শোনা যাচ্ছে।
মাঝখানের ১০ জন দর্শক ভাস্কর্যের মতো স্থির হয়ে আছে- তাদের চোখ, মুখ বন্ধ। ডমিনগাজ শেষবারের মতো দর্শকদের চারপাশে ঘুরে আসল। এরপর বলল, ১০ সেকেন্ডের ভেতর সে লাফ দেবে- ১০ জন ভলান্টিয়ার দর্শক যেন ৩টি শর্ত মনে রাখে, আর বাকি দর্শকরা যেন তাদের দিকে চোখ রাখে।
ডমিনগাজ ২০ ফুট দূর থেকে যখন দৌড় শুরু করল। তখন সবার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এরপর সে মাঝখানের ১০ জন দর্শকের উপর খুব দক্ষতার সাথে লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল। কাউকেই স্পর্শ করল না। সবাই হাত তালি এবং ওলে ওলে ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। সহকারী ৪ জন হাতে বক্স নিয়ে দর্শকদের কাছে গেল। কেউ কেউ কিছু টিপস দিল। আমরাও দিলাম। অনেকে ডমিনগাজ ও তার দলের সাথে ছবি তুলল। তাদেরকে বাহবা দিল। তারা চলে যেতেই সবাই আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করল। অবশ্য কিছু দর্শক রয়ে গেল শেষ রাতের হাওয়া খেতে- মাঝ রাত তো প্রায়ই এসে গেল। আমরা পরিতৃপ্ত ও পরিশ্রান্ত- তাই বিদায় নেবার পালা।
আজ রাতের এই স্ট্রীট শো ছিল আমাদের জন্য এক উত্তেজনাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। সে অনুভূতি নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওয়ানা দিলাম। (চলবে)
Ref:
১. En el Café de Chinitas ,এল কাফে দে চিনিতাস এর মাঝে
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-

তিন প্রহরের শকুন
-
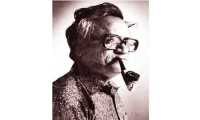
ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা
-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-
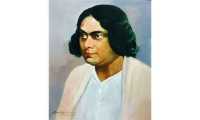
নজরুলের গল্প ও উপন্যাস