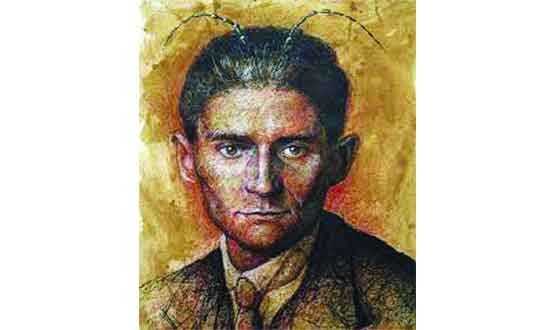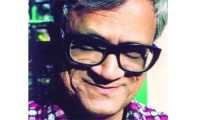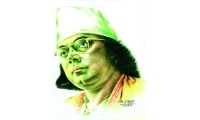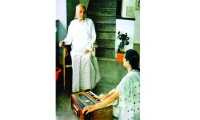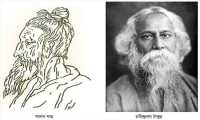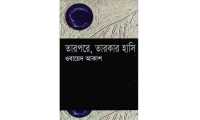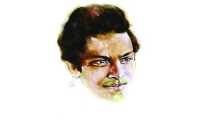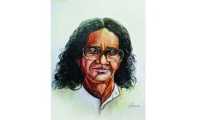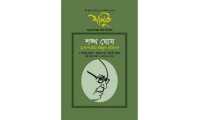literature » samoeky
কাফকাকে পড়া, কাফকাকে পড়ানো
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
ফ্রান্ৎস কাফকা
কাফকাকে পড়ার একটা শাস্তি যদি হয় প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি বর্ণনাকে একটা বিন্যাসে ফেলে অর্থ করার সিসিফাসিও প্রয়াস, তাহলে তাঁকে পড়ানোটা হয়ে দাঁড়ায় সিসিফাসের অবস্থানে থেকে ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ের গাঁ বেয়ে তোলা পাথরটাকেই বুঝতে চেষ্টা করা, পাথরটার ইচ্ছাশক্তিকে বোঝা, যা তাকে উপরে উঠে স্থিত হতে না হতেই গড়িয়ে নিচে নামায়। পাথরটা কি সিসিফাস নিজে? এই পাথর ওঠানো-পাথর গড়িয়ে পড়া-আবার ওঠানো কি কোনো গেইম, কোনো লীলা? এই পরিশ্রম কেন করবে সিসিফাস বলতেই পারত, শক্তিধর, যা ইচ্ছা করো, আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। এই পাথর কি তার সেই নিয়তি যা সে জন্ম থেকে নিজেই নিশ্চিত করেছে? একসময় সিসিফাস মিথ নিয়ে লেখা ক্যামুর একটি দার্শনিক রচনা (দ্য মিথ অফ সিসিফাস, ১৯৪২) পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর ভাবনাটাই হয়তো ঠিক। এই পাথর-ঠেলাটাকে জগতের ‘অব্যাখ্যাত নীরবতা’ হিসেবে না দেখে তিনি দেখছেন একটা কিছু করতে পারার তৃপ্তি হিসেবে। এ্যাবসার্ড বা উদ্ভটের ব্যাখ্যাহীনতার সঙ্গে এই চিন্তা যায় না। তারপরও এর পেছনেও যুক্তি আছে। এজন্য শেষ বিচারে সিসিফাস যতটা হতাশ, ততটা খুশি। একসময় কাফকাকে পড়ানো কঠিন সংগ্রাম বলে মনে হতো। এখন মনে হয়, একটা গল্পের একটা বা পাঁচটা যে অর্থ থাকবে তা নয়, পঞ্চাশটাও থাকতে পারে। সিসিফাস যেমন পাথরে তার নিজেকে দেখতে পায়, অথবা জোসেফ কে যেমন তার দুই ঘাতকের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সেজন্য একটা বা পাঁচটা অর্থের নিরিখে বিচার না করে- যে বিচারে কাফকার গল্প-উপন্যাসটা সিসিফাসের পাথরের মতো ভারি হয়ে যাবে, এবং পাঁচবার ঠেলেঠুলে উপরে তুলে ষষ্ঠবার আর পারা যাবে না, পাথরটার ভার হাতের শক্তিকে তুচ্ছ করে নিচে গড়িয়ে যাবে- বরং যতবার এর একাধিক অর্থ করা যাবে, যার কিছু হয়তো ধোপে টিকবে না, ততবার ওই পাথরটা উপরে তোলার পরিশ্রমটা প্রাণঘাতী মনে হবে না, বরং সহনীয়ই মনে হতে পারে। যেমন, কোভিডকালীন বুদ্বুদ জীবনে শ্রেক্সপিয়ারের তুলনামূলকভাবে অল্পপঠিত এবং আলোচিত কোরিওলেনাস নাটকটি আরেকবার পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এর নায়ক যে তার অহংকারকে অলংকারের মতো পরে দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী হয়েছিল, তাতে ভালোমন্দের যে একপেশে ধারণা জন্মায়, তা এড়িয়ে ভিন্ন একটা দৃষ্টিাকোণ থেকে দেখলে কেমন হয়? ধরা যাক, তার অহংকারটা বাজিয়ে দেখতে, এ থেকে মুক্তি পেতে সে হয়তো বিদ্রোহী হয়েছে। একটা ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে জগতের কাছে যতটা না একে প্রমাণ করা প্রয়োজন, তার থেকে বেশি নিজের কাছে। জগৎ এটি ভুল বলে অবশ্যই আগে স্বীকার করবে, কিন্তু নিজে স্বীকার না করা পর্যন্ত এ থেকে মুক্তি নেই। হয়তো কোরিওলেনাস চেয়েছে তার যে দেশের প্রতি ভালবাসা আছে, তার ভুলের অনল তার অহংকার পুড়িয়ে তা প্রকাশ্যে আনুক- সবার আগে নিজের কাছে। অর্থাৎ সে যতটা দেশদ্রোহী, ততটা দেশপ্রেমী, যেহেতু তার সকল কাজের প্রত্যক্ষে আছে দেশ। সেজন্য, হয় সে দেশান্তরে মরবে, না হয় নিজের শর্তে দেশে ফিরবে। কাফকা পড়ানো যদি কঠিন হয়, শেক্সপিয়ার সেই অর্থে ততটা না। কিন্তু সিসিফাসের জন্য একটা পাথর তিনিও রেখে দেন। তাঁর কোনো নাটক পড়ে একটা চিন্তা মনে জমতে থাকলে ওই পাথরটা নড়তে শুরু করে। এবার ঠেলতে শুরু করো- সে আহ্বান জানায়।
কাফকার একাডেমিক পাঠকেরা যে কতগুলি বিষয়কে মাথায় রেখে তাঁর তিনটি উপন্যাস ও কয়েকটি ছোটগল্প পড়তে শুরু করেন (শৌখিন পাঠক অথবা কাফকার কারিসমা মেনে প্রথমবার যারা পড়তে বসেন তারা হয়তো তেমন পূর্ব-অনুমান বা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা করেন না) সেগুলির তালিকা খুব বড় নয়। এর মধ্যে প্রথমেই আছে ওই কাফকাত্ব এবং কাফকীয় বিষয়টি- সেই বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, অস্তিত্বের অসহনীয় লঘুত্ব (কুন্ডেরা থেকেও জটিল এবং লঘু-গুরুর দোলাচলে পরিবর্তনশীল), অর্থহীনতা, দুঃস্বপ্নের অত্যাচার, যৌনতা, নারীসঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক-যৌনতাসূচক তৃপ্তি-অতৃপ্তি এই সব। আরো আছে তাঁর সৃষ্টির পেছনে কাফকার আত্মজীবনীমূলক নানা ঘটনা-অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপস্থিতি, বিশেষত তাঁর বাবার সঙ্গে চরম দ্বন্দ্বপীড়িত তাঁর সম্পর্ক; প্রাগ শহরে জার্মান ভাষাভাষি ইহুদী হিসেবে তাঁর অবস্থানের ভঙ্গুরতা (প্রাগের বেশিরভাগ মানুষ ছিল খৃস্টান এবং তাদের ভাষা ছিল চেক, এবং কাফকা ইহুদী হলেও ইহুদীবাদে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। এক অর্থে তিনি ছিলেন রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, এমনকি পরিবারের পক্ষে তৈরি করা নানান ভক্তিশ্রদ্ধা-আদর্শের প্রতিমা ভাঙ্গার দলে)। এর বাইরে পাঠক তাঁকে পড়ে কুড়ি শতকের প্রথম দুই দশকের ভয়াবহ নানা সংকটে পড়া ইউরোপ ও ইউরোপের মানুষজনের পাল্টাতে থাকা জীবনের প্রতিচ্ছবি পেতে, যে প্রতিচ্ছবি অনেক কবি-সাহিত্যিক দিয়েছেন উনিশ শতকের আশির দশক থেকে সক্রিয় হওয়া সাহিত্যিক আধুনিকতার বোধ-অনুভূতি-ভাষা-শৈলী-প্রকাশভঙ্গীতে। কাফকার আধুনিকতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, যতটা হয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে এই সময়েরও সংকটের ছায়াপাত নিয়ে। কিন্তু ক্যামুর প্রধান চরিত্রগুলিতে যেমন সংকটকে আধুনিকতার সেই সময়-চিহ্নিত হিসাবে মাপা যায় না- তারা কেন জানি সর্বকালের একটা দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়- কাফকার ক্ষেত্রেও অনেকটা যেন তাই হয়। জোসেফ অথবা মি. কে কি সংকট পীড়িত ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের কোনো মানুষ, নাকি তারা আরো পুরনো, সমাজের এবং প্রতিষ্ঠানের সমান বয়সী? এই প্রশ্নটি কাফকার আধুনিকতাকে তাঁর নিজ দর্শন অনুযায়ী ভেবে দেখতে অনুপ্রাণিত করে।
কাফকার লেখালেখিকে সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনীতির কাচের ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন অনেক সমালোচক, মধ্য ইউরোপের জন্য কুড়ি শতকের শুরু থেকেই সময়টা প্রকৃতই ছিল এক ঘনায়মান সংকট এবং সম্ভাব্য বিপর্যয়ের। হ্যাপসবার্গ সা¤্রাজ্যের পতন এবং ১৯১৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মপ্রকাশের সময় ও এর আগে ইউরোপ প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছে। কাফকা এর আঘাতটা মানুষের ভেতরটাকে এলোমেলো করতে দেখেছেন। ১৯৩০-এর দশকে জার্মানিতে নাৎসিদের উত্থান একদিনে ঘটেনি- প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকেই ফ্যাসিবাদ ও নানা চরমপন্থা, ইহুদী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জিপসি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অরক্ষিত জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং বৈরিতার প্রকাশ ক্রমিকভাবে বাড়ে, শারীরিক নির্যাতন এবং সংগঠিত হত্যাকা- লুকানো ঘটনা হিসেবে আর থাকেনি (কাফকার গল্প “ইন দ্য পিনাল কলোনি”র একেবারে শুরুতে যে ‘এক্সিকিউশন’- বা মেকি বিচার অথবা শক্তিমানের একক সিদ্ধান্তে কাউকে হত্যা করা- কথাটি এসেছে, দ্য ট্রায়াল-এর শেষেও তাই ঘটেছে)। এটি অবাক করার মতো একটি বিষয় যে একদিকে ইউরোপ (এবং পশ্চিমা) সাহিত্যে শিল্পকলায় আধুনিকবাদের যুগ পাল্টানো প্রভাব পড়ছে, মানুষ নান্দনিক-সৃজনশীল সমুন্নতির সম্ভাবনা দেখছে, অন্যদিকে মধ্য ইউরোপে ব্যক্তির স্বাধীনতা অরক্ষিত হয়ে পড়ছে, অনাধুনিকতার নানা প্রকাশ এক প্রকট বৈপরীত্যের মিছিল মূর্ত করেছে। আলোকায়ন যুগের আদর্শ ধরে তৈরি করা আধুনিকবাদের বয়ানে তাই অনেক ফাঁক থেকে গেছে, যেগুলির ভেতর দিয়ে কিছু আদিম অন্ধকার বেরিয়ে আসে। যখন ইংলন্ডের কবিরা শিল্পীরা নতুন নানা আশাবাদী ঘরানায় তাদের সৃষ্টি সাজাচ্ছেন (ইমেজিজম, উত্তর-প্রভাববাদ ইত্যাদি), সে সময় আয়ারল্যান্ডের মানুষ ইংরেজ উপনিবেশায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ব্যক্তিকে আধুনিকবাদ সার্বভৌমত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছে, তার ভেতরের নানা দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সত্ত্বেও- যেগুলিকে গভীর করেছে নগরায়ন, অদমিত শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং তা থেকে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্ববোধ। কিন্তু কাফকার নিজস্ব যে সংকট তাকে দমিত রেখেছে, তার শুরু তাঁর বাবার সঙ্গে তার বাড়তে থাকা দূরত্বের জন্যই। এজন্য, কাফকার চরিত্ররা যে অবাস্তব নয়, বরং কাফকার ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত ব্যক্তি যে অস্বাধীন এক অস্তিত্বে নিক্ষিপ্ত হয়, তার নিক্তিতে খুবই বাস্তব। কাফকার “দ্য মেটামরফসিস” গল্পটার কথাই ধরা যাক, গ্রেগর সামসা যখন তার পোকার জীবনে বুঝতে পারল, তার উপার্জনের উপর তার বাবার নির্ভরশীলতা চলে যাওয়ার পর তিনি কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছেন, এবং তার অফিসকর্তাও কর্তৃত্ববাদ দেখাচ্ছেন সহানুভূতির পরিবর্তে, এবং এক ভয়ানক নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির চক্রে পড়ে তার অসহায়ত্ব তীব্র হচ্ছে, সে হাল ছেড়ে দিল। পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ সমাপ্ত হলো। সে মারা গেল তার বাবার ছুঁড়ে দেয়া আপেলের আঘাত থেকে তৈরি হওয়া অনিরাময়যোগ্য ক্ষত থেকে। সেই মৃত্যু কি প্রতীকী অর্থে বাবার সঙ্গে কাফকার প্রকট দ্বন্দ্বের পরিণতির দিকে ইঙ্গিত দেয়? সে যাই হোক, ইউরোপীয় রাজনীতির বিধ্বংসী দিকটি কাফকার মতো বিপন্ন মানুষ তীব্রভাবেই অনুভব করেছেন। তাঁর তিনটি বোন নাৎসিদের কনসেন্ট্রশন ক্যাম্পে মারা পড়েছেন। ফলে কাফকার লেখালেখিতে যে রাজনীতি আসে, তা একই সঙ্গে বৃহত্তর ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে এবং তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হবে। তাঁর বাবাকে এবং তাঁকে নিয়ে লেখা চিঠিগুলিতে এর অনেক সূত্র সন্নিহিত আছে। এগুলো বিবেচনায় নিলে দু’টি জিনিস পরিষ্কার হবে- প্রথমত, কেন তাঁর অনেক চরিত্র রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অত্যাচারিত হয়ে নিজের মনস্তাত্ত্বিক অখ-তা হারায়, কেন একজন শিকার বা ভিকটিম তার শিকারীর সঙ্গে যুদ্ধ না করে বরং নিজের অপরাধ নিয়েই বিভ্রান্ত হয় এবং বলা যায় এক ধরনের আত্মসমর্পণই করে বসে। দ্বিতীয়ত, তার আত্মপরিচিতে যে ফাটল ধরে তা কাফকার সুবিন্যস্ত, ‘ফাটলহীন’, ঘনবদ্ধ ভাষা ও শৈলীতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যেমন সাদার পাশে কালোর দাগ বৈপরীত্যের সহঅবস্থানকে স্পষ্ট করে। বিষয় ও ভাষার এমন পারস্পরিক সমুন্নতি কাফকার এক অসামান্য অর্জন।
একই সঙ্গে কাফকার নিজস্ব রাজনীতি কী ছিল, তা নিয়েও নানা অনুমান চলেছে, দু’এক সমালোচক কাফকার এক উদ্ধারহীন, সম্ভাবনাহীন বিশে^র প্রতিরূপ আঁকার পেছনে এরকম একটা ফন্দিও দেখেছেন যে, তিনি যেন বোঝাতে চাইছেন, এই ছবিটি যে হতাশা তৈরি করে, এরকম একটা চিন্তাকে বৈধতা দেয় যে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতেই হবে, তাহলে তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের যুক্তিটাও তো মিলে যায়। এই পঠনের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের বৈকল্য দেখানোর উদ্দেশ্য একে টিকিয়ে রাখতে সংকল্পবদ্ধ কোনো অপশক্তির পক্ষে ওকালতি করা নয়, কোনোকালে কোনো লেখক শিল্পী তা করেননি, তবে কাফকার সময়ে, এরকম চিন্তা অনেক মহলে যে ঘুরত, তাও অনুমিত নয়, বাস্তব। এরই সূত্র ধরে কেউ কেউ কাফকাকে অরাজনৈতিক প্রাণি, সামাজিক নীতির প্রতি উদাসীন- এরকম তকমায় চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত বিষয়টি হলো এই যে, কাফকার ব্যক্তিত্বে বা জীবনে কোনো সংঘবদ্ধ কাজ, কোনো নিয়ন্ত্রিত কৃত্য অথবা আগ-পিছ পরম্পরা বজায় রেখে চলার পক্ষে কোনো সমর্থন কেউ পায়নি। তিনি এক অব্যাখ্যাত নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন, নিজেই তাঁর সব ‘অভাব’ বা ষধপশরহম এর জন্য যে দায়ী, সেই দায় স্বীকার করে নিতেন, কোনো সঙ্গে, এমনকি দাম্পত্য সঙ্গেও, স্বস্তি পেতেন না। তারপরও তাঁর রাজনীতি যে জনমানুষের, আরো বিশেষ করে বললে শিল্পশ্রমিকদের পক্ষে ছিল, তার বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। প্রাগের ওয়ার্কার্স এ্যাক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স ইনস্টিটিউটে তিনি যখন কাজ করতেন, তাঁর দায়িত্ব ছিল শ্রমিকদের জন্য ওকালতি করা, তাদের স্বার্থ দেখভাল করা। তাঁর দেন দরবার ছিল মিল মালিকদের সঙ্গে। মিল মালিকদের চেহারা, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সবখানে একই রকম হয়। কাফকা যাদের সঙ্গে বসতেন, শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলতেন, তারা নানাভাবে তাঁর কাজে বাধা দিত। কারখানা পরিদর্শন এবং কারাখানায় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত করা হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য যেতে তাকে নিরস্ত করার নানা চেষ্টা করত, ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় নীতি প্রয়োগে এবং অন্যান্য দু’এক ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য তাঁকে আলাদা একটা মর্যাদা দিত। কিন্তু এসব আইনকানুন যে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের পক্ষে যাবে না, আইন যে নানা মিথ্যাকে সত্যের রূপে হাজির করে, এই সন্দেহটা তাঁর নিজের এবং মি. কে’র ছিল। বলা যায়, তাঁর সাহিত্যে রাজনীতি যথেষ্টই আছে, এবং তা আছে এক প্রবল অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির পরাজয়-নির্দিষ্ট সংগ্রামের চিত্রায়নে, প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিত্রাণহীন শৃঙ্খলের চাপে ব্যক্তির ভেঙ্গে পড়া, তার বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ থেকে এক সাহিত্যনির্ভর সমালোচনা তৈরি হওয়া যার অভিঘাত গল্প পড়া শেষ হলেও পাঠকের চিন্তাগত সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বৈধতা পেতে থাকে।
এজন্যই কিনা, কাফকা তাঁর অনেক লেখাই সত্যিকারভাবে সমাপ্ত করেননি। তাদের অসমাপ্ততা কি এই ঘোষণা দেয় যে, সমাপ্তি যদি আদৌ সম্ভব, তবে হয়তো তা বাস্তবে, সাহিত্যের পাতায় নয়? অথবা, সমাপ্তি, এমনকি বাস্তবেও অনেক সময় একটি অপূর্ণতা, একটি বিভ্রম বা সিদ্ধান্তের নাম? (আগামী সংখ্যায় পড়ুন)
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-

তিন প্রহরের শকুন
-
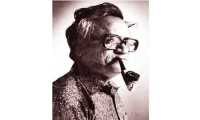
ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা
-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-
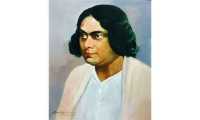
নজরুলের গল্প ও উপন্যাস