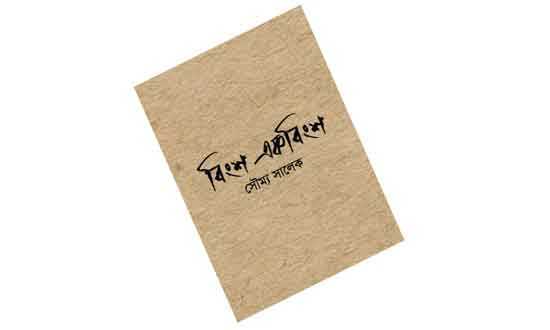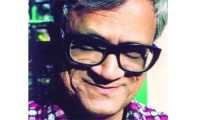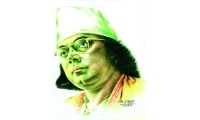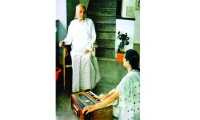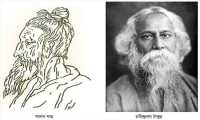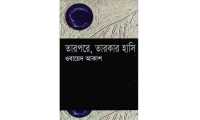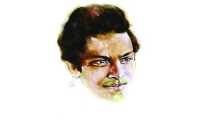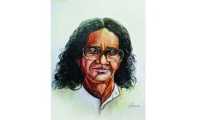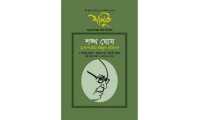literature » samoeky
বিংশ একবিংশ
মননশস্যের অমৃত মন্থন
পীযূষ কান্তি বড়ুয়া
নান্দনিকতা বিষয়টি পাকা বেলের মতো। বেল পাকলেও তা সবার আস্বাদনযোগ্য হয়ে ওঠে না শক্ত বহিরাবরকের কারণে। নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুও তেমনই। যার প্রগাঢ় মননশীলতা নেই, যার বিচিন্তার স্রোত নেই, তার পক্ষে নন্দনতত্ত্বকে ধারণ করা বেশ কঠিন বৈকি। এ কারণেই পাঠকসমাজে মননশীল প্রবন্ধের অনুরাগীর সংখ্যা হাতেগোনা মাত্র। অধিকাংশ পাঠকের মন তাৎক্ষণিক বিনোদন কিংবা জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনীতে মজে থাকলেও প্রগাঢ় সৌন্দর্য চেতনার উদ্বোধন অনেকের ক্ষেত্রে ঘটে না। তাই সৃজনশীল সাহিত্য বা ফিকশনের কদর প্রতি ঘরে ঘরে থাকলেও মননশীল সাহিত্য বা নন ফিকশন রচনাবলির প্রতি আগ্রহ পাঠকসমাজে বিরল। বাঙালি পাঠক লেখাকে যত সহজে গিলে নিতে পারে, তত সহজে লেখাকে চিন্তার যাঁতাকলে ফেলে তা থেকে রসের ধারা তৈরি করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এ কারণে উত্তরাধুনিক বাঙালি সমাজে সমালোচনা সাহিত্য তেমন কল্কে পায়নি। কারণ সমালোচনা সাহিত্যের কঠিন বহিরাবরণ ভেদ করে তার রসের সরোবরে অবগাহনের মানসিক প্রজ্ঞা এখনও বাঙালি পাঠকসমাজে সাধারণ হয়ে ওঠেনি। ফলে হাল্কা মেজাজের উপন্যাস বা ছোটগল্প আমাদের যত দ্রুত টেনে নেয়, তত দ্রুত ধ্রুপদী সাহিত্য সমালোচনা কিংবা এ জাতীয় উর্বর চিন্তামান সমৃদ্ধ প্রবন্ধ আমাদের অন্তর-প্রাচীরে আবেদনযোগ্য হয়ে ওঠে না। যে প্রসঙ্গে ধান ভানতে শিবের গীত, তা হলো ‘বিংশ একবিংশ’ শিরোনামে রচিত গ্রন্থখানি, যা কবি ও প্রাবন্ধিক সৌম্য সালেকের একটি মৌলিক মননশস্য।
সৌম্য সালেক কবি হিসেবে নিজ ভাষাভঙ্গি আয়ত্ব করেছেন আয়াসসিদ্ধ প্রয়াসে। তার সেই ভাষাভঙ্গির ছায়া-ছাপ তার প্রবন্ধেও সওয়ার হয়েছে। ফলে যারা তার কবিতার পাঠক, তাদের পক্ষে তার প্রাবন্ধিক সত্তাকে জারণ করা কঠিন কিছু নয়। ‘আত্মপক্ষ’ শিরোনামের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘বিংশ একবিংশ’র প্রবন্ধগুলো গত এক দশকে রচিত। গ্রন্থটি ছয়জন নন্দনতাত্ত্বিক প্রাবন্ধিকের সম্মানে উৎসর্গীকৃত যাঁরা হলেন : প্রমথ চৌধুরী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী, বুদ্ধদেব বসু ও সৈয়দ আলী আহসান। একুশটি প্রবন্ধকে পাঁচটি ভাগে করে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। যথা : কবিতা, চারুকলা, সংগীত, নাটক, সাহিত্য সংস্কৃতি ও অন্যান্য। কবিতায় মধুসূদন, জীবনানন্দ, নজরুল, আল মাহমুদ, কহলিল জিবরান ও ময়ূখ চৌধুরী গ্রন্থবদ্ধ হয়েছেন সৌম্য সালেকের আলোচনায়। চারুকলা বিষয়ে শিল্পী এস এম সুলতান এবং দেশীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংগীতে রবীন্দ্রনাথকে ‘পৌষ ফাগুনের পালা’ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। তার সাথে আছেন আরও দুই নারী। একজন মিশরীয় কণ্ঠশিল্পী উম্মে কুলসুম এবং অন্যজন নজরুল সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগম। বুদ্ধদেব বসুর নাটক আমরা তিনজন, প্রতœনাটক মহাস্থানগড় এবং শহীদুল জহিরের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আলোচিত হয়েছে নাট্য বিভাগে। সাহিত্য সংস্কৃতি ও অন্যান্য শিরোনামে আব্দুল কাদিরের নজরুল চর্চা, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্প, শাহযাদ ফিরদাউসের উপন্যাস ‘ব্যাস’, অ্যাম্ফিথিয়েটার, যুগযাত্রায় নারী, বিংশ একবিংশ বিষয়ক প্রবন্ধ পত্রস্থ হয়েছে। সমালোচনাপ্রধান প্রবন্ধগুলো লেখকের আপনভাষ্যে রচিত, দোহাইয়ের অযাচিত ভারে ন্যুব্জ নয়। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম দোহাইয়ের অবতারণা তার আলোচনাকে প্রাঞ্জল ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।
‘আত্মবিলাপ’ নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তিনি চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করেছেন, কবিতাকে আধুনিক শিল্পে রূপায়নে মাইকেলের ভূমিকা অগ্রগণ্য। শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং বাংলা সনেটের ¯্রষ্টারূপে নয়, তিনি সার্থক বাংলা নাটকেরও রূপকার। মাইকেলের পূর্ণ জীবন আত্মবিলাপে ভরা। যে আশার ছলনায় তিনি মা-মাতৃভূমিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন, সে উচ্চাভিলাষের কুহকিনী তাঁকে পদে পদে বিলাপগ্রস্ত করে তুলেছে। আত্মবিলাপের প্রগাঢ় অনুশোচনা প্রকট হয়ে ওঠে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায়। মাইকেল আত্মবিলাপের মাধ্যমে বাংলা ভাষার রতœভা-ারের বিশালতাকে তুলে ধরেছেন। হে বঙ্গ ভান্ডারে তব, বিবিধ রতন / তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি/ পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ/ পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি, বলে কবি মাইকেল যে আত্মবিলাপে মগ্ন থেকেছেন, তা তুলনারহিত। আত্মবিলাপের কবি মাইকেল একজন পরিণত সাহিত্যস্রষ্টা।
সৌম্য সালেকের আলোচনায় কবি জীবনানন্দ তাঁর ‘ধূসর পান্ডুলিপি’ নিয়ে হাজির হয়েছেন। ‘ঝরা পালক’-এর জীবনানন্দ অপরিণত এবং নজরুলের সুরে শরাহত। জীবনানন্দ তাঁর নিজের সুর খুঁজে পেয়েছেন ধীরে ধীরে ‘ধূসর পা-ুলিপি’ হতে। জীবনানন্দের মৃত্যু ও বিষণœতার প্রকাশ প্রাবন্ধিককে ঘোরাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই শাদা হাত, হিম-মৃত্যু ও বিষণœতার প্রতীক হয়ে প্রাবন্ধিকের আলোচনায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।
চিত্রকলার ছাত্র না হলেও সৌম্য সালেক কর্মপরিধির বদৌলতে চিত্রশিল্পের অমৃতে অবগাহনের সুযোগ পেয়েছেন। সেই সুবাদে শিল্পী সুলতানও কাছে এসে গেছে তার। এমনিতেই শক্তিমান চিত্রশিল্প দিয়ে এস এম সুলতান তথা লাল মিয়া বাঙালির শক্তিমত্তাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সেই পবিত্র অভিলাষের স্রোতে সৌম্য সালেকেরও চেতনার বাপ্তিস্ম ঘটেছে। সুলতানের ছবি তাই সৌম্য সালেকের প্রবন্ধকে শক্তিসুধায় আশীর্বাদ করে গেছে। পাশাপাশি দেশীয় চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি পাঠককে জানাতে গিয়ে তিনি নবীন চিত্রশিল্পীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সময়ের ও সম্ভাবনার। ‘বিপন্ন গৌরি’, ‘ক্ষুধা’ কিংবা ‘প্রাজ্ঞ গায়ক’ শিরোনামের শিল্পকর্মে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মন্দ সময়কে শাঁসানোর অদম্য হাতিয়ার।
রবীন্দ্রনাথকে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন ‘পৌষ ফাগুনের পালা’য়। কবিকে নয়, গানের রবিকে। তাঁর গানের কবিতাগুলো দু’তিনটা একত্রে পাঠ করা যায় না, মাথা ধরে আসে। বুদ্ধদেব বসুর এই বাণী কাঁধে নিয়ে সৌম্য সালেক সৈয়দ মুজতবা আলীর বয়ানে বলে দিয়েছেন শেষ কথা, ‘চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান।’ প্রাবন্ধিকের সুযোগ হয়েছিলো, ক্লিওপেট্রার দেশ, নীলনদসিক্ত মিশর ভ্রমণের। সেই ভ্রমণেই তার প্রেম হয়ে যায় আঠারোশ আটানব্বই সালে জন্ম নেওয়া এক মিশরীয় গায়িকার সঙ্গে, যাঁর নাম উম্মে কুলসুম। সেই প্রেমানুরাগ তিনি বহন করে এনেছেন সংগীতসুধায়। এক-দেড় ঘণ্টা এক এক গানের ব্যাপ্তি নিয়ে শ্রোতার মনে আনন্দ-লহরী তোলা গায়িকা উম্মে কুলসুম সৌম্য সালেকের বয়ানের সূত্র ধরে আমাদেরকেও বিমোহিত করে রাখেন।
বুদ্ধদেব বসুর নাটক নিয়ে প্রাবন্ধিকের আগ্রহ গভীর। তিনি নিজেও তাঁর ‘আমরা তিনজন’-এ আখ্যানকে নাট্যরূপ দেন দুহাজার চৌদ্দ সালে। তাই সংগত কারণে এ বিষয়ে প্রবন্ধে বুদ্ধদেব অর্ঘ্যে বরিত হন সৌম্য সালেকের পর্যালোচনায়। শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাসটি সৈয়দ জামিল আহমেদের হাতে নাটক হিসেবে মঞ্চায়িত হয়। সেই প্রযোজনাকে নিয়েই একটা প্রবন্ধ মলাটবন্দী হলো।
কবি ও প্রাবন্ধিক সৌম্য সালেক এক ঋদ্ধিমান পাঠক। তার পাঠ-আহার্যে যুক্ত হয়েছে বিচিত্র বিষয়। তারই প্রভাব ফেলেছে তার প্রবন্ধে ও গদ্যে। আলোচ্য গ্রন্থে স্থানলব্ধ তার সবকটা প্রবন্ধ ও পাঠ পর্যালোচনা সুলিখিত ও সুচিন্তিত। ‘বিংশ একবিংশ’ কোনো মামুলী গ্রন্থ নয়। এটি নিরন্তর জ্ঞানচর্চা ও অধ্যবসায়ের প্রমাণক সৃজনশস্য। বইটি পাঠকের আত্মমনোজগত উন্নয়নের হাতিয়ার হয়ে উঠবে বলে মনে করি। ‘বিংশ একবিংশ’ সহ¯্রাব্দের দলিল হয়ে থাকুক সৃজনে-মননে।
বিংশ একবিংশ। সৌম্য সালেক। প্রচ্ছদ: খালেদ চৌধুরী। প্রকাশকাল: অমর একুশে বইমেলা ২০২৫। মূল্য: ৪০০ টাকা।
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-

তিন প্রহরের শকুন
-
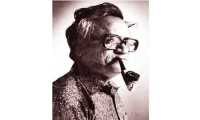
ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা
-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-
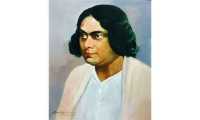
নজরুলের গল্প ও উপন্যাস