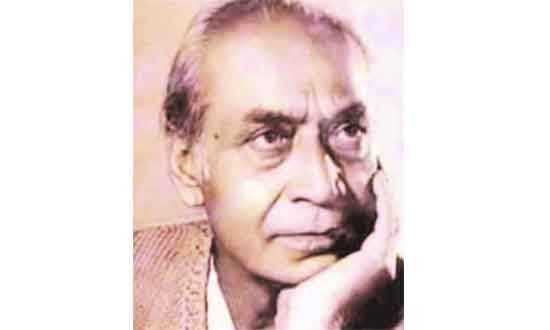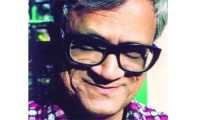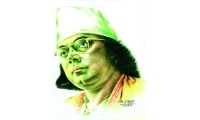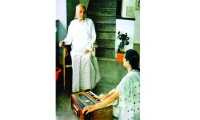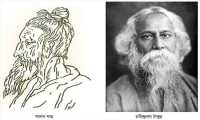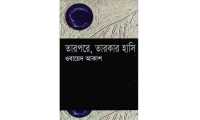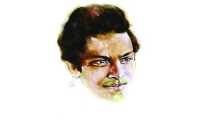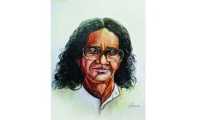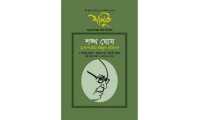literature » samoeky
কবি নওশাদ নূরী
আহমেদ ইলিয়াস : উর্দু থেকে অনুবাদ: হাইকেল হাশমী
নওশাদ নূরী / জন্ম: ২১ অক্টোবর ১৯২৬; মৃত্যু: ১৮ জুলাই ২০০০
১৮ জুলাই বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রগতিশীল ও জনবান্ধব কবি নওশাদ নূরীর মৃত্যুবার্ষিকী।নওশাদ নূরী ১৯২৬ সালের ২১ অক্টোবর ভারতের বিহার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় বিহারকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই অবস্থার ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ বঞ্চনার অনুভূতিতে ভুগছিল, অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার জোয়ার উঠেছিল। এই রাজনৈতিক পরিবেশই নওশাদ নূরীর চিন্তাভাবনা ও চেতনার বিকাশে ভূমিকা রাখে এবং তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটায়।
নওশাদ নূরীর আসল নাম মোহাম্মদ মুসস্তাফা মাসুম হাশমী, কিন্তু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে তিনি নওশাদ নূরী নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি পাটনার বি.এন. কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন, তবে তাঁর কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল ওই একই বছর, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে। সে সময় তিনি প্রগতিশীল লেখক সংঘের অন্তর্ভুক্ত লেখক ও কবিদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান এবং তাঁদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- সোহেল আজিমাবাদি, আখতার ওরাইনভী, মুখতারউদ্দিন আরজু এবং কালাম হায়দরী।
প্রগতিশীল সাহিত্যে আগ্রহ থাকার কারণে নওশাদ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকা-েও অংশ নিতে শুরু করেন। ১৯৫০ সালে তিনি যখন ভারত থেকে ঢাকায় আসেন, তখন তাঁর সাহিত্য ভা-ারে “ভিখারি” নামে একটি বিখ্যাত কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তাঁকে ভারতে নির্বাসিত ও পাকিস্তানে জনপ্রিয় করে তোলে। এই কবিতা তিনি ১৯৪৯ সালে প-িত জওহরলাল নেহরুর আমেরিকা সফরের প্রতিবাদে লিখেছিলেন এবং পাটনার এক জনসভায় পাঠ করেছিলেন- যা কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজন করেছিল নেহরুর সফরের বিরোধিতায়। বিহারের কংগ্রেস সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে এবং গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়।
ভারত ত্যাগের পর ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বহু ঐতিহাসিক কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে লেখা “মহেঞ্জোদারো” অন্যতম। এই কবিতায় তিনি ওই সময়ের প্রেক্ষাপটকে মহেঞ্জোদারোর সাথে তুলনা করেছেন এবং ওই শহরটা কেন বিলীন হয়ে গেল তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ওই মহামারির ছায়া আমাদের দেশেও দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে সাবধান করেছিলেন-কবিতার কিছু অংশ নিম্নে বর্ণিত হলো-
আমার শহরবাসীরা শোনো!
তোমাদের পুঁথি, তোমাদের গীতা
তোমাদের লোককথা, তোমাদের গীতমালা
তোমাদের বর্ণমালা, তোমাদের মায়ের ভাষা
পাতা, পাথর, চামড়া, পাপাইরাস
তামা, লোহার ওপর লিখে রেখ
ঐ মহামারী আবার এসেছে
ঐ দুর্যোগ আবার নেমেছে।
(মহেঞ্জোদারো: অনুবাদ, হাইকেল হাশমী)
নওশাদের এই কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে যেমন, ইংরেজি, বাংলা, জার্মান, সিন্ধি ইত্যাদি।
এছাড়াও ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ রচিত কবিতা “ছাব্বিশে মার্চ” সম্ভবত পাকিস্তানি আমলের ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানে লেখা এটাই শেষ উর্দু কবিতা, যার কৃতিত্ব নওশাদ নূরীর। কবিতার শেষ অংশ নিচে দেয়া হলো-
এখন এই ঢাকাতে, করাচীর কল্পনা দুঃখজনক
কাগান থেকে রাঙ্গামাটির দূরত্ব আজ অনেক গুণ বেড়ে গেছে।
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়াই একমাত্র পথ,
আর কোনো ওষুধ নেই
ঘৃণার প্রচ- আবেগ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই।
জনগণের প্রচ- বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।
(ছাব্বিশে মার্চ: অনুবাদ, আসাদ চৌধুরী)
নওশাদের দুটি কাব্যগ্রন্থ- “রহ ও রসম-ই-আশনাই” এবং “রওজন-ই-দেওয়ার”- বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পরে জুলাই ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়।
নওশাদের জীবনের পরিপূর্ণ সময়কাল ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ অতিক্রম করেছে। প্রথমত, তিনি ব্রিটিশ সা¤্রাজ্যবাদের সময় দেখেছেন, যখন উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল এবং প্রগতিশীল লেখক সংঘের গোড়াপত্তন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি দেখেছেন উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন, যার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মানুষ নানা রাজনৈতিক-সামাজিক পরিক্রমা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। ভারতে গণতন্ত্রের শিকড় দৃঢ় হলেও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেয়; পাকিস্তানে স্বৈরতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল নওশাদ নূরী নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, উর্দু কবিতা আবার সেই স্থানে ফিরে আসে যেখান থেকে ১৯৪৭ সালে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল।
উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী তাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল, এবং ভূমির সঙ্গে তাদের সম্পর্কই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। এটা ছিল তাদের এক সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের পতনের সময়।
এই প্রেক্ষাপটে নওশাদ লেখেন কবিতা “কেবলা-ই-আওয়াল” অর্থাৎ প্রথম কেবলা কবিতার চরণ উল্লেখ করা যেতে পারে-
“এই মাটি, যা তোমার পা ধরে রেখেছে,
তাতেই আজ সিজদার মোহনীয় ক্ষণ এসেছে”।
নওশাদ নূরীর কবিতায় যেমন আবেগের তীব্রতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে গভীর বোধ ও চিন্তার প্রসার। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো কবিতা “তারিখ কা দিবাচা” অর্থাৎ ইতিহাসের মুখবন্ধ। কবিতায় তিনি বলেন:
“বিগত যুগের আমরাই প্রহরী,
অদৃশ্য কালের দিকে ধাপিত আমরা সেই যাত্রী,
এই বেদনাদায়ক সময়ের আমরাই প্রত্যক্ষদর্শী,
আমরাই বর্ণনাকারী।”
তাঁর কবিতায় গজল ও সুরেলা আবহ পুরোপুরি বিরাজ করে। নওশাদ নূরী কিছু গজলও লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি সেগুলো প্রকাশ করতে চাননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পর, তাঁর একটি অপ্রকাশিত গজল ঢাকায় কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশ পায়।
নওশাদ নূরী ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে ১৮ জুলাই ২০০০ সালে, ৭৫ বছর বয়সে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবি নিজের সম্বন্ধে আর নিজের যুগ সম্বন্ধে লিখেছেন-
ধর্মগ্রন্থের মতো মর্ত্যে আমার আগমন-
জ্ঞান, অভিজ্ঞান, আর প্রজ্ঞার আলোকিত প্রকাশ।
দুর্লভ পা-ুলিপি সব সামলে রেখো
ইতিহাসবেত্তার প্রয়োজনে লাগে, রেফারেন্স টোকার জন্য।
যন্ত্রণাক্লিষ্ট এ যুগের অনুচ্চারিত সকল সত্য
প্রকাশ পাবে কেবল আমার মধ্যে।
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-
সাময়িকী কবিতা
-

তিন প্রহরের শকুন
-
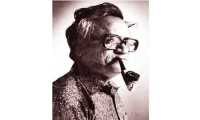
ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা
-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার
-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী
-

চরফুলের কন্যা
-
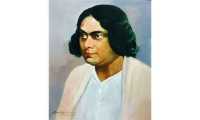
নজরুলের গল্প ও উপন্যাস