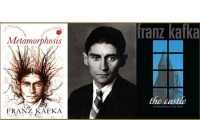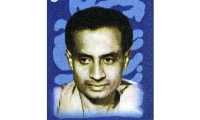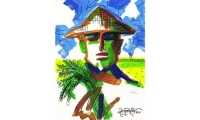সাময়িকী
জীবনানন্দ : সময়সাগরতীরে সূর্যস্রোতে নিবিড় নাবিক
সোনালি বেগম
মৃত্যুর এক বছর আগে সপরিবারে জীবনানন্দ দাশ
জীবনানন্দের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের শক্তিমান কবিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেও বলতে হবে, জীবনানন্দের তুলনা জীবনানন্দ স্বয়ং। তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক ‘নগ্ন নির্জন’ পথ। সে পথে তিনি একা এবং একক। বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব এখনও গভীর। প্রেম, ইতিহাস, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, ক্লান্তি, মৃত্যু, ইত্যাদি- এমন বহু বিষয় নিয়ে তিনি বারবার প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তর খোঁজেন। কেউ বলেন, তিনি বিষন্নতার কবি। আবার কেউ বলেন, জীবনানন্দ মানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মেলবন্ধন। কোনো কোনো সমালোচক আবার জীবনানন্দীয় কবিতাকে দুর্বোধ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনানন্দও ছিলেন স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। বুদ্ধদেব বসুর অনুভবে তিনি ‘একটি জ্বলন্ত তারা’।
রবীন্দ্রোত্তর যুগে, রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত হয়েও, ত্রিশের কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধিতার পদক্ষেপটি শুরু করেছিলেন মূলত বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রকাশে। যদিও কিছুটা রবীন্দ্রছায়া ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে। সম্পূর্ণ রবীন্দ্রছায়ামুক্ত ছিলেন জীবনানন্দ। জীবৎকালে জীবনানন্দ ছিলেন স্তিমিত ও অস্বীকৃত কবি। তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ প্রকাশে তিনিই বাংলা কবিতার সুদূরপ্রসারী কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেন। এমনকি, শতবর্ষ পেরিয়ে তাঁর প্রভা আমাদের আরও বেশি বেশি আকৃষ্ট করে চলেছে।
জীবনানন্দ-পাঠের সময় বারবার মনে হচ্ছে কবিতার অন্তর্গত স্রোতে বিকশিত চিত্রকল্পের উদ্ভাস দিয়ে বারবার আঘাত করতে করতে, আমাদের প্রথাবদ্ধ দেখার চোখটাকেই পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। এর ফলে প্রচলিত বাস্তবের ওপর যেন ঝুঁকে পড়েছিল এক ভিন্ন বাস্তব। বাইরে থেকে দেখলে এই বাস্তব দৃশ্যত নিরাকার। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো এক কল্পনামনীষার সাহায্যে এই বাস্তবকে দেখলে বোঝা যায়- বাস্তবের ভেতর অন্য এক আবছায়া পরিপ্রেক্ষিতের বাস্তব ক্রমাগত তরঙ্গায়িত হচ্ছে। বাস্তবের মধ্যেই বাস্তবের এই জন্ম-মৃত্যু বা উত্থান-পতন চলতে থেকে।
রবিন স্কেলটন তাঁর ‘পোয়েটিক প্যাটার্ন’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন- ‘Constant building up and breaking down of the image that come out of the central seed’। এর জন্য স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বান্দ্বিক চিত্রকল্পকে ধারণকৃত এক আন্তর ভাষারূপ জরুরি। আন্দ্রে ব্রেঁতো, তিনিও এই স্বপ্নের চিত্রকল্প সৃজনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মত ছিল এমন এক বাস্তব রচিত হোক, যে বাস্তবকে ইচ্ছেমতো প্রসারিত করা যায়। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় জীবনানন্দ এভাবেই building up Ges breaking down-এর সাহায্যে প্রতিটি মুহূর্তে চেনা বাস্তবকে বদলে বদলে অচেনা বাস্তবে পরিণত করেছেন। জীবানানন্দ একে বলেছেন- ‘সমন্বয়ের সেতুলোক’। যেখানে দেখা ও না-দেখা দুই বাস্তবই মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। তা আসলে গভীর অর্থে ইনার রিয়ালিটি বা ডিপার রিয়ালিটি। একথা সত্য যে এই নবতর বাস্তব ও ভাষ্যরচনায় বিশ্বাস করতেন বোদলেয়ার, এলিয়ট, র্যাঁবো, ব্রেঁতো, প্রভৃতি এবং অতি অবশ্যই জীবনানন্দ। বিশ শতকের প্রায় শুরুতে (১৮৯৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি) জন্ম জীবনানন্দের। অস্থির জীবনযাপন তাঁর। বরিশাল থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি জীবিকাগত কারণে তাঁকে নানা স্থানে আকুলভাবে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। চারদিকে যখন তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা ও প্রহেলিকা নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় ক্রমশ কুৎসিত বিতর্কের রূপ ধরেছিল, তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ‘প্রগতি’ পত্রিকায় জীবনানন্দের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি বলেছিলেন : ‘বস্তুত জীবনানন্দবাবু বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে মনে করি। তিনি এ পর্যন্ত মোটেই পপুলারিটি অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধহয় বিমুখ- অচিন্ত্যবাবুর মতো তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য Imitator জোটেনি। তার কারণ বোধহয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ; তিনি ঝড়ের মতো উড়ে এসে পাঠকের মন এক দমকায় কেড়ে নিয়ে যান না। তাঁর কবিতা একটু ধীরে সুস্থে পড়তে হয় এবং আস্তে আস্তে বুঝতে হয়।’ রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কারো সহৃদয় প্রশ্রয় জীবনানন্দ যখন পাননি, তখন সেই ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতাকে অনেকটা একাই সামলেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু।
বঙ্গদেশের দেশ কাল ধর্ম ও পুরাণের গভীর অনুরণন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। জীবনানন্দের চিত্রকল্প কখনও কখনও এতখানি জান্তব যে অনেক সময়েই ভীষণভাবে শিউরে উঠতে হয়। কবিতাকে করে তুলেছিলেন বিপন্ন বিভ্রমের যন্ত্রনাদগ্ধ স্বীকারোক্তি- ‘অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ’। অদ্ভুত আঁধারের সঙ্গে তথা সমকালীন রক্তিম বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জীবনানন্দ স্পষ্ট অনুভব করলেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের এই পৃথিবী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তৎসহ মানুষও সময়ের পঙ্কিলতায় ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে আশ্রয় চায়। এই অধঃপতিত বাস্তবের বিকল্প হিসেবে তিনি মানসভ্রমণে উপযোগী স্বপ্নজগৎ রচনায় মগ্ন হলেন। বিভ্রান্ত মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি লিখে চললেন ঝরা-পালক, ধূসর-পান্ডুলিপি, রূপসী-বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, শ্রেষ্ঠ কবিতা, বেলা-অবেলা-কালবেলা-র কবিতাগুচ্ছ।
পিকাসো যেমনটা বলেছিলেন, I attempt to reconstruct, ঠিক তেমনভাবেই জীবনানন্দও সেই একই সৃজনকর্ম করে গেছেন। তিনি বাস্তবের নৈঃশব্দ্যকে জাগ্রত রেখেছেন। কবির প্রকৃতি-তন্ময়তার ছোটো ছোটো ছবি আছে তাঁর একাধিক কবিতায়। যেমন, ‘রূপসী বাংলা’য় তিনি বলেছেন- ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/ খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/ চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে/ ভোরের দোয়েল পাখি- চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ/ জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;/ ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;/ মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে/ এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ’। প্রকৃতির অমলিন স্মৃতি যে মানুষকে এত স্মৃতিকাতর করে তুলতে পারে, এই কবিতাটি পড়ে জানতে পারা যায়। প্রকৃতি তাঁকে নতুন নতুন কবিতা লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।
জীবনানন্দের সব থেকে বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বনলতা সেন’। ‘বনলতা সেন’ কবিতায় কবি মহাজীবনের সাথে মহাপ্রেমকে মিলিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের রোমন্থনে মেতে উঠেছেন কবি। ‘নাটোরের বনলতা সেন’ এই তিনটি শব্দের মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর হৃদয়ের অনেক অপূর্ণ বাসনার কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন- ‘আমি ক্লান্ত প্রাণ এক’ অথবা, ‘যে নাবিক হাল ভেঙে হারায়েছে দিশা’, কিংবা, ‘চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন’- এই শব্দগুলি পড়লে মনে হয় যে, কবি বড্ড ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। এই কবিতার একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন :
‘সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/ সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;/ পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন/ তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;/ সব পাখি ঘরে আসে- সব নদী- ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;/ থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।’ (‘বনলতা সেন’ : বনলতা সেন)
জীবনানন্দ তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা-র ভূমিকায় লিখেছেন- ‘আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মনে নিশ্চেতনার; কারও মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরও নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য- কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হতে হয়।’
জীবনানন্দ একসময় বলেছেন, ‘মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা, আমার কাব্যে এটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খন্ড-বিখন্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক একসময় যেন থেমে যায়, একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে-ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।’
‘ধূসর পান্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের ‘বোধ’ কবিতায় কবি জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত, তার তাড়নায় তিনি একা হয়ে যান। কবিসত্তার চিরন্তন একাকিত্ব, বাংলা কবিতায় যার মূর্ততা ও বিমূর্ততার স্রষ্টা জীবনানন্দ। ‘আমার মতন কেউ নাই আর’- কবির এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। তাঁর পরাদৃষ্টির উন্মেষের ভিতর থেকেই নিঃসারিত হয়েছে অনিবার্য অন্তর্গত তাড়না। কোনো বাইরের দাবি নয়, পৃথিবীকে বোঝার চেষ্টাতেই তিনি বিচলিত- ‘নক্ষত্রে হইতেছে ক্ষয়,/ নক্ষত্রের মতন হৃদয়/ পড়িতেছে ঝরে’ (‘নির্জন সাক্ষর’ : ধূসর পান্ড্রলিপি)
কিন্তু মৃত্যু নয়, জীবনের কাছেই দ্বারস্থ কবি। শেষ পর্যন্ত জীবনে ফেরারই গাথা তাঁর কবিতা। সর্বকালীন সত্যের উন্মোচন জীবনানন্দের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই রয়েছে। দর্শন ও ইতিহাসের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অবাধ যাতায়াত তাঁর। তিনি একাধারে যেমন সুররিয়্যাল, অন্যদিকে তেমনই বিজ্ঞানমনস্ক। বাংলা কবিতার যে-সুর তিনি তৈরি করলেন, তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁকে সরাসরি আত্মস্থ করল বা করে চলেছে। সমাজকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ভাবতে চেয়েছেন: “আমি তবু বলি :/ এখন যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি/ দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস/ সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর/ নিষ্পেষিত মনুষ্যতার/ আঁধারের থেকে আনে কী ক’রে যে মহা-নীলাকাশ,/ ভাবা যাক- ভাবা যাক- / ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি/ ভেদ ক’রে শোনা যায় শুশ্রষার মতো শত-শত/ শত জলধর্নার ধ্বনি।” (হে হৃদয়, বেলা-অবেলা-কালবেলা)
আরো কিছু পংক্তি এইরকম : ‘রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;/ বাতাস ঝাড়িছে ডানা- মুক্তা ঝরে যায়’ (‘হরিণেরা’ : বনলতা সেন)। ‘সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়/ কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।’ (‘সময়ের কাছে’ : সাতটি তারার তিমির)। ‘নিবিড় নাবিক হলে ভালো হয়;/ হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।’ (‘নাবিকী’ : সাতটি তারার তিমির)। ‘সাহস সাধ স্বপ্ন’ নিয়ে যে ‘উচ্ছল প্রাণশিখা’ তিনিই কবি জীবনানন্দ ‘কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে/ ধানক্ষেতের কাছে’।
তথ্য ঋণ : ১. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, ২. প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ / শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩. জীবনানন্দ /গোপালচন্দ্র রায়, ৪. পরিচয় (শারদ সংখ্যা ২০১০), ৫. দেশ (জীবনানন্দ সংখ্যা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)
-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব
-

লোরকার দেশে
-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা
-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প
-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব
-
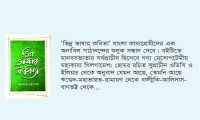
আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’
-
সাময়িকী কবিতা
-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ
-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য
-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া
-

লোরকার দেশে
-
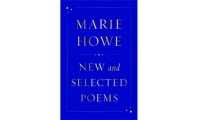
কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান
-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার
-
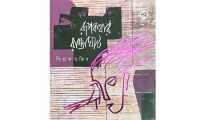
পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’
-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ
-

বাঘাডাঙা গাঁও