উপ-সম্পাদকীয়
প্রসঙ্গ কৃষি ঋণ নীতিমালা
মিহির কুমার রায়
কৃষি উৎপাদন বাড়াতে চলতি অর্থবছরে কৃষকদের ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেবে সরকারি-বেসরকারি সব বাণিজ্যিক ব্যাংক। টেকসই উন্নয়নের নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রথম ও প্রধান তিনটি লক্ষ্য তথা দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা মুক্তি এবং সুস্বাস্থ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
নীতিমালা অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্য; যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১৩ দশমিক ৬০ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরে কৃষি ঋণের লক্ষ্য ছিল ৩০ হাজার ৮১১ কোটি টাকা। এবার চাহিদা বিবেচনায় চলতি অর্থবছরে মোট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ১২ হাজার ৩০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ২১ হাজার ৯২৩ কোটি টাকা, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ১ হাজার ৪৭ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকগুলো মোট ৩২ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা অর্থবছরের মোট লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি।
কোভিড-১৯ অতিমারি পরবর্তী চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে বেড়েছে জ্বালানি তেল-গ্যাসসহ খাদ্যশস্য এবং নিত্যপণ্যের দাম। বিশ্বব্যাপী বিরাজমান মন্দাবস্থা। ২০২৩ সালে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাসহ খাদ্য সংকট দেখা দেয়ার সতর্ক বার্তাও উচ্চারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল থেকে। সেই আশঙ্কা আমলে নিয়ে বর্তমান সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। ধান-চাল-শাকসবজি-ফলমূল ও মাছ উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর হলেও গম-ভোজ্যতেল-চিনি-ডালসহ কিছু নিত্যপণ্য আমদানি করতে হয় এখনো। সরকার পর্যায়ক্রমে এসব ঘাটতিও অন্তত কমিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। ধান-চালের পাশাপাশি গম, তেলবীজ ও অন্যান্য সহযোগী ফসল উৎপাদনে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
কৃষি ও জনবান্ধব এই আবেদনের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, দেশে কৃষি ঋণ বিতরণে গতি বেড়েছে ইতোমধ্যেই। স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ পদ্ধতিও সহজ করা হয়েছে কৃষকের জন্য। এর পাশাপাশি সরকার গত বোরো মৌসুমে ধানের আবাদ ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রায় ১৭০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দিয়েছে ২৭ লাখ কৃষককে। এর আওতায় প্রত্যেক কৃষক বিঘাপ্রতি চাষের জন্য ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পেয়েছেন বিনামূল্যে। দেয়া হয়েছে কৃষি যন্ত্রের সুবিধাও।
সবাইকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কৃষকরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির জীবনীশক্তি এবং মূল চালক। করোনা অতিমারির ভয়ংকর দুর্বিপাকসহ বিভিন্ন জাতীয় অর্থনৈতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্দাবস্থা সর্বোপরি খাদ্যাভাব মোকাবিলায় দিন-রাত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা বাঁচিয়ে রেখেছেন দেশের মানুষকে। কৃষি ও কৃষকরাই নিরন্তর অবদান রেখে চলেছেন দেশের মানুষের কল্যাণে। দেশ বর্তমানে খাদ্য বিশেষ করে ধান-চাল উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য মজুতও সন্তোষজনক। ফলে, খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা নেই দেশে।
এখন প্রশ্ন উঠেছে- অর্থনীতিতে খাতওয়ারি এত বিনিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও এই ঋণের বিনিয়োগ এত কম কেন এবং জাতীয় বাজেটের আলোকে এই খাতের বরাদ্দ অগ্রাধিকার তালিকায় আসে না কেন? সাম্প্রতিক এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, দেশের ৬১টি ব্যাংকের প্রায় ১০ হাজার শাখার অর্ধেকেরই বেশি গ্রামাঞ্চলে, যাদের কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দিতে অনীহা রয়েছে। সরকারি এক হিসাবে দেখা যায়, গ্রামে ঋণ গ্রহনকারী কৃষক পরিবারের শতকরা ৭৫ ভাগই চড়া সুদে ২০ থেকে ৩০ শতকরা হারে ঋণ নিয়েছে এনজিওদের কাছ থেকে।
ব্যাংকগুলো কাগজে-কলমে গ্রামীণ শাখা খুললেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো শহরের মতো গ্রামীণ মানুষের বাণিজ্য, শিল্প ও ভোক্তা ঋণ বিতরণ করছে। সরকারি এক হিসাবে বলা হয়েছে- দেশে প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে যাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ; যা সংখ্যায় ৬৫ লাখ মাত্র; যাদের মধ্যে ৫০ লাখ ঋণ নিয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এনজিও থেকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মতে, দেশের ৪১ লাখ গ্রামের পরিবার ঋণের জন্য ব্যাংকে আবেদন করলেও সফল হতে পারেনি এবং এর কারণ হিসাবে ব্যাংকের অনীহা ও প্রচারের অভাবকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এরপরও ঋণ প্রক্রিযায় জটিলতা, পদ্ধতিতে ত্রুটি ও অলিখিত লেনদেন খরচ ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাওয়ায় কৃষক আর এই কৃষ্টির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারছে না, অথচ কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন বিকেবি ও রাকাব রয়েছে। তাছাড়াও অন্য ব্যাংকগুলোর জন্য মোট ঋণের কমপক্ষে ৫ শতাংশ কৃষি খাতে দেয়ার বাধ্য বাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পকে দেয়া ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এ নিয়ম পরিচালনা হয়েছে বলে দেখায়। বর্তমানে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের উপরে সুদহার নির্ধারণ করে দিয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু ব্যাংকগুলো একে লাভজনক বলে মনে করে না বিধায় ব্যাংকগুলো এজেন্সি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এনজিওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করায় কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর ব্যাংকগুলো লাভবান হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, কৃষি ঋণ অকৃষি খাতে ব্যবহৃত হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে; যেখানে প্রকৃত কৃষকেরা ঋণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, যা তদারকির মাধ্যমে বন্ধ করার দাবি উঠছে। মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) এক প্রবিবেদনে বলা হয়েছে এনজিওগুলো থেকে যে কৃষি ঋণ বিতরণ হচ্ছে তার বেশিরভাগ কৃষি কাজে ব্যয়িত না হয়ে অন্য খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার বিবিএসের তথ্যমতে, মাত্র ১১ শতাংশ কৃষক তাদের ঋণের অর্থ কৃষি কাজে ব্যবহার করছে। আবার গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ঋণের অর্থ ব্যয় করছে প্রায় ৩৮ শতাংশ কৃষক পরিবার। এই তো গেল সনাতনী কায়দায় কৃষি ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়ন ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত রোজনামচা। এর একটি সংস্কার এখন সময়ের দাবি। কারণ ঋণের যে গ্রতিপ্রবাহ যা কর্মসূচি ভিত্তি ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে; তা দিয়ে পরিবারতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার হয়ত কিছুটা উপকার আসবে; কিন্তু কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে কিংবা কৃষির আধুনিকায়নে তেমন কোন অবদান রাখার সুযোগ নেই বলেই প্রতীয়মান হয়। একদিকে জমির স্বল্পতা অপরদিকে জনসংখ্যার চাপে প্রতি বছর এক শতাংশ হারে কৃষি জমি কমে যাওযার কারণে আধুনিক পদ্ধতিতে নিবিড় চাষ ছাড়া কোনভাবে কৃষিজাত পণ্যের বর্ধিত উৎপাদন ধরে রাখা সম্ভব নয়।
কৃষি নীতিমালায় কর্মসূচিভিত্তিক কৃষি ঋণের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতি নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়। এ পর্যায়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে শস্য কিংবা শাকসবজি চাষের পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তা মোকাবেলায় পরিবারভিত্তিক খামার বিন্যাসের পরিবর্তে ব্যবসায়িকভিত্তিক আধুনিক খামার কিংবা শস্যপর্যায়ের দিকে এগোতে হবে। আধুনিক কৃষক সৃষ্টির মাধ্যমে আগামী দিনের কৃষি উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে হবে; যার মধ্যে প্রথম প্রয়োজন হবে ঋণের পরিবর্তে বিনিয়োগ, যাকে বলা হবে কৃষি বিনিয়োগ নীতি। এর আওতায় গ্রিনহাউসভিত্তিক শস্য ও শাকসবজি উৎপাদন স্কিম গ্রহণ করতে হবে; যা হবে সারা বছরভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম অর্থাৎ সারা বছর সব জাতের সবজি পাওয়া যাবে। এজন্য সনাতনী কায়দায় মৌসুমভিত্তিক সবজি লোপ পাবে। এতে কৃষিপণ্য, শস্য সবজি ব্যবসা জমজমাট হবে, পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে, ফসল আমদানি কমবে, রফতানি বাড়বে ও দেশ সমৃদ্ধির দিকে যাবে। এই নতুন শস্য ব্যবস্থাপনার কথা বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত কৃষি ঋণ নীতিতে নেই, অথচ যেগুলো থাকার প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নতুন নতুন কৃষি উদ্যোক্তা প্রকল্প তৈরি হতে পারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।
দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হলো কৃষি ঋণ নীতিতে শতকরা ১০ ভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে, যার পেছনে ইলিশ মাছের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশের মোট জিডিপির ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপির ২৫.৩ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। দেশে নিরূপিত মাছের চাহিদা ৩৯.৯২ লাখ টনের বিপরীতে উৎপাদন হচ্ছে ৪১.৩৮ লাখ টন, যাকে বলা হয় মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে চলেছে মৎস্য বিজ্ঞানীরা এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্য বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির ১৮টি মাছের পোনা উৎপাদন করছে বিজ্ঞানীরা।
এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশের মাছ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪১.৩৪ লাখ মেট্রিক টন। দেশের মৎস্যচাষীরা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত জাতগুলো সঠিকভাবে চাষ করে দেশের মৎস্য খাতকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করছে সত্যি, কিন্তু মাছের খাবারের মূল্য ও পুকুর সেচসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্বালানির অর্থ জোগান করতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় তা শতকরা দশ ভাগ কৃষি ঋণ দিয়ে পোষাচ্ছে না। এ বিষয়টিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষভাবে মনোযোগী হবে- বিশেষত কৃষি ঋণ নীতিমালা তৈরিতে।
[লেখক : অধ্যাপক, সিটি ইউনিভার্সিটি]
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
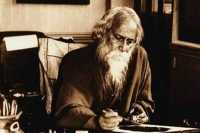
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম
-
রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়
-
মে দিবসের চেতনা বনাম বাস্তবতা
-
শ্রম আইন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই আন্তরিকতা
-
বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা কেন এত পিছিয়ে
-
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল : নিরাপদ যাত্রার প্রত্যাশা
-
কর ফাঁকি : অর্থনীতির জন্য এক অশনি সংকেত
-
১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় : উপকূলীয় সুরক্ষার শিক্ষা
-
যখন নদীগুলো অস্ত্র হয়ে ওঠে
-
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবন
-
বজ্রপাত ও তালগাছ : প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা
-
কুষ্ঠ ও বৈষম্য : মানবাধিকারের প্রশ্নে একটি অবহেলিত অধ্যায়
-

প্রান্তজনের বাংলাদেশ
-
অতীতের ছায়ায় নতুন বাংলাদেশ : দুর্নীতি, উগ্রপন্থা ও সরকারের দায়
-
সাইবার নিরাপত্তা : অদৃশ্য যুদ্ধের সামনে আমাদের প্রস্তুতি








