উপ-সম্পাদকীয়
উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি
মিহির কুমার রায়
গত ২৬ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৪। গতবার এই হার ছিল ৮৪ দশমিক ৯৫। সেই হিসাবে এবার পাসের হার ৭.৩১ শতাংশ কমেছে।
করোনাকালীন পিছিয়ে পড়া লেখাপড়ার সমন্বয় করতে সিলেবাস কমিয়ে ছোট করা হয়। সেই স্বল্প সিলেবাসের এটিই প্রথম পরীক্ষা। তবে ফল বিশেষত গত তিন বছরের তুলনায় পাসের হারের দিক থেকে নিম্নমুখী; যা একটি শুভ লক্ষণই বলে মনে করছেন শিক্ষা গবেষকরা। কারণ পরীক্ষা দিলেই এ+ এ কৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসার এটাই প্রকৃষ্ঠ সময় যা একটি গুণগত পরিবর্তনও বটে!
দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ইংরেজি বিষয়কে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। অথচ ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, এ বিষয়েই সর্বাধিক ছাত্রছাত্রী ফেল করছে। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলেও সে চিত্র ফুটে উঠেছে। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে বিষয়ভিত্তিক পাসের হার সবচেয়ে বেশি বাংলায়, ৯৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আর সবচেয়ে কম ইংরেজিতে, ৮২ দশমিক ৭৩ শতাংশ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইসিটি ও পদার্থবিজ্ঞানে ৯২ দশমিক ৪৬, রসায়নে ৯২ দশমিক শূন্য ৭, অ্যাকাউন্টিংয়ে ৮৪ দশমিক ৯৬ ও পৌরনীতিতে গড় পাসের হার ৯৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। বিগত কয়েক বছরের ফলাফল তুলনা করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা প্রায় প্রতি বছরই অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইংরেজিতে খারাপ ফলাফল করেছে। তবে গত দুই বছর সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হওয়া পরীক্ষায় পাসের হার কিছুটা বেড়েছিল। এর আগে সর্বশেষ ২০১৯ সালে ইংরেজিতে পূর্ণ নম্বরেই পরীক্ষা দেয় শিক্ষার্থীরা। ওই বছর সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে বিষয়টিতে গড় পাসের হার ছিল প্রায় ৯১ শতাংশ, যা এবারের চেয়ে প্রায় ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের ইংরেজি-ভীতি, শিখন পদ্ধতির জটিলতা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব এবং করোনাকালীন শিখন ঘাটতিই শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে খারাপ ফলাফলের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন উইং থেকে করা সমীক্ষায় বা জরিপেও বিষয়টি উঠে এসেছে। তাতে দেখা যায়, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে ভীষণ দুর্বলতা নিয়ে মাধ্যমিকের গন্ডি পার হচ্ছে। আবার এ বিষয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে করা জরিপে দেখা যায়, তাদের অবস্থাও করুণ। ব্যানবেইসের তথ্য বলছে, দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের ৮০ শতাংশেরই নেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ফলাফল অস্বস্তি দিলেও মূল প্রতিযোগিতা শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায়।
এবার ৯২ হাজার ৩৬৫ জন শীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এই বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থী দেশের ৫৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ হাজার আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য লড়বেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীন ৮৮১টি কলেজে স্নাতকে ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৮৫টি আসন রয়েছে, আবার দেশের সরকারি নতুন পুরাতন মিলে ৩০টিরও বেশি মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেগুলোতে ভর্তির আসন সংখ্যা ৫ হাজারের কাছাকাছি রয়েছে। যেখানে ভর্তিযুদ্ধ খুবই প্রতিযোগীতামূলক বিশেষত সেরা ছাত্রদের মধ্যে। যারা সরকারি কাঠামোতে ভর্তির স্থান করে নিতে পারবে না তারাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে ১০৮টি) ও বেসরকারি কলেজগুলোতে ভর্তিন জন্য আসবে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কষ্টকর বটে!
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ভর্তি যোগ্যতা ও নিয়মের বলয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয় যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে একক কোনো নিয়ম না থাকায়। ফলে কাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে হলে নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের কাঠামো ঘিরে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিতে হয়। তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ এসব ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরে মাত্র ০. ১ পার্থক্য থাকলেই কেউ সুযোগ পাচ্ছেন আবার কেউ অকৃতকার্য হচ্ছেন। আবার দেখা যায়, এসব ভর্তি পরীক্ষায় টিকে যাওয়া শিক্ষার্থীরা মূল পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর চেয়ে কম নম্বর পেয়েও মেধাক্রম স্কোরকে এগিয়ে নেন। দেখা যায় যে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার স্কোরে যোগ হচ্ছে। ফলে কম জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থী মূল ভর্তি পরীক্ষায় অনেক সময় বেশি নম্বর পেয়েও মেধা স্কোরে টিকতে পারছেন না। কিন্তু কেন এই নিয়ম, তার সুনির্দিষ্ট সন্তেষজনক ব্যাখ্যা নেউ দেয় নি। বরং এসব জিপিএ স্কোর থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটি নির্দিষ্ট গ্রুপকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে। বিশ বছর আগেও যেখানে জিপিএ-৫ পাঁচ হাজারের ঘরে থাকত, সেটি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ঘরে ঘরে জিপিএ-৫ এ ঠেকছে, যা দেশের শিক্ষার মানকে সংকুচিতই করছে না, বরং রাষ্ট্রকে ভুল পথে পরিচালিত করার প্রয়াস জোগাচ্ছে।
জিপিএ-৫ যে বা যাহারা মেধার মানদন্ড মনে করছেন, তারা হয়তো জানেন না- এই জিপিএ-৫ পাওয়া মানেই মেধাবী নয়, এটি কেবল একটি নির্দেশক হতে পারে, সেটি কিছুতেই একজন শিক্ষার্থীর মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম হতে পারে না। সৃজনশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী শিক্ষার্থী গড়ায় নজর না দিয়ে কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন আয়ত্ত করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে জিপিএ-৫ বাগিয়ে নেয়া গেলেও আমাদের শিক্ষার্থীরা কতা কম জানেন, তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন থাকছে, তেমনি দেশের বাইরে যখন উচ্চশিক্ষায় আসছেন তখন তারা ঠিকই টের পাচ্ছেন।
বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় পূর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত জিপিএ মূল ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরে বিবেচনায় নেয় না অতছ বাংলাদেশে এই নিয়ম চালু রখেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেউ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেনি। এর মধ্য দিয়ে দেশে এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সুবিধা দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে বঞ্চিত হচ্ছে কম জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথচ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিযোগিতা করার অধিকার সব শিক্ষার্থীদের হওয়া উচিত, প্রকৃত মেধাবীদের বের করে আনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিক। তারা যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে, সেই প্রতিযোগিতার আরও একটু আধুনিকায়নের সুযোগ নিক।
করোনা মহামারির পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শ্রেণীকক্ষের মূল্যায়ন, অবিরত মূল্যায়ন বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। দেশের শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি পুরো ব্যবস্থা অবিরত মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য প্রস্তুত করতে হবে, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে যাতে বাস্তবধর্মী পরীক্ষা নেয়া হয়, সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীরা বহুদিন যাবৎ প্রকৃত লেখপড়ার সঙ্গে সেভাবে সংযুক্ত নেই। পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল অর্জন করার মধ্যে যে আনন্দ উচ্ছশিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি যাতে বহাল থাকে সেদিকে সবার দৃষ্টি দিতে হবে। পাসের হারে এক বোর্ড থেকে আরেক বোর্ডের এগিয়ে থাকা কিংবা পিছিয়ে যাওয়ার কারণ কোন বছরেই খতিয়ে দেখা হয় না যা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে প্রতিটি বোর্ডেই এজন্য একটি গবেষণা সেল থাকা উচিত।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তবে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ সবাই শিক্ষার্থীকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন দেয়া সম্ভব হয় না। বরাদ্দ আসনের প্রতিটির জন্য একাধিক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষামূলক বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এতে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীরা পছন্দের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলেও বাকিদের জাতীয় অথবা বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া যথেষ্ট ব্যয়বহুল। সবার পক্ষে তা চালানো সম্ভব হয় না। অবশ্য দেশে কারিগরি খাতে শিক্ষাগ্রহণের অনেক সুযোগ রয়েছে। তবে বিভিন্ন কারণে কারিগরি শিক্ষা পিছিয়ে আছে। শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কেউই এই শিক্ষায় খুব আগ্রহী নয়। খানিকটা মান উন্নয়নের মাধ্যমে এই খাতকে সমৃদ্ধ করতে পারলে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিক্ষা ও কর্ম জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে।
উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী এই সময়ে শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং অভিভাবকদের উচিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পাশাপাশি সরকারি পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য হরতাল-অবরোধ প্রতিরোধসহ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। উচ্চশিক্ষা উন্মুক্ত রাখা উচিত কেবলমাত্র মেধাবীদের জন্য এবং অন্যদের জন্য কারিগরি-উদ্যোক্তা উন্নয়নে শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া উচিত।
[লেখক : ডিন, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা]
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
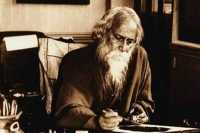
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম
-
রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়
-
মে দিবসের চেতনা বনাম বাস্তবতা
-
শ্রম আইন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই আন্তরিকতা
-
বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা কেন এত পিছিয়ে
-
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল : নিরাপদ যাত্রার প্রত্যাশা
-
কর ফাঁকি : অর্থনীতির জন্য এক অশনি সংকেত
-
১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় : উপকূলীয় সুরক্ষার শিক্ষা
-
যখন নদীগুলো অস্ত্র হয়ে ওঠে
-
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবন
-
বজ্রপাত ও তালগাছ : প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা
-
কুষ্ঠ ও বৈষম্য : মানবাধিকারের প্রশ্নে একটি অবহেলিত অধ্যায়
-

প্রান্তজনের বাংলাদেশ
-
অতীতের ছায়ায় নতুন বাংলাদেশ : দুর্নীতি, উগ্রপন্থা ও সরকারের দায়
-
সাইবার নিরাপত্তা : অদৃশ্য যুদ্ধের সামনে আমাদের প্রস্তুতি








