উপ-সম্পাদকীয়
জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের মনস্তত্ত্ব
নুসরাত জাহান পন্নি
দিনকে দিন জলবায়ু পরিবর্তন একেকটা নতুন মাত্রা লাভ করছে। ২০২৩ সালকে তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের রেকর্ড ভাঙার বছর বলা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা শেষ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে নিজেদের এরকম বৈরী পরিবেশে মানিয়ে চলেছি। এর পেছনে কাজ করছে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক দিক। সেগুলোর দিকেই আজকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্রান্থাম রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২০২২ সালের অক্টোবরে ‘অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ ইকোনমিকস’ নামে একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ৪৬ শতাংশ বেড়েছে। গবেষণাটিতে মূলত ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপরে আঘাত হানা দুর্যোগগুলোর তথ্য নেয়া হয়েছে। তবে গবেষকদের মতে, পরবর্তী সময়ে সংঘটিত আবহাওয়ার বিপদের তথ্যগুলো যোগ করলে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বৃদ্ধির হার আরও বাড়বে। এক্ষেত্রে আবার বিশ্ব আবহাওয়া বিষয়ক সংস্থা ডব্লিউএমও আরও এক কাঠি এগিয়ে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের চেয়েও ২০২৪ সালের আবহাওয়া আরও ভয়ংকর ও চরমভাবাপন্ন আচরণ করতে পারে। এতে বিশ্বজুড়ে দুর্যোগের বিপদ তো বটেই, রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাবও বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে দেশে ৫ মাত্রার উপরে মোট ছয়টি ভূমিকম্প আঘাত করেছে। এর আগে ২০২২ সালে মাঝারি মাত্রার বা রিখটার স্কেলে ৫-এর উপরে মোট তিনটি ভূমিকম্প হয়। অথচ ১৯৭২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যে কটি ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে মাঝারি মাত্রার কম্পনের ঘটনা ঘটেছে প্রতি দুই থেকে চার বছরে একবার। আর ২০২৩ সালে ৪ থেকে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে মোট ৪৮টি। নিয়মিত ওই কম্পন রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে মনে করেন তারা।
ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইআইইডি) একটি গবেষণার বরাত দিয়ে গত বছরের মাঝামাঝি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ র্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রায় ৪৩ শতাংশ গ্রামীণ বসতি বন্যার কবলে পড়ে। আর প্রায় ৪১ শতাংশ বসতি ঝড়ের আঘাতের শিকার হয়।
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ র্যাপোর্টিয়ারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সব ধরনের দুর্যোগ বাড়ছে। বিশেষ করে বজ্রপাত ও তাপপ্রবাহের মতো নতুন ধরনের বিপদ দ্রুত বেড়ে ক্ষতি ও জীবনহানি বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন প্রথম আলোর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ দাবদাহ, বজ্রপাত ও শৈত্যপ্রবাহের মতো দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগের কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে প্রায় তিন মিটার উঁচুতে থাকা হাওর এলাকায় কয়েক বছর পরপর হঠাৎ বন্যা হয়। এর বাইরে খরা ও উপকূলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার সমস্যাও বাড়ছে। খুলনা এলাকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র এক মিটার উঁচুতে হওয়ায় ঝড়বৃষ্টি হলে সেখানে জোয়ারের পানি উঠে যায়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বেড়ে গেছে। প্রতি বছর তিন শতাধিক মানুষ বজ্রপাতে মারা যান। নতুন এ দুর্যোগ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বাংলাদেশে অবনতি হচ্ছে দাবদাহ পরিস্থিতিরও। গত বছর, মানে ২০২২ সালটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম উষ্ণ বছর ছিল।
প্রত্যেকটা প্রাণীই নিজের সবটুকু দিয়ে বেচে থাকতে চায়। মানুষও এর ব্যতিক্রম না। সেজন্য আমরা কৌশল অবলম্বন করি। এমনকি বারবার পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও। এর বেশির ভাগ দিকটাই মনস্তাত্ত্বিক। আমেরিকার বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য ও সমাজকর্মী লাপরিশা বেরি ড্যানিয়েলের মতে, আমরা মূলত তিনটি ধাপে মানসিকভাবে নিজেদের প্রস্তুত করি। এটাকে বলা হয় ট্রিপল এ।
প্রথমেই আসে অ্যাকসেপ্টেন্স বা স্বীকারোক্তি। আমরা প্রথমেই এটা মেনে নেই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে সেটা অনেক বেশি অস্বাভাবিক কিছু না। এটা ঘটবেই। এটা আমাদেরই কর্মের ফল। এই ধাপটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করি। পাশাপাশি, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ঠিক করি যাতে যে কোন ধরনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।
দ্বিতীয়ত, এইড বা সাহায্য। আমরা একা কখনোই কোন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নই। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এই মূলমন্ত্র অনুধাবন করেই আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি। তারই সূত্র ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আমাদের একটা কমিউনিটি তৈরি করতে হবে যা আমরা সব সময়ই করে থাকি। এর মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগে পরস্পরকে সাহায্য করার মন-মানসিকতা বহাল থাকে। এর উদাহরণ আমরা সব জায়গায় দেখতে পাই। যখন উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ভাঙতে শুরু হয় তখন পুরো গ্রামবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টার নজির অহরহ দেখতে পাওয়া যায় আমাদের মতো নদীমাতৃক দেশে।
আর সর্বশেষ হলো এডাপটেশন বা অধিগ্রহণ। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা। যেমন আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে বন্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্যাসহিষ্ণু ফসল উদ্ভাবন, খরাপ্রবণ এলাকার জন্য খরাসহিষ্ণু ফসল উদ্ভাবন ইত্যাদি।
এই ধাপগুলো অনুসরণ করেই মূলত আমাদের পূর্বপুরুষরা নানা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে ছিলেন। একইরকম ধারা অব্যাহত আছে আমাদের মাঝেও এবং টিকে থাকবে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের মনস্তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। তবে এই প্রাথমিক ধাপগুলো অনুসরণ করে আমরা যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে পারি।
[লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]
-
প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন
-
গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
-
টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি
-
রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা
-
রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...
-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক
-
জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা
-
টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং
-
ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়
-
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট
-
আসামি এখন নির্বাচন কমিশন
-
কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?
-
এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?
-
মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
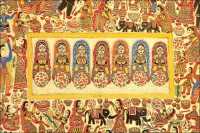
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?








